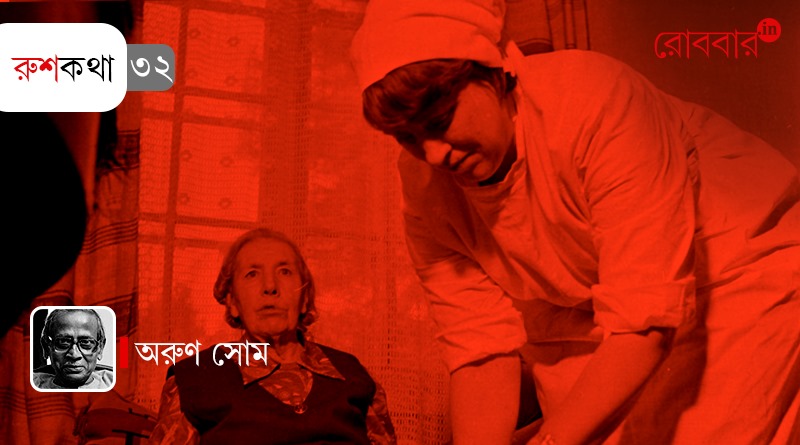
মহিলাদের কিছুকাল অন্তর অন্তর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাটাও ছিল বাধ্যতামূলক। অনেক সময় রোগীকে ধরপাকড় করেও হাসপাতালে ভর্তি করে দেওয়া হত। ঠিক এমনটাই এক সময় আমার স্ত্রীর ক্ষেত্রে হয়েছিল। ১৯৯০ সালের গোড়ার দিকে ডাক্তারি পরীক্ষায় দেখা গিয়েছিল আমার স্ত্রীর দেহে একটি অস্ত্রোপচার অত্যাবশ্যক। কিন্তু অস্ত্রোপচারে সে কিছুতেই রাজি নয়। স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে অনেকবার তাড়া দেওয়া সত্ত্বেও সে এড়িয়ে যেতে লাগল। দু’বছর তার পিছনে লেগে থেকে স্বাস্থ্যকেন্দ্র তাকে হাসপাতালে জোরজবরদস্তি ভর্তি করিয়ে সেই অপারেশন করিয়ে ছাড়ল। দেখা গেল সময় মতো অপারেশন না করলে বিপদই ঘটত।

৩২.
নাক-কান কাটা গেলেও আস্থা হারাইনি
মস্কোয় সে বছরই (১৯৭৮) শীতকালে আমার নাক কাটা গেল। পরে অবশ্য এক সময় একে একে নাক-কান দুইই কাটা যায়। সেসবই হয় শল্য চিকিৎসকের হাতে পড়ে। তাতে অবশ্য আমার ভালো বই মন্দ হয়নি। তাছাড়া এর ফলে সোভিয়েত স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গেও আমার প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সুযোগ ঘটে।
এ দেশে প্রসূতিসদন থেকে নবজাত শিশু ও প্রসূতিকে ছেড়ে দেওয়ার পরও স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে বেশ কয়েক মাস ধরে নিয়মিত একজন চিকিৎসক বাড়িতে এসে তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে যান। এটা ছিল এখানকার জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। আরও অনেক সামাজিক ব্যবস্থার মতোই প্রসূতি এবং চিকিৎসক উভয়ের ক্ষেত্রেই বাধ্যতামূলক। তাই গরম জলের অভাবে প্রসূতিভবনের পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর হয়ে পড়ার দরুন প্রসূতি ও সদ্যোজাত শিশুকে তাড়াহুড়ো করে ছেড়ে দেওয়া হলেও বাড়িতে চিকিৎসক এসে নিয়মিত দেখাশোনা করে যেতে লাগলেন।

তিনিই শিশুর শরীরে একটি বিষফোড়া আবিষ্কার করলেন। যথারীতি তার চিকিৎসাও শুরু হয়ে গেল; এবেলা-ওবেলা ইঞ্জেকশন চলতে লাগল। শিশু বিপন্মুক্ত হল ঠিকই, কিন্তু ঘরের উষ্ণ পরিবেশে রোগ-জীবাণু সংক্রমণের আকার ধারণ করল। আমার নাকের ভেতরে একটা বিষফোড়া দেখা দিল। প্রথমে তেমন আমল না দিয়ে ডাক্তারে শরণাপন্ন না হয়ে চিরাচরিত ঘরোয়া পদ্ধতিতে চিকিৎসা চালিয়ে যেতে লাগলাম, কিন্তু হিতে বিপরীত হল, এক সময় ফোড়ার মুখ ছিঁড়ে গিয়ে পরিস্থিতি বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াল– অসহনীয় যন্ত্রণার সঙ্গে হাড় কাঁপিয়ে জ্বর এল। পরের দিন রাত ১২টার সময় যখন আমার প্রায় বেহুঁশ অবস্থা, তখন আমার সমস্ত ওজর আপত্তি উপেক্ষা করে আমার স্ত্রী ফোন করে অ্যাম্বুলেন্স ডেকে পাঠাল। এই পরিষেবাটিরও তৎপরতার পরিচয় পেয়ে আমি একাধিকবার চমৎকৃত হয়েছি। মিনিট পনেরোর মধ্যে প্রাথমিক পরীক্ষার যাবতীয় সরঞ্জাম-সহ অ্যাম্বুলেন্স করে চিকিৎসক এসে হাজির। অবস্থার আরও অবনতি ঘটতে পারে এই আশঙ্কায় ডাক্তার আমাকে সেই হাড়হিম করা ঠান্ডার মধ্যে মাঝরাতেই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া সমীচীন বোধ করলেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্য আরও অনেক নাগরিক পরিষেবার মতো তার চিকিৎসা-ব্যবস্থাও ছিল অবৈতনিক এবং অনেকটা যেন পুলিশি ব্যবস্থার মতোই জোরজবরদস্তি করে চাপিয়ে দেওয়া। ডাক্তারের কথায় আপত্তি করার সুযোগ নেই। এমনকী, ১৯৯১ সালেও সোভিয়েত দেশটাই যখন ভেঙে যায় তার বেশ কিছুকাল পর পর্যন্ত এই ব্যবস্থাটা মোটামুটি চালু ছিল।

মহিলাদের কিছুকাল অন্তর অন্তর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাটাও ছিল বাধ্যতামূলক। অনেক সময় রোগীকে ধরপাকড় করেও হাসপাতালে ভর্তি করে দেওয়া হত। ঠিক এমনটাই এক সময় আমার স্ত্রীর ক্ষেত্রে হয়েছিল। ১৯৯০ সালের গোড়ার দিকে ডাক্তারি পরীক্ষায় দেখা গিয়েছিল আমার স্ত্রীর দেহে একটি অস্ত্রোপচার অত্যাবশ্যক। কিন্তু অস্ত্রোপচারে সে কিছুতেই রাজি নয়। স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে অনেকবার তাড়া দেওয়া সত্ত্বেও সে এড়িয়ে যেতে লাগল। দু’বছর তার পিছনে লেগে থেকে স্বাস্থ্যকেন্দ্র তাকে হাসপাতালে জোরজবরদস্তি ভর্তি করিয়ে সেই অপারেশন করিয়ে ছাড়ল। দেখা গেল সময় মতো অপারেশন না করলে বিপদই ঘটত। আমার ক্ষেত্রেও সেদিন অনেকটাই সেরকম হয়েছিল– আরও কয়েক ঘণ্টা গড়িমসি করলে নাকি প্রাণসংশয় দেখা দিত। নাক কাটা যাওয়ার মতো কান কাটা যাওয়ার ঘটনাটাও এদেশের অবৈতনিক আর উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার আরও একটি দৃষ্টান্তস্থল হতে পারে।
কান নিয়ে সমস্যাটা দেখা দিয়েছিল ১৯৮০ সালের কাছাকাছি কোনও এক সময়। আমার শ্রবণশক্তি ধীরে ধীরে হ্রাস পেয়ে যাচ্ছিল। এই অবস্থায় স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরীক্ষার জন্য যেতে বিশদ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যা করণীয় তার জন্য সুপারিশ করে সেখান থেকে আমাকে মস্কোর কেন্দ্রীয় হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হল– আগেরবারের মতো এবারেও সেই বোত্কিন হাসপাতালে। প্রথমবারের অভিজ্ঞতাটা হয়েছিল শীতকালে, এবারেরটা গ্রীষ্মকালে।
হাসপাতালের চত্বরটা যে এত বিশাল এর আগে শীতকালে আসার দরুন তা তেমন বোঝার অবকাশ পাইনি। চারধার এক পাক ঘুরে আসতেই কমপক্ষে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় লেগে যায়। সর্বত্র সবুজের সমারোহ, প্রাচীরের গায়ে অনেক জায়গায় সুন্দর করে ছাঁটা গাছপালা আর লতাপাতার ঝোপঝাড়। জায়গায় জায়গায় বসার বেঞ্চও আছে। রোগীদের মধ্যে যাদের সাধ্য আছে, তারা অনেকেই চত্বরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ প্রাতঃকালীন ভ্রমণরত, কেউ কেউ বেঞ্চে বসে গল্পগুজব করছে। এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বিভিন্ন ওয়ার্ড। হাঁটাহাঁটির সময় পাশের বিশাল রন্ধনশালা থেকে ক্ষুধা উদ্রেককারী খাবারের সুঘ্রাণ নাকে এসে লাগছে। মোটকথা, পরিবেশটা আগের বারের মতো ভীতিকর আদৌ মনে হচ্ছিল না।
পরীক্ষানিরীক্ষার পর আমার রোগ নির্ণয় করলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যতম খ্যাতনামা কর্ণ রোগ বিশেষজ্ঞ সূক্ষ্ম শল্যচিকিৎসক প্রফেসর রাদুগিন। আমার কানের শল্যচিকিৎসা তিনিই করেন। প্রফেসরের বয়স তখনই সত্তর পেরিয়ে গেছে; কিন্তু সারা সোভিয়েত ইউনিয়নে চিকিৎসক হিসেবে তাঁর জুড়ি মেলা ভার: বিমানে করে সারা দেশ ঘুরে ঘুরে তিনি চিকিৎসা করে বেড়াচ্ছেন– কখনও মধ্য এশিয়ার উজবেকিস্তানের কোথাও, কখনও রাজধানী মস্কোয়, কখনও বা সুদূর সাইবেরিয়ার কোথাও। অথচ আমার অভিজ্ঞতায় তাঁকে ধরাছোঁয়ার বাইরে বলে একবারও মনে হয়নি, কথা দিয়ে সাক্ষাতের খেলাপ করতে তাঁকে কখনও দেখিনি। পরে তাঁরই মুখে শুনেছি, সাইবেরিয়ার কোনও এক অঞ্চলের মানুষ তিনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পড়াশোনার পাট সাময়িকভাবে স্থগিত রেখে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে ফ্রন্টে লড়াই করেছেন, ফিরে এসে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি আমাকে পরামর্শ দিলেন যেহেতু আমার নাকের হাড় খানিকটা বাঁকা তাই আগে ছোটখাটো একটা অপারেশনের সাহায্যে সেটা সিধে করা দরকার, তা নইলে সঠিক শল্য চিকিৎসার পরও কানের ওই সমস্যা আবারও দেখা দিতে পারে। সেই প্রাথমিক চিকিৎসার ভার তিনি তাঁর এক তরুণী ছাত্রীকে দিয়ে অপারেশনের মাসখানেক বাদে আমাকে তাঁর চেম্বারে গিয়ে আবার দেখা করতে বললেন। রাজি না হয়ে উপায়ই বা কী?
তাছাড়া সেই সুন্দরী ডাক্তারের রূপে আমি তখন মুগ্ধ, কিন্তু সুন্দরী যে কত নিষ্ঠুর হতে পারেন, সে ধারণা তখন আমার ছিল না।
প্রসঙ্গত, এদেশের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির সাধারণ ডাক্তাররা অধিকাংশই মহিলা। তারা যখন রোগীর স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য অম্লান বদনে তার গাত্রাবাস খুলতে বলে, তখন আমাদের মতো রোগীদের বেশ অস্বস্তিতে পড়তে হয়। তাছাড়া ইঞ্জেকশনগুলিও দেওয়া হয় সাধারণত পশ্চাদ্দেশে– দেন সিস্টাররা, তাও অল্প মাত্রায় বারবার করে। সেও কী বিড়ম্বনা! ইঞ্জেকশনের গুঁতোয় না যায় শোওয়া, না যায় বসা। তখন আবার ঘর গরম করার ব্যাটারির গায়ে ঠেস দিয়ে সেঁক নিতে হয়। যা হোক, ভর্তি তো হলাম, কিন্তু ঠিক সেই সময় হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারে বড় রকমের মেরামতি চলছিল, তাই ছোটখাটো অপারেশন পাশের একটা ছোট ঘরে করা হচ্ছিল। সেখানে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ছাড়া আসবাব বলতে কয়েকটি চেয়ার আর ছোটখাটো একটা টেবিল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলাম না। ওরকম একটা চেয়ারে আমাকে বসিয়ে দিয়ে সিস্টার আমার নাকের ভেতরে হাড়ের কাছাকাছি কোনও এক জায়গায় ইঞ্জেকশনের ছুঁচ বিঁধিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ বাদে আমার হাতে একখানা পাত্র ধরিয়ে দিয়ে সেটাকে তিনি আমার বুকের কাছাকাছি জায়গায় ধরে রাখতে বললেন।
আরও খানিকটা সময় বাদে নাকের অনুভূতি একেবারে অসাড় হয়ে এলে ডাক্তার শুরু করে দিলেন তাঁর আসুরিক চিকিৎসা। ডাক্তারের হাতে একটা ছোট্ট নরুন জাতীয় অস্ত্র– তিনি সেটাকে আমার নাকের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে সেখানে খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করে দিলেন। এদিকে সিস্টারও হাতুড়ি ধরনের ছোট্ট একটা অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছেন। ডাক্তারের নির্দেশে মাঝে মাঝে তাই দিয়ে নরুনটার মাথায় ঘা মারছেন, সঙ্গে সঙ্গে চাঁছা হাড়ের কিছু ছিলকে আর সেই সঙ্গে গলগল করে রক্ত আমার হাতের ধরা পাত্রে এসে পড়ছে। খাসা ব্যবস্থা। আমার মনে হচ্ছিল আমি বোধহয় সত্যি সত্যি নাকের বদলে নরুন পেতে চলেছি আর টাক ডুমা ডুম বাজনার বদলে থেকে থেকে হাতুড়ির ঘায়ে আমার মাথাটা ঝনঝন করে বাজছে। এক সময় একটু একটু করে বেদনানাশকের প্রভাব ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসতে আমার চোখ দিয়ে দরদর ধারে জল পড়ে হাতে ধরা পাত্রের রক্তের সঙ্গে মিশে যেতে লাগল, তাতেও সুন্দরীর মন এতটুকু ভেজার নাম নেই।
বার দুয়েক প্রশ্ন করেছিলেন বটে লাগছে কি না, কিন্তু আমার উত্তরের অপেক্ষা না করে যথারীতি তাঁর কাজ
চালিয়ে গেছেন। কিন্তু সবেরই শেষ আছে। এক সময় এই আসুরিক চিকিৎসার অবসান ঘটল। কোনও এক রাসায়নিক দ্রব দিয়ে তুলো ভিজিয়ে তাই দিয়ে আমার নাকের ফুটো দুটোই বন্ধ করে দেওয়া হল। ওই অবস্থায় পরের দিন সকাল পর্যন্ত শুয়ে থাকতে হল, কিছু সময় অন্তর অন্তর নাকে ড্রপ দিয়ে তুলো ভিজে রাখতে হচ্ছিল। মুখ দিয়ে নিশ্বাস প্রশ্বাস নিতে হচ্ছিল। সুন্দরীর নিষ্ঠুর ব্যবহারে তাঁকে মন থেকে বিদায় দিতে হল।
সুস্থ হয়ে ওঠার পর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার আরও মাসখানেক বাদে নির্ধারিত দিনে প্রফেসরের সঙ্গে তাঁর চেম্বারে গিয়ে দেখা করলাম। পরীক্ষা করে দেখে ওই হাসপাতালেই কানের অপারেশনের জন্য তিনি আমাকে ভর্তি করে নিলেন। আজ থেকে তিন দশকেরও বেশি সময় আগে কানের এই মাইক্রো সার্জারিটা বোধহয় অন্য ধরনের হত– কানের পর্দা ভেদ করে তবেই স্নায়ুতন্ত্রীকে সচল করা যেত।
স্থানীয় ভাবে অবশ করার জন্য কানের এক পাশে একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে আমাকে অপারেশন টেবিলে শুইয়ে দেওয়া হল। চোখমুখ ঢেকে দেওয়া হলেও কানের পর্দা-ভেদ করে ভেতর থেকে যে কিছু একটা বের করার চেষ্টা চলছে তা বেশ বুঝতে পারছিলাম। কিছু বাদে পায়ের পাতার ওপর একটা ইঞ্জেকশন এবং তারপরেই পিঁপড়ের কামড়ের মতো একটা চিনচিন জ্বালা টের পেলাম। আমাকে যখন ছেড়ে দেওয়া হল তখন আমি তো অবাক: কানে তুলো গোঁজা আছে সেটা তো স্বাভাবিকই, কিন্তু পায়ের পাতায় ব্যান্ডেজ কেন? প্রফেসরকে সেই মুহূর্তে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারছি না, তিনি নিজেই আমাকে বললেন, পরদিন যখন রাউন্ডে আসবেন তখন আমাকে সব ব্যাখ্যা করে বলবেন।
………………………………………………..
ফলো করুন আমাদের ফেসবুক পেজ: রোববার ডিজিটাল
………………………………………………..
পরের দিন কানের গোঁজা তুলো খুলে দিতে সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা: ঘরের ভেতরের কথাবার্তা আার আশপাশের যত আওয়াজ যেন হলঘরে রাখা মাইক্রোফোনের ভেতর দিয়ে গমগম করে কানে এসে লাগছে। আমার খুশি আর ধরে না। কিন্তু প্রফেসর যা বললেন, তাতে আমি হতাশ। তিনি জানালেন, অপারেশন সফল হয়নি। অপারেশন করতে গিয়ে নার্ভে যতটুকু নাড়াচাড়া লেগেছে তারই ফলে সাময়িক ভাবে সেটা সচল হয়ে উঠেছে। ওটা তিনি টেনে ওপরে আনতে পারেননি, যেহেতু আমার কানের ভেতরের প্যাসেজটা বড় বেশি সঙ্কীর্ণ, এদিকে নার্ভটা যে একেবারে কঠিন হয়ে গেছে তাও নয়– একটু আধটু নড়াচড়াও করছে– এই অবস্থায় জোর খাটাতে গেলে নার্ভের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তাই আপাতত অপারেশন স্থগিত রাখতে হল, যখন নড়াচাড়া একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে, অর্থাৎ কানে আর শুনতেই পাব না তখন কাজটা সহজ হবে, তখন তাঁর কাছে এলে তিনি অপারেশন করে দেবেন। আপাতত এই পর্যন্ত: হরিষে বিষাদ। কিন্তু পায়ে ব্যান্ডেজ কেন? তা হবে না? ওখান থেকে চামড়া তুলে নিয়ে কানের পর্দা মেরামত করতে হয়েছে যে!
আরও প্রায় বছরখানেক এরকম অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে কাটানোর পর অবস্থার আরও অবনতি হয়ে প্রফেসরের কাছে গেলাম। এবারে তিনি সত্যি সত্যি সফল হলেন। আমি আবার শ্রবণশক্তি ফিরে পেলাম।
…পড়ুন রুশকথা-র অন্যান্য পর্ব…
পর্ব ৩১। আমার স্ত্রী ও দুই কন্যা নিজভূমে পরবাসী হয়ে গিয়েছিল শুধু আমার জন্য
পর্ব ৩০। শান্তিদা কান্ত রায়ের প্রিয় কাজ ছিল মস্কোয় ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের কমিউনিজম পড়ানো
পর্ব ২৯। পেরেস্ত্রৈকার শুরু থেকেই নিরাপত্তার অভাব বোধ করছিলেন গোপেনদা
পর্ব ২৮। দেশে ফেরার সময় সুরার ছবি সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি পাননি গোপেনদা
পর্ব ২৭। বিপ্লবের ভাঙা হাট ও একজন ভগ্নহৃদয় বিপ্লবী
পর্ব ২৬। ননী ভৌমিকের মস্কোর জীবনযাত্রা যেন দস্তইয়েভস্কির কোনও উপন্যাস
পর্ব ২৫। ননীদা বলেছিলেন, ডাল চচ্চড়ি না খেলে ‘ধুলোমাটি’র মতো উপন্যাস লেখা যায় না
পর্ব ২৪। মস্কোয় শেষের বছর দশেক ননীদা ছিলেন একেবারে নিঃসঙ্গ
পর্ব ২৩। শেষমেশ মস্কো রওনা দিলাম একটি মাত্র সুটকেস সম্বল করে
পর্ব ২২। ‘প্রগতি’-তে বইপুথি নির্বাচনের ব্যাপারে আমার সঙ্গে প্রায়ই খিটিমিটি বেধে যেত
পর্ব ২১। সোভিয়েতে অনুবাদকরা যে পরিমাণ অর্থ উপার্জন করত, সে দেশের কম মানুষই তা পারত
পর্ব ২০। প্রগতি-র বাংলা বিভাগে নিয়োগের ক্ষেত্রে ননীদাই শেষ কথা ছিলেন
পর্ব ১৯। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নাকি খুব ভালো রুশভাষা জানতেন, প্রমথনাথ বিশী সাক্ষী
পর্ব ১৮। লেডি রাণু মুখার্জিকে বাড়ি গিয়ে রুশ ভাষা শেখানোর দায়িত্ব পড়েছিল আমার ওপর
পর্ব ১৭। একদিন হঠাৎ সুভাষদা আমাদের বাড়ি এসে উপস্থিত ফয়েজ আহমেদ ফয়েজকে নিয়ে
পর্ব ১৬। মুখের সেই পরিচিত হাসিটা না থাকলে কীসের সুভাষ মুখোপাধ্যায়!
পর্ব ১৫। রুশ ভাষা থেকেই সকলে অনুবাদ করতেন, এটা মিথ
পর্ব ১৪। মস্কোয় ননীদাকে দেখে মনে হয়েছিল কোনও বিদেশি, ভারতীয় নয়
পর্ব ১৩। যিনি কিংবদন্তি লেখক হতে পারতেন, তিনি হয়ে গেলেন কিংবদন্তি অনুবাদক
পর্ব ১২। ‘প্রগতি’ ও ‘রাদুগা’র অধঃপতনের বীজ কি গঠনপ্রকৃতির মধ্যেই নিহিত ছিল?
পর্ব ১১। সমর সেনকে দিয়ে কি রুশ কাব্যসংকলন অনুবাদ করানো যেত না?
পর্ব ১০। সমর সেনের মহুয়ার দেশ থেকে সোভিয়েত দেশে যাত্রা
পর্ব ৯। মস্কোয় অনুবাদচর্চার যখন রমরমা, ঠিক তখনই ঘটে গেল আকস্মিক অঘটন
পর্ব ৮: একজন কথা রেখেছিলেন, কিন্তু অনেকেই রাখেননি
পর্ব ৭: লেনিনকে তাঁর নিজের দেশের অনেকে ‘জার্মান চর’ বলেও অভিহিত করত
পর্ব ৬: যে-পতাকা বিজয়গর্বে রাইখস্টাগের মাথায় উড়েছিল, তা আজ ক্রেমলিনের মাথা থেকে নামানো হবে
পর্ব ৫: কোনটা বিপ্লব, কোনটা অভ্যুত্থান– দেশের মানুষ আজও তা স্থির করতে পারছে না
পর্ব ৪: আমার সাদা-কালোর স্বপ্নের মধ্যে ছিল সোভিয়েত দেশ
পর্ব ৩: ক্রেমলিনে যে বছর লেনিনের মূর্তি স্থাপিত হয়, সে বছরই ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙার সূচনাকাল
পর্ব ২: যে দেশে সূর্য অস্ত যায় না– আজও যায় না
পর্ব ১: এক প্রত্যক্ষদর্শীর চোখে রাশিয়ার খণ্ডচিত্র ও অতীতে উঁকিঝুঁকি
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
