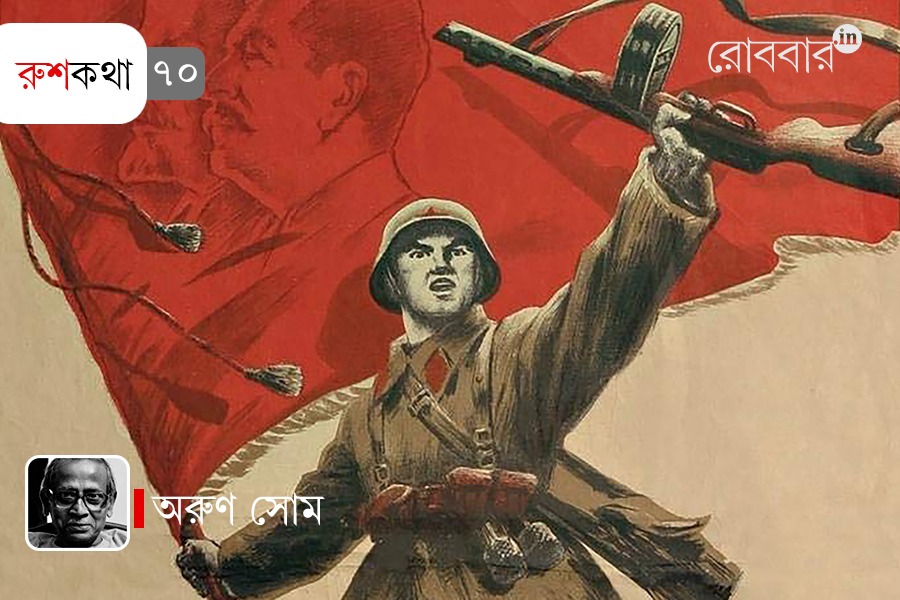
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে হিটলারের আগ্রাসনের আশঙ্কা যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্বেগের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছিল, তখনই ১৯৩৮ সালে জনগণকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে তোলার উদ্দেশ্যে বিশ্ববিখ্যাত চিত্রপরিচালক সের্গেই আইজেনস্টাইনকে দিয়ে স্তালিন প্রচারমূলক ছবি ‘আলেকসান্দ্র নেভ্স্কি’ নির্মাণের উদ্যোগে নিয়েছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে (১২৪০ খ্রিস্টাব্দে) যে জার টিউটনিক নাইটদের আক্রমণ রুখে দিয়ে দেশকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন, তিনি আলেকসান্দ্র নেভ্স্কি। তাঁর এই নীতির জন্য আরও কয়েক শতাব্দী পরে (১৫৪৭ খ্রিস্টাব্দে) রাশিয়ার অর্থোডক্স চার্চ তাঁকে সন্তের মর্যাদায় ভূষিত করেছিল। মনে রাখতে হবে, এই জার নিজে কিন্তু সুইডিস বংশোদ্ভূত প্রথম রুশ জার রুরিকের বংশধর। যিনি দেশপ্রেমের জ্বলন্ত দৃষ্টান্তস্বরূপে একজন জারকে তুলে ধরার পরিকল্পনা করেছিলেন, তিনি জন্মসূত্রে খাঁটি জর্জীয়। আর সেই যুগান্তকারী চলচ্চিত্রের যিনি নির্মাতা, সেই আইজেনস্টাইন জন্মসূত্রে একজন ইহুদি। বাইবেলের ‘নূতন নিয়ম’-এর লিখিত সুসমাচারের একটি জায়গায় কথিত হয়েছে: ‘… যাহারা তরবারি ধারণ করে তাহারা সকলে তরবারির দ্বারাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।’ (মথি ২৬:৫২)। এই ছবিতে নেভ্স্কির ভূমিকায় অবতীর্ণ তৎকালীন খ্যাতনামা অভিনেতা চের্কাসেভের মুখে আমরা বাইবেলের সেই বাণীর ঈষৎ পরিবর্তিত প্রকারভেদে শুনতে পাই– ‘যারা তরবারি হাতে আমাদের সম্মুখীন হবে তারা তরবারিতেই নিপাত যাবে।’

৭০.
রুশ জাতীয়তাবাদের স্বরূপ: সত্য মিথ্যা ও মিথ বা অতিকথন
রুশ জাতিসত্তা গঠিত হয়েছিল একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতকের প্রথম চতুর্থাংশে। প্রাচীন রুশ সাহিত্যের অন্যতম নিদর্শন ‘ইগর বাহিনীর গাথা’কে তারা ‘রুসিচি’ নামে অভিহিত করে। ‘রুসিচি’রা ছিল রুশ উক্রাইনীয় ও বেলারুস্– এই তিন ভ্রাতৃজাতির আদিপুরুষ।
উত্তরের জনগোষ্ঠী বোঝাতে ‘রুস্’ (লাল; লোহিতাভ কেশবর্ণের জন্য?) শব্দটি প্রতিবেশী রাজ্য ফিনল্যান্ডের লোকেরাই প্রথম ব্যবহার করত। মোটামুটিভাবে ৮৫০ খ্রিস্ট্রাব্দ নাগাদ সময়ে রুশভূমির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাচীন স্লাভদের মধ্যে যারা পরবর্তীকালে দ্নেপ্র তীরে কিয়েভ নগর (বর্তমানে উক্রাইনার অন্তর্ভুক্ত, উক্রাইনার রাজধানী) পত্তন করে তারাই কিয়েভ্-রুস্ এই যুগ্ম নামে পরিচিত। কিয়েভ্-রুস্ বলতে প্রাচীনকালে যে অঞ্চলটি বোঝাত বর্তমানে তা উক্রাইনা, যার এককালে পরিচিতি ছিল মালায়া রুস্ বা উপ-রাশিয়া নামে। এছাড়া আছে বেলারুস্ বা শ্বেত রাশিয়া, যার রাজধানী মিন্স্কি। সমগ্র অঞ্চলটি নিয়ে গঠিত হয়েছিল ‘ভেলিকো রুস্স্কি’– মহারুশ। উক্রাইনীয়রা পরবর্তীকালে পৃথক জাতিসত্তা নামে পরিচিত হলেও তার নামের মধ্যেই মহারাশিয়ার অন্তর্ভুক্তির পরিচয় নিহিত: ‘উক্রাইনা’ অর্থ প্রান্তবর্তী– রুশদেশের প্রান্তবর্তী অঞ্চল। আর উক্রাইনার পূর্বাঞ্চল, যেখানে রুশিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, আজও, আনুষ্ঠানিকভাবে যদি নাও হয়, সাধারণভাবে ‘নোভোরসিয়া’ বা ‘নব রাশিয়া’ নামে পরিচিত।
প্রাচীন রুশ নগর নোভ্গোরদ ও কিয়েভ্ শহরের অবস্থান ছিল ‘ভারিয়াগ্’ (স্ক্যান্ডিনেভিয়ার প্রাচীন নাম, যে অঞ্চলের অধিবাসীরা ‘ভারাঙ্গিয়ান’ অথবা ‘ভাইকিং’ নামেও পরিচিত) থেকে গ্রিসদেশের গুরুত্বপূর্ণ নৌবাণিজ্য পথে। এই শহরগুলি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যোগসূত্রও ছিল বটে। নবম শতাব্দীতে রু্যরিক্ নামে এক স্ক্যান্ডিনেভীয় ভাগ্যান্বেষী রাজপুত্র স্বদেশীয় সৈন্যদের সহায়তায় এবং কোনও কোনও স্লাভ উপজাতির সম্মতিক্রমে কিয়েভের শাসক হয়ে এক নতুন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। রু্যরিকের আত্মীয় অল্যেগের নেতৃত্বে কিয়েভ্ এবং অন্যান্য সামন্তরাজ্য মিলিত হয়ে ‘রুশ’ নাম গ্রহণ করো। সুতরাং দেখাই যাচ্ছে রুশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, প্রথম রুশ জার আদৌ রুশি ছিলেন না।
এটা যেমন সত্য তেমনি শেষ যিনি রুশ সম্রাট, রমানভ্ বংশের শেষ প্রতিনিধি বলে যাঁকে আমরা জানি সেই জার নিকলাই রমানভের ধমনীতেও এক ফোঁটাও রুশ রক্ত ছিল না। আশ্চর্য কাকতালীয় ঘটনা! তাছাড়া রুশ জারদের অর্ধেকের ধমনীতেই অমনিতেও জার্মান ও ইংরেজ রক্তের মিশেল ছিল।
রমানভ্ রাজবংশ ১৬১৩-১৯১৭– মোট তিনশো বছরেরও বেশি রাশিয়ায় রাজত্ব করে। এই বংশের প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাট মহামতি পিয়োত্র্-এর মৃত্যুর পর প্রাসাদ ষড়যন্ত্র এবং রমানভ্ পরিবারের বিভিন্ন শাখার মধ্যে উত্তরাধিকারের লড়াই এবং হানাহানি খুনোখুনি বেধে যায়– সিংহাসন একের পর এক হাত বদল হতে হতে হতে শেষকালে প্রকৃত রমানভ্দের হাত থেকে চলে গিয়েছিল। বস্তুতপক্ষে শেষ রমানভ্ ছিলেন সাম্রাজ্ঞী য়েলিজাভিয়েতা। ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর তৃতীয় পিয়োত্র্ নাম ধারণ করে যিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র Holstein Gritarp. তাঁর মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারিণী হন তাঁর স্ত্রী দ্বিতীয় য়েকাতেরিনানা (১৭২৯-১৭৯৬) ১৭৬২ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন)। তিনি নিজেই ছিলেন জার্মান প্রিন্সেস (সফিয়া ফ্রেডারিকা আউগুস্ট)। এরপর থেকে রাজত্ব পুরোপুরি চলে যায় জার্মান বংশোদ্ভূতদের হাতে। য়েকাতেরিনার উত্তরাধিকারীক পাভেলকে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তাঁর সভাসদরা পিটিয়ে খুন করে। তাঁর পুত্র প্রথম আলেক্সান্দ্র নেপোলিয়নের পরাজয়ে তাঁর অবদানের জন্য ইউরোপের প্রশংসা অর্জন করেন।
তাঁর উত্তরাধিকারীর– রুশ জাতি অনন্যসাধারণ– এই তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন রুশ জাতির এই ব্যতিক্রমী চরিত্রই তাঁর শক্তি, তাঁর আত্মা। দ্বিতীয়ত, আরও যে একটি তত্ত্বে তাঁরা বিশ্বাস করতেন এবং রুশিরা নিজেরাও যাতে আস্থাবান সেটা এই যে রুশ জাতি স্বাভাবিক ভাবেই স্বৈরতন্ত্রের অনুগামী। তাঁর সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাও ছিল এই ঐতিহ্যেরই অনুগামী। নিকলাই গোগল তাঁর ‘মৃত আত্মা’ উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদে এই প্রসঙ্গে যে ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন, তা প্রণিধানযোগ্য: কোনও এক নিঃস্ব জমিদার তার হতদরিদ্র ভূমিদাস প্রজাদের প্রসঙ্গে খেদ করে বলছে, ‘আমি ওদের পারলে এখনই মুক্তি দিতে পারতাম। কিন্তু তাতে ওদের অবস্থার কোনও উন্নতি হত না। ওদের মাথার ওপর এমন একজন কারও থাকা দরকার যে তার নিজের অদম্য উৎসাহ আর কর্মোদ্যোগ দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে ওদের উৎসাহিত করে তুলবে। নিজেকে দিয়েই দেখতে পাচ্ছি রুশ মানুষের স্বভাবটাই এমন যে তাকে তাড়া দেওয়ার মতো কেউ না থাকলে সে চলতে পারে না। তা না হলে সে ওই ঝিমিয়েই থাকবে, পচে মরবে।’
কিন্তু যাদের সম্বন্ধে এত কথা সেই রুশি আসলে কারা? সে প্রশ্নেরও উত্তর দিয়েছেন উক্রাইনীয় বংশোদ্ভূত সেই রুশীভূত মানুষ, রুশ লেখক নিকলাই গোগল, তাঁর ওই ‘মৃত আত্মা’ উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডের আরেকটি জায়গায়। লেখক উপন্যাসে তাঁর সৃষ্ট একটি চরিত্র সম্বন্ধে লিখেছেন: ‘আসলে সে কোন জাতির লোক? রুশদেশে এমন অসংখ্য মানুষ আছে যারা অরুশি বংশোদ্ভূত। কিন্তু তারা সকলেই মনেপ্রাণে রুশি। নিজে যে জন্মসূত্রে কোন জাতের লোক, তা নিয়ে সে কখনও মাথা ঘামায়নি। ও নিয়ে তার কোনও আগ্রহও নেই, বিষয়টা তার কাছে অপ্রাসঙ্গিক, অবান্তর। তাছাড়া রুশ ভাষা ছাড়া আর কোনও ভাষা সে জানত না।’
রুশ জাতির এই ‘অনন্যতা’র, রুশ জাতীয়তাবাদের চরম অভিব্যক্তিও আমরা দেখতে পাই গোগোলের ‘মৃত আত্মা’ উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের উপসংহারে: ‘প্রবল ঘন্টাধ্বনিতে দশদিক মুখরিত করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে তিন ঘোড়ার গাড়ি ত্রোইকা।’ লেখকের প্রশ্ন: কোথায় চলেছ তুমি রুশ? উত্তর দাও। উত্তর মেলে না। আকাশ বাতাস উথালপাতাল করে ছিন্নভিন্ন করে শূন্যে শিস দিয়ে আছড়ে পড়ছে ত্রোইকার আশ্চর্য ঘণ্টার ঘনঘোর মন্দ্র, উড়িয়ে নিয়ে চলেছে তার চলার পথের ধারের সব কিছু; অপাঙ্গে তার দিকে তাকিয়ে এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে, তাকে পথ করে দেয় আর সব দেশ, অন্য সব জাতি।’
জাতীয়তাবাদ? স্বদেশপ্রীতি? উগ্র স্বাজাত্যবোধ? যে কোনও ভাবেই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। মনে রাখতে হবে, ১৮৮০-তে নেপোলিয়নের আক্রমণের বিরুদ্ধে এবং ১৯৪১ সালে হিটলারের সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে– ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর দু’টি বড় বড় যুদ্ধকেই ‘পিতৃভূমির যুদ্ধ’ বা ‘পিতৃভূমির মহাযুদ্ধ’ অ্যাখ্যা দিয়ে রাশিয়া বা সোভিয়েত ইউনিয়ন লড়াই করতে নেমেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আসলে ১৯৩৯ সালে শুরু হয়ে গেলেও সোভিয়েত ইউনিয়ন ভুলেও আন্তর্জাতিক সৌভ্রাত্রের খাতিরে তাকে ‘বিশ্বযুদ্ধ’ অ্যাখ্যা দেয়নি, যদিও এটাও ঠিক যে, মিত্রশক্তি যুদ্ধের গোড়া থেকেও সোভিয়েত ইউনিয়নকে একঘরে করে রেখে দিয়েছিল।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে হিটলারের আগ্রাসনের আশঙ্কা যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্বেগের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছিল, তখনই ১৯৩৮ সালে জনগণকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে তোলার উদ্দেশ্যে বিশ্ববিখ্যাত চিত্রপরিচালক সের্গেই আইজেনস্টাইনকে দিয়ে স্তালিন প্রচারমূলক ছবি ‘আলেকসান্দ্র নেভ্স্কি’ নির্মাণের উদ্যোগে নিয়েছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে (১২৪০ খ্রিস্টাব্দে) যে জার টিউটনিক নাইটদের আক্রমণ রুখে দিয়ে দেশকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন, তিনি আলেকসান্দ্র নেভ্স্কি। তাঁর এই নীতির জন্য আরও কয়েক শতাব্দী পরে (১৫৪৭ খ্রিস্টাব্দে) রাশিয়ার অর্থোডক্স চার্চ তাঁকে সন্তের মর্যাদায় ভূষিত করেছিল। মনে রাখতে হবে, এই জার নিজে কিন্তু সুইডিস বংশোদ্ভূত প্রথম রুশ জার রুরিকের বংশধর। যিনি দেশপ্রেমের জ্বলন্ত দৃষ্টান্তস্বরূপে একজন জারকে তুলে ধরার পরিকল্পনা করেছিলেন, তিনি জন্মসূত্রে খাঁটি জর্জীয়। আর সেই যুগান্তকারী চলচ্চিত্রের যিনি নির্মাতা, সেই আইজেনস্টাইন জন্মসূত্রে একজন ইহুদি। বাইবেলের ‘নূতন নিয়ম’-এর লিখিত সুসমাচারের একটি জায়গায় কথিত হয়েছে: ‘… যাহারা তরবারি ধারণ করে তাহারা সকলে তরবারির দ্বারাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।’ (মথি ২৬:৫২)। এই ছবিতে নেভ্স্কির ভূমিকায় অবতীর্ণ তৎকালীন খ্যাতনামা অভিনেতা চের্কাসেভের মুখে আমরা বাইবেলের সেই বাণীর ঈষৎ পরিবর্তিত প্রকারভেদে শুনতে পাই– ‘যারা তরবারি হাতে আমাদের সম্মুখীন হবে তারা তরবারিতেই নিপাত যাবে।’
সোভিয়েত আমলে পার্টি ও সরকার মহলে আন্তর্জাতিকতাবাদ স্লোগানটার প্রচলন ছিল ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে পার্টি ও সরকার মহল থেকে জনগণকে বিশ্বনাগরিকতাবোধ (Cosmopolitanism) সম্পর্কেও বারবার সতর্ক করে দেওয়া হত এই বলে যে Cosmopolitanism ‘মাতৃভূমি, স্বদেশবাসী ও স্বদেশের সংস্কৃতির প্রতি এক ধরনের উদাসীন মনোভাব বুর্জোয়া সুলভ মনোবৃত্তি, প্রলেতারীয় Internationalism (আন্তর্জাতিকতাবাদ)-এর বিরোধী।’
পিয়োতর ছাড়া রাশিয়া অচল
জার মহামতি পিয়োতরের স্বপ্নের পেতের্বুর্গ এবং তাঁর স্বপ্ন নিয়ে দু’-একটি কথা না বললে বর্তমান রাশিয়াকে বোঝার পক্ষে কিছু অসুবিধা থেকে যায়। রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক গঠন কাঠামোর ক্ষেত্রে পিয়োতর যে-বিধান দিয়ে গেছেন, তা যেন অনেকাংশেই অতীত বর্তমান এমনকী ভবিষ্যৎ রাশিয়ারও শেষ কথা। সুশাসনের জন্য দেশের যে প্রশাসনিক বিভাগগুলি পিয়োতর করে গিয়েছিলেন, সোভিয়েত আমলেও বিভিন্ন নামে সেই ব্যবস্থাই চালু ছিল, আজও সেই ধারা অব্যাহত আছে। সোভিয়েত আমলের যে Administrative Command System নিয়ে পরবর্তীকালে এত বিতর্ক, তারও স্রষ্টা মহামতি পিয়োতর। এখনও সে-দেশে তার দৌরাত্ম্য চলছে।
প্রশাসনের ক্ষেত্রে পিয়োতরের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অবদান দেশে অভ্যন্তরীণ পাসপোর্ট ও রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থার ব্যাপক প্রচলন। না, ইংরেজিতে ‘পাসপোর্ট’ শব্দটির অর্থ আমরা যা জানি, তা থেকে এই পাসপোর্ট-এর অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন। জার আমলের রাশিয়াতে প্রতি নাগরিকের কাছে অভ্যন্তরীণ পাসপোর্ট থাকত। এটা ছিল এক-ধরনের আইডেন্টটি কার্ড বা পরিচয়পত্র। প্রশাসনিক ও আইন-শৃঙ্খলাগত সুবিধার কারণে এই ব্যবস্থার ওপর পিয়োতর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন।
এছাড়া পেতের্বুর্গের মতো বড় বড় শহরের জন্য আরও একটি ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল– তারও সূচনা পিয়োতরের উদ্যোগে। পেতের্বুর্গে কেউ সাময়িকভাবে বা পাকাপাকিভাবে বসবাস করতে এলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে নাগরিক গৃহ পরিচালন সংস্থার অফিসে নাম-ঠিকানা ইত্যাদি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আরও নানা তথ্যসমেত ফর্ম পূরণ করে পুলিশের অনুমোদনের জন্য জমা দিতে হত। এইভাবে নাম রেজিস্ট্রি হলে তবেই সেখানে থাকার অনুমোদন মিলত।
এই একই পাসপোর্ট ও রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থা সোভিয়েত আমলে শুধু যে অব্যাহত ছিল তা-ই নয়, বরং আরও কড়াকড়ি এবং সারাদেশ জুড়েই বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়ায়। কোনও কারণে কারও যদি এ-দু’টির একটি না থাকত (অবশ্য পাসপোর্ট না থাকলে রেজিস্ট্রেশনের কোনও প্রশ্নই ওঠে না) তাহলে তার কোনও নাগরিক অধিকারই স্বীকৃতি পেত না– পরন্তু কারাদণ্ড, জরিমানা এবং তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থাগ্রহণ অবধারিত ছিল। বিপ্লবের অব্যাহিত পরে বেশ কিছুকালের জন্য এই প্রথা উঠে গিয়েছিল, কিন্তু পরে তিনের দশকে স্তালিন আমলে জারের ওই উত্তরাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।
সোভিয়েত আমলে ১৯৩২ সালে অভ্যন্তরীণ পাসপোর্ট ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক হয়েছিল বিশেষত মস্কো লেনিনগ্রাদ খারকভ এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলগুলির জন্য। পরে ১৯৪০ সালের ১০ এপ্রিল গণ কমিসার পরিষদে বিশেষ ডিক্রি জারি করে সারা সোভিয়েত ইউনিয়ন জুড়ে পাসপোর্ট ও রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক হয়।
এতে প্রশাসনের যেমন সুবিধা হল, সাধারণ নাগরিকদের তেমনি পদে পদে নানা বাধার সম্মুখীন হতে হল। শুধু গ্রাম থেকে শহরে কেন, ভাগ্যের সন্ধানে এক শহর থেকে আর এক শহরে গিয়ে বসবাসের চেষ্টা করতে যাওয়াটাই একটা অবাস্তব ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। পাসপোর্টে যে-অঞ্চলের রেজিস্ট্রেশন আছে তার বাইরে কোথাও চাকরি এবং বাসস্থান পাওয়া যাবে না। বিশাল দেশের মানুষ এলাকায় এলাকায় বিভক্ত হয়ে দ্বৈপায়নের জীবন-যাপন শুরু করে দিল।
আজকের দিনে সোভিয়েত-পরবর্তী আমলে অবশ্য আর সেই জটিলতা নেই– পৃথক বাড়িঘর অনায়াসেই কেনা যায় এবং রেজিস্ট্রেশনও আইনতই কেনা যায়। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের এত বছর পরও বাধ্যতামূলক পাসপোর্ট ও রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থা থেকে দেশ আজও মুক্ত হতে পারেনি। সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে।
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
