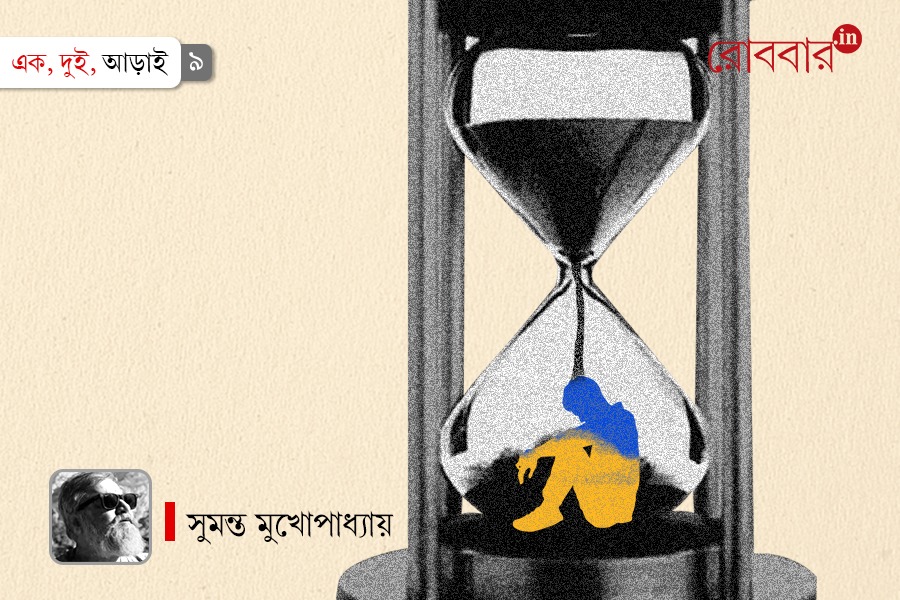
অতীত বা পুরনোর প্রতি একটা মর্মান্তিক আশ্রয়বোধ ঔপনিবেশিকতাবাদের এবং উত্তর ঔপনিবেশিকতার অবশ্যম্ভাবী ফল। সেটা পৃথিবীর সর্বত্র নানা সময়ে নানা আকারে দেখা দিয়েছে। আফ্রিকা মহাদেশ বা লাটিন আমেরিকান লেখকদের লেখায় শুধু নয়, ভারতের লেখক-শিল্পীদের কাজে এর অজস্র উদাহরণ আর উপকরণ ছড়িয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের ‘মেঘদূত’ প্রবন্ধ এই স্মরণ উদ্যোগের অপূর্ব নমুনা।

ঘোড়া দেখলেই সবার পায়ে বেমালুম বাত। কোনও কিছু লিখতে গেলে এই তেজি প্রাণীর চলাফেরা মনে আসে। সোজা গট গট করে কিছু যে বলে যাব, এমন কনফিডেন্স কস্মিনকালেও ছিল না। আড়ে আড়ে কোনাকুনি চলতে গিয়েও লজ্জায় মাথা কাটা যায়। তাই আড়াই চালে ভাবি। বাধা টপকে আদার ব্যাপারীও মোক্ষম ঘরটিতে গিয়ে বসতে পারে চোখের পলকে। কাটাকুটি– সে পরের কথা। তবে নিওলিথ স্তব্ধতায় না হোক মহীনের পোষা জীবটির আপন মনে ঘাস খাওয়ার দৃশ্য নিউটাউনেও দেখা যায়, সূর্যাস্তে, সন্ধ্যায়। স্যুররিয়াল। বিষাদ মন্থর। দিনশেষের লালচে আলোয় পিঠের ভাবনা-ক্ষতগুলো চিক চিক করে। কারও হাসি পায়, কারও চোখে জল আসে।
………………………….
৯.
পুরানো সেই দিনের কথা
বছর ১০-১২ আগে, একেবারে নতুন লিখতে আসা তরুণ-তরুণীদের অনেকের কবিতা-গদ্য এইরকম নানা লেখায় একটা আশ্চর্য ট্রেন্ড দেখতে পাচ্ছিলাম। সবাই খুব আবেগ নিয়ে নিজেদের অতীতের কথা লিখছেন। বলছেনও। বলছেন পাড়ার কথা, ফেলে আসা জনপদ-স্মৃতি, নিজেদের ৫-৭ বছর আগের ব্যাপার-স্যাপারগুলোকেই অনেকের কেন যেন মনে হচ্ছে কবেকার কোন হারিয়ে ফেলা জগৎ। কথাটা যে শুধু কমবয়সিদের ক্ষেত্রেই খাটছে তা নয়। এর দু’-তিনটে ব্যাপার আছে। নস্টালজিয়া যে একটা বড় রকমের অসুখের মতো সে-কথা নানা বই পড়ে আমাদের বিশদে জানিয়েছেন দীপ্তনীল রায় ওঁর অতি চমৎকার ‘নেটিভ কেতাব নস্টালজিয়া’ বইটায়। যুদ্ধ করতে গিয়ে অনেকদিন দেশ-গ্রাম ছাড়া হতভাগ্য সৈনিকদের মধ্যেই এমন অসুখ দেখা দিত। তারা তখন কিচ্ছুটি করতে চাইত না। সে প্রসঙ্গ দীপ্তনীল খুব সুন্দর করে লিখেছেন। তবে মাথায় সেই নস্টালজিয়া এখন জিজ্ঞাসার মেঘ জমাচ্ছে না। ছোটবেলার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলে– সেই যে আমরা এককালে এতটুকু ছিলাম, আর কী যে ভালো ছিল সেসব দিন, আর চাদ্দিকে সব কিছুই যে কী চমকপ্রদ ছিল, আমরা কত আনন্দে দিন কাটাতাম, আর সেই যে অমুক সময় তুই স্কুল কেটে ধরা পড়ে গেলি ইত্যাকার চর্বিতচর্বণজনিত আড্ডার আনন্দ একদিন কি দু’দিন চলে। কিন্তু এরকম আলোচনা রেগুলার হলে সর্বনাশ! তারপরেই আসে কে কত মাইনে পায়, অথবা বর বা বউ চাকরি করে কি না। আর তার পরেই ঝুলি থেকে বেরিয়ে পড়বে কেঁদো বাঘ, পলিটিক্যাল-এর তোড়ে কুমির নামবে খালে। খুব বেশি টানা যায় না এসব। রি-ইউনিয়ন ঠিক আছে, কিন্তু নস্টালজিক রেগুলারিটি অসম্ভব বিরক্তিকর।
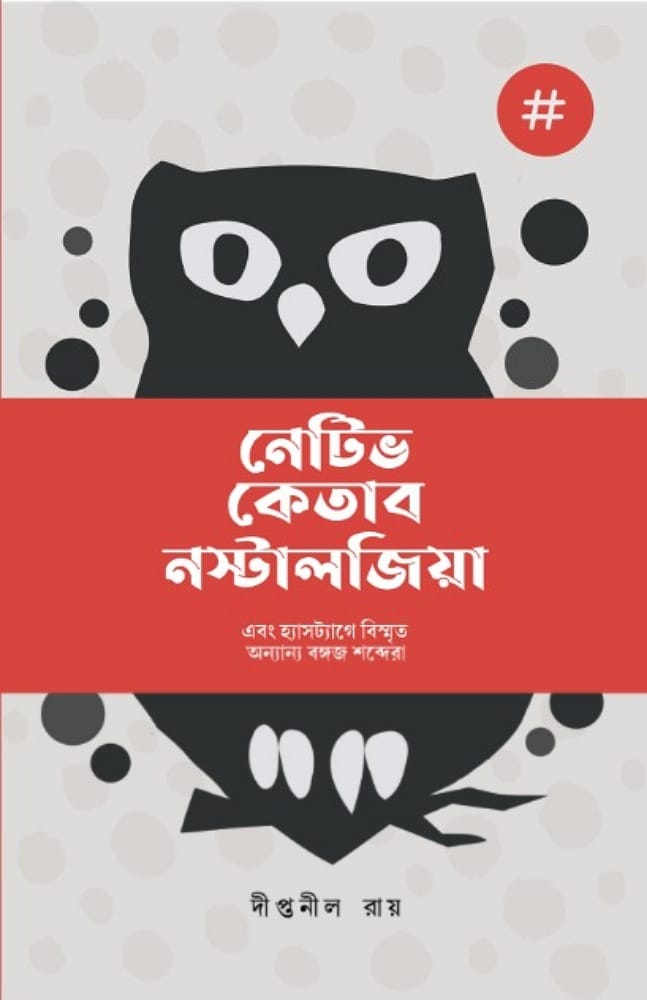
সেটা নিয়ে অত বলার কিছু নেই। চিন্তা হল, একেবারে নতুন তাজা মন যদি বর্তমানটার প্রতি অজানা এবং আজব উদাসীনতায় নিজের বা নিজেদের কথা বলতে গিয়ে অতীতকালটাকে চাঙ্গা করে নেয়, তখনই। অর্থাৎ ২০ বছরের মেয়ে বলে বসে যদি, আমাদের ছোটবেলায় আমরা গঙ্গার ধারে বেড়াতে বেড়াতে লালুদার ঘুগনি খেতুম– তা’হলে মুশকিল। ব্যাপারটা দেখা যাবে বছর পাঁচ সবে পার হয়েছে। মানে একে বর্ধিত বর্তমান বললে, ভূত মানে অতীত ছাড়া কেউ ভয় পাবে না। এইটে নিয়েই সমস্যা। কারণ লালু নামক ব্যাক্তিটি নিত্যবর্তমান এবং তাঁর চা-পাঁউরুটি-ঘুগনিও তাই। স্মৃতি-কন্ডূয়ন বা গতকালের চুলকানি চিরকেলে লেখক-লেখিকাদের সমস্যা তা নয়, কিন্তু মাঝে মাঝে দেখা দেয় নতুন নতুন আকারে, এবং বিশেষ কারণে। যাদের সবাই ‘গেঞ্জি’ বলছে, এইরকম ট্রেন্ড যদি তাদের কথাবার্তা আড্ডা কিংবা লেখার ভেতর দেখা যায়, তখন বর্তমানটাকে বোঝার জন্য তাদের দলে ঢুকে পড়া দরকার। ভারতের অন্য ভাষাভাষী মানুষের কথা ততটা জানি না। কিন্তু বাংলায় এই বছর পনেরোর মধ্যে অতীতচারণ আর সদ্য অতীতের আশ্রয়ে কথা বলার ঝোঁক মনে হচ্ছে একটা বড়সড় চেহারা নিয়ে দেখা দিয়েছে।
অতীত বা পুরনোর প্রতি একটা মর্মান্তিক আশ্রয়বোধ ঔপনিবেশিকতাবাদের এবং উত্তর ঔপনিবেশিকতার অবশ্যম্ভাবী ফল। সেটা পৃথিবীর সর্বত্র নানা সময়ে নানা আকারে দেখা দিয়েছে। আফ্রিকা মহাদেশ বা লাটিন আমেরিকান লেখকদের লেখায় শুধু নয়, ভারতের লেখক-শিল্পীদের কাজে এর অজস্র উদাহরণ আর উপকরণ ছড়িয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের ‘মেঘদূত’ প্রবন্ধ এই স্মরণ উদ্যোগের অপূর্ব নমুনা। কালিদাসের কর্মে অবহেলা করা স্বাধিকার প্রমত্ত বিরহী যক্ষ-কেই যুবক রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল স্ব-কালের প্রতিভূ, যে সবার হয়ে বোঝাতে চাইছে এক বিপুল বিরহ বিচ্ছেদ, না, প্রেমিকার কাছ থেকে নয়, তার নিজস্ব সময়ধারা থেকে ধারাবাহিক দেশ থেকে বিচ্ছেদ। মুহূর্ত মধ্যে যক্ষ আর সমালোচক রবীন্দ্রনাথ এক হয়ে গিয়ে ভাবতে থাকেন, সে এক অতীত কাল থেকে যেন দেশের সবার চিরবিদায় ঘটে গিয়েছে। সেই অতীত তাই ডাকে, বারে বার হাতছানি দিয়ে ডাকে। পৌঁছনোর উপায় নেই, মাঝখানে চির ব্যবধান। এই স্মরণ উদ্যোগের নাম ‘প্রতি-স্মরণ’। বিষয়টি আলোচনা করেছিলেন শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘আলিবাবার গুপ্ত ভাণ্ডার’ বইয়ের ‘ঋত্বিক ঘটকের নাগরিক: নির্বাস বিরহী যক্ষ’ প্রবন্ধে। এর আধুনিক উপক্রম দেখেছি মণিপুরে মেমচৌবি-র কবিতা অনুবাদ করতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে মোলাকাতের সময়।

মেমচৌবি কবিতায় এবং নিজের কথাবার্তায় এমন একটা অতীতের কথা ভাবতে চাইছেন যেটা মণিপুরের নিজস্ব অতীত বলে তিনি ভাবতে চাইছেন। তাঁর কবিতায় মণিপুরের নিজস্ব মিথ থেকে এসে পড়ে ‘কাংলাসা’। খানিক ঘোড়া খানিক সিংহ মেশানো এক পৌরাণিক জন্তু, ইম্ফল শহরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পা ঠুকছে। একেই মেমচৌবি-র মনে হচ্ছে মুক্তির প্রতীক। এখন এই ধরনের কল্পনার গোড়ায় যেমন ঔপনিবেশিকতা থেকে বেরিয়ে আসার দায় আছে, তেমনই আছে ভারতের মধ্যাঞ্চলের অতীতকথা থেকে বেরিয়ে আসারও চেষ্টা। রতন থিয়ামের কথা বলতে গিয়ে মেমচৌবি বলে বসেন, রতন ভারতীয় মিথ মহাভারত-কে আশ্রয় করে সর্বভারতীয় হতে চেয়েছেন, মণিপুরের অতীতলোক তাঁর ভাবনায় এল না। এই তর্কটায় এই মুহূর্তে যেতে চাইছি না। কিন্তু মণিপুর শুধু নয়, উত্তর-পূর্ব ভারতে অসংখ্য জনগোষ্ঠীর কোন অতীতকে বলা যাবে ‘সব্বার’? মণিপুরেই যে গৃহযুদ্ধ চলেছে এতকাল ধরে, কোনটা তার নিজস্ব সার্বজনিক অতীত? কথাটার উত্তর নেই। কিন্তু বোঝা যায়, জোর দিয়ে অতীতকে বানিয়ে তুললে এক ধরনের বানিয়ে তোলাই হয়। তার ওপর নির্ভর বা আশ্রয় করে ঘর বাঁধলে জলে ভেসে যেতে হবে।
ঘুরে ফিরে সেই কাব্যকলা! সত্যি বলতে ওই কাব্যকলাচলচিত্রে অনেক লক্ষণ দেখা যায়, যা সাদা চোখে দেখেও আমরা দেখি না। এতক্ষণ যে সব বিষয় নিয়ে মনে মনে এপাশ-ওপাশ করছিলাম সেগুলো বিদ্যাজীবীরা নানা জায়গায় আলোচনা করে এসেছেন, কিছু বা করেননি। বুদ্ধদেব বসুর চল্লিশের কোঠায় সেই আক্ষেপ– তিনি বৃদ্ধ, প্রায় বৃদ্ধ, মত্ত তিক্ত স্মৃতি ছাড়া তাঁর হাতে আর কী-ই বা আছে। সেটাও তত ভাবায় না, চল্লিশের বদলে এখন হয়তো ৫০-৬০ বছরে ওরকম কেউ বলতেই পারেন। ওদিকে সমবেতভাবে সবাই অতীতের জয়গান গাইতেও পারে– সেটা ঐতিহাসিক রাজনৈতিক চাপে ঘটে। যেমন ভারতীয় চলচ্চিত্রে আলাউদ্দিন বা শম্ভাজীর প্রেতাত্মার আবির্ভাব। এই লাইনে ভারত চাম্পিয়ন। হলিউডকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। ঐতিহাসিক ফেরো-র ‘ইউসেস আন্ড আবিউসেস অফ হিস্ট্রি’ বইটায় নাম তুলতে পেরেছে। আমার এই শব্দচালনায় তারও বিশেষ গুরুত্ব নেই। কমবয়সি ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অনেক সময় আমার মনে হচ্ছিল– এরা যখন একা, এক্কেবারে একা নিজের কথা লিখতে বলতে চাইছে, এদের সদ্য পেরিয়ে আসা সময়টাকেই মনে হচ্ছে একমাত্র আশ্রয়। বর্তমান বা ভবিষ্যতের স্বপ্ন নয়, প্রতিদিনের নতুন অভিজ্ঞতা নয়, গতদিনের কিছু মায়া জড়িয়ে যাচ্ছে তাদের কথায়। এর কোনও উদাহরণ আমি দিতে পারব না। সব বই বা কথপোকথন হাতের কাছে নেই। সত্যজিতের ছবির ‘চারুলতা’র প্রথম লিখনের মতো অনেকে একসঙ্গে ফিরে যাচ্ছে তার সদ্য বিগত দিনের আশ্রয়ে।

এইবার কথাটা শেষ করতে চাইলে একটা হাইপোথিসিসের ওপর ভর করেই বিদায়রেখা টানতে হবে। নিজের গতকালের আশ্রয় তখনই মধুর লাগতে পারে যখন, প্রতিদৈনিক জীবনটাকে অর্থহীন মনে হয়। ঘুমের ভেতর থেকেই কাকের মতো গলায় যদি বাপ-মা ডেকে ওঠে, পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছিস, এর হয়ে গিয়েছে, বারোটা বেজে গিয়েছে, কিসসু হবে না– তাহলে দিনটা একেবারে চায়না টাউন হয়ে যাবে তা তো নয়। কলেজে বিরস গলায় ব্যাজার মুখে অধ্যাপকদের বছরের পর বছর একই অর্থহীন লেকচার, একই সিলেবাস, একই প্র্যাকটিকাল, মুশকো ছেলে আর ধাড়ি ধাড়ি মেয়ের কলেজ গেটে থেবড়ে বসে থাকা। বন্ধুভাগ্যে কারও লাভ কারও ক্ষতি। মাঝে মাঝে একেকটা ঢেউয়ে রাস্তায় নেমে পড়ে আবার যে-কে সেই। এই জীবন কমবেশি সবাই কাটিয়ে এসেছি। এখানে যাদের ‘প্রেম’ নামক বিপুল এনগেজমেন্টে পড়তে হয়, তারা এতরকম ঝুটঝামেলায় রোজ জড়িয়ে থাকে যে ‘বিতে হুয়ে দিন কোয়ি লওটা দে মুঝে’ বলে গান গাওয়ার দরকার পড়ে না। এখানেই কি তাহলে সংকট? আমরা এই মুহূর্তের হাতে কোনও রকম বিশ্বাস, স্বপ্ন, রাজনীতি তুলে দিতে পারিনি? এটা আমার কাছে আপাদমস্তক সত্যি। পারিনি তো বটেই। আজকের ২০ থেকে ৩০ বছরের কোনও ছেলেমেয়েকে আমি বলতে পারছি না, এই পথে আলো জ্বেলে এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে। ব্রাজিলের মডেল হরিয়ানায় ভোট দিয়ে গেলেন, তাও বার ২০-রও বেশি! বেগুসরাইয়ের নেতা বছরের শুরুতে দিল্লির ভোটার, আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গেও দেখা দিতে পারেন। গতবার বাংলা ভাষায় সাহিত্য অকাদেমির পুরস্কার দেওয়া যায়নি, অনিবার্য কারণবশত। মামদানি ভোটে জিতেছেন, আবার দেশের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলছেন এবার খেলা শুরু। এর কোনও শেষ নেই। একটা আপাদমস্তক অর্থহীন সমাজ পৃথিবী জুড়ে তৈরি হয়ে উঠেছে গত বিশ বছরে।
রাজনীতির একটা মস্ত বড় দিক হল স্থিরতা। সব কিছু ঠিকঠাক থাকে যেন। অন্তত সিস্টেমটা চাঙ্গা থাকা চাই। প্লাতো যে তাঁর রিপাবলিক থেকে কবিদের বের করে দিতে চেয়েছিলেন তার কারণ কবিরা ওই স্থিরতার নানা কোণে ফাটল ধরায়। পশ্চিমি রাজনৈতিক তত্ত্বচিন্তায় এই অটল স্থিরতার সন্ধান আর তার বিচ্যুতি সম্ভাবনা নিয়ে আরিস্তোতল ম্যাকিয়াভেলি-ও তৎপর ছিলেন। রাজনীতি মানে তাই ক্রমে হয়ে দাঁড়াল ক্ষমতা ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার বিপুল জাল। এর উল্টোদিকের ভাবনাগুলোকে ছেনে-বেছে এক নতুন তত্ত্ব কাঠামো তৈরি করলেন কার্ল মার্কস। তাঁর ফয়েরবাখের ওপর ১৩ দফা থিসিসে মার্কস বলে দেন, দার্শনিকরা এ যাবত জগৎটাকে ব্যাখ্যাই করে গিয়েছেন। আসল কথা হল সেটা বদলানো। এই বদল খুব বড় ব্যাপার প্রতিদিনের জীবনযাপনে। এ হল উল্টোদিকের রাজনীতি। বর্তমান অবস্থাটাকে বুঝতে বলতে পাল্টাতে এই রাজনীতি যেমন সাহায্য করে তেমনি বিচ্ছিন্নতার উল্টোদিকে নবীন জীবন-কে জগতের সঙ্গে জুড়ে দিতেও সাহায্য করে।
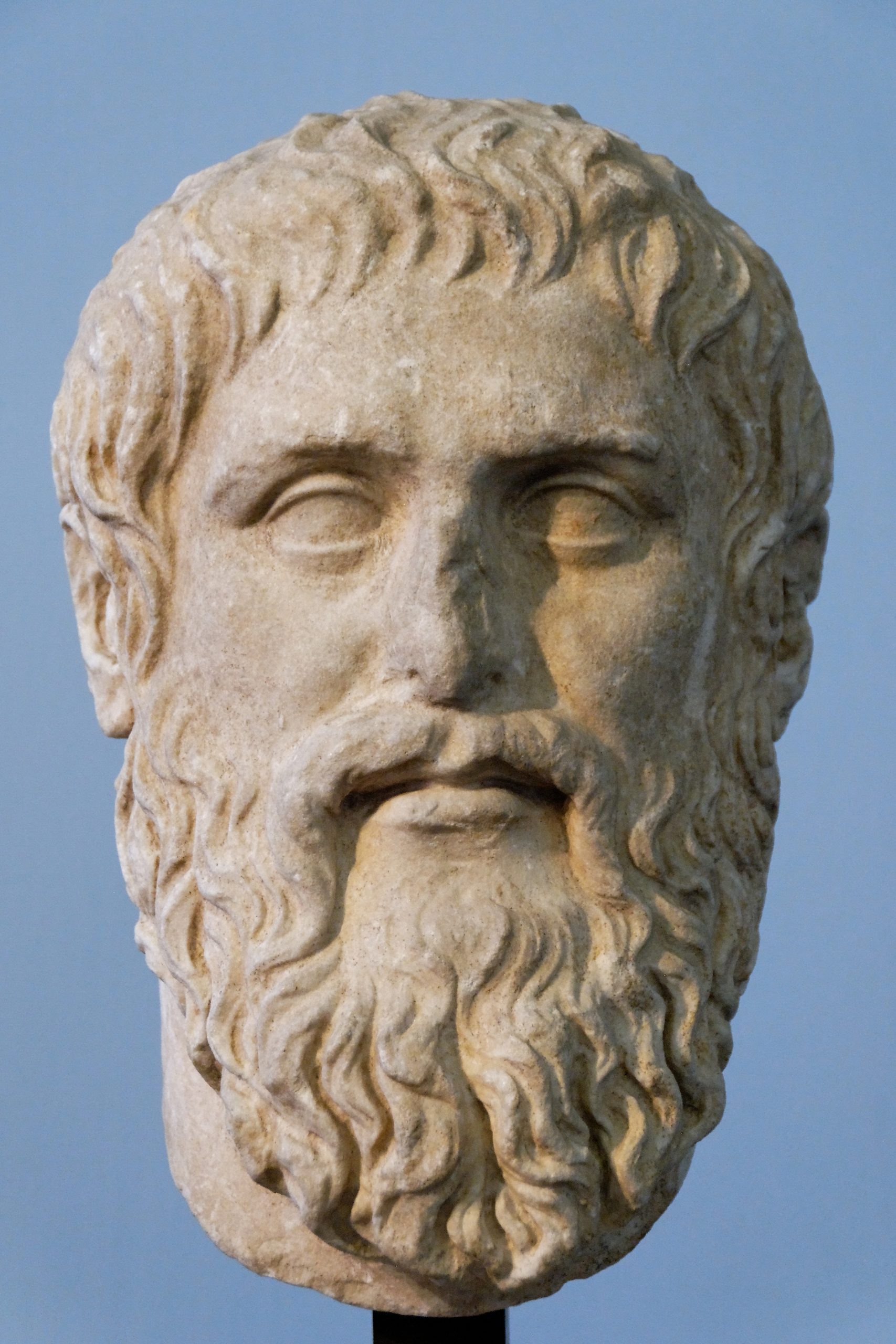
গত ৩৫ বছরে পৃথিবীর রাজনীতি বা ভারতের রাজনীতিতে বদলের সম্ভাবনা উড়ে গিয়ে বার বার স্বেচ্ছাচারের সমর্থন আর টিকে থাকার নানা ফন্দিই গড়ে উঠতে দেখছি। আর বদল যেখানে যেখানে ঘটতে পারছে, সেখানেই এই নতুন ছেলেমেয়েদের বিপুল ভূমিকা থাকছে। ভারতে এন আর সি আন্দোলনের সময় দেশ জোড়া যে ছেলেমেয়েদের এগিয়ে আসতে দেখেছি, তাদের মধ্যে অনেকে ৫ বছর বিনা বিচারে জেলে। ওমর খলিদের কথা অনেকে জানেন, কিন্তু তাদের ছাড়িয়ে আনতে কতজন বিশিষ্ট এগিয়ে এলেন?
আমার মনে হচ্ছে এই নতুন ছেলেমেয়েদের বদল ক্ষমতা আর রাজনৈতিকভাবে প্রতিদিনের জীবনটার সঙ্গে নিজেকে জুড়ে নেওয়ার শক্তি খুঁজে পাওয়া দরকার। নইলে এক একটা মুহূর্তে বাংলাদেশের মতো, নেপালের মতো বা শ্রীলংকার মতো তাদের শক্তি ব্যবহৃত হতে হতে শুয়ারের মাংস হয়ে যাবে। যেমন আমাদের গিয়েছে। নিজের প্রতিটা পদক্ষেপের দিকে সচেতনে তাকিয়ে যদি সেটা নিয়ে ভাবি, বদলে যেতে পারি আমি। বদলে যেতে পারে প্রতিদিনের সৌধগুলো। এই বদলটাই বেঁচে থাকার রাজনীতি। তা প্রেমে-যুদ্ধে-প্রাত্যহিকে সবখানেই আছে। থাকবে।
… এক, দুই, আড়াই-এর অন্যান্য পর্ব …
৮. কলকাতার মূর্তি-আবর্জনা কি বাড়ছে?
৭. ভাবা প্র্যাকটিস করা, কঠিন এখন
৬. লেখার অত্যাচার, লেখার বাঁচা-মরা
৫. বিশ্বকর্মা পুজোর সন্ধেবেলাটার মতো বিষাদ আর হয় না
৪. কথা শেষ হতে পারে, ‘শেষ কথা’ বলে কিছু হয় না
৩. দেখা হলে বলে দিও, আজও বেঁচে আছি
২. ফুলের রং শেষ পর্যন্ত মিশে যায় নন্দিনীর বুকের রক্তের ইমেজে
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
