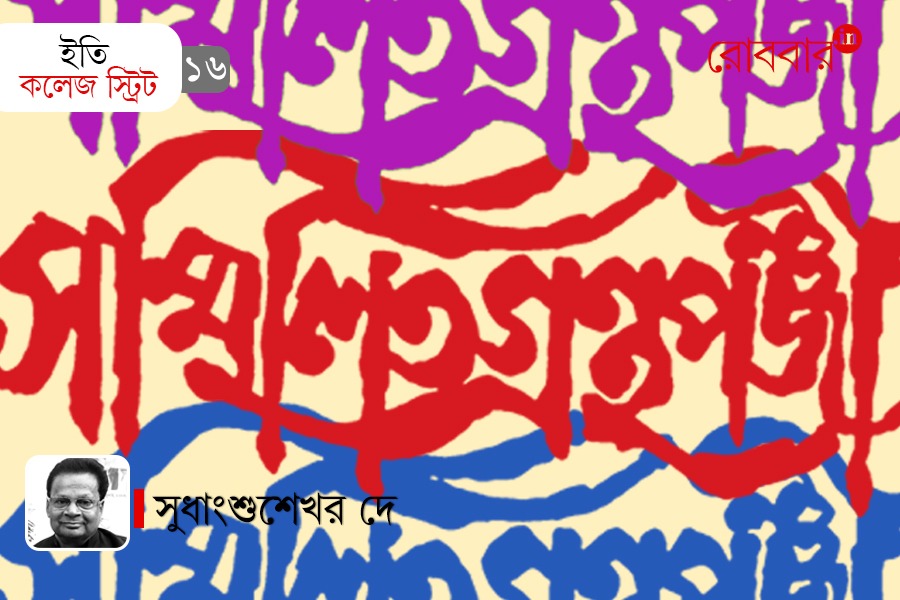
আমরা পশ্চিমবঙ্গ সাহিত্য প্রকাশক সংস্থার পক্ষ থেকে ১৯৮২-তেই এই রকম একটি বই ছেপেছিলাম। ‘কলেজ স্ট্রীট’ পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যার দ্বিতীয় প্রচ্ছদেই সেই ‘সম্মিলিত গ্রন্থপঞ্জী’র বিজ্ঞাপন দেখছি। বিজ্ঞাপনে লেখা হয়েছিল, ‘পুস্তক বিক্রেতাদের কাছে/ গ্রন্থাগারসমূহের কাছে/ গবেষকদের কাছে/ এমন কি/ সাধারণ পাঠকদের কাছেও/ অপরিহার্য/ সম্মিলিত গ্রন্থপঞ্জী/ দাম : তিন টাকা // ডাকে : ছয় টাকা/ পশ্চিমবঙ্গ সাহিত্য প্রকাশক সংস্থার/ উদ্যোগে প্রকাশিত একখানি মূল্যবান/ পুস্তক তালিকা/ কলেজস্ট্রীটের সব বইয়ের দোকানেই পাবেন’।

১৬.
‘কলেজ স্ট্রীট’ পত্রিকা প্রকাশের প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে একটি সংবাদপত্র গোষ্ঠীর পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়ার কথা আগেই বলেছি। কিন্তু পত্রিকার সলতে পাকানোর সবটা গল্প বলা হয়নি। সেসময় একদিন প্রসূনদা বেশ কয়েকজন প্রকাশককে ৬ নম্বর বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিটে তাঁর নবপত্র প্রকাশনার দপ্তরে ডাকলেন। আমি, সবিতেন্দ্রনাথ রায় (ভানুদা), ব্রজকিশোর মণ্ডল (ব্রজদা), সুপ্রিয় সরকার (বাচ্চুদা), বামাচরণ মুখোপাধ্যায় (বামদা)– সবাই সেদিন নবপত্র-এ গিয়েছিলাম। সেখানে বিজ্ঞাপন নিয়ে যে-সংকটে আমরা পড়তে চলেছি তার সব দিক তুলে ধরে প্রসূনদা নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করার পর একে-একে সকলেই নিজের মতামত জানালাম। একটা বিষয়ে সবাই একমত হওয়া গেল যে, এতটা বাড়তি হারে বিজ্ঞাপন দিতে হলে প্রকাশনার অবস্থা কাহিল হবে। সুতরাং, নতুন কোনও উপায় খুঁজতেই হবে। তখনই স্থির হল আরেকটা বড় সভা ডাকা হবে যেখানে এই বিষয়ে আরও সুনির্দিষ্ট কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে। সেই সভার আহ্বায়কদের মধ্যে আমিও ছিলাম এবং সভাটি হল আমাদের ১৩ নম্বর বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিটের বাড়ির দোতলায়। বহু প্রকাশক এসেছিলেন সেদিনের বৈঠকে। যতদূর মনে পড়ছে, সেদিন আনন্দ পাবলিশার্সের বাদলদাও (বাদল বসু) এসেছিলেন। ব্রজদা সেই সভায় তুমুল বক্তৃতা করেন। এমনিতেই তাঁর ভাবনাচিন্তা চিরকালই ছিল একটু প্রতিবাদী ধরনের, তবে সেই সভার কিছুদিন আগেই ওই সংবাদপত্রের সাপ্তাহিক সাংস্কৃতিক কলামে ব্রজদার নাম করে তাঁকে ‘বইপাড়ার দস্যু’ শিরোপা দেওয়ায় তাঁর তেজ স্বাভাবিক কারণেই দ্বিগুণ হয়েছিল। আমাদের বাড়ির সভাতে স্থির হল যে ওই সংবাদপত্র গোষ্টীকে জানিয়ে দেওয়া হবে যে তাদের পত্রিকায় আমরা আর কেউ বিজ্ঞাপন দেব না। এরপর দফায়-দফায় সেই সংবাদপত্রের মালিক পক্ষ এবং প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। ব্যক্তিগত উদ্যোগেও অনেকে বরফ গলানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। এরকম এককাট্টা বইপাড়া আমি তার আগে বা পরে আর কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

একটি সংবাদপত্র গোষ্ঠী বিজ্ঞাপনের হার বাড়ানোয় অন্য কাগজগুলি সেই সময় আমাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়। বিশেষ করে সদ্য প্রকাশিত একটি খবরের কাগজ এবং অন্য একটি পত্রিকা গোষ্ঠী, যাদের নিজেদের সাপ্তাহিক পত্রিকাও ছিল– তারা সেই সংকটের সময় উলটে বিজ্ঞাপনের হার কমিয়ে দেয়। ফলে ওই দুই হাউসে বিজ্ঞাপন যেতে থাকল বেশি-বেশি। কিন্তু কিছুদিন এভাবে চলার পর বোঝা গেল যে, ওই দুই কাগজের বিজ্ঞাপনে বিশেষ কোনও কাজ হচ্ছে না। তবে ইতিমধ্যে প্রায় ছ’-মাস কেটে গেছে। এই ছ’-মাস আমাদের কেউ সেই বিখ্যাত সংবাদপত্র গোষ্ঠীর কাগজে কোনও বিজ্ঞাপন দেয়নি। তারপর অবশ্য আস্তে-আস্তে পরিস্থিতি বদলে যায়। এরপরেই তো আমাদের নিজেদের কাগজ ‘কলেজ স্ট্রীট’ বেরিয়ে গেল। মধ্যবর্তী সময়ে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সাহিত্য প্রকাশক সংস্থা-ও গঠিত হয়ে গেছে, যার প্রথম সভাপতি ছিলেন ভানুদা, সম্পাদক প্রসূনদা আর কোষাধ্যক্ষ হয়েছিলাম আমি।

শুরু থেকেই ‘কলেজ স্ট্রীট’ পত্রিকায় প্রকাশকদের লেখা বা তাঁদের সাক্ষাৎকারভিত্তিক ফিচার ছাপা হত। দ্বিতীয় প্রস্তুতি সংখ্যায় ‘কলেজ স্ট্রীট : সেকাল’ কলামে ছাপা হল বাবাকে নিয়ে একটি সাক্ষাৎকারভিত্তিক ফিচার ‘বইপাড়ার ভগবান’। আগে বাবার কথা বলতে গিয়ে দু-তিনটে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বলা হয়নি। বাবা প্রথমে যে-করপোরেশন স্কুলে বেয়ারার কাজে ঢুকেছিলেন, সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের নাম ছিল প্রভাসচন্দ্র ঘোষ। তিনিই বাবার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। সেসময় বাবার জীবনে আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ হলেন প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক ধীরেন্দ্রলাল ধর। তিনিও স্কুল শিক্ষক ছিলেন। পরে দে’জ পাবলিশিং থেকে ধীরেন্দ্রলালের ‘বাংলার ডাকাত’, ‘নীলকর এলো দেশে’ এইসব বই প্রকাশিত হয়েছে। ধীরেনবাবুর বই তখন প্রকাশিত হত এম সি সরকার থেকে। বাবাকে এম সি সরকার-এ নিয়ে গিয়ে ধীরেনবাবুই প্রথম পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। এ সেই সময়ের কথা যখন বাবা স্কুলের কাজের শেষে কলেজ স্ট্রিট আসা শুরু করেছেন। তখন প্রকাশনার চিন্তা তো দূর অস্ত, একটা বইয়ের স্টলও যে হবে তা সম্ভবত বাবাও ভাবেননি। কিন্তু বাবার স্বপ্ন ছিল চিরকালই উঁচু তারে বাঁধা। সুকিয়া স্ট্রিটের করপোরেশন স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রভাসবাবু বাবাকে তাঁর লেখা বই বিক্রির জন্য দিতেন, সেকথা আগেও বলেছি। কিন্তু তিনিও ভাবেননি, বাবা এ-কাজে এতদূর এগিয়ে যাবেন। একসময় তিনি বাবার পরিশ্রমের ক্ষমতা আর সততার জোর দেখে গাড়ি চালানো শিখতেও বলেছিলেন। যদিও বাবা সবিনয়ে সে-প্রস্তাব খারিজ করে দেন। প্রভাসবাবুর বইয়ের সেলিং এজেন্ট ছিল ২০৪ কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের (এখনকার বিধান সরণি) শ্রীগুরু লাইব্রেরী। শ্রীগুরু লাইব্রেরী আর এম সি সরকার এই দুটো দোকান থেকে বই নিয়ে বিক্রি করা শুরু করে বাবা ধীরে-ধীরে নিজের পুস্তক-বিক্রেতা পরিচয় গড়ে তোলেন। তবে প্রথমেই তো আর দে বুক স্টল হয়নি। বাবা হিন্দুস্থান লাইব্রেরির (আগে দোকানটি ‘মনিরুদ্দিনের দোকান’ বলে পরিচিত ছিল) সামনের রকে (ভবানী দত্ত লেনের উলটোদিকের ফুটপাথে, কলেজ স্ট্রিট মোড়ের একেবারে কাছেই) চট পেতে শনি-রবিবার বই বিক্রি করতেন।

আজ ‘কলেজ স্ট্রীট’ পত্রিকার দ্বিতীয় প্রস্তুতি সংখ্যার পাতা উলটে দেখতে গিয়ে ফের বাবার জীবনসংগ্রামের কথা মনে পড়ে গেল। তবে পত্রিকায় ‘বইপাড়ার ভগবান’ লেখাটি ছাপার আগে কম ঘটনা ঘটেনি। পত্রিকায় লেখাটি ছাপতে যাওয়ার ঠিক আগে বাবার কানে গেল সেই লেখায় তাঁর মুখে কিছু অবান্তর কটু মন্তব্য বসিয়ে ছাপতে দেওয়া হচ্ছে। বাবা সঙ্গে-সঙ্গে প্রসূনদাকে বিষয়টা জানান। প্রসূনদার সঙ্গে বাবার খুবই আন্তরিক সম্পর্ক ছিল। বাবার মুখে সবটা শুনে তিনি তক্ষুনি সেই লেখাটি চেয়ে পাঠান এবং দেখেন বাবা যে-কথা লোকমুখে শুনেছিলেন, তা পুরোপুরি সত্যি। আজ এত বছর পরে কে, কেন, কীভাবে এই অনৈতিক কাজ করেছিল, তা বলে আর কোনও লাভ নেই। বাবার মতো নির্বিবাদী মানুষকে আঘাত দিতে এভাবে তাঁর মুখে কথা বসিয়ে দেওয়ার বিষয়টা সেসময় আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সাহিত্য প্রকাশক সংস্থা-র কেউই ভালোভাবে মেনে নিতে পারেনি। প্রসূনদা লেখককে ডেকে ফের সে-লেখা নতুন করে লিখিয়ে নেন। তার পরেই পত্রিকায় লেখাটি ছাপা হয়।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সাহিত্য প্রকাশক সংস্থা কেবলমাত্র সাহিত্যের বই যেসব প্রকাশক ছাপতেন তাদেরই সংগঠন ছিল। তবে বাংলার প্রকাশকদের আদি সংগঠন হল– বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তকবিক্রেতা সভা। গ্রেস সিনেমার পাশে হিন্দু সৎকার সমিতির বাড়ি– ৯৩ নম্বর মহাত্মা গান্ধী রোডের তিনতলায় সংগঠনের অফিস আজও আছে। এই বাড়িরই দোতলায় ছিল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং-এর দপ্তর। বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তকবিক্রেতা সভা-র প্রতিষ্ঠা ১৯১২ সালে। এই সংগঠনের প্রথম সভাপতি ছিলেন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এবং সম্পাদক শরৎকুমার লাহিড়ী।
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্-এর কথা বাঙালি পাঠকের অজানা নয়। তাঁদের বইতে ঠিকানা লেখা থাকত, ‘২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট’। শুনেছি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় প্রথমজীবনে মেডিক্যাল ছাত্রদের হিন্দু হস্টেলের বাজার সরকার ছিলেন। সেখানকার ছাত্ররা প্রায় সকলেই ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর-এর (যাঁর নামে আজকের আর জি কর হাসপাতাল) বাবা প্রখ্যাত চিকিৎসক দুর্গাদাস কর-এর লেখা ‘মেটেরিয়া মেডিকা’ বইটি কেনে দেখে, তিনি সে-বইয়ের বেশ কিছু কপি কিনে ডাক্তারি ছাত্রদের কাছে বিক্রি করতে শুরু করেন। এভাবেই হিন্দু হস্টেলের সিঁড়ির নিচের একটি আলমারি থেকে ধীরে-ধীরে কলেজ স্ট্রিটে তৈরি হয় তাঁর বিখ্যাত বইয়ের দোকান বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী, যা সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে বিবর্তিত হয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্-এ। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের ছেলে হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের আগ্রহে পরবর্তী সময়ে প্রকাশিত হয় ‘ভারতবর্ষ’ মাসিক পত্র। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ছিলেন এই পত্রিকার সম্পাদক। কিন্তু ১৯১৩ সালের জুন মাসে কাগজের প্রথম সংখ্যা বেরুনোর মাত্র কিছুদিন আগে– ১৭ মে তারিখে ডি এল রায় প্রয়াত হন। এরপর টানা প্রায় ২৬ বছর জলধর সেন পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন। জলধর সেনের সহকারী ছিলেন অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকায় অন্য অনেক বিখ্যাত লেখকের সঙ্গে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়েরও বহু লেখা ছাপা হয়েছে।
শরৎকুমার লাহিড়ীর পরিচয় হয়তো আজ ততটা চেনা লাগবে না। তাঁর বইয়ের দোকানের নাম ছিল এস কে লাহিড়ী অ্যান্ড কোং, ঠিকানা ছিল ৫৬ কলেজ স্ট্রিট। কলেজ স্ট্রিট মার্কেটের (বর্ণপরিচয়) উলটো দিকের ফুটপাথে, পাতিরাম-এর পাশে এই ঠিকানায় এখন দেখি আদি ইন্ডিয়ান সিল্ক হাউসের দোকান হয়েছে। শরৎকুমার লাহিড়ী ছিলেন ‘ইয়ং বেঙ্গল’ দলের অন্যতম সদস্য রামতনু লাহিড়ীর পুত্র। শরৎকুমার লাহিড়ীর বই ব্যবসায় আসা নিয়েও মজার গল্প আছে। একসময় তিনি চাকরি করতেন। কিন্তু তাঁর ইচ্ছে ছিল নিজে একটা ব্যবসা শুরু করা। বাড়িতে তখন তাঁর বৃদ্ধ পিতা, পরিবারের আর্থিক অবস্থাও ভালো নয়। এরকম সময়ে শরৎকুমার একদিন হাজির হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কাছে। বিদ্যাসাগরমশাই সব কথা শুনে বলেন– তুমি যদি বই বিক্রির ব্যবসায় আসো তাহলে মান, সম্ভ্রম এবং সততা রক্ষা করতে পারবে। তিনি পরামর্শ দেন, কিছু টাকা জোগাড় করে ব্যাবসায় নেমে পড়তে এবং তাঁর নিজের সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটরি থেকে ১০০ টাকার বই বিনামূল্যে অগ্রিম পাওয়ার ব্যবস্থাও করে দেন। ওই বই বিক্রি করে ঋণ শোধ করলে সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটরি আবার অগ্রিম বই দেবে এরকম বন্দোবস্ত হয়। বিদ্যাসাগর এভাবে শরৎকুমারকে নতুন রাস্তা দেখালেও, তাঁর বাবা রামতনু লাহিড়ী সব শুনে না কি জিগ্যেস করেন যে, ব্যবসা করে কীভাবে সততা বজায় রাখা সম্ভব? উত্তরে শরৎকুমার বলেন, উচিত মূল্যে বই কিনে উচিত মূল্যে বিক্রি করলে সততা রক্ষা করা যাবে। এই শুনে রামতনু লাহিড়ী বলেছিলেন, উচিত মূল্যে কিনে উচিত মূল্যে বিক্রি করলে লাভটা কোত্থেকে আসবে! অবশ্য তিনি পুত্রের পুস্তকব্যবসায় আসার ইচ্ছেয় কোনও প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেননি। ক্রমে এস কে লাহিড়ী অ্যান্ড কোং বইপাড়ার একটি বড় সংস্থায় পরিণত হয়।
বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তকবিক্রেতা সভা প্রকাশক এবং পুস্তক বিক্রেতাদের যৌথ সংগঠন। আমাদের তৈরি করা পশ্চিমবঙ্গ সাহিত্য প্রকাশক সংস্থা সেদিক থেকে প্রকাশকদের তৃতীয় সংগঠন। এর আগে ১৯৭৫ সালে গঠিত হয়েছিল পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ড। গিল্ড প্রতিষ্ঠার পরের বছর থেকে শুরু হয় ‘কলিকাতা পুস্তক মেলা’ আর আমরা শুরু করলাম ‘কলেজ স্ট্রীট’ পত্রিকা। ‘কলেজ স্ট্রীট’ পত্রিকা শুরু করার পর থেকেই আমরা চাইছিলাম একটা ডিরেক্টরি জাতীয় বই প্রকাশ করতে যাতে বইপাড়ার সব প্রকাশনার যাবতীয় বইয়ের হদিশ পাওয়া যাবে, যাকে বলা যায়, বুকস ইন প্রিন্ট। ১৯৮৯ সাল থেকে এই নামে পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ড থেকে একটি বই প্রকাশ করা হয়। এখন বইটির নাম, ‘Fair Directory & বাংলা প্রকাশনা’। গত বইমেলাতেও সত্যব্রত ঘোষাল বইটি সংকলন করেছেন, প্রচ্ছদ করেছেন মৃণাল শীল। আমরা পশ্চিমবঙ্গ সাহিত্য প্রকাশক সংস্থার পক্ষ থেকে ১৯৮২-তেই এই রকম একটি বই ছেপেছিলাম। ‘কলেজ স্ট্রীট’ পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যার দ্বিতীয় প্রচ্ছদেই সেই ‘সম্মিলিত গ্রন্থপঞ্জী’র বিজ্ঞাপন দেখছি। বিজ্ঞাপনে লেখা হয়েছিল, ‘পুস্তক বিক্রেতাদের কাছে/ গ্রন্থাগারসমূহের কাছে/ গবেষকদের কাছে/ এমন কি/ সাধারণ পাঠকদের কাছেও/ অপরিহার্য/ সম্মিলিত গ্রন্থপঞ্জী/ দাম : তিন টাকা // ডাকে : ছয় টাকা/ পশ্চিমবঙ্গ সাহিত্য প্রকাশক সংস্থার/ উদ্যোগে প্রকাশিত একখানি মূল্যবান/ পুস্তক তালিকা/ কলেজস্ট্রীটের সব বইয়ের দোকানেই পাবেন’। বিজ্ঞাপনের নিচে ঠিকানার জায়গায় আমাদের দে’জ পাবলিশিং-এর ঠিকানা, ১৩ নম্বর বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট লেখা আছে। যদি খুব ভুল না করি তাহলে এই ‘সম্মিলিত গ্রন্থপঞ্জী’ দু-বার মাত্র প্রকাশিত হয়েছিল। ‘সম্মিলিত গ্রন্থপঞ্জী’ সংকলন ও ছাপার ভার ছিল বামাদার ওপর।
১৯৮২ সালের বইমেলাতেই পশ্চিমবঙ্গ সাহিত্য প্রকাশক সংস্থার একটি স্টল হয়েছিল এবং সেই স্টল প্রচুর মানুষের নজর কেড়েছিল। লেখক-শিল্পী-সহ সমাজের বহু বিশিষ্টজন সেবার স্টলে আসেন। এই স্টলে আমাদের পত্রিকার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন উপলক্ষে সাংবাদিক সম্মেলনও হয়েছিল। সেবার দশ দিনের বইমেলায় প্রায় ২৫ হাজার কপি পত্রিকা বিক্রি হয়ে যায়। কবি শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, বিজয়া মুখোপাধ্যায় এবং উৎপলকুমার বসুকে নিয়ে একদিন স্টলে কবিতাপাঠের আসরও বসেছিল।
বইপাড়ার বহু পুরোনো দিনের কথার পরে এবার এমন কয়েকজনের কথা বলি যাঁদের আমি দেখেছি। প্রথমেই বলি শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কথা। ১৯৪৩ সালের ১১ অগাস্ট শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আর মনোজ বসুর সম-স্বত্বে যৌথ মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বেঙ্গল পাবলিশার্স। মনোজ বসু বেঙ্গল পাবলিশার্সের স্বত্বাধিকারী হলেও সাহিত্যিক হিসেবে তিনি ততদিনে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর ‘নিশিকুটুম্ব’ তো বাংলার চিরায়ত সাহিত্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। অন্যদিকে, শচীনবাবু ছিলেন আদ্যন্ত সুরুচিসম্পন্ন পুস্তক ব্যবসায়ী ও প্রকাশক। বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তকবিক্রেতা সভা-র তিনি ছিলেন সামনের সারির মুখ, দক্ষ সংগঠক। তিনি দীর্ঘদিন সংগঠনের সম্পাদকের পদে কাজ করেছেন। বেঙ্গল পাবলিশার্সের আগে শচীনবাবু ডা. নীহাররঞ্জন গুপ্ত-র সঙ্গে যৌথভাবে ‘সবুজ সাহিত্য আয়তন’ নাম দিয়ে কিছু কিছু বই প্রকাশ করেন। সেইসব বই বিক্রি হত কমলা বুক ডিপো থেকে। কেননা সেসময় শচীনবাবু কমলা বুক ডিপোর পাবলিকেশন ম্যানেজার ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ডা. গুপ্ত যুদ্ধে আহতদের চিকিৎসার কাজে চলে গেলে সবুজ সাহিত্য আয়তন বন্ধ হয়ে যায়। শচীনবাবু যোগ দেন বেঙ্গল পাবলিশার্সে। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রতিষ্ঠার বেশ কয়েক বছর পর প্রতিষ্ঠিত হয় প্রকাশ ভবন। এটিও ছিল মনোজ বসু এবং শচীনবাবুর যৌথ মালিকানায়। তক্ষণ বেঙ্গল থেকে গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ বেরুত, আর প্রকাশ ভবন থেকে ইশকুল-পাঠ্য বই এবং সামান্য কিছু কলেজ-পাঠ্য বই। এই সময় মনোজ বসু আর শচীনবাবু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে অনুরোধ করে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ‘ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ’ বইটি ছাপার ব্যবস্থা করেন। এর আগে বইটি ছাপা হত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই। কিন্তু ১৯৬৪ সালে বেঙ্গল পাবলিশার্সের বদলে প্রকাশ ভবন থেকে প্রকাশিত হয় সুনীতিকুমারের আগ্রহেই। ততদিনে বেঙ্গল পাবলিশার্স আর প্রকাশ ভবন আলাদা হয়ে গেছে। মনোজ বসুর রয়ে যায় বেঙ্গল পাবলিশার্স আর প্রকাশ ভবন হয় শচীনবাবুর। বই ও টাইটেল দুই কোম্পানির মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। পরে শচীনবাবু বাক্-সাহিত্য নামেও একটি প্রকাশনার কাজ শুরু করেন।
শচীনবাবুর সঙ্গে আমার বাবার একটা ঘটনার কথা সাহিত্যিক শংকর-এর মুখে শুনেছিলাম সেকথা আগেই বলেছি। শংকর-এর অনেক বই প্রকাশ ভবন করত। বিশ্ববাণীও করত। শচীনবাবু অনেক ক্লাসিক বই তৈরি করেছিলেন– সুনীতিবাবুর ‘রবীন্দ্র-সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যাম-দেশ’; বিনয় ঘোষের ‘বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ’, ‘পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি’ ১-৪ খণ্ড; সতীনাথ ভাদুড়ীর একাধিক বই– ‘ঢোঁড়াইচরিত মানস’, ‘অচিন রাগিনী’, ‘সতীনাথ বিচিত্রা’; ‘অবনীন্দ্র রচনাবলী’; জরাসন্ধের ‘লৌহ কপাট’, তারাশঙ্করের ‘আরোগ্য নিকেতন’, ‘নাগিনী কন্যার কাহিনী’; নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘উপনিবেশ’, ‘কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ’; পুলিনবিহারী সেন-এর সম্পাদনায় ‘রবীন্দ্রায়ণ’ দু-খণ্ড; বনফুলের ‘জঙ্গম’; মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’, ‘শহরবাসের ইতিকথা’ ইত্যাদি অসাধারণ সব বই। প্রকাশ ভবন থেকেই প্রকাশিত হত ‘কালি ও কলম’ পত্রিকা। প্রথমে এর সম্পাদক হওয়ার কথা ছিল শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের। তিনি তখন আবার ‘গল্প ভারতী’র সম্পাদক, ফলে সাহিত্যিক বিমল মিত্র এর প্রথম সম্পাদক হন। পরে অবশ্য শচীনবাবু নিজেই সম্পাদনা করতেন। একসময় তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র শুভ মুখোপাধ্যায় তাঁকে সম্পাদনার কাজে সাহায্য করতেন। শচীনবাবু আমার থেকে বয়সে অনেকটাই বড়ো ছিলেন, তাই তাঁর কাছে স্লিপ নিয়ে বই আনতে গেলেও কথা বিশেষ হত না। তবে শচীনবাবুর পরে তাঁর ছেলে স্বপনবাবু প্রকাশ ভবন-এর কর্ণধার হলে তাঁর সঙ্গে আমার খুবই হৃদ্যতা হয়। অমায়িক, সজ্জন স্বপনবাবু বয়সে আমার থেকে হয়তো বেশ খানিকটা বড়ো ছিলেন, তবু আমার সঙ্গে বন্ধুর মতোই ব্যবহার করতেন।

শচীনবাবুর প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল, আমি যখন বইপাড়ায় এলাম তখন বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তকবিক্রেতা সভার সামনের সারিতে শচীনবাবু ছাড়াও ছিলেন বিভাস ভট্টাচার্য, সুনীল বসু (কাটুদা), মজহারুল ইসলাম, মৃণাল দত্ত, এম আর আখতার প্রমুখ। সারস্বত প্রকাশনীর বিভাসদা (বিভাস ভট্টাচার্য) আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। তাঁদের দোকান ছিল ২০৬ নম্বর বিধান সরণিতে। বিভাসবাবুরা কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের পরিবারের সদস্য। সেই সূত্রে সদ্যপ্রয়াত আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যেরও নিকটাত্মীয়। সারস্বত প্রকাশনী থেকে ‘সারস্বত’ নেমে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা বেরুত। দিলীপকুমার গুপ্ত (ডি কে) এবং অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশিত ‘সারস্বত’ আর সারস্বত প্রকাশনীর পত্রিকা ‘সারস্বত’ কিন্তু এক নয়। ডি কে, অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত পত্রিকার প্রকাশক ও মুদ্রক ছিলেন প্রখ্যাত শিল্পী রঘুনাথ গোস্বামী। তবে সারস্বত প্রকাশনীর পত্রিকার কারণেই তাঁরা নিজেদের পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যা থেকে প্রচ্ছদের নামলিপির নিচে ‘প্রকাশ’ শব্দটি যোগ করেন। ‘সারস্বত প্রকাশ’-এর মাত্রই আটটি সংখ্যা ছাপা হয়েছিল, কিন্তু প্রতিটি সংখ্যাই নিজস্বতায় ভরপুর ছিল। তাঁরা পত্রিকার নাম বদল নিয়ে চতুর্থ-পঞ্চম সংখ্যায় লিখেছিলেন– “ ‘সারস্বত’ নামে অন্য একটি পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ায় পাঠকদের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। সেই কারণে আমাদের পত্রিকার নাম রাখা হয়েছে সারস্বত প্রকাশ”। সারস্বত প্রকাশনীর ত্রৈমাসিক সেই অর্থে কালেক্টর্স আইটেম হয়ে উঠতে না পারলেও তাদের লেখক সূচিও কিছু কম আকর্ষণীয় ছিল না। ন্যাশনাল বুক এজেন্সীর কাটুদা আবার এই সময়ের ঔপন্যাসিক কুণাল বসুর বাবা। কুণাল বসুর ‘তেজস্বিনী ও শবনম’ এবং ‘এঞ্জেল’ নামে দুটি বই আমরা প্রকাশ করেছি। মজহারুল ইসলামের ছিল তাঁর নবজাতক প্রকাশনী– কলেজ স্ট্রিট মার্কেটে। এশিয়া পাবলিশিং-এর মৃণাল দত্তের দোকান প্রথমে কলেজ স্ট্রিট মার্কেটে ছিল, পরে এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পাশে উঠে আসে। এম আর আখতারের প্রকাশনা সংস্থার নাম এখন আর মনে করতে পারছি না– তাঁরও কলেজ স্ট্রিট মার্কেটে দোকান ছিল।
কলেজ স্ট্রিটে আমার বয়োজ্যেষ্ঠ প্রকাশক ছিলেন নিউ এজ-এর জানকীনাথ সিংহ রায়। আমি যখন প্রকাশনা শুরু করিনি, তখন থেকেই তাঁর কাছে বিভিন্ন সময়ে বই আনতে গিয়েছি। তাঁর প্রকাশনা থেকে বেরুনো বইগুলো আমাকে টানত। তখনকার বিখ্যাত লেখদের অসামান্য সব বই তিনি প্রকাশ করেছিলেন। নিউ এজের বই সেসময় খুবই জনপ্রিয় ছিল– বিমল মিত্রের ‘সাহেব বিবি গোলাম’, সৈয়দ মুজতবা আলীর ‘দেশে-বিদেশে’ শংকর-এর ‘কত অজানারে’, যাযাবার-এর (বিনয় মুখোপাধ্যায়) ‘দৃষ্টিপাত’, মহাশ্বেতা দেবীর ‘ঝাঁসির রানী’। আমি প্রকাশনা শুরু করেছি খবর পেয়ে উনি আমাকে মাঝে-মাঝে দু’-একটা প্রশ্ন করতেন। খুবই সাধারণ প্রশ্ন, কিন্তু আমার করা বই তাঁর নজরে এসেছে দেখে আমি মনে মনে খুশি হতাম। তিনি মূলত জানতে চাইতেন আমাদের বই নিয়ে পাঠকের কাছ থেকে কেমন সাড়া পাচ্ছি সে-বিষয়ে, সঙ্গে যোগ করতেন আমাদের বড়ো কাউন্টার থাকার সুবিধার কথাও।
আমি আবার ৭৩ নম্বর মহাত্মা গান্ধী রোডে সুবর্ণরেখা-য় ইন্দ্রনাথ মজুমদারের কাছেও মাঝে-মাঝেই যেতাম। প্রথম দিকে মূলত তাঁর প্রকাশ করা বই কিনতেই যেতাম। কিন্তু ধীরে-ধীরে ইন্দ্রদার সঙ্গে আমার খুব ভালো সম্পর্কও তৈরি হয়ে যায়। আমি বুঝতে পেরেছিলাম মানুষটা অসম্ভব ক্রিয়েটিভ। আমি এমনিই কখনও-কখনও তাঁর সঙ্গে গল্প করতে যেতাম। তিনি নানারকম বইয়ের কথা বলতেন, পরামর্শও দিতেন। আমাদের কোনও বই ভালো লাগলে সেকথাও বলতেন। ইন্দ্রদার সুবর্ণরেখা-র ঠিকানা থেকেই ‘এক্ষণ’ পত্রিকা প্রকাশিত হত। আমি বেশ কয়েকবার সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার বইয়ের প্রুফও ইন্দ্রদার কাছে দিয়ে এসেছি। সেসময় দে’জ পাবলিশিং থেকে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘হায় চিরজল’, ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’, ‘হে সায়ংকাল’– এই তিনটে কবিতার বই প্রকাশিত হয়। সুবর্ণরেখার ওই বাড়িতেই একসময় অনেকগুলো প্রকাশনা ছিল– বর্ণালী, রূপরেখা, অপর্ণা, নাথ পাবলিশিং ইত্যাদি।

বেঙ্গল পাবলিশার্সের মনোজ বসুকে কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। মনোজ বসুর দুই ছেলে– মণীশ বসু আর ময়ূখ বসু। মণীশদা সম্ভবত কোথাও চাকরি করতেন। বইপাড়ায় তিনি অনিয়মিত ছিলেন। তবে ময়ূখদার সঙ্গে বলতে গেলে আমার প্রাত্যহিক যোগাযোগ ছিল। আমরা যৌথভাবে একটা বইও করেছিলাম। এর আগে বেঙ্গল পাবলিশার্স দুই কবির যৌথ বই করেছিল– শক্তি চট্টোপাধ্যায় আর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘যুগলবন্দী’। সে-বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ আমি ছেপেছিলাম। কিন্তু দু’-জন বাংলা প্রকাশক যৌথভাবে বই ছাপছে এটা বেশ অভিনব ব্যাপার ছিল। সেটা ১৯৮৩ সাল। ভারত সেবছর প্রথম বার ক্রিকেটের বিশ্বকাপ জিতেছে। স্বাভাবিকভাবেই ক্রিকেট নিয়ে মানুষের উৎসাহ খুব বেশি। ময়ূখদা একদিন বললেন সুনীল গাভাসকরের ‘আইডলস’ বইটা বাংলায় করলে বেশ হয়। আমি উত্তরে বললাম, ‘তা করুন না। ভালোই তো হবে।’ কিন্তু তিনি বললেন, ‘চলো আমরা দু-জনে মিলে করি।’ তারপর উনিই সে-বইয়ের অনুবাদ করালেন। রূপা-র সঙ্গে আমাদের বাংলায় বই ছাপার চুক্তি হল ১৯৮৩-র ডিসেম্বর মাসের ৫ তারিখে, আর ১৯৮৪-র ফেব্রুয়ারিতে বইমেলায় প্রকাশিত হল সুনীল গাভাসকরের ‘আইডলস’-এর বাংলা অনুবাদ। ‘আইডলস’ ছাপা হয়েছিল মদন মিত্র লেনে ব্রজলাল চক্রবর্তীর মহামায়া প্রেসে। বইয়ের একত্রিশটি লেখা বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন– সূর্য ঘোষ, ধীমান দত্ত, পল্লব বসু মল্লিক, অরূপ বসু, অলক চট্টোপাধ্যায় এবং অশোক দাশগুপ্ত। যৌথ প্রকাশনা হওয়ায় বইয়ের স্পাইনে লেখা থাকত ‘D/B’। হাজার কপি ছাপা হলে আমরা পাঁচশো-পাঁচশো করে ভাগ করে নিতাম। বেশিরভাগ সময়েই আমার ভাগেরটা আগে শেষ হয়ে যেত, তখন আবার ময়ূখদার কাছ থেকে তাঁর অবশিষ্ট বইগুলো এনে বিক্রি করতাম। শেষ হয়ে গেলে ফের হাজার কপি ছাপতাম। সে একটা অন্য সময় ছিল বলে এখন মনে হয়, যখন হাজার কপির কমে বই ছাপার কথা কোনো প্রকাশক ভাবতই না। একটু সাহস করে একবারে বাইশ-শো ছেপে নিলে আরও সুবিধে হত। দে’জ পাবলিশিং-এর শুরুর দিন থেকে আমি কখনও অল্প সংখ্যায় বই ছাপতাম না।
লিখন শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়
…………………… ইতি কলেজ স্ট্রিট-এর অন্যান্য পর্ব ……………………
পর্ব ১৫: নিছকই একটা পত্রিকা নয়, ‘কলেজ স্ট্রীট’ আমাদের আবেগ
পর্ব ১৪: খুদে পাঠকদের জন্য মিনিবই তৈরির কথা প্রথম ভেবেছিলেন অভয়দা
পর্ব ১৩: কয়েকটি প্রেসের গল্প
পর্ব ১২: দীর্ঘায়ু বই ও আইয়ুব পরিবার
পর্ব ১১: প্রেমের নয়, অপ্রেমের গল্প সংকলনের সম্পাদনা করেছিলেন সুনীল জানা
পর্ব ১০: ছোট্ট অপুকে দেখেই রঙিন ছবিতে ভরা টানটান গল্পের বই করার ইচ্ছে জেগেছিল
পর্ব ৯: চানঘরে গান-এ সত্যজিৎ রায়ের চিঠি থাকায় ব্যাপারটা গড়িয়েছিল কোর্ট কেস পর্যন্ত
পর্ব ৮: প্রকাশক-লেখকের কেজো সম্পর্কে বুদ্ধদেব গুহর বিশ্বাস ছিল না
পর্ব ৭: পুজো সংখ্যায় না-বেরনো উপন্যাস বই আকারে সুপারহিট
পর্ব ৬: মানবদার বিপুল অনুবাদের কাজ দেখেই শিশির দাশ তাঁর নাম দিয়েছিলেন– ‘অনুবাদেন্দ্র’
পর্ব ৫: সাতবার প্রুফ দেখার পর বুদ্ধদেব বসু রাজি হয়েছিলেন বই ছাপানোয়!
পর্ব ৪: লেখকদের বেঁচে থাকার জন্য অনেক কিছুই লিখতে হয়, প্রফুল্ল রায়কে বলেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র
পর্ব ৩: পয়লা বৈশাখের খাতায় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় মজাচ্ছলে লিখেছিলেন, ‘সুধাংশুরা রাজা হোক’
পর্ব ২: বাংলা মাসের সাত তারিখকে বলা হত ‘গ্রন্থতিথি’, বিজ্ঞাপনেও বিখ্যাত ছিল ‘৭-ই’
পর্ব ১: সত্তরের উথাল-পাথাল রাজনৈতিক আবহাওয়ায় আমি প্রকাশনার স্বপ্ন দেখছিলাম
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
