
সিনেমার ভাষা যে কি অলৌকিক পর্যায়ে যেতে পারে তার উদাহরণ কোমল গান্ধার। ‘বিদ্রোহ আজ, বিদ্রোহ চারিদিকে’ গানের সময় দেখা যাবে দেওয়ালে টাঙানো একটি সিংহের মূর্তির শট। সের্গেই আইজেনস্টাইনের ‘ব্যাটলশিপ পোটেমকিন’-এর বিখ্যাত ওডেসা স্টেপস দৃশ্যের শেষে সেই সিংহের মূর্তিগুলোর মতো। বিপ্লব এবং মন্তাজ। সতীন্দ্র ভট্টাচার্য (শিবনাথ) এবং অনিল চ্যাটার্জীর একটি দৃশ্যে (প্রায় ডুয়েলের মতো) আশ্চর্য ওয়ান এইটি ডিগ্রি জাম্প। কিছু জটিল কম্পোজিশন, লাইটিং এবং মুভমেন্ট। বিশেষত যেখানে অনসূয়া চলে যাচ্ছে এবং একটি বাচ্চা তার আঁচল টেনে ধরে। লো অ্যাঙ্গেলে বাচ্চাটার সাজেশনে অনসূয়ার মিড এবং ব্যাকগ্রাউন্ডে থামটা এমনভাবে আলো করা হয়েছে, দেখে মনে হবে কাস্তে।

‘কোমল গান্ধার’ সংক্রান্ত কিছু পয়েন্ট, যা দেখতে দেখতে মনে হল
এ লেখাটি লিখতে বসার জন্য আরেকবার ‘কোমল গান্ধার’ দেখলাম। আগে অনেকবার দেখেছি। এবারে লিখব বলে প্রথম ১০ মিনিট বেশ থামিয়ে থামিয়ে নোট নিতে নিতে দেখছিলাম। থামাতে পারলাম না। আবার গোটাটা একবারেই দেখে ফেললাম। অনেক কিছু লিখে কাটাকুটি করার পর বুঝতে পারছি, একটা জাবদা গদ্য লিখে ফেলা আমার পক্ষে একান্তই মুশকিল। ‘কোমল গান্ধার’ নিয়ে বেশি লেখার ক্ষমতা আমার নেই। তাই ছবি দেখতে দেখতে যা মনে হয়েছে তাই পয়েন্ট আকারে তুলে দিলাম। কিছুটা অগোছালো লাগতে পারে। পাঠক, ক্ষমা করবেন।
এক.
প্রথমেই বলতে হয়, ছবির টাইটেল কার্ডের আগে সেন্সর কার্ডের কথা। ভারতের সেন্সর ব্যবস্থা অনুযায়ী, ছবি সেন্সরপ্রাপ্ত হলে ছবির আগে সেই কার্ড জুড়ে দিতে হয়। সেখানে দেখতে পাচ্ছি, ছবিটি ৩৫ মিমি সেলুলয়েডে তোলা, ১৪ রিলের ছবি। তারিখ ৬ মার্চ, ১৯৬১। সেন্সর কার্ডে অ্যাপ্লিক্যান্টের নাম দেওয়া আছে চিত্রকল্প। প্রযোজকের নাম ঋত্বিক ঘটক। মূল টাইটেল কার্ডটি অপূর্ব হাতের লেখায় একটি আলোছায়া সমৃদ্ধ ব্যাকগ্রাউন্ডের ওপর লিখিত। আবহসংগীতে ছবির মূল সুর এবং ছন্দ ধরা আছে। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত থেকে লোকগীতি– আমের তলায় ঝামুর ঝুমুর/ কলাতলায় বিয়া/ আইলেন গো সুন্দরীর জামাই/ মুটুক মাথায় দিয়া/ আজ হইব সীতারও বিয়া। এছাড়া ছবিটিতে পরে গিয়ে রবীন্দ্র সংগীত, গণসংগীত যুক্ত হয়ে আরেকটি সাংগীতিক চিত্রনাট্য তৈরি করবে। যাই হোক, টাইটেল কার্ডে অন্য অনেক নামের সঙ্গে একটি নাম দৃষ্টি আকর্ষণ করল– পুনু সেন– সহকারী পরিচালক। পুনু সেন সম্ভবত রমেশ সেন, যিনি মূলত সত্যজিৎ রায়ের সহকারী ছিলেন। মৃণাল সেন, তরুণ মজুমদার এবং আরও অনেকেরই পরিচালনায় সহকারী হয়েছেন। আমার কাছে সব থেকে চিত্তাকর্ষক ব্যাপার হল– ‘শ্রী ঋত্বিক কুমার ঘটক প্রণীত’, এই কথাটি। প্রণয়ন অর্থে রচনা, নির্মাণ ইত্যাদি। আলাদা করে চিত্রনাট্য, পরিচালনা ইত্যাদির উল্লেখ নেই। এরকমভাবে ছবির চিত্রনাট্যকার, পরিচালকের নাম আসাটা ভারতীয় ছবিতে বিরল। আজকাল বেশিরভাগের ছবিতেই ‘এ ফিল্ম বাই অমুক’ বা ‘তমুকের ছবি’ লেখা দেখতে পাই। ব্যাপারটা ফরাসিতে আরও মনোহর লাগে দেখতে। ‘Un film de’– আমরা বলতাম– উন ফিল্ম দে। সঠিক উচ্চারণ জানি না।

দুই.
ছবিটির শুরুতে একটি মুখবন্ধ লেখা আছে:
–নানা জায়গা থেকে নাটক-পাগল ছেলেমেয়েরা এসে জড়ো হয়, একত্রে দল করে– সেই দলের মধ্যে গড়ে ওঠে স্নেহ-ভালবাসা-ঈর্ষা-হিংসায় জড়িয়ে তাদের পরিবার। সাধারণ অর্থে পারিবারিক জীবন তাই এঁদের নেই। এইরকম একটি পরিবারের ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের কথটুকু মাত্র এ ছবিতে বলার চেষ্টা করা হয়েছে।।
মুখবন্ধেই মোটামুটি আভাস দিয়ে দেওয়া আছে ছবিটি কাদের নিয়ে তৈরি বা কাদের কথা বলবে। যদিও আমরা সবাই জানি, এ ছবি শুধু এইটুকু বলে থেমে থাকেনি। দেশভাগের ফলাফল, তৎকালীন আইপিটিএ-র নিজস্ব সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব এবং সেই সূত্রে ছবির চরিত্রদের নিজস্ব দ্বিধাদ্বন্দ্বের জটিলতা সম্পৃক্ত অবস্থানের কথা বলছে এই ছবি। শুধু চিত্রনাট্যের বিন্যাস, সংলাপ বা গল্পের মাধ্যমে বলছে না। সমস্ত শট ডিভিশন, ফ্রেম কম্পোজিশন, ক্যামেরা মুভমেন্ট, লেন্সের ব্যবহার (বিশেষত ক্লোজ আপের ক্ষেত্রে), আলোকসম্পাত, শব্দ ব্যবহারের স্বাতন্ত্র্য, শিল্প নির্দেশনা, সম্পাদনার নিয়মভাঙা কাট, অভিনয়ের আঙ্গিক, সংগীতের অভাবনীয় বুনন, রবীন্দ্রনাথ থেকে শেক্সপিয়র, অভিজ্ঞান শকুন্তলা, লোকগীতি– সব কিছু দিয়েই ছবিটি তার নিজের কথা বলছে। ঋত্বিক ঘটকের ছবি দেখতে গিয়ে প্রতিবার আমার কাছে ভাবনাচিন্তার নতুন নতুন দিক উন্মোচিত হয়।
তিন.
–ক্যান যামু? বুঝা আমারে, এমন কোমল দ্যাশটা ছাইড়া, আমার নদী পদ্মারে ছাইড়া, আমি যামু ক্যান?
–যাইবা খাইবার লাইগ্যা, এই শেষ সুযোগ এখনও শরণার্থী হও।
–শরণার্থী?
–বাস্তহারা শরণার্থী, নাম দিসে কাগজের বাবুরা।
–আ… ছি ছি ছি ছি…
ভৃগু নাটকে বৃদ্ধ গ্রামবাসীর চরিত্রে অভিনয় করছে। ওপরের সংলাপগুলি হওয়ার খানিক বাদে শেষ সংলাপে হল হাততালিতে ফেটে পরে।
– …আমি কপালপুড়া, আমার বাপ কপালপুড়া, আমার চোদ্দ পুরুষ কপালপুড়া, এই যে কয়টার জন্ম দিসি সব কয়টা কপালপুড়া, নইলে আমি পদ্মার পাড়ে জন্মাইলাম ক্যান?
এই আর্তি, এই আর্তনাদ শুধু ওই নাটকটির চরিত্র বৃদ্ধ গ্রামবাসীটির নয়। এই আর্তনাদ ছবির অন্যতম মূল চরিত্র ভৃগুর। ঘটনাচক্রে এই আর্তনাদ অনসূয়ারও। অনসূয়া ছাড়া ভৃগু চরিত্র অসম্পূর্ণ। ভৃগু ছাড়া অনসূয়া চরিত্র অসম্পূর্ণ। কেন, সে কথায় পরে আসছি। আমার মা একটা কথা বলেন– ঠাঁইনাড়া। সমস্ত ছবি জুড়ে এই ঠাঁইনাড়া হওয়ার বেদনা কখনও দমকা হাওয়ার মতো কখনও তিরতির করে দর্শকের মনে বইতে থাকে।
চার.
ভৃগুকে ছবির প্রথম দিকে দেখে মনে হবে, লোকটা খারাপ না হলেও অত্যন্ত রাগী, উদ্ধত, একবগ্গা একজন যুবক। নিজের কাজটুকু বুঝে নেওয়ার জন্য লোকের সঙ্গে যারপরনাই খারাপ ব্যবহার করতে পারে। থিয়েটার দল চালায় স্বৈরাচারীর মতো। সবাই ওকে ভয় পায়। এমনকী, অনসূয়াও তাকে রুক্ষ, নির্বান্ধব বলে অভিহিত করে। অথচ ভৃগু তার নাটকের প্রতি, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ এবং অসম্ভব প্যাশনেট। বিভিন্ন ফিল্ম থিয়োরিস্টরা ‘জঞ্জির’ ছবিতে অমিতাভ বচ্চনের চরিত্রটিকে স্বাধীনতা উত্তর ভারতীয় ছবিতে অ্যাংরি ইয়ং ম্যান চরিত্রের আবির্ভাব বলে থাকেন। আমার মনে হয়েছে অবনীশ ব্যানার্জি অভিনীত ভৃগু চরিত্রটিই সম্ভবত ভারতীয় ছবিতে প্রথম অ্যাংরি ইয়ং ম্যান বা রাগী যুবক চরিত্র।
ভৃগুর সঙ্গে অনসূয়ার প্রথম দেখা হয় থিয়েটার চলতে চলতে। চরিত্র কম পড়ে যাওয়ায় প্রতিদ্বন্দ্বী দলে (যে দল ভৃগুদের দল ভেঙে তৈরি হয়) সদ্য যোগ দেওয়া অনসূয়া ভূগুদের সাহায্য করার জন্য একটি ক্রাউড চরিত্র করে দিতে রাজি হয়। ব্যাকস্টেজে ভৃগু এবং অনসূয়ার দেখা হয়। ভৃগু অনসূয়াকে মাথায় ঘোমটা তুলে নিতে বলে নিজেই ঘোমটা তুলে দেয়। নিজেই এহেন অনধিকার চর্চা বুঝতে পেরে খানিক অনভ্যস্ত লজ্জায় জিভ কাটে, একটু হাসে তারপর গম্ভীর হয়ে চলে যায়। অনসূয়া ভৃগুর দিকে তাকিয়ে থাকে। আবহে বাজতে থাকে– ‘আজ হইব সিতারও বিয়া।’ সুপ্রিয়া দেবী এগিয়ে আসেন ক্যামেরার দিকে (সুপ্রিয়া দেবী বলছি, কারণ, এর’ম অপূর্ব সুন্দরী সুপ্রিয়া দেবীকে ‘মেঘে ঢাকা তারা’ ছাড়া আর কোনও ছবিতে দেখতে পাবেন না)। ক্লোজ আপে মুখের ওপর আলোছায়ার খেলা চলতে থাকে। প্রেম। মিরান্ডার আবার প্রেম হয়। এবার ফার্দিনান্দ নয়। ভৃগু। অনসূয়ার ফার্দিনান্দ অনেক দূরে বিদেশে থাকে। বহু যুগ দেখা হয়নি। অনসূয়া আশা করে বসে আছে কবে ফার্দিনান্দ (যার আসল নাম সমর) তাকে নিতে আসবে।
‘ওর জীবনের তানপুরা যে ওই সুরেতেই বাঁধা,
সেই কথাটি ও জানে না।
চলায় বলায় সব কাজেতেই ভৈরবী দেয় তান
কেন যে তার পাই নে কিনারা।
তাই তো আমি নাম দিয়েছি কোমল গান্ধার –
যায় না বোঝা যখন চক্ষু তোলে
বুকের মধ্যে অমন ক’রে
কেন লাগায় চোখের জলের মিড়।’
খুব মন খারাপ থাকলে একবার ‘কোমল গান্ধার’ দেখে নেওয়া ভালো।
পাঁচ.
ছবি যত এগোয়, তত ভৃগু চরিত্রের কোমল দিকগুলো উন্মোচিত হতে থাকে। স্নেহশীল দাদা, বউদির কাছে ছোট খোকাটির মতো অবুঝ যে কি না অতিরিক্ত বড় হয়ে যাওয়ার হাবভাব করে, কখনও কখনও নিজের দলের লোকের বিশ্বাসঘাতকতায় অসহায়, সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগা একটি যুবক। লালগোলায় নাটক করতে যায় ভৃগুর দল। এই পর্যায়ে ছবিতে সংগীত এবং ভিজুয়ালকে যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, তা ভারতীয় ছবির ইতিহাসে বিরল (বেশি ডিটেইলে যাচ্ছি না, আরেকটা লিখতে হবে)। এখানেই ভৃগু এবং অনসূয়া নিজেদের ঠাঁইনাড়া হওয়ার বেদনা, অসহায়তা নিজেদের কাছে বিবৃত করে।
ভৃগু– …ওখানে দাঁড়িয়ে একটা মজার কথা মনে এল। মনে হল, ওই রেললাইনটা তখন ছিল একটা যোগচিহ্ন, আর এখন কেমন যেন বিয়োগচিহ্ন হয়ে গেছে। দেশটা কেটে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।
অনসূয়া– সত্যি আমাদের বাংলাদেশটা যে কী হয়ে গেল।
![Cinemascope: Komal Gandhar (E-Flat) [1961]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7W_NJ2LhdwFOnMiWc2tJ3kAEtgtQ8_fnjp0WPX29A4PmV-3xhomT_MvaeVYLFCvIBEvijABZsmjY8_ililoMoEtayFm7s6SXGhqFF3Qv-och0ey55THfYe40txQlZEXgbbNQEnPkvrOA/s1600/Komal+Gandhar3.jpg)
ভৃগু– তুমি সেদিন বললে আমি অকারণ রুক্ষ, আমি কোনও বন্ধু পাব না, ঠিক, কিন্তু জানো, আমি সবসময় এমন ছিলাম না, এমন একদিন ছিল, যেদিন পদ্মার ওপাড়ে বসে, অল্প অল্প শাঁখ ঘণ্টার শব্দ ভেসে আসত, আকাশের মেঘগুলো মুহূর্তে মুহূর্তে রং বদলাত। কিন্ত তারপর, এক মুহূর্তে সর্বস্বান্ত হয়ে গেলাম আমরা। বাবা মারা গেলেন ভিখিরির মতো, মা, একরকম না খেতে পেয়েই শেষ হয়ে গেলেন চোখের সামনে। মরার ঠিক আগেই বাবা বলেছিলেন, জীবনটাকে আরম্ভ করেছিলাম কি নির্মল ছন্দে, এইভাবে শেষ হয়ে যাওয়াটা কি উচিত? সেদিন থেকে আমি কেমন যেন হয়ে গেলাম। কী ভীষণ একা হয়ে গেছি। তুমি জানো না।
অনসূয়া– ভৃগু, আমিও বড় একা, কী ক্লান্তি…
অতঃপর সেই বিখ্যাত শট। বন্ধ রেললাইনের ওপর ট্র্যাক শট। পিছনে ‘দোহাই আলি’ বাজছে। রেললাইন শেষ হলে ভিজুয়ালের বদলে ফিল্ম-লিডার চলে আসে (আমরা ছাত্রাবস্থায় তাই দেখেছিলাম, এখন দেখি কালো ফ্রেম), আবহে প্রায় তার ছিড়ে যাওয়ার শব্দ। ভয়ংকর অভিঘাত এই দৃশ্যের, এই সৃজনশীলতার, এই আর্তনাদের। বিয়োগচিহ্ন।
যদিও এই ‘দোহাই আলি’ গানটিই ছবির ক্লাইম্যাক্সে এসে মিরান্ডা এবং ফার্দিনান্দের বিচ্ছেদের দ্যোতক হয়ে উঠবে। ভৃগুর এবং অনসূয়ার মিলনের।
ছয়.
বরঞ্চ আমার মনে হয়েছে, ভৃগু যতটা না একা, তার থেকে অনেক বেশি একা অনসূয়া। ভৃগুর দাদা, বৌদি আছে। নাটকের দলের লোকজন আছে। ঋষি, শিবনাথ, জয়া এবং সর্বোপরি বিজন ভট্টাচার্য তাঁর অননুকরণীয়, ঐতিহাসিক উপস্থিতি নিয়ে আছেন যেরকম থাকেন ঋত্বিক ঘটকের প্রায় সব ছবিতেই। অনসূয়া দাদার সঙ্গে থাকে। দূরদেশে থাকা এক প্রেমিকের জন্য অন্তহীন অনিশিচত অপেক্ষা করে চলেছে বছরের পর বছর। সঙ্গী বলতে মায়ের ডায়েরি। অনসূয়া আঁকড়ে ধরতে চাইছে ভৃগুকে। অথচ নিজের মনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠতে পারছে না। বদনামের স্বীকার হচ্ছে। কেউ মনে করছে মেয়েটা ফ্লার্ট। কেউ মনে করছে মেয়েটা দল ভাঙাতে এসেছে। ভৃগু এবং অনসূয়া দু’জনেই দেশভাগের শিকার। নাটকের দলের অন্তর্দ্বন্দ্বের শিকার। দু’জনেই অসহায়। অতঃপর ঋত্বিক ঘটক আমাদেরকে স্বস্তি দেবেন ঠিক করলেন!

ফার্দিনান্দ আসে। অনসূয়া প্রত্যাখ্যান করে। ফার্দিনান্দকে ফ্লাইটে তুলে দিয়ে আসে। ভূগু এবং অনসূয়ার মিলন হয়। ‘আমের তলায় ঝামুর ঝুমুর’। দুই হাতের মিলন আমরা ক্লোজ আপে দেখি। বাংলার বিভিন্ন ল্যান্ডস্কেপের আমরা প্যানিং শট দেখতে পাই। আমি জানি না, ঋত্বিক ঘটক এখানে দুই বাংলার মিলনের কথা বলছেন কি না। এক জায়গায় ভৃগু অনসূয়াকে শকুন্তলার চরিত্র বোঝাতে গিয়ে বলেছিল–
… সাতচল্লিশ সালে ফিরে যাও, যেদিন উৎখাত হয়ে চলে আসতে হয়েছিল নিজের বাড়ি থেকে, নিজের চেনাশোনা সবকিছু থেকে, কেন? মনে করো না, এই কলকাতা তোমার তপোবন। ওই যে মিছিল চলেছে, ওই তোমার নবমালিকা, বনজ্যোৎস্না।
হয়তো মনে করো কোনও ভিখারি মেয়ে তোমার কাছে পয়সা চায়, সেই মাতৃহীন হরিণ শিশুটি ভেবে দেখো, ভেবে দেখো, যদি কোনও দিন এই কলকাতা থেকে, এই বাংলাদেশ থেকে চিরকালের মতো তোমাকে চলে যেতে হয়, এই কলকাতার সবকিছু তোমার পায়ে পায়ে আঁকড়ে আঁকড়ে জড়িয়ে ধরবে না?
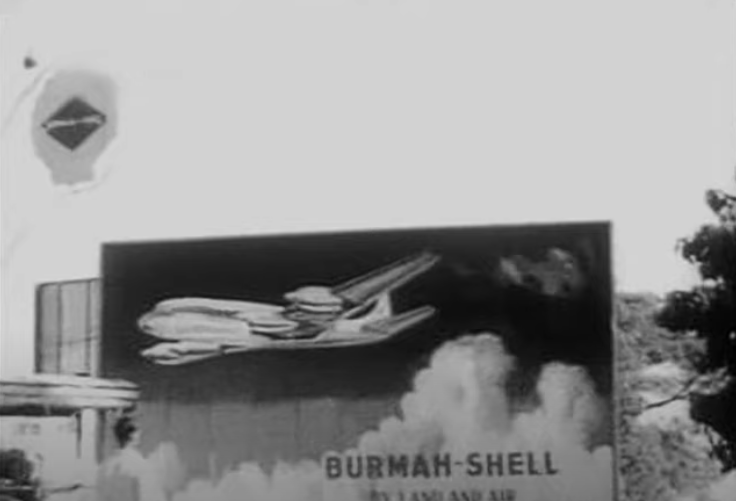
কলকাতাকেও এই ছবিতে আমরা অন্যভাবে দেখতে পাই, টপশটে, বৃষ্টিতে, রাজনৈতিক মিছিলে, দমদম এয়ারপোর্টের রাস্তাকে চেনাই যাবে না। তবে ভৃগু ও অনসূয়ার মিলনে আমি স্বস্তি পাই, শান্তি পাই। ক্লাইম্যাক্স দৃশ্যের এর’ম অসাধারণ বুনন আজকালকার ‘সুপারহিট’ ছবির নির্মাতারাও ভেবে উঠতে পারবেন না।
সাত.
ক্লিশে যদিও, তবু দু’একটা কথা না বললেই নয়। সিনেমার ভাষা যে কি অলৌকিক পর্যায়ে যেতে পারে তার উদাহরণ ‘কোমল গান্ধার’। ‘বিদ্রোহ আজ, বিদ্রোহ চারিদিকে’ গানের সময় দেখা যাবে দেওয়ালে টাঙানো একটি সিংহের মূর্তির শট। সের্গেই আইজেনস্টাইনের ‘ব্যাটলশিপ পোটেমকিন’-এর বিখ্যাত ওডেসা স্টেপস দৃশ্যের শেষে সেই সিংহের মূর্তিগুলোর মতো। বিপ্লব এবং মন্তাজ। সতীন্দ্র ভট্টাচার্য (শিবনাথ) এবং অনিল চ্যাটার্জীর একটি দৃশ্যে (প্রায় ডুয়েলের মতো) আশ্চর্য ওয়ান এইটি ডিগ্রি জাম্প। কিছু জটিল কম্পোজিশন, লাইটিং এবং মুভমেন্ট। বিশেষত যেখানে অনসূয়া চলে যাচ্ছে এবং একটি বাচ্চা তার আঁচল টেনে ধরে। লো অ্যাঙ্গেলে বাচ্চাটার সাজেশনে অনসূয়ার মিড এবং ব্যাকগ্রাউন্ডে থামটা এমনভাবে আলো করা হয়েছে, দেখে মনে হবে কাস্তে।

এই দৃশ্যটির সম্পাদনা এবং শব্দ ব্যবহার বারবার দেখা যেতে পারে। ছবিতে দেখতে পাই, সেইসময়ও দূরদূরান্ত গ্রাম থেকে প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকেরা কলকাতায় আন্দোলন করতে এসেছেন। এরকম অজস্র উদাহরণ আছে। আরকটা কথা মনে পড়ল। একজায়গায় বিজন ভট্টাচার্য বলছেন আর্টিস্টের দম্ভ থাকা দরকার। আবার ছবির শেষের দিকে দলে ভাঙন ধরার পড় ঋষি (অনিল চ্যাটার্জী) ভৃগুকে বলছে– এই হয়, লিডারস অফ মেন, প্রায় সবসময় রুক্ষ আর দাম্ভিক হয়, নিজেদের সম্বন্ধে বেশি রোয়াবই নেয়, ওদের শ্রদ্ধা করা উচিত এবং ফ্রম টাইম টু টাইম, লাখি মারা উচিত।
ঋত্বিক ঘটক নিজের জীবনে বহু ছবিই শুরু করে অর্থাভাবে শেষ করতে পারেননি। ‘বগলার বঙ্গদর্শন’, ‘রঙের গোলাম’ ইত্যাদি। ‘বগলার বঙ্গদর্শন’-এ সুনীল ভট্টাচার্যকে মূল চরিত্রে দেখতে পাই। যিনি কিনা কোমল গান্ধারে অনসূয়ার দাদা পাখির ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। এঁকে আরও অনেক বাংলা ছবিতে দেখতে পেলে ভালো হত। যেমন ভালো হত সতীন্দ্র ভট্টাচার্যকে দেখতে পেলে। অবনীশ ব্যানার্জিকে আর বোধহয় সুবর্ণরেখায় দেখেছি। যেমন ভালো হত সুপ্রিয়া দেবীকে আরও এর’ম কিছু আশ্চর্য চরিত্রে দেখতে পেলে।
যাই হোক, ২০২৪ সালের শেষে আবার ‘কোমল গান্ধার’ দেখে আমার মনে হয়েছে ‘কোমল গান্ধার’ একটি খুবই জরুরি সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এমনকী, ৬০ বছর পরের ভবিষ্যৎ অর্থনীতির (‘কাবুলিওয়ালা’র দৃশ্য দ্রষ্টব্য) দলিল হয়েও একটি অপূর্ব প্রেমের ছবি। একটি ব্যক্তিগত ছবি। ব্যক্তিগত দলিল। ঋত্বিক ঘটকই ভৃগু।
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
