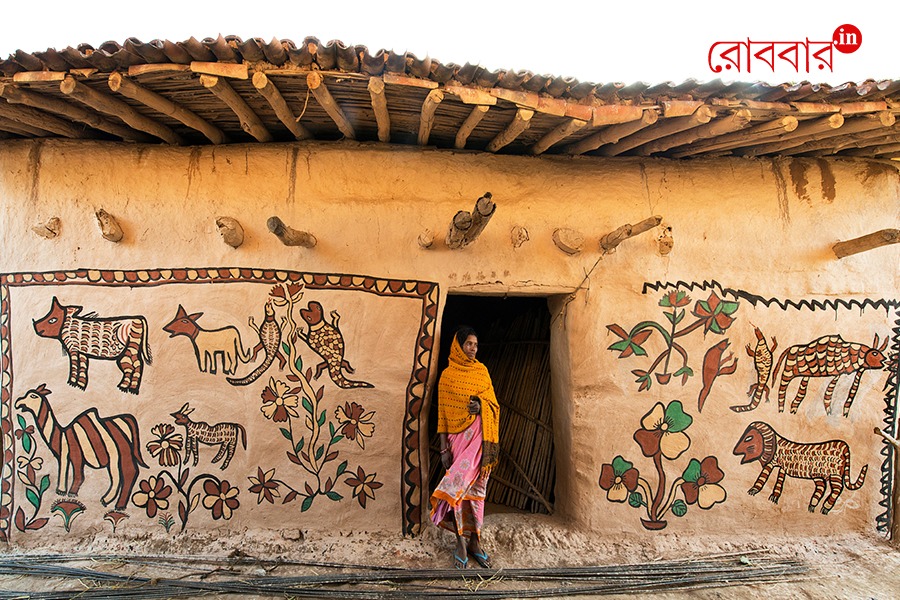
অরণ্য কেবল আদিম উদ্যমতা নয়। এতে আছে অফুরন্ত আনন্দ। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাস থেকে খেত-খামারে কাজ করতে নামার আগে, শরীরের আলসেমি কাটিয়ে তরতাজা করার এক বিশেষ পদ্ধতি এই শিকার উৎসব। সেই দুর্বার আকর্ষণে পুরুষরা বন্য শুয়োরের সঙ্গে লড়াই করে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। অভিজ্ঞ মানুষেরা শিকারের নানাপ্রকার কৌশল শিখিয়ে দেন। বুঝিয়ে দেন যৌবনের মাদকতা, দীক্ষা ও আদিমতা।

ঠা ঠা রোদ্দুর। ঝাঁ ঝাঁ বাতাস। জানান দিচ্ছে যে, বৈশাখ এসেছে। পুরুলিয়া জেলার বাঘমুণ্ডি থানার পূর্ব প্রান্তে অযোধ্যা পাহাড়। সাঁওতালদের ‘অযোধিয়া বুরু’। বৈশাখী বুদ্ধপূর্ণিমার রাতে অযোধিয়া বুরু আন্দোলিত হয় শিকার উৎসবে। শুধু শিকার নয়, এ হল উৎসব, ‘সেঁদ্রা পরব’। পশ্চিমবঙ্গে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বর্ধমানের আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে এ উৎসব সোৎসাহে পালিত হয়। বিশেষত পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড় বা আরষা গ্রামের কাছে, তালডুংরি পাহাড়ের কোলে ‘শালগা দুমদুমি’ গ্রামের জনৈক গ্রামবাসীর কাছে জানা যায় যে, এই শিকারপর্ব বীরত্ব ও পৌরুষের প্রতীক। কারও কারও মতে, একে ‘যৌবন মেলা’ও বলা হয়। এই মেলায় ছেলেরা সাবালকত্বের সিঁড়িতে পা রাখে। এই পরব বীর কিশোরদের যৌবনে পদার্পণের দীক্ষা ক্ষেত্রও। প্রবাদ আছে, ‘যে মরদ অযোধ্যা পাহাড়ে যায়নি, সে মায়ের পেটেই রয়ে গেছে।’

শিকার পরবের প্রস্তুতি শুরু হয় কিছুদিন আগে থেকে। সাঁওতাল সমাজের পুরোহিত বা ‘দিহরি’র ওপর এই উৎসবের যাবতীয় ব্যবস্থার ভার থাকে। শিকারের দিন ধার্য করে তিনি স্থানীয় সমস্ত মাঝি হাড়ামের কাছে খবর পাঠান। আগে শিকার যাত্রার আগেই দিহরি শিকারিদের মিলিত হওয়ার স্থান (দুপুডুপ টৌন্ডি) আর শিকার শেষে সমবেত হওয়ার স্থান (গিপিতি চটৌন্ডি) ঘোষণা করে শালগাছের শাখা গ্রামে গ্রামে পাঠাতেন। এর নাম ‘শালগিরৌ’। কোথাও দু’টি আমপাতা দিয়েও জানানো হয় নিমন্ত্রণ। শিকারে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়। শুরু হয় ধনুকে ছিলা পরানো। শান্ দিয়ে সূচালো করা হয় ফলা, বেট পরানো হয় টাঙ্গিতে, লাঠিতে পরানো হয় বল্লম, ঝকঝক করে তলোয়ার। মেয়েরা তৈরি করে মহুয়ার মোয়া, ভুট্টা-যব-গমের ছাতু। চাল-ডাল গামছায় বেঁধে দেয় মা-বোনেরা। ‘দাকা পটম’ বা ভাতের পোঁটলা, ‘উড়ু পটম’ বা তরকারির পোঁটলা, ‘উল পটম’ বা আম-পোড়ার পোঁটলাও তৈরি হয়। গেয়ে ওঠে,
‘…কৈলাস বজা কুনামীরে অসেদিয়া সেঁদ্রা
রসিক কনে সেঁদ্রা হরি আনায় মানাঞ্চা কাহু
চোড়য় রা লেখান বহ সিঁদুর, আবুর মেঃ
কইলী চেঁড়স রাঃ লেখান কয় হরিঞ মেঃ…’।
(কৈলাস পূর্ণিমাতে অযোধ্যা পাহাড়ে শিকার। হে স্ত্রী শিকারে যেতে আমায় বাধা দিও না। কাক ডাকলে মাথার সিঁদুর মুছে ফেলবে আর কোকিল ডাকলে আমার জন্য অপেক্ষা করবে।)

পুরুষেরা শিকার গেলে মেয়েরা দিন গুনতে থাকে। ফিরে না আসা পর্যন্ত কাচা হয় না জামাকাপড়, সিঁথিতে পরে না সিঁদুর, চিরুনি দেওয়া হয় না মাথায়। জলভরা পিতলের কলস ঘরের ভেতর এনে রাখেন দিহরি। শিকারের আগের রাতে সেই কলসের জলে দুটো শালগাছের ডাল ডুবিয়ে দেওয়া হয়। ভোরবেলায় দেখা হয় তাজা আছে কি না ডালগুলো। ডাল যদি তাজা ও সবুজ থাকে শিকার শুভ, জলঘোলা হয়ে উঠলে ঘোষিত হয় ছোট প্রাণী বা পাখি মারার সংবাদ। লাল হলে ইঙ্গিত করে শিকার হয়েছে বাঘ, ভালুক বা বুনো শুয়োর।
ঘোষিত দিনে গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন জায়গা থেকে দলে দলে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সশস্ত্র পুরুষেরা নির্দিষ্ট জায়গায় একত্রিত হয়। মোরগ বলিদান দিয়ে পুজো দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য বনদেবীকে তুষ্ট করা। শিকারের সময় যেন কোনও বাধা-বিপত্তি না ঘটে। শিকারিরা তাদের অস্ত্রশস্ত্র রেখে গোল হয়ে দাঁড়ায়, শিকারিদের সংখ্যা গণনার পর গ্রামের ওঝা এ সময় বাধা-বিপত্তি যাতে না হয় তাই কিছু তুকতাক করে। জঙ্গলে প্রবেশের পূর্বে দিহরির সঙ্গে দেখা করে গ্রামের নাম বলে, নিজেদের পরিচয় দিয়ে, অনুমতি প্রার্থনা করলে দিহরি তাদের ভবিষ্যৎ গণনা করে। জেনে নেয় কোনও বিপদ-আপদ আসবে কি না। তারপর অনুমতি আদায়ের পর শিকারিরা বাদ্যের তালে তালে জঙ্গলে প্রবেশ করে। বিকেলের দিকে পাহাড়ে ওঠা শুরু হয়। পাহাড়ে তখন জনারণ্য। সবাই রণসজ্জায় সজ্জিত। লাগড়া-ধামসা-বাঁশি-মরিন্দার শব্দ উত্তাল করে তোলে নিঃশব্দ চিরমৌন পাহাড়কে। সমবেত স্বরে শোনা যায় গান–
‘জংলি মোরগ ডাকছে দূরে সিংঘিরে
মানবিরের গভীর বনে কেকাধ্বনি
অযোধিয়া কাঁপছে যেন ঢেঁকির পাড়
রেগড়া টামাক বাজছে কেন বাজছে কেন আজ!’
শিকারিরা ক্রমশ এগিয়ে যায়। শিকার চলাকালীন কোনও শিকারি ভয়ে পিছপা হতে পারবে না বা প্রাণ ভয়ে পালিয়ে আসতে পারবে না– এটাই নিয়ম। বিপুল উদ্যম আর অফুরন্ত প্রেরণায় মনোবল বেড়ে যায়। সারাদিন শিকার চলে– হরিণ-খরগোশ-বনশুয়োর-পাখি। সন্ধের মুখে শিকার শেষ হলে নিজের নিজের আখড়ায় ফিরে আসেন শিকারিরা। তারপর শুরু রান্নার পালা। ঘর থেকে নিয়ে আসা চাল, ডাল আর শিকার করা মাংস রান্না করা হয়। সুগন্ধে ম ম করে সারা পাহাড়। মাংস আর হাড়িয়ার সংস্পর্শে তাঁরা তখন এক ভিন্ন জগতের মানুষ। শয়ে শয়ে মশাল জ্বলে ওঠে– মশালের আলোয় পাহাড় তখন অগ্নিবর্ণ– আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ হাসছে। জ্যোৎস্নার গুঁড়ো মেখে জঙ্গল-পাহাড়-মানুষ সবাই যেন বুঁদ।
এখানে এক পাথর চাটান আছে নাম ‘সীতা-চাটান’। পায়ের ছাপের মতো দেখা যায় সেই পাথর-চাটানে, লোকে বলে এটি সীতা দেবীর পায়ের ছাপ। প্রবাদ আছে, রাম-সীতা বনবাসের সময় এই জঙ্গলে এসেছিলেন। একটি কুয়ো আছে এখানে, নাম সীতাকুণ্ড। ক্ষীণ ধারার দু’টি ঝরনা আছে– ‘বামনী’ ও ‘টুর্গা’। চলতি কথায় ‘ভুড়ভুড়ি’– মাটি থেকে আপনা আপনি ভুরভুর করে জল বের হয়। চাটানের গাছে ঘন চুলের মতো কালো শিকড় দেখা যায়। লোকবিশ্বাস, এসব সীতাদেবীর চুল। প্রেমিকার খোঁপায় দিলে ঘন ও কালো হয় চুল। শিকারি প্রেমিকরা সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন সেই শিকড়। আর নিয়ে আসেন স্বর্ণচাঁপা।
সীতা-চাটানের কাছে আড্ডাগুলি বসে। নিজ নিজ আখড়ায় নাচ-গান-নাটক হয়। প্রতিযোগিতাও হয় এবং সেখানেই বিচার হয় তার যোগ্যতা। বন্ধুত্বও হয় দলে দলে। শিকারের শেষ অধ্যায়ে ‘সুতানটাণ্ডি’ বা বিশ্রাম- প্রান্তরে বিভিন্ন জায়গা থেকে আসেন আদিবাসিরা– পুরুলিয়া-বাঁকুড়া-মেদিনীপুর-রাঁচি-হাজারিবাগ-ছোটনাগপুর। সে এক বিরাট জনসভা। এ হল সাঁওতাল সমাজের সুপ্রিম কোর্ট। সাঁওতাল সমাজে বিভিন্ন স্থানে যে সব অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা আর অসামাজিক কাজ ঘটছে, প্রতিনিধিরা পরপর তার বিবরণ দিতে থাকে। আলাপ- আলোচনার পর হয় তার বিচার। এমনকী, মৃত্যুদণ্ডও নির্দেশিত হয়। চলতি কথায় একে বলা হয় ‘ল-বীর’।

পূর্ণিমার থৈ থৈ জ্যোৎস্নায় রাত-ভোর নাচ গান বাজনার পর সকালের দিকে ঘরে ফেরার পালা। যে পথে শিকারিরা গ্রাম থেকে জঙ্গলে গিয়েছিলেন আবার সে পথেই তারা গ্রামে ফিরে যায়। গ্রামে হৈ-হুল্লোড় ও আনন্দে মাতোয়ারা সবাই। দু’চোখে বইতে থাকে আনন্দধারা। ঘরে ফিরলে জল নিয়ে থালার ওপর শিকারিদের পা ধুইয়ে দেয় মেয়েরা। মহিলারা নিজেদের আঁচল পেতে গ্রহণ করে চাঁপা ফুল। তারপর তা রেখে দেয় গোয়াল ঘরে বা পবিত্র কোনও স্থানে। শিকারে যাওয়ার আগে বিবাহিত পুরুষটি তার স্ত্রীর হাতের যে লোহার খাড়ুটি (বালা জাতীয়) খুলে দিয়ে গিয়েছিল, শিকার থেকে ফিরে সেই লোহাটি আবার পরিয়ে দেয় স্বামী। মাথায় চিরুনি দেয় মেয়েরা, চুল আঁচড়ায়, সিঁদুর পরে। দেবতাদের উদ্দেশ্যে হাঁড়িয়া সম্প্রদান করা হয়। শিকারের মাংস শালপাতায় বেঁধে পৌঁছে দেওয়া হয় পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয় কুটুম্বদের বাড়ি বাড়ি।

অরণ্য কেবল আদিম উদ্যমতা নয়। এতে আছে অফুরন্ত আনন্দ। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাস থেকে খেত-খামারে কাজ করতে নামার আগে, শরীরের আলসেমি কাটিয়ে তরতাজা করার এক বিশেষ পদ্ধতি এই শিকার উৎসব। সেই দুর্বার আকর্ষণে পুরুষরা বন্য শুয়োরের সঙ্গে লড়াই করে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। অভিজ্ঞ মানুষেরা শিকারের নানাপ্রকার কৌশল শিখিয়ে দেন। বুঝিয়ে দেন যৌবনের মাদকতা, দীক্ষা ও আদিমতা। এই শিকার উৎসবে জয়ী হয়ে না ফিরলে কেউ তাঁকে পাত্তা দেবে না। সবাই কাপুরুষ বলবে। আর জয়ী হয়ে ফিরলে সকলের কাছ থেকে পাবে এক বিশেষ সম্মান। আদিবাসীদের শিকার উৎসবের মধ্যে দেখা যায় সাম্যবাদ নীতির প্রয়োগ। যেমন, শিকারের মাংস সমানভাবে বণ্টন। সঙ্গী কুকুরটিকেও সমপরিমাণ ভাগ দেওয়া হয়। এছাড়া জঙ্গলে পাওয়া ফলমূলের খাওয়ার মতো অংশ নিয়ে বাকি অংশটি আবার ওই মাটিতেই পুঁতে দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে অন্য কোনও ব্যক্তির খাবারে যাতে টান না পড়ে। তাই এই নীতি।
সাঁওতালি ভাষায় যাকে বলে ‘সেন্দ্রা’, তার বাংলা অর্থ ‘অনুসন্ধান’। বিগত বছরে জঙ্গলের মধ্যে যেসব প্রজাতির গাছপালা, লতাপাতা, কীটপতঙ্গ, পশুপাখি ইত্যাদি পাওয়া গিয়েছে, তা এই বছর পাওয়া যায় কি না সেই বিষয়ে খোঁজতল্লাশ। আসলে শিকার অভিযানের মধ্যে দিয়ে বনের নানারকম উদ্ভিদ ও প্রাণীকূল সম্বন্ধে সম্যক ধারণা নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার মধ্য দিয়ে সমগ্র প্রাণ ও প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যোগ স্থাপনই এই উৎসবের মূল উদ্দেশ্য।
এই ‘শিকার উৎসব’ এখন ঐতিহ্যরক্ষার স্বার্থে প্রতীকী তাৎপর্যেই শুধুমাত্র দৃশ্যমান। অন্যথায় শিকারির যাবতীয় অনুষঙ্গই অনুপস্থিত থাকে যুক্তিসংগত কারণেই। বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আইন (১৯৭২) অনুযায়ী, বিভিন্ন ধরনের পশু-পাখি শিকার সম্পূর্ণ বেআইনি। কেউ বন্যপ্রাণ নিধনে লিপ্ত হলে, তা দণ্ডনীয়। আজ সাঁওতালদের বিভিন্ন অভিবাসিত ধারা যে সমস্ত জায়গায় জীবন জীবিকার সংগ্রামে ব্যস্ত, সেসব জায়গার অধিকাংশেই বন অথবা বন্যপ্রাণীর দেখা পাওয়াই দুর্লভ। আইনি নিষেধাজ্ঞায় শিকার সন্ধান সাঁওতালিদের কাছে আজ স্বপ্ন মাত্র, তবু বৈশাখী পূর্ণিমার দিনটিতে তারা শিকার উৎসবে মনপ্রাণ উজাড় করে মেতে উঠতে চায় চিরাচরিত প্রথাকে মনে রেখে। ক্ষুন্নিবৃত্তির স্বার্থে নয়, কোনও কিছু প্রাপ্তির আশায় নয়, এমনকী, সামাজিক সমস্ত আনন্দের ঊর্ধ্বে উঠে উত্তেজনার প্রবল আকর্ষণে এক স্বতন্ত্র অধিকারের সহজাত বোধে উদ্দীপ্ত হয়ে তারা নিয়ম ভেঙেই শিকারে বেরিয়ে পড়ে প্রাচীন প্রথা বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে। তীব্র আকর্ষণের প্রেক্ষিতে বছরের এই বৈশাখী বুদ্ধপূর্ণিমার দিনে শিকার উৎসবে বেরিয়ে গভীর বনে প্রবেশ করে প্রচুর পশু শিকার করে ‘গিপিতি চটৌন্ডি’তে ফিরে আসা আজ যে কোনও সাঁওতালের কাছে স্বপ্ন দেখারই শামিল।
……………………………
ফলো করুন আমাদের ওয়েবসাইট: রোববার ডিজিটাল
……………………………
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
