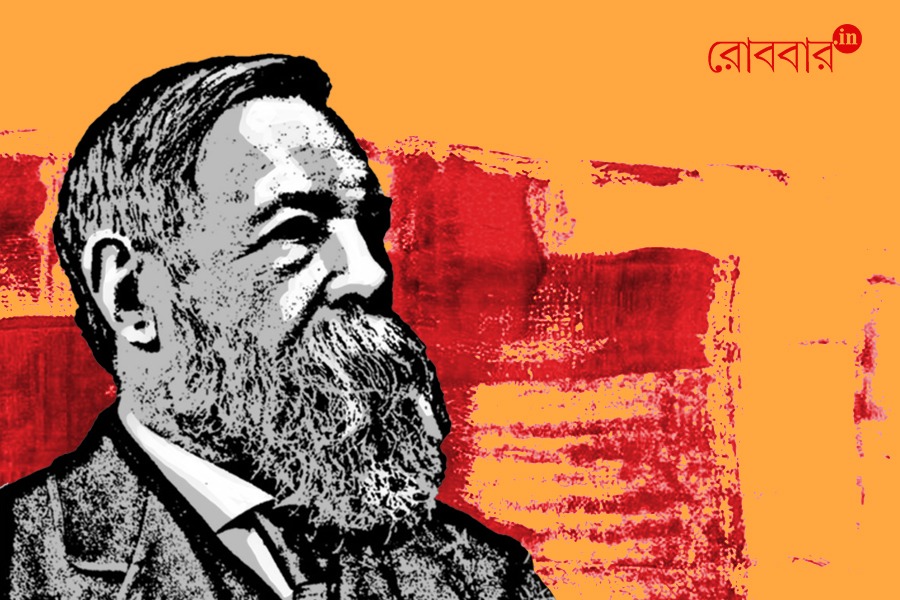
আজকার মার্কসবাদীরা মার্কসবাদ বিষয়ে আলাপ করতে গেলে এঙ্গেলসেরই দর্শন সংক্রান্ত লেখাগুলিকে ধরেই আলোচনা করেন, যেহেতু মার্কস ব্যস্ত ছিলেন অর্থশাস্ত্র নিয়ে। অথচ ‘নেতির নেতি’ বিষয়ে তাঁরা এঙ্গেলস-এর সীমানা স্বীকার করলেও সেই দর্শনের সরাসরি প্রভাবযুক্ত এইসব আর্থ-সামাজিক সিদ্ধান্তের মধ্যে কোনও সীমানা দেখতে পান না যে, এটিই আদতে বস্তু বা সমাজবিকাশের বিচারে এঙ্গেলসের অবদানকে কলঙ্কিত করে, মার্কসবাদকে এমন একটি অথর্ব তত্ত্ব হিসাবে প্রমাণ করে, যা প্রয়োগে বিকশিত হয় না।

সেই দামাল তাত্ত্বিকের আজ প্রয়াণদিন, যিনি অকাদেমির ঘাসপাতা খেয়ে ও খাইয়ে বিপ্লবের বাণী সংগ্রামরত শ্রমিকদের জন্য ছুড়ে দেননি বরং একজন অভিজ্ঞ যোদ্ধা হিসাবে উনিশ শতকের ইংল্যান্ডে শ্রমিক আন্দোলনগুলিতে ধারাবাহিকভাবে অংশ নিয়েছেন, এমনকী ফরাসি বিপ্লবকালে, যখন একদিকে তিনি ও তাঁর প্রিয় পার্টনার দুনিয়া কাঁপানো ইশতেহার লিখছেন, এঙ্গেলস অগুনতি যোদ্ধাদের সঙ্গে বরফ পাহাড় ডিঙিয়ে রাইফেল কাঁধে পা মিলিয়ে পাড়ি দিচ্ছেন প্যারিসে।
এই কথা দিয়ে আলোচনা শুরু করার কারণ হচ্ছে: ‘প্রকৃতিতে দ্বান্দ্বিকতা’ আবিষ্কার করে এঙ্গেলস তত্ত্বের দুনিয়ায় কী বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন– এই পুরানা, জিতে যাওয়া প্রসঙ্গে হাল বছরে একবার করে স্মৃতিমন্থন করে আজ আর কোনও লাভ নাই। বরং ‘বৈপরীত্যের ঐক্য’ তত্ত্বে তাঁর সীমাবদ্ধতা মাও সে তুং অতিক্রম করে যাচ্ছেন, সেইদিকে তাকালে আমরা এঙ্গেলস নির্মিত ‘দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ’ তাঁর বিশ শতকীয় সন্তানাদির হাতে পড়ে কীভাবে পুঁজিকে ও পুঁজি আনত শ্রেণি সভ্যতার উন্নয়নবাদকে এখনও দার্শনিক ভাবে রক্ষা করে চলেছে, তার তাত্ত্বিক আলাপের কিছু হালসঙ্গতি পাই; কারণ এঙ্গেলসই সেই বৈপ্লবিক সূত্র ইতিহাসে যিনি প্রথম বিজ্ঞানের দর্শনকে হাজির করছেন বস্তুবাদী দৃষ্টি থেকে; ‘ধর্ম’ ও ‘দর্শন’ সংক্রান্ত প্রশ্নে, এমনকী ধারণা হিসাবে ‘শ্রেণি’ ও তার ‘ইতিহাস’ সংক্রান্ত প্রশ্নে এঙ্গেলসের ‘মার্কসবাদী সিদ্ধান্তগুলি’র সঙ্গে মার্কসের দর্শনচিন্তার যতই ফারাক থাক, এখানেই এঙ্গেলস ঐতিহসিক অর্থেই এখনও প্রাসঙ্গিক, এটা জোর গলায় বলতেও পারি।

১৮৭২ সালের প্যারিস কমিউনের পর শ্রমিক শ্রেণির রাষ্ট্র সম্পর্কে যে সমস্ত প্রতর্কের আবার নতুন করে জন্ম হয়; বাকুনিন কিংবা ক্রপোৎকিনের সমালোচনায় মুখর এঙ্গেলস ‘কর্তৃত্ব প্রসঙ্গে’ লিখতে গিয়ে সমকালীন নৈরাজ্যবাদীদের ‘স্বতঃস্ফূর্ততা’ কিংবা ‘প্রতিষ্ঠানবিরোধিতা’ প্রসঙ্গে তার জবাব দেন। রাষ্ট্র বিলোপের প্রশ্নে তা নৈরাজ্যবাদীদের শিশুসুলভ প্রতর্কগুলিকে আলোচনার মাধ্যমে তাঁর নিজের প্রস্তাবিত সাম্যবাদী ইউটোপিয়ার বাস্তব উপাদানগুলিকেই তত্ত্ব থেকে বাদ দিয়ে দিল। অর্থাৎ একটা সহজ, কর্তৃত্বহীন সমাজ গঠনের সংগ্রামে চেতনা ও কর্তৃত্বের যে দরকার আছে, তার সীমানা ও সম্ভাবনা উহ্য থেকে গেল। আজকার মার্কসবাদীরা মার্কসবাদ বিষয়ে আলাপ করতে গেলে এঙ্গেলসেরই দর্শন-সংক্রান্ত লেখাগুলিকে ধরেই আলোচনা করেন, যেহেতু মার্কস ব্যস্ত ছিলেন অর্থশাস্ত্র নিয়ে। অথচ ‘নেতির নেতি’ বিষয়ে তাঁরা এঙ্গেলস-এর সীমানা স্বীকার করলেও সেই দর্শনের সরাসরি প্রভাবযুক্ত এইসব আর্থ-সামাজিক সিদ্ধান্তের মধ্যে কোনও সীমানা দেখতে পান না যে, এটিই আদতে বস্তু বা সমাজবিকাশের বিচারে এঙ্গেলসের অবদানকে কলঙ্কিত করে, মার্কসবাদকে এমন একটি অথর্ব তত্ত্ব হিসাবে প্রমাণ করে, যা প্রয়োগে বিকশিত হয় না।
‘প্রকৃতির দ্বান্দ্বিকতায়’ এঙ্গেলস দেখালেন প্রকৃতির মধ্যে দ্বন্দ্ব কীভাবে নানারূপে কাজ করছে এবং বস্তু হচ্ছে আদতে দ্বন্দ্বের এক একটা অবস্থা, যে ক্রমাগত নাকচ বা বিভাজিত হতে হতে নানা বস্তু হিসাবে রূপ পরিগ্রহ করছে। নতুন দ্বন্দ্বের আবির্ভাব কিংবা পুরনো দ্বন্দ্বের নিষ্ক্রান্তি: বস্তুর অভ্যন্তরে এই দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়াই পরিবর্তন বা বিকাশের ধ্রুব নিয়ম, যা নতুন বস্তু সৃষ্টির কিংবা পুরনো বস্তু ধ্বংসের কারণ। এখন মাও এই তাত্ত্বিক জটকে ‘বিকশিত’ করার কাজে ঢুকলেন কেন? কারণ তাঁর কাছে ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস কোনও ইতিহাসের রাশ ছিলেন না, ছিলেন প্রকৃতই এমন দার্শনিক যিনি তত্ত্ব বা সিদ্ধান্ত বা প্রকল্পের নীতিমালাও যে একটা (বৈষয়িক) দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার অভিব্যক্তি, যার বিকাশও খোদ ধ্রুব: এই দিগন্তকেও উন্মোচিত করেছিলেন, মাও যা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন নিজের দেশে বিপ্লব করতে গিয়ে। সমস্যা হল আমরা যখন এই আলোচনায় ঢুকব এবং দেখব দ্বন্দ্বতত্ত্ব আলোচনায় মাও সে তুং যে প্রস্থানগুলি নিচ্ছেন, সেগুলি জীবদ্দশায় এঙ্গেলসের সাধারণ দার্শনিক সিদ্ধান্তের বিপরীতগামী, তখন একদল মার্কসবাদী ঝান্ডা ডান্ডা তুলে প্রতিবাদ করবেন আর ‘গেল গেল’ রব তুলবেন; আদতে নিজেদের গোঁড়ামি আর মূর্খামি দিয়ে এঙ্গেলসের প্রকৃত প্রাসঙ্গিকতা লুকোবেন মাত্র।

মাও এঙ্গেলসকে কোথায় ‘বিকশিত’ করছেন, তা আমাদের দেখাবে বস্তুর ধ্রুব গতি বিচারের নিয়ম কীভাবে আর্থ-সামাজিক বিকাশের নিয়ম সংক্রান্ত মূল সূত্র হয়ে দাঁড়াচ্ছে। একটি নিবন্ধে এঙ্গেলস রুশ নৈরাজ্যবাদী তাত্ত্বিক পিটার ক্রপোৎকিনকে খোরাক করে লিখছেন– ‘রুশদেশে কেন আগে বিপ্লব হবে না’ তার সমাজ-বিজ্ঞান। কারণ হিসাবে তিনি দেখাচ্ছেন পুঁজির যথাপর্যাপ্ত বিকাশ সেখানে ঘটেনি, সমাজতন্ত্রের রূপকার সর্বহারা শ্রেণি গঠিত হয়নি। ক্রপোৎকিনের দাবি ছিল– রুশদেশের কৃষক কারিগর সমাজ পুঁজি বা কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রের কবল থেকে ইতিমধ্যেই অনেকটা বাইরে বলে সেখানেই রাষ্ট্র বিলোপের সংগ্রাম সবচেয়ে আগে ঘটার সম্ভাবনা বেশি। এঙ্গেলস এখানে পরে কতটা এবং কীভাবে ভুল প্রমাণিত হলেন, তা আমাদের কাছে আলোচ্য নয়, বরং কেন তিনি ক্রপোৎকিনের নিদান নিয়ে মশকরা করছিলেন, যার মধ্যেই আদতে ‘নেতির নেতি’ তত্ত্বের বিকাশের সম্ভাবনা লুকিয়ে ছিল, সেইটা। ফলস্বরূপ উদ্দেশ্যপূর্ণ ভাবেই যখন তার হদিশ আমরা করি, দেখি, সমাজ বিকাশের প্রধান চালিকাশক্তি উৎপাদন সম্পর্ক ও উৎপাদিকা শক্তির মধ্যেকার দ্বন্দ্ব সংক্রান্ত যে তত্ত্ব, তার প্রবাহ ধরেই এমনকী রুশদেশের স্বাধীন ছোট কৃষক ও কারিগর সমাজকে ‘সামন্ততান্ত্রিক’ সমাজের অংশ ঠাওরে সেইসব অঞ্চলে রাষ্ট্র বিলোপ ও সাম্যবাদ স্থাপনের আবশ্যক পর্যায় হিসাবে তিনি বুর্জোয়া ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশকে নতুন করে ব্যাখ্যা করছেন। আজ যখন ধনতান্ত্রিক উন্নয়নের বিরুদ্ধেই পৃথিবীজোড়া লড়াই সংগ্রামেই মার্কসবাদীরা সবচেয়ে বেশি রক্তঘাম ঝড়াচ্ছেন, তখন সমাজ-বিকাশের বস্তুবাদী ইতিহাস বলতেই ‘দাস সমাজ’, ‘সামন্ত সমাজ’, ‘ধনতান্ত্রিক সমাজ’ ইত্যাদি যে একমুখী বিকাশের ধারণাটি সেই কর্মরত মার্কসবাদী সংগঠনগুলি একচ্ছত্র পালন করে, অধ্যাপক অমিয় কুমার বাগচী দেখাচ্ছেন– এর উৎস ও দায় হচ্ছে একমাত্র সোভিয়েত অকাদেমির। সমস্যা হল এটি যে অর্ধসত্য, এঙ্গেলসের দিকে আঙুল তুলতে হবে বলে অনেকের মতোই তিনিও হয়তো তা এড়িয়ে যেতে চাইলেন। অথচ, কোন স্থান ও কাল অনাপেক্ষিক উদ্বৃত্ত শ্রম আলোচনায় মার্কসকে দিয়ে লেখাল– গ্রীষ্মদেশে জ্ঞান, সাহিত্য, সতর্কতা বিকাশ লাভ করেনি কারণ প্রকৃতি সেখানে সেইসব বিকাশের বাধ্যতা মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয়নি, কিংবা এঙ্গেলসকে দিয়ে লেখাল– উৎপাদিকা শক্তির উচ্ছৃঙ্খল বিকাশের মাধ্যমে (অতি) উদ্বৃত্ত-উৎপাদনই সাম্যবাদী অর্থনীতির ভিত্তি হিসাবে রাষ্ট্রকে এককালে বাতিল অপ্রয়োজনীয় করে তুলবে– সেই আলোচনায় না গিয়ে অধ্যাপকের মতো আমরা সকলেই (শুধু মার্কসবাদীরা নন) এতাবধি যৌথতা, সহযোগিতার উপনিবেশিক পাঠ নিজের দেশের দিগ্গজ উৎপাদক সমাজকে দান করতে গেলাম। রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া থেকে ফিরে বললেন, সেখানে একজন শিশু একটি চকোলেট ছয়জনের সঙ্গে ভাগ করে খায়। আমরা আরও দম পেলাম।
আদতে শুধু দ্বন্দ্ব নয়, বস্তুর গতি নির্ণীত হচ্ছে ঐক্যের দ্বারা; এবং বস্তু হচ্ছে আদতে একাধিক দ্বন্দ্বেরই একপ্রকার ঐক্যবদ্ধ সমাহারস্বরূপ (কম্পোজিশন); ‘নেতি ইতি নেতি ইতি’ তত্ত্বে মাও সে তুং এটি লিখে জানান দিলেন এভাবেই বস্তুর শঙ্খিল বিকাশে শুধু বাহ্যিক শক্তি হিসাবেই নয়, অভ্যন্তরীণ দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার মধ্যেও ঐক্য একটি প্রধান প্রবণতা হিসাবে কাজ করে। অর্থাৎ প্রতিটি বস্তুর মধ্যে আবশ্যক ভাবে দ্বন্দ্ব থাকলেও প্রতিটি বস্তুই প্রতি মুহূর্তে সেইসব দ্বন্দ্বকে নিষ্ক্রান্ত করতে চায় বা অপর অর্থে অপর বস্তুতে বিলীন হতে চায় কিংবা অপর বস্তুর সঙ্গে মিলিত হতে চায়। মানুষ যেহেতু জৈবিক ভাবেই দলবদ্ধ প্রাণী, তাই মানুষের মধ্যে ঐক্য বা পরস্পর নির্ভরশীলতা বা যৌথতা একটি সহজাত ব্যাপার। তার শ্রমের দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় মানুষের দেহই দেখা গেল শুধু এই প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রভাবিতই হয় না, একে নিয়ন্ত্রণও করতে পারে। মানবিক শ্রমপ্রক্রিয়া ‘প্রকল্পনা’ ও ‘ফলাফল’ নামক ঐক্যের সংশ্লেষ দ্বারা এভাবেই সৃষ্টিশীল হয়। দুঃখের কথা হল: শ্রমপ্রক্রিয়া দখল করার মাধ্যমে, অর্থাৎ ‘প্রকল্পনা’ ও ‘ফলাফল’ নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে দাসমালিক, ভূমিদাস-মালিক ও পুঁজিপতিরা উৎপাদকের সৃষ্টিশীল শ্রমকে ‘অর্থনৈতিক’ উৎপাদনের অযোগ্য ও ‘সাংস্কৃতিক’ উৎপাদনের বিনোদনকারী ব্যাপার প্রতিপন্ন করেছে, এবং সারা বিশ্বের স্বাধীন সৃষ্টিশীল উৎপাদক সমাজকে ‘রিপিটেটিভ’ ‘অপর্যাপ্ত’ দেগে দিয়ে খোদ শ্রমকে সৃষ্টির সাধনার বদলে ঘৃণ্য, শোষণের পীড়া হিসাবে খাড়া করেছে।

লক্ষণীয় হল, কেন মাও ইঙ্গিত সহকারে এইসব অভিচার পুনর্বিচারের অবকাশ রাখলেন? আমরা সমান্তরাল ভাবে দেখব ‘নয়া গণতন্ত্রের’ নীতিগত রাস্তাটি সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ক্ষেত্রেও এক ছিল, অর্থাৎ আমূল ভূমিসংস্কার ও গণতান্ত্রিক কৃষিনীতি। কিন্তু রুশদেশের ক্ষমতাকাঠামো যতটা কেন্দ্রীভূত ছিল, চিন দেশের ক্ষমতা ছিল ততটাই বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা সামন্ত যুদ্ধবাজদের হাতে। ফলস্বরূপ যেখানে রুশদেশে বিপ্লবের পর ছয় বছর ধরে জারের বাহিনীর সঙ্গে বলশেভিক বাহিনীর যুদ্ধ চলল, সেখানে চিনদেশে বিপ্লব করার জন্যই কুড়ি বছর ধরে রক্তক্ষয়ী গেরিলা যুদ্ধ চালাতে হল। বিষয় হল, ‘নয়া গণতন্ত্র’ তত্ত্বটি ‘প্রয়োজনীয়’ পুঁজি বিকাশের রণনৈতিক দায় নিলেও আদর্শগত ভাবে পুঁজি বিলোপের ‘গণতান্ত্রিক’ নীতিমালার তত্ত্বায়ন ছিল। এটি বলার অর্থ হল: পুঁজি সঞ্চয়নের ঐতিহাসিক নিয়ম, পুঁজির আঙ্গিক গঠনবিন্যাস এবং মুনাফার পরম উদ্দেশ্যে বা আচারে শিল্পকারখানাগুলি প্রচালিত করার বিপরীতে, অর্থাৎ অতি উৎপাদন, চাহিদা জোগানের পুঁজিবাদী বিপর্যয়, বর্ধিত পুনরুৎপাদন ইত্যাদি মার্কসের দ্বারা আবিষ্কৃত পুঁজির বিচলনপদ্ধতি ও প্রভাবগুলিকে জয় করা এমন নীতি, যা এই সবগুলির বিপরীতে চাহিদা জোগানের ভারসাম্য বজায় রেখে উৎপাদকদের উৎপাদন ক্ষমতার প্রকৃত সুব্যবহারের মাধ্যমে লোকের ক্রয়ক্ষমতা ঠিক রেখে পারস্পরিকভাবে নির্ভরশীল যৌথ সমাজকে ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের কবল থেকে মুক্ত করে স্বাবলম্বী করে তুলবে।
যে সমস্যা কেউই বুঝতে চান না, তা হল যে কোনও সত্যেরই চরম (অবজেক্টিভ) শর্ত ‘স্থান’ ও ‘কাল’। মার্কস যখন ‘পুঁজি’ লিখছেন, তখন তাঁর কাছে না ছিল গ্রীষ্মদেশের শ্রুতি ও স্মৃতিনির্ভর জ্ঞানপরম্পরার হাল, না ছিল চাষা কারিগরদের হাজার হাজার বছরের পুঁথিচর্চার হদিশ। আবার, এঙ্গেলস যখন লিখছেন, যন্ত্রোন্নত সভ্যতার কাছে পর্যদুস্ত ভারতের সমাজ, তখনও তাঁর কাছে না ছিল পলাশির যুদ্ধকে বিচার করার মতো মুঘল সমর-প্রশাসন সম্পর্কে ঐতিহাসিক সূত্রাদি, না ছিল ব্রিটিশপূর্ব এশিয়ার আন্তর্জাতিক উদ্বৃত্ত-বাণিজ্য কিংবা নৌবিদ্যা সম্পর্কে ধারণা। সেই এঙ্গেলস যখন লিখছেন অতি-উৎপাদনের পক্ষে, তা বাস্তবতই ইউরোপের সামাজিক অবস্থায় একটি প্রযোজ্য সত্য থেকে উদ্ভূত, যেখানে এনক্লোজারে উচ্ছিষ্ট শ্রমিক জনতার ভিড় শহরে উপচে পড়ছে এবং সামান্য বাসার সংস্থানও নাই। আমরা ভুলে যাই সেইসব পারিপার্শ্বিকতা, যা থেকে এঙ্গেলসের মার্কসবাদ নির্মিত হচ্ছে; এক তরুণ হেগেলিয়ন, যিনি হেগেলের ধর্ম ও দর্শন সংক্রান্ত রাজনৈতিক ব্যাখ্যাগুলির দ্বারা অনুপ্রাণিত– সিদ্ধান্তগুলির দ্বারা হতাশ, মার্কসের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে খুঁজে পাচ্ছেন হেগেল সম্পর্কে তাঁর সকল বেগ ও রহস্যের বৈপ্লবিক উত্তর। অথচ যে ‘দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ’ তিনি নির্মাণ করবেন, তাতে হেগেল সম্পর্কে মার্কসের বিচার যত না ভিত্তিস্বরূপ হবে, তার চেয়ে অধিকতর যান্ত্রিক বস্তুবাদী ফয়েরবাখের প্রভাব সেই দর্শনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তত্ত্বচর্চার গতিমুখ নিয়ন্ত্রণ করবে। মার্কসবাদ খোদ ও কেবল ‘ভাববাদ বনাম বস্তুবাদ’, ‘মাথা বনাম হাত’, ‘ধর্ম বনাম বিজ্ঞান’, এমনকী ‘শোষক বনাম শোষিত’ এইসব বাইনারিতে তত্ত্ব ও ইতিহাসচর্চ্চা করবে। যদিও তরুণ বয়সে দর্শন সংক্রান্ত মার্কসের সামান্য লেখাপত্রের মধ্য দিয়ে বোঝা যায় যে তাঁর নিজস্ব দার্শনিক সিদ্ধান্তগুলি হেগেল সম্পর্কে ফয়েরবাখের লেখা সমালোচনা থেকে ফয়েরবাখের বদলে হেগেলেরই সিদ্ধান্তগুলির তাৎপর্যের দিগন্তকে একপ্রকার নতুন ভাবে উন্মোচন করে।

তা যাক, স্থান ও কালের কথা এবং আরওবিধ কারণেই, মাও সে তুং-ও, যখন নয়া গণতন্ত্রের তত্ত্বায়ন করছেন, নামকরণেই বোঝা যায় তা কতটা যুগোপযোগী এবং কার্যত বিপ্লবের দায়ভাগী হয়ে এমন ধরনের ‘গণতন্ত্র’কে তত্ত্বায়িত করছে যা মূলগত ভাবেই বুর্জোয়া ধনতান্ত্রিক বিকাশের পর্যায়বাদকে নীতিগত এবং আদর্শগত ভাবে খারিজ করে নির্মিত। ছয়ের দশকের চিনে ‘সাংস্কৃতিক বিপ্লব’ কালে মাও যখন এই প্রশ্নে লড়ছেন যে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ নয়, বরং শ্রেণি সংগ্রামই সাম্যবাদের দিকে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান মাধ্যম হবে, তখন আমরা বুর্জোয়া বিকাশের পর্যায়বাদকে তাঁর ‘নতুন ধরনের গণতন্ত্র’ থেকে সোচ্চারে বাতিল করে বলতে পারি শ্রেণি শোষণভিত্তিক সমাজের উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ আদতে উৎপাদকের ‘ইচ্ছানিরপেক্ষ’ এবং অনুৎপাদক শোষকের ‘ইচ্ছাধীন’; যে বিকাশ ধনতন্ত্র নামক পর্যায়টিতেই পৃথিবী ও জীবতন্ত্রকে ধ্বংস করে ফেলার মতো অস্ত্র হাজির করে ফেলেছে, সেই বিকাশ সাম্যবাদ অবধি যাওয়ার অনেক আগেই ‘ইচ্ছানিরপেক্ষ ভাবে’ সংখ্যাগুরু মানুষকে বন্যা, খরা, ভূমিকম্প, মহামারীর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে সমরসজ্জিত রোবটে পরিণত করবে, বা উল্কাপাতের মতোই একটামাত্র পরমাণু যুদ্ধে এই যাত্রার মনুষ্য সভ্যতার সমাপ্তি ঘটাবে।
নৈরাজ্যবাদী নৃবিজ্ঞানী ডেভিড গ্রেবার থেকে লালনবাদী কবি ফরহাদ মজহার, এখনও সকলে যখন ‘গণতন্ত্র’ নামক পশ্চিমা ‘টার্মিনেটর’-কেই রাজনৈতিক অঙ্গনে ‘উন্নতি’র লব্জ হিসাবে ব্যবহার করেন, এটি এখনও কতটা যুগোপযোগী, সেই প্রতর্কে না গিয়েই বলা যায়, শুধু মার্কসবাদ নয় বরং পশ্চিমা গণতন্ত্রের প্রকৃত ধাত্রী পুঁজিরও দর্শন বিচার-পুনর্বিচার শুরু হবে এঙ্গেলস থেকেই। বোঝা শুরু হয়: ধর্ম, দর্শন যেসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য সাধনা চালিয়েছে, তার নিষ্ক্রান্তিই মনুষ্য সভ্যতার নিষ্ক্রান্তি। আজ তাই এঙ্গেলসের প্রাসঙ্গিকতা বিচার আজকের স্থান ও কালের নিরিখে ঘটবে; যখন আমরা দেখাব বাংলাদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আর ইংল্যান্ডের এনক্লোজার আইন পদ্ধতিগত ভাবে লুঠ, গণহত্যা আর দখলদারিতে কোনও ফারাক রাখেনি, বরং বাংলাদেশে তার বাড়তি কাজ ছিল জমি, উৎপাদন, বন্টন ও সামাজিক ক্ষমতা থেকে মেয়েদের উৎখাত করা। আমরা আরও দেখাব, পুঁজির আদিম সঞ্চয়ন শুধুমাত্র সম্পদ কিংবা শ্রমের কেন্দ্রীভবন ছিল না, ছিল আরব, এশিয়া ও আফ্রিকা থেকে লুঠ করা জ্ঞান ও প্রযুক্তিরও কেন্দ্রীভবন। আজ আমরা সোচ্চারে জানাব: যে-প্রকারে জ্ঞান, ক্ষমতা, উৎপাদন, বাজার, শিক্ষা সকলের কাছে সমান ও স্বতন্ত্র্য হতে পারে, তা হল অজস্র সত্যকে ধারণ করতে পারার মতো একটি সমাজতান্ত্রিক সত্য, যার সর্বৈব উপাদান শোষণ নিরপেক্ষ, পরস্পর নির্ভরশীল, সহযোগিতামূলক, স্থানীয় এবং একইসঙ্গে আন্তর্জাতিকতাবাদী অবাধ বিনিময়ের মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকা কৌম সমাজগুলির ঐতিহাসিক শ্রমবিভাজনেই শামিল। আমরা এঙ্গেলসের বিশ শতকীয় সন্তানাদির মতো সাম্যবাদ বলতে আর আকাশে হাঁটা, কায়িক শ্রম গায়েব হয়ে যাওয়া কিংবা গোটা গোটা গোষ্ঠীর সকলের একই রান্না একই খাবার একই রুটিন রোজ একযোগে পালন করা বুঝি না; এমনকী কোনও ‘সমাজতান্ত্রিক দেশ’-ও যখন যুদ্ধের বাধ্যতায় মহাকাশবিদ্যায় উন্নতি করে, উচ্ছ্বাস তো দূর, তার চোখে চোখ রেখে নিখুঁত জবাবদিহি চাই।
…………………………….
ফলো করুন আমাদের ওয়েবসাইট: রোববার.ইন
…………………………….
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
