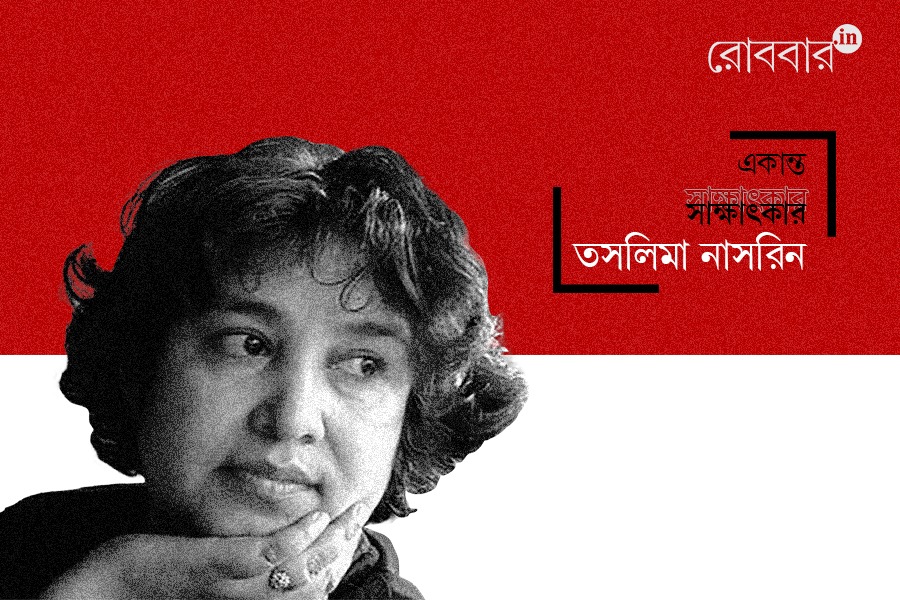
‘অনেক লেখক তার শিকড়ের থেকে দূরে গিয়ে প্রচুর ভালো লিখেছে, আবার অনেক লেখক তার শিকড়ের কাছে থেকে সারা জীবন ভালো লিখে গিয়েছে। সুতরাং এটা বলা যায় না যে সব লেখকের কাছে সমানভাবে তার শিকড়ের গুরুত্ব রয়েছে। আমার মনে হয় একজন লেখক যে কোনও পরিস্থিতিতে ভাবনাচিন্তা করতে পারে এবং লিখতে পারে। মিলান কুন্দেরা তাঁর সবথেকে ভালো লেখাগুলো লিখেছে প্যারিসে বসে। এরকম প্রচুর মানুষ স্থান বদল করেছে। তাতে কোনও অসুবিধে নেই। আমি তাদের তুলনায় একটু ‘গ্রাম্য’ বলতে পারো। পিছুটান আমার একটু বেশি। আমি শিকড়ের কাছে ফেরত আসতে চেয়েছি বারবার।’ বলছেন তসলিমা নাসরিন। রোববার.ইন-এর পক্ষ থেকে শুনলেন ঔষ্ণীক ঘোষ সোম।

আপনি আপনার কবি সত্তাকে নাকি গদ্যকার সত্তাকে আগে রাখবেন?
দেখো, আমি একজন সৎ মানুষ আর এটাই আমার সবথেকে বড় পরিচয়। কখনও কবিতা লিখি কখনও গদ্য লিখি কখনও অন্য কিছু। কারও আমার কবিতা ভালো লাগে, কারও কাছে আমার গদ্য বেশি প্রিয়। এমনটা নয় যে, আমি গদ্যলেখক হিসেবেই বেশি পরিচিতি পেতে চাই কিংবা কবি হিসেবে। মানুষের ভালো লাগতেই পারে কিন্তু আমার কাছে আমার সততাই বড় পরিচয়। এমন তো হয়েই থাকে কখনও কবিতা লিখতে ভালো লাগে, কখনও প্রবন্ধ– কিন্তু আমি কোনও একটাকে ওপরে রাখতে চাই না।

আপনার কবিতা যাপনের শুরুর দিকের কথা যদি একটু বলেন?
সেই ১৩ বছর বয়স থেকে কবিতা লিখতে শুরু করেছি। আমার বাড়িতে না কবিতা লেখার একটা ব্যাপার ছিল। আমার বড় দাদা ‘পাতা’ নামের একটা কবিতা পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। ওখানে আমার দাদা নিজে কবিতা লিখতেন। আমি তো ছোট ছিলাম, তো আমার কবিতা ওখানে ছাপার প্রশ্ন ওঠে না তবে আমি লুকিয়ে লুকিয়ে দাদার কবিতা পড়তাম। ছোট বলে আমাকে সেগুলো ধরতে দেওয়া হত না। মনে আছে, একবার আমার নামে একটা ছড়া আমার দাদা লিখে দিয়েছিল ওখানে। আমার খুব খারাপ লেগেছিল আমার নাম যাচ্ছে যখন ছড়াটা তো আমি লিখব, আমার দাদা কেন লিখে দেবে? এছাড়া স্কুলের বইয়ে তো রবীন্দ্রনাথের কবিতা নজরুলের কবিতা সব পড়তামই। আমার মা খুব কবিতা ভালোবাসত।
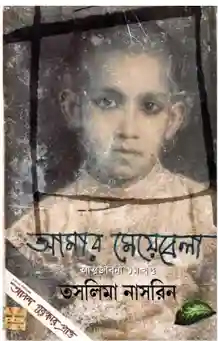
আমি আর একটু বড় হওয়ার পর আমার বাবা কবিতায় কথা বলত। বাবা একটা জায়গায় কবিতা লিখে যেত। আমি তার উত্তরে আরেকটা কবিতা লিখতাম। বাবা যখন দুপুরে চলে আসত দেখার জন্য, কী লিখেছি– ওটার উত্তর আবারও কবিতায় লিখে যেত। এমনটা চলত আমাদের মধ্যে। একটা কবিতার পরিবেশ ছিল। আমার যখন ১৭ বছর বয়স, তখন আমি প্রথম কবিতা পত্রিকা সম্পাদনা করি। প্রতি তিন মাসে একবার করে বেরত। ওই পত্রিকায় ভারতের অনেক কবি কবিতা লিখতেন। তাঁরা অনেকেই নিজেরাও পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। আমরা সাতের দশকের লিটল ম্যাগাজিনের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। এখন কবিতা লিখে নাম করেছে এমন অনেকের লেখা আমার সেই পত্রিকায় ছাপা হত। আমার কবিতাও ওঁদের পত্রিকায় ছাপা হত। তার পরে মেডিকেল কলেজে যাওয়ার পর অত সময় পেতাম না। থার্ড ইয়ার পর্যন্ত সম্পাদনা করতে পেরেছি। তবে ওখানে থাকাকালীন আমি ‘শতাব্দী’ নামে একটা সাহিত্যচক্র করেছিলাম। এটা থেকেও একটা লিটল ম্যাগাজিন বের করতাম। আমার প্রথম বই কবিতার বই ‘শিকড়ে বিপুল ক্ষুধা’ ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত হয়। তখন আমি ডাক্তার হয়ে গিয়েছি।
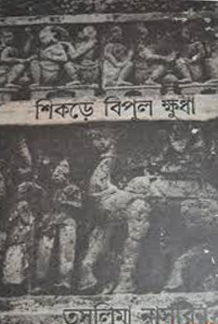
আপনার কলাম লেখার শুরু কি এর পর থেকেই?
আমার দ্বিতীয় কবিতার বই ‘নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে’ এত বেশি জনপ্রিয় হয়েছিল যে, বাংলাদেশের বিভিন্ন ম্যাগাজিন থেকে আমার কাছে কলাম চাইতে শুরু করল। তখন আমি মেয়েদের বিষয়ে কলাম লেখা শুরু করি। একদিকে মেডিকেল কলেজে ডাক্তার হিসেবে চাকরি করছিলাম, অন্যদিকে লেখালেখিও চলছিল। মেয়েদের বিষয় লিখতে শুরু করার কারণ তাদের নিয়ে খুব বেশি কেউ লেখে না। মেয়েদের কষ্টের কথা কেউ লেখে না। মেয়েরা যেভাবে নির্যাতিত হয় তার প্রতিবাদ সেভাবে লেখালেখিতে কেউ করত না। পুরুষতান্ত্রিক সিস্টেমটাকেই সবাই মেনে চলে। কিন্তু এটা ভাঙার কথা কেউ বলে না। এটা সমালোচনা কেউ করে না। আমি নিজে যেহেতু একজন মেয়ে, আমি নিজের অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখলাম। বাংলাদেশের মতো একটা সোসাইটিতে একজন মেয়েকে প্রচুর ভ্রমণ করতে দেওয়া হয় না, ছেলেদের মতো বাইরে ঘোরাঘুরি করতে দেওয়া হয় না। একটা গণ্ডির মধ্যে থাকতে হয়। আমার গণ্ডিটা ছিল ঘর থেকে স্কুল কলেজ। হয়তো কখনও বান্ধবীদের বাড়ি। তাছাড়া আর বেশি কিছু অভিজ্ঞতা নেই। মাঝেমধ্যে সিনেমা-থিয়েটার দেখতাম, ওইটুকুই। সেই কারণে আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে শুরু হল লেখা। নিজের জীবনে যা প্রত্যক্ষ করেছি, তা হৃদয় দিয়ে লিখেছি। তাতে হয়েছে কী, প্রচুর মেয়েরা আমার সঙ্গে রিলেট করতে পেরেছে। তাদের জীবনেও একই ঘটনা ঘটেছে। একই অভিজ্ঞতা, একই অনুভূতি। তাই আমার লেখা বেরলে পত্রিকা অনেক বেশি পরিমাণে বিক্রি হত। প্রচুর চিঠি আসত। যারা পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার, তারা গালাগালি দিয়ে চিঠি লিখত পত্রিকায়। আর আমার মতো অভিজ্ঞতা যাদের বা পুরুষরাও যারা ‘সিমপ্যাথেটিক’, সমান অধিকারে বিশ্বাসী, তারা উৎসাহ দিয়ে চিঠি লিখত।
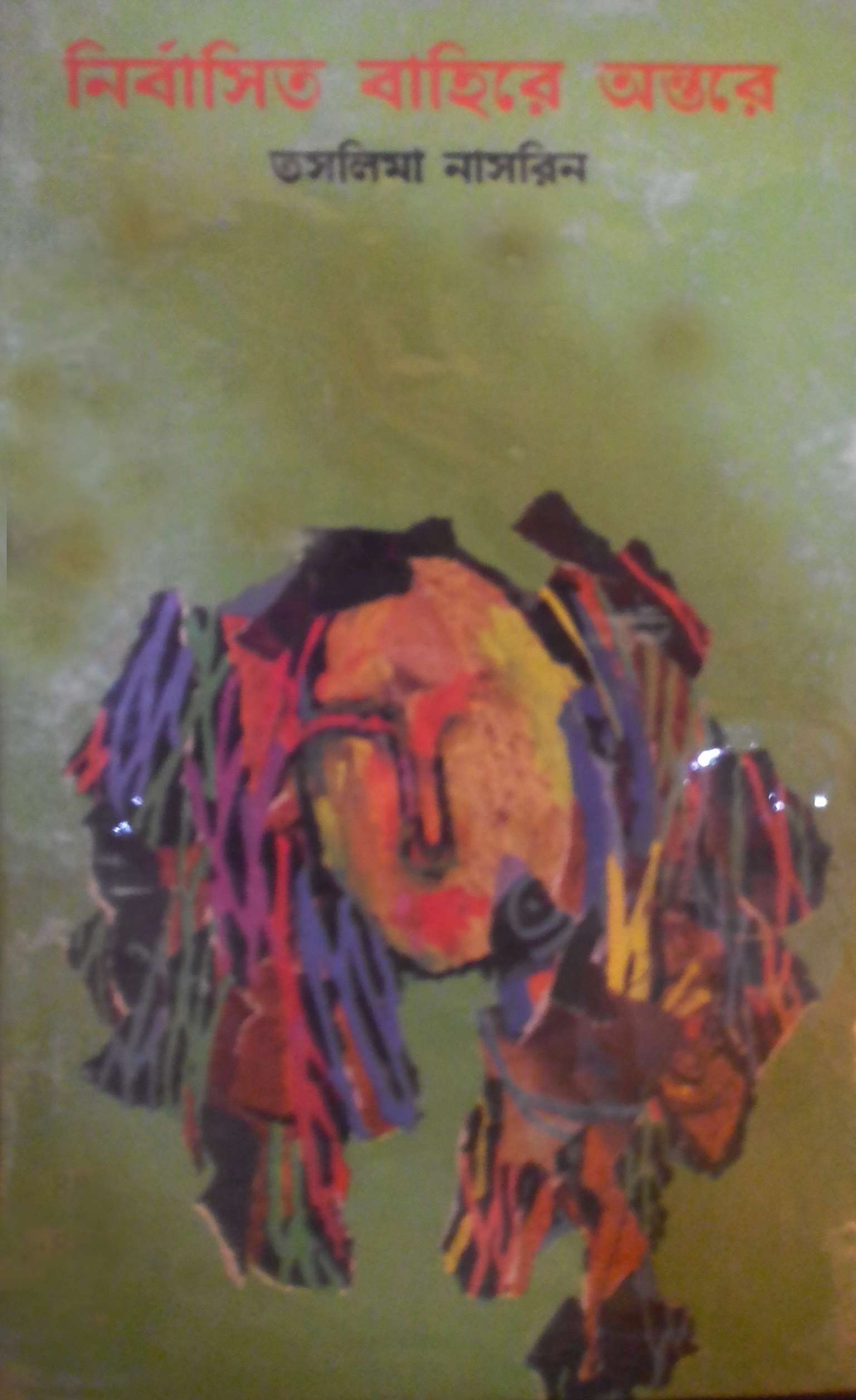
‘লজ্জা‘ কি আপনার এই কলাম লেখার একটা এক্সটেনশন?
ভারতে বাবরি মসজিদ ভাঙার পর বাংলাদেশে একটা বড় আকারের রিঅ্যাকশন হয়। মৌলবাদীরা হিন্দুদের ওপর এক ধরনের অত্যাচার চালাচ্ছিল। আমি তখন ঢাকায় থাকি। আমার কিছু হিন্দু বন্ধুদের বাড়িতে গিয়ে দেখতাম তারা ঠিক আছে কি না, কিছু হিন্দু মেয়েকে আমি বাড়িতে এনে রেখেছিলাম প্রোটেকশনের জন্য, বহু জায়গায় ঘুরে ঘুরে দেখেছি পরিস্থিতি কেমন। এইসব দেখে আমার মনে হয়েছিল আমার একটা কিছু লেখা উচিত। প্রতিবাদ করা উচিত। ‘লজ্জা’ ঠিক সম্পূর্ণ উপন্যাস নয়, ফ্যাক্টের সঙ্গে সঙ্গে প্যারালাল একটা পরিবারের গল্প বলেছি মাত্র।

‘লজ্জা’ বইটা লিখতাম আমার কাজের ফাঁকে ফাঁকে। তখন আমি ঢাকা মেডিকেল কলেজে অ্যানেস্থেশিওলজিস্ট হিসেবে কাজ করি। ধরো রোগীকে অ্যানেস্থেশিয়া দিয়ে এক ফাঁকে এসে কিছুটা লিখলাম, আবার কাউকে ইনজেকশন দিয়ে একফাঁকে এসে লিখছি। দিনে ডিউটি থাকত, রাতে ডিউটি থাকত– তার ফাঁকে ফাঁকেই এভাবে লিখেছি। এই সময় আমাকে প্রচণ্ড বেশি লেখালেখি করতে হত কারণ আমি বাড়ি নিয়ে থাকতাম ঢাকা শহরে। ময়মনসিংহে আমাদের বাড়ি, তো ঢাকায় ভাড়া থাকতাম। আর ডাক্তারিতে আমাদের মাইনে বেশি ছিল না। কলাম লেখার টাকা দিয়ে আমার সংসার চলত।
আর সেই সময় আমার কলাম এতটাই জনপ্রিয় ছিল যে, বই আকারে বেরলে সেগুলো প্রচুর পরিমাণে বিক্রি হত। এই দেখে প্রকাশকরা অগ্রিম টাকা দিয়ে যেত উপন্যাস লেখার জন্য। আমি ওদের বলেছিলাম, আমি উপন্যাস লিখতে জানি না। ডাক্তারিরও একটা চাপ ছিল। কিন্তু তারা শুনতে নারাজ! আর আমার তখন টাকাটারও প্রয়োজন ছিল। কেননা আমি যেসব জায়গায় ভাড়া থাকতাম সেইসব বাড়িওয়ালা চাইত না আমি সেখানে থাকি। কারণ তখন প্রায় প্রতিদিন মৌলবাদীরা আমার বিরুদ্ধে মিছিল করত। আমার কলামের জন্য তারা ক্ষুব্ধ হয়েছিল। কেননা আমি সেখানে ইসলামের সমালোচনা করেছি। বাড়িওয়ালারা ভয় পেত তাদের বাড়ি আমার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এই ভেবে। আমার একটা বাড়ি কেনার দরকার ছিল। তাই পরপর আমাকে বেশ কিছু উপন্যাস লিখতে হয়েছে।
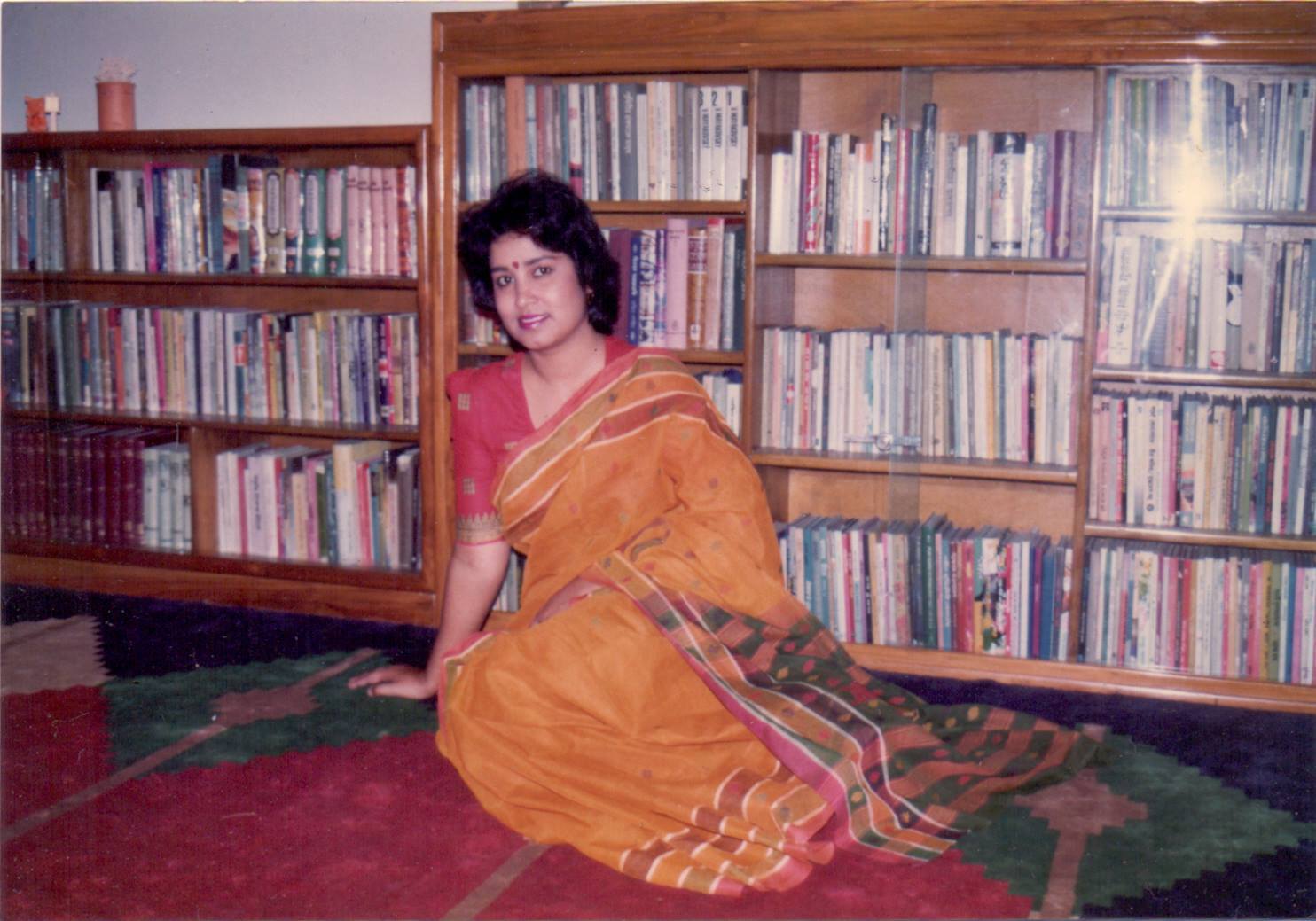
এই সময় তো আপনার ওপর সামাজিক এবং রাষ্ট্রের চাপ দৃঢ়বদ্ধ হতে শুরু করেছিল…
১৯৯৪ সালে প্যারিসে ‘প্রেস ফ্রিডম’-এর একটা অনুষ্ঠানে আমাকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বাক স্বাধীনতার ওপর অনেকগুলো অনুষ্ঠান হয়েছিল ওখানে। ফেরার সময় আমি কলকাতা হয়ে ঢাকায় ফিরি। কলকাতার একটা সংবাদপত্রে আমার একটা ইন্টারভিউ করা হয়েছিল। সেখানে আমি শরিয়া আইনের সংশোধনের কথা বলেছিলাম কিন্তু ভুল করে সেটাকে তারা কোরানের সংশোধন লিখে হেডলাইন করেছিল। ঢাকায় ফিরতেই দেখি– বিরাট আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছে আমার বিরুদ্ধে। তখন বাংলাদেশের সরকার ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করার জন্য আমার বিরুদ্ধে মামলা করল এবং আমি হাইডিংয়ে যেতে বাধ্য হলাম। তারপর দেশ ছাড়তে বাধ্য করা হল। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ঘটনাগুলো ঘটে গেছে। আমার নতুন ফ্ল্যাট কেনার পর বোধহয় আমি ছ’মাসও থাকতে পারিনি।
আমাকে কোনও একটা নির্দিষ্ট বই লেখার জন্য দেশ ছাড়তে হয়েছে, তেমনটা নয়। দেশ ছাড়তে হয়েছে আমার ইসলামের সমালোচনা করার জন্য। এই সমালোচনা আমায় করতেই হয়েছে কারণ আমি যদি মেয়েদের সমানাধিকার চাই, সবচেয়ে বেশি বাধা হয়ে দাঁড়ায় ধর্ম। পুরুষতন্ত্র তো আছেই।
নির্বাসন একজন মুক্তচিন্তকের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ। দেশের থেকে দূরে থাকা আপনার কাজে কতটা ব্যাঘাত ঘটিয়েছে বলে আপনার মনে হয়?
মুক্তচিন্তার ওপর হস্তক্ষেপ অবশ্যই। কিন্তু নির্বাসন একটা জায়গা বদল। এই যে আমাকে নির্বাসনের জন্য বিভিন্ন দেশে থাকতে হয়েছে, এটাকে আমি খুব একটা ‘নেতিবাচক’ হিসেবে দেখি না। শুধু একটাই নেগেটিভ জায়গা যে, আমি যখন দেশে যেতে চাই, আমাকে যেতে দেওয়া হয় না। এই যে, ইউরোপ-আমেরিকায় থেকেছি, কত মানুষের সঙ্গে মিশতে পেরেছি। কত কিছু দেখেছি। আমার অভিজ্ঞতা আরও বেড়েছে। আমার চিন্তা আরও উন্নত হয়েছে। সমৃদ্ধ হয়েছি। যদিও সেখানে আমাকে ‘সেলিব্রেটি’ হিসেবে দেখা হত। কিন্তু আমি সাধারণ মানুষ হিসেবে জীবনযাপন করতে চাইতাম। কিছু কিছু দেশে সেটা সম্ভব হত না।
হ্যাঁ আমি হোমসিক ছিলাম, এটা সত্যি। দেখো, দেশে তারাই ফিরতে চায় না, যাদের সেখানে কিছু নেই। কিন্তু আমার তো ছিল। দেশে খুবই জনপ্রিয় ছিলাম আমি। আমার বই বেস্টসেলার লিস্টে ছিল। কিন্তু আমাকে থাকতে হচ্ছিল এমন মানুষদের মধ্যে, যারা আমার লেখা পড়েনি– শুধু আমি মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে কথা বলেছি বলে হাততালি দেয়, গলায় মালা পরায়। এতে আমি সন্তুষ্ট ছিলাম না। যারা আমার লেখা পড়ে, আমাকে বোঝে, যেই সমস্যার কথা বলছি তার অংশীদার তারা– তাদের মধ্যে আমি ছিলাম না। নারীর যে ‘বেসিক’ স্বাধীনতার কথা আমি বলেছি সে স্বাধীনতা ফ্রান্সে, সুইডেনে, নরওয়েতে তখন চলে এসেছে। ওখানে যদি থাকতে হয়, তাহলে ওদের সমস্যাগুলো ওদের সমাজে একেবারে মিশে গিয়ে ওদের মতো করে ভাবতে হবে লেখার জন্য। তখন আমি ভেবেছি একটা নতুন সমাজে একেবারে নতুন করে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করার চেয়ে আমি যেটা লিখছিলাম… যেখানে আমাকে অজস্র মেয়েরা বলত যে, আমি তাদের শক্তি জোগাচ্ছি, সাহস জোগাচ্ছি, আমার লেখা পড়ে তারা তাদের জীবনবদল করে ফেলছে, এগুলো আমাকে যতটা আনন্দ দিত ততটা আনন্দ দিতে পারত না যখন ইউরোপীয় মেয়েরা আমাকে বলত যে, আমার লেখা তাদেরকে শক্তি জোগায়। অবশ্যই সেখানেও নির্যাতিত মেয়েরা রয়েছে, কিন্তু আমি যাদের জন্য লিখতাম তারা অনেক বেশি অপ্রেসড। তাই এইখানেই বেশি প্রয়োজন আমার।

তাই তখন আমি কলকাতায় আসতাম। আমার এত ভালো লাগত বাংলার পরিবেশ! এখানে আমার প্রকাশক রয়েছে, আমার বই বিক্রি হচ্ছে– সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমার পাঠক, তারা রয়েছে। সুইডেনে আমার বাংলা ভাষার মধ্যে থাকা হচ্ছিল না। ভাষা তো বিবর্তিত হয়, তার সাক্ষী থাকা দরকার ছিল। তাই কলকাতায় থাকার মনস্থির করলাম। কিন্তু সেখানেও থাকতে দেওয়া হল না।
প্রথম জীবনে বাংলাদেশ তারপর দীর্ঘদিন প্রবাসে থাকা এই পটভূমির পরিবর্তন আপনাকে কতটা প্রভাবিত করেছে, দুই গোলার্ধের মানুষের মধ্যে কতটা পার্থক্য এবং মিল চোখে পড়েছে?
আমি বলব, আমার মধ্যে রক্ষণশীলতার যতটুকু অবশিষ্ট ছিল, বাইরে যাওয়ার পর সব গিয়েছে। অনেক কিছুকে একটা বড় পরিপ্রেক্ষিত থেকে দেখতে পেরেছি। আমার লেখালেখিতে তা সামগ্রিকভাবে প্রভাব ফেলেছে। আমাদের এখানে যারা মুক্তচিন্তক এবং স্বনির্ভর– তারাও কোনও না কোনওভাবে কিছু কিছু প্রেজুডিজ লালন করে। আমি সেই ছোটবেলা থেকেই প্রথাগুলোকে ভাঙতে শুরু করেছিলাম। এটা আরও বেশি করে করতে পেরেছি বাইরে যাওয়ার পর। তা বলে এমন নয় যে, বাইরে আমি কোনও রক্ষণশীল মানুষ দেখিনি। ইউরোপ-আমেরিকায় সবাই কিন্তু ‘মুক্তচিন্তক’ নয়। আমি এরকম প্রচুর মানুষ দেখেছি যারা ধর্মান্ধ এবং নারীবিদ্বেষী। ওখানেও ধর্ষণ হয়। অ্যাবিউসিভ হাজবেন্ড থাকে। এখানেও যেমন রক্ষণশীল এবং মুক্তচিন্তক– দুই ধরনের মানুষেরা রয়েছে, ওখানেও তাই। ইউরোপ আমাদের থেকে অনেক আগে সভ্য হয়েছে এটা ঠিক, অর্থনৈতিক উন্নতি তাদের আগে হয়েছে, তুলনায় মানুষ অনেক বেশি শিক্ষিত ওখানে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, সেখানে সবাই মুক্তচিন্তা করে কিংবা নারীর সমাধিকারে বিশ্বাস করে। এখন তুমি কার সঙ্গে মিশছ, কার সঙ্গে থেকে তোমার চিন্তাভাবনা পরিবর্তন হচ্ছে বা উন্নতি হচ্ছে– সেইটা দেখতে হবে। ওখানে যেহেতু আমার কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা হত, তাই আমার আদর্শে বিশ্বাস করে এমন মানুষের সংস্পর্শে বেশি এসেছি।
একজন লেখকের কাছে তার শিকড়ের গুরুত্ব কতটা?
দেখো, একেকজন লেখক একেকরকম হয়। অনেক লেখক তার শিকড়ের থেকে দূরে গিয়ে প্রচুর ভালো লিখেছে আবার অনেক লেখক তার শিকড়ের কাছে থেকে সারা জীবন ভালো লিখে গিয়েছে। সুতরাং এটা বলা যায় না যে, সব লেখকের কাছে সমানভাবে তার শিকড়ের গুরুত্ব রয়েছে। আমার মনে হয়, একজন লেখক যে কোনও পরিস্থিতিতে ভাবনাচিন্তা করতে পারে এবং লিখতে পারে। মিলান কুন্দেরা তাঁর সবথেকে ভালো লেখাগুলো লিখেছে প্যারিসে বসে। এরকম প্রচুর মানুষ স্থান বদল করেছে। তাতে কোনও অসুবিধে নেই। আমি তাদের তুলনায় একটু ‘গ্রাম্য’ বলতে পারো। পিছুটান আমার একটু বেশি। আমি শিকড়ের কাছে ফেরত আসতে চেয়েছি বারবার। তাই বিদেশে আমার থাকতে ভালো লাগেনি। আমি শিকড়ের কাছে এসেছি।

এই একুশ শতকে দাঁড়িয়েও একজন নারীর কি আদৌ কোন দেশ আছে?
দেশ মানে হল নিরাপত্তা। আমি যদি রাস্তাঘাটে নিরাপদ বোধ না করি, যদি যে কোনও মানুষের সঙ্গে কথা বলে নিরাপদ বোধ না করি, ক্রমাগত আমার ওপর আক্রমণ চলে কিংবা শুধু নারী বলেই অতর্কিতে আমার ওপর আক্রমণ হয়, এমনকী, ঘরেও নারী হওয়ার কারণে যদি আমাকে হেনস্তার শিকার হতে হয়, তাহলে নারীর দেশ থাকবে কী করে। দেশ মানে কেবল নাগরিকত্ব এবং ভোট দেওয়া নয়, এই নিরাপত্তাগুলো যদি না থাকে তাহলে আমি বলব নারীর কোনও দেশ নেই।
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
