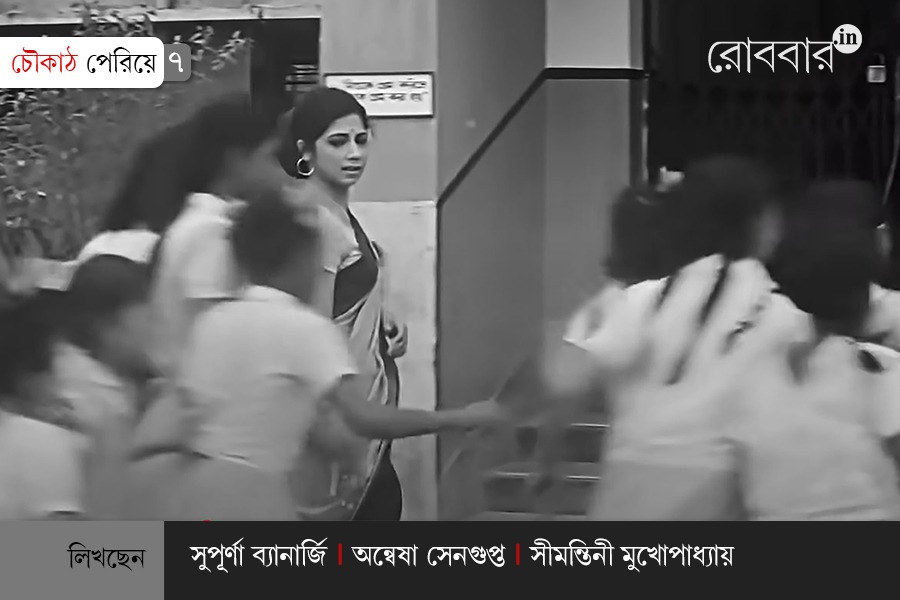
অবশ্য দেশভাগের পরেকার পরিস্থিতিতে, একথা বললে ভুল হবে যে, স্কুল শিক্ষিকাদের সংসার ও চাকরির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে অসুবিধা হত না। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্প ‘ছোটদিদিমণি’তে আমরা পড়ি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তির কথা। মূল কারণ স্ত্রী স্কুলে চাকরি নেওয়ার পর সন্তানদের দেখাশোনায় গাফিলতি ঘটছে। এই প্রসঙ্গে বলি শিপ্রা দত্তের কথা। স্কুলে পড়িয়েছেন তিনি দীর্ঘদিন। সংসার আর চাকরির টানাপোড়েন বিপর্যস্ত করেছে তাঁকে বারবার। মেয়ে ছোট, তাকে দেখাশুনো করতে হবে –এই ভেবে প্রথম স্কুলের চাকরি ছাড়েন শিপ্রা। কিন্তু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কৃতি ছাত্রীর পক্ষে শুধু ঘরসংসার নিয়ে থাকা ছিল দুঃসহ। তাই নানা স্কুলে আংশিক সময়ের চাকরি করতে শুরু করেন।



৭.
১৮৪৯ সালে বেথুন সাহেবের হাত ধরে মেয়েদের ইশকুল শুরু হল কলকাতায়। তার প্রায় ১০০ বছর পর দেশ স্বাধীন হল, ভাগও হল। আস্তে আস্তে মেয়ে-ইশকুলের দিদিমণিদের ধরনও পাল্টাল। দেশভাগের সময়ে চরম আর্থিক টালমাটালের মধ্যে সংসারের হাল ধরতে অনেক শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত মেয়ে স্কুলের দিদিমণি হলেন। আগে এই চাকরিতে মেয়েরা ছিলেন বটে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তাঁদের সংখ্যা ছিল কম। আর তাঁদের সিংহভাগই ছিলেন খ্রিস্টান বা ব্রাহ্ম। খ্রিস্টানদের অনেকেই আবার ছিলেন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ও ইউরোপিয়ান। নতুন দেশে নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত হয়ে তাঁদের অনেকেই ইংল্যান্ড, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও অন্যান্য দেশে পাড়ি দিলেন। ১৯৪৮-’৫১ এ লা মারটিনিয়ার ফর গার্লসে পড়তেন এলিজাবেথ জেমস। তাঁর স্মৃতিকথায় পাওয়া যায় একের পর এক শিক্ষিকাদের স্কুল ছেড়ে চলে যাওয়ার বিবরণ। ‘বছরের মাঝখানে শ্রীমতি সিম্পসন চলে গেলেন। চলে গেলেন শ্রীমতি স্টিভেন্স। তিনি আমাদের অঙ্ক পড়াতেন, যেমন লম্বা তেমন চওড়া। বছরের প্রথমেই সব পড়ার বই শেষ করে ফেলার অভ্যাস ছিল আমার। তাই খুব একটা মুখস্থ করতে হত না। শ্রীমতি স্টিভেন্স জানতে পেরে আমাকে বলতেন ক্লাসকে পড়া বোঝাতে, নিজে চেয়ারে চুপ করে বসে থাকতেন। আমার খুব উপকার হয়েছিল। পড়া মনে রাখার সব চেয়ে ভাল উপায় অন্যদের বোঝানো। তিনিও চলে গেলেন।’
একদিকে যেমন আমরা পাই এই চলে যাওয়ার গল্প, অন্যদিকে নতুন করে শুরু করার গল্পও পাওয়া যায়, বিশেষ করে, উদ্বাস্তুদের বয়ানে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পের চরিত্র বিদিশা দেশভাগের ঠেলায় পূর্ববঙ্গ থেকে কলকাতা আসে। স্কুলে পড়ানোর চাকরি হয়ে ওঠে তার সম্বল। ঠিক তেমনই আসেন বীথি, ময়মনসিংহ থেকে কলকাতা। তাঁর কথা আমরা পেয়েছি গার্গী চক্রবর্তীর বইতে। সালটা ১৯৫০। অসুস্থ বাবা, ছোট ছোট ভাইবোনের দায়িত্ব তার ওপর। বহু অসুবিধার মধ্যে কলেজের পড়াশুনো শেষ করেই বীথি নেন স্কুলের চাকরি। স্কুল শিক্ষিকাদের মধ্যে উদ্বাস্তু মহিলাদের চোখে পড়ার মতো উপস্থিতির ফলে বাস্তুহারা ছাত্রীদের জীবন হয়তো কখনও কখনও সামান্য সহজ হয়েছিল। রেণুকা চোধুরী নামে জনৈক মহিলা তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন এই কথা। বাবার মৃত্যুর পর তাঁরা যখন কলকাতায় আসেন– আর্থিক ও মানসিক অবস্থা তাঁদের বেসামাল। সেই সময় তিনি ও তাঁর বোন ভর্তি হন বেনেপুকুর বিদ্যাপীঠে, ‘বড়দি অঞ্জলি সেন, মিনুদি, তৃপ্তিদি, সরযূদি, অপর্ণাদি, এঁরা সবাই এত আন্তরিক ছিলেন যে বিদ্যালয়কে যেন গৃহপরিবেশ মনে হতো। তাঁদের স্নেহ-মমতায় আমাদের পড়ার উৎসাহ অনেক গুণ বেড়ে গেল।’ বিয়ের জন্য যখন তাঁর পড়ায় বিরতি হওয়ার উপক্রম হল, স্কুলের বড়দি দেরি করে ক্লাসে আসার অনুমতি দেন। উদ্বাস্তু মেয়েদের নানা প্রতিকুলতার কথা মাথায় রেখেই মেয়েদের স্কুল-কলেজ ব্যবস্থার কিছু রীতি নিয়ম গড়ে উঠছিল সেই সময়। একটা উদাহরণ দিই। ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় সুরেন্দ্রনাথ কলেজ ফর উইমেন। উদ্বাস্তু মেয়েদের চাকরির পাশাপাশি পড়াশোনার সুযোগ করে দিতে এই কলেজ ভোরে চালু হয়।
…………………………………….
একদিকে যেমন আমরা পাই এই চলে যাওয়ার গল্প, অন্যদিকে নতুন করে শুরু করার গল্পও পাওয়া যায়, বিশেষ করে, উদ্বাস্তুদের বয়ানে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পের চরিত্র বিদিশা দেশভাগের ঠেলায় পূর্ববঙ্গ থেকে কলকাতা আসে। স্কুলে পড়ানোর চাকরি হয়ে ওঠে তার সম্বল। ঠিক তেমনই আসেন বীথি, ময়মনসিংহ থেকে কলকাতা। তাঁর কথা আমরা পেয়েছি গার্গী চক্রবর্তীর বইতে। সালটা ১৯৫০। অসুস্থ বাবা, ছোটছোট ভাইবোনের দায়িত্ব তার ওপর। বহু অসুবিধার মধ্যে কলেজের পড়াশুনো শেষ করেই বীথি নেন স্কুলের চাকরি।
…………………………………….
উদ্বাস্তুরা আসার ফলে অবশ্য মেয়েদের স্কুলের চাকরিতেও প্রতিযোগিতা বাড়ে। আমরা বিদিশায় পড়ি– ‘‘…পাঁচ সাত বছর আগেও এ রকম ছিলনা। মেয়েদের স্কুলে একজন ভালো টিচার পাওয়া দুঃসাধ্য ছিল, একজন গ্র্যাজুয়েটকে দু’ তিনটে স্কুলে টানাটানি করত। কিন্তু রাতারাতি সব বদলে গেল। পার্টিশন। পূর্ববঙ্গের ঘরছাড়া মানুষ বন্যার মতো এসেছে কলকাতায়, জীবিকার সংগ্রাম হয়েছে নির্মমতম। আজ আর বিএ এমএদের সেধে আনতে হয় না, মেয়েদের ইস্কুলের দরজায় তারা ধর্না দিয়ে বেড়ায়। পঁচিশ টাকা, ত্রিশ টাকা, চল্লিশ টাকা– কিছুতেই তাদের আপত্তি নেই। একটা কিছু পেলেই হল– অনিশ্চয়তার চোরাবালির ওপরে সংকীর্ণতম শক্ত ভিত্তি একটুখানি”। (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিদিশা)।
‘অবতরণিকা’ গল্পের মুখ্য চরিত্র আরতি প্রথমে স্কুলের চাকরিই খোঁজে। কিন্তু সে গ্র্যাজুয়েট নয়। “দু একটা স্কুল থেকে ইন্টারভিউ হয়ত আসে। তারপর দেখা সাক্ষাৎ ক’রে আসবার পর শোনা যায়, তারা সেই পোস্টে একজন গ্র্যাজুয়েট পেয়ে গেছে”। (নরেন্দ্রনাথ মিত্র, অবতরণিকা) । শুধু কলেজের গণ্ডি পেরনোই যথেষ্ট না, ক্রমে বিটি বা টিচার ট্রেনিং প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে স্কুলে চাকরির জন্য। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনই তার প্রমাণ। ১৮ মে ১৯৫৮-এর আনন্দবাজার পত্রিকায় বেরয় দুর্গাপুর স্টিল প্রজেক্টের মাল্টিল্যাটারল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের জুনিয়র টিচারের কয়েকটি পদের জন্য বিজ্ঞাপন, শুধুমাত্র মহিলা প্রার্থীদের জন্য। আবেদনকারীদের আবশ্যক যোগ্যতা টিচার ট্রেনিং-সহ আইএ পাশ। কয়েক দিন পর, এই একই কাগজে চোখে পড়ে রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের এক ঘোষণা। সেখানে বলা হয়েছে, সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ে যে সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাকে নিযুক্ত করা হবে, তাঁদের সরকারি ব্যয়ে ট্রেনিং দেওয়া হবে। তারপরে তাঁরা পড়ানো শুরু করতে পারবেন।
মেয়েদের স্কুলের চাকরিতে প্রতিযোগিতার আরেকটা কারণ ছিল এই চাকরির সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা। স্বাধীনতার পর বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের চোখে মেয়েদের ইশকুলে পড়ানো ছিল তুলনায় সম্মানের কাজ। আন্দাজ করি, এর পিছনে ছিল নানা কারণ– যেমন আগে থেকেই এই পেশায় মেয়েদের উপস্থিতি, ঘড়ি ধরে যাওয়া-আসা, বেশি ছুটি, অন্যান্য সহকর্মী ও পড়ুয়াও মেয়ে, আর সাধারণভাবে সমাজে শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস ‘অর্জুন’-এ আমরা পাই লাবণ্যকে। কলেজে পড়ে সে। তাঁর বাবা আশা করেন লাবণ্য পাশ করে স্কুলে চাকরি নেবে, অভাব কমবে সংসারের। কিন্তু বাবা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ‘ইশকুল ছাড়া আর কোথাও চাকুরি করতে পাঠাবে না তাকে।’ মুক্তি মিত্রের লেখা, যুগান্তরে প্রকাশিত ‘সুধার চাকুরি’ (২১.১০.৪৭) গল্পেও আমরা স্কুলে পড়ানো মেয়েদের জন্য যে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ, এমন ইঙ্গিত পাই। বিয়ের বাজারে স্কুলে চাকরি করা মেয়েদের চাহিদাও লক্ষ করা যায় এই সময়। ১৯৫০-এর ৪ জুন যেমন একাধিক বিজ্ঞাপনে ‘শিক্ষয়িত্রী’ পাত্রী বাঞ্ছনীয় বলা হয়েছে। ঠিক তেমনই ২২ জুলাই ১৯৫১-এর যুগান্তর-এ পাত্রপাত্রীর বিজ্ঞাপনে রূপবান পাত্রের জন্য সুন্দরী স্কুল শিক্ষিকা পাত্রীর আবেদন চাওয়া হয়েছে।

অবশ্য একথা বললে ভুল হবে যে, স্কুল শিক্ষিকাদের সংসার ও চাকরির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে অসুবিধা হত না। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্প ‘ছোটদিদিমণি’তে আমরা পড়ি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তির কথা। মূল কারণ স্ত্রী স্কুলে চাকরি নেওয়ার পর সন্তানদের দেখাশোনায় গাফিলতি ঘটছে। এই প্রসঙ্গে বলি শিপ্রা দত্তের কথা। স্কুলে পড়িয়েছেন তিনি দীর্ঘদিন। সংসার আর চাকরির টানাপোড়েন বিপর্যস্ত করেছে তাঁকে বারবার। মেয়ে ছোট, তাকে দেখাশুনো করতে হবে–এই ভেবে প্রথম স্কুলের চাকরি ছাড়েন শিপ্রা। কিন্তু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কৃতি ছাত্রীর পক্ষে শুধু ঘরসংসার নিয়ে থাকা ছিল দুঃসহ। তাই নানা স্কুলে আংশিক সময়ের চাকরি করতে শুরু করেন। মূলত তিনি ডেপুটেশনে পড়াতেন অন্য কোনও শিক্ষিকার ছুটির সময়। এইরকম চাকরির সঙ্গে সঙ্গে তিনি নাইটে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিটি কোর্স করেন কিছু বছর পর। তা সত্ত্বেও পাকা চাকরি পেতে সময় লাগে অনেক। অবশেষে তিনি ঋষি বঙ্কিম ঘোষ মেমোরিয়াল স্কুলে চাকরি পান। শিপ্রার জীবনের অনুরণন আমরা পাই লেখিকা সাবিত্রী রায়ের জীবনে। স্কুলে পড়ানোর কাজ নিয়েছিলেন সাবিত্রীও, চাকরি করতে গিয়ে শিশুকন্যার দেখাশোনায় সমস্যা হচ্ছে দেখে ছেড়ে দেন সে কাজ। শিক্ষিতা মেয়ে অথচ নিজে উপার্জনক্ষম নন, এই আক্ষেপ ছিল তাঁর মনে। সংসার আর চাকরির এই টানাপড়েনই হয়তো চায়নি তালপুকুর আপার প্রাইমারি বালিকা বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ। যুগান্তর-এর (২২.০৭.১৯৫০) পাতায় চোখে পড়ে হেডমিস্ট্রেসের চেয়ে বিজ্ঞাপন। আবেদনকারীদের আইএ বা বিএ পাশ প্রার্থী, মাসিক বেতন ৭০ টাকা ও থাকা খাওয়া ফ্রি। ব্রাহ্মণ ও নিঃসন্তান বিধবা বাঞ্ছনীয় কারণ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে প্রেসিডেন্টের বাড়িতেই থাকতে হবে। এর সঙ্গে এ-ও বলা আছে যে, প্রেসিডেন্টের মেয়েকে পড়াতে হবে।
স্কুলে চাকরির আরেকটা সমস্যা ছিল নিতান্ত কম মাইনে। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আশা ও বাসা গল্পে উল্লেখ আছে রাখীর স্কুলের ‘মাইনের অঙ্কটা কেমন জ্যোতিশুন্য ঠেকতে লাগল চোখে।’ মুক্তি মিত্রের লেখা, যুগান্তর-এ প্রকাশিত ‘সুধার চাকুরি’ গল্পে সুধা কর্মক্ষেত্রে নানা হয়রানি সত্ত্বেও টাইপিস্টের চাকরি ছেড়ে স্কুলে পড়ানোর কথা ভাবতেই পারে না। অত কম মাইনেতে সংসার চলবে না, সেকথা সুধা জানে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় ১৯৫৭ সালে লেখা পরিমল গোস্বামীর ‘স্কুলের মেয়েরা’ উপন্যাসে দুই ছাত্রীর কথোপকথন–
বড়লোকের মেয়ে চপলা বলে, ‘‘ভাল টীচার হ’লে কি আর ভাল শাড়ী পরতে নেই? ভাল গয়না পরতে নেই?” কনক বলল, ‘ওঁদের মাইনেটাও তো দেখতে হবে। টীচারদের তাই দামী শাড়ী গয়না বাড়াবাড়ি মনে হয় আমার কাছে, তা তুমি ভাই যাই মনে কর।’ ‘আরে না না, আজকাল এই রকমই হাবভাব, যেন এটা একটা স্টাইল! যেন এতে কত গৌরব! যেন এঁরা সবাই বিদ্যেসাগর!’ কনক চপলাকে যতই মনে মনে আদর্শ মনে করুক, এই একটি বিষয়ে সে একটু প্রতিবাদ জানাতে বাধ্য হ’ল। তার চোখের সম্মুখে হঠাৎ ভেসে উঠল তার এক দূর-সম্পর্কীয়া দিদির চেহারা। সেই দিদি গরিব, এবং টীচার। কনককে সে কি ভালই না বাসে! চপলার কথায় আজ সে তার সেই দিদির ভিতর দিয়ে বাংলাদেশের সব টীচারেরই চেহারা যেন হঠাৎ দেখতে পেল। তাই সে আর কিছু বলল না। চপলা নিজেই বলতে লাগল, “ও রকম হয় কেন জানিস? ও হচ্ছে একটাকে ঢাকবার জন্য আর একটাকে বাড়িয়ে তোলা। ভাল শাড়ী কেনবার ক্ষমতা নেই, তাই ওটাকে স্টাইল নাম দিলে আর দোষ ধরে কে! আমি হ’লে তো বাবা, মরে যেতাম।” কনক বলল, “তোমাকে কখনো টীচার হতে হবে না, এই যা সুবিধে তোমার, ভাই।’’
কম মাইনে বিষয়ে অবশ্য চুপ করে থাকেননি শিক্ষক সম্প্রদায়। ১৯৫৪ সালে সংগঠিত ভাবে আন্দোলন করেছিলেন তাঁরা মাইনে ও ডিএ বাড়ানোর জন্য। শিক্ষিকারাও অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন এই আন্দোলনে। পথে বসেছিলেন দশটা দিন। সে কথা আমরা জানাব পরের কোনও কিস্তিতে।
তথ্যসূত্র
Gargi Chakravarthy. Coming Out of Partition: Refugee women of Bengal. Tulika Books. 2005
Elizabeth James. An Anglo Indian Tale: The Betrayal of Innocence. Delhi: Originals, 2004.
রেণুকা চোধুরী. পথ পেরিয়ে যখন. শিলালিপি. ২০০১
… পড়ুন চৌকাঠ পেরিয়ে কলামের অন্যান্য পর্ব …
পর্ব ৬: স্বাধীনতার পর মহিলা পুলিশকে কেরানি হিসাবেই দেখা হত, সেই পরিস্থিতি কি আজ বদলেছে?
পর্ব ৫: প্রেম-বিবাহের গড়পড়তা কল্পকাহিনি নয়, বাস্তবের লেডি ডাক্তাররা স্বাধীনতার নিজস্ব ছন্দ পেয়েছিলেন
পর্ব ৪ : নার্সের ছদ্মবেশে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কেও যৌন হেনস্তার কবলে পড়তে হয়েছিল
পর্ব ৩ : উদ্বাস্তু মেয়েদের রোজগারের সুযোগ মিলেছিল টাইপ-শর্টহ্যান্ডের কাজে
পর্ব ২ : পিতৃতন্ত্রের কাঠামোয় কিছু ফাটল নিশ্চয়ই ধরিয়েছিলেন সে যুগের মহিলা টেলিফোন অপারেটররা
পর্ব ১ : দেশভাগের পর ‘চঞ্চল চক্ষুময়’ অফিসে চাকুরিরত মেয়েরা কীভাবে মানিয়ে নিলেন?
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
