
বাংলার নিজস্ব পারিবারিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক গতি, আবহমান বাংলার সাংগীতিক স্রোত থেকেই একমাত্র সাহিত্যের উপাদান নিয়েছিলেন রজনীকান্ত। রবীন্দ্র-সমসাময়িক যে তিন সংগীতকারের নাম একসঙ্গে উচ্চারিত হয়, তাঁদের থেকে এখানেই তিনি একটু আলাদা। ‘পাশ্চাত্য-প্রভাবিত’ বা ‘বিলাতি সুর ভাঙা’ কোনও গান লেখেননি তিনি। জনপ্রিয় ‘থিয়েটারি গান’ লেখেননি। দ্বিজেন্দ্রলাল বা অতুলপ্রসাদ রজনীকান্তের তুলনায় অনেক বেশি নাগরিক পরিমণ্ডলে থেকেছেন, নব্য আধুনিক সংস্কৃতির সংসর্গ করেছেন, আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাও তাঁদের স্পর্শ করেছে বেশি। রজনীকান্তের কাব্যে বা গীতবাণীতে যে পুরাতনের আমেজ, যে সারল্যের আনন্দ, সত্যি কথা বলার যে স্বস্তি, তা তাঁর একান্ত নিজেরই।

১১৫ বছর আগে। ১৯১০ সালের সেপ্টেম্বর। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ওয়ার্ডে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন এক রোগী। গলা ক্যানসারে ক্ষতবিক্ষত, কথা বলা প্রায় বন্ধ, খাওয়া হয়ে গেছে দুর্বিষহ এক কাজ, কিন্তু গান গাইতে চাইছেন তিনি। কাগজ-কলমে কথা বলেন, গানও লেখেন ওতেই, হারমোনিয়াম আনা হয়েছে একখানা, তাতে সুর বাজিয়ে বাজিয়ে সেসব গান শিখিয়ে দেন ছেলেমেয়েকে। ওই অবস্থাতেই। কী করা যাবে! সময় তো ফুরিয়ে আসছে! গানগুলোকে বাঁচাতে তো হবেই! মাত্র ৪৫ বছর বয়স। দুর্বল হাতে লেখা শব্দ আর বাজানো সুর থেকেই ছড়িয়ে পড়ল গানের সৌরভ।
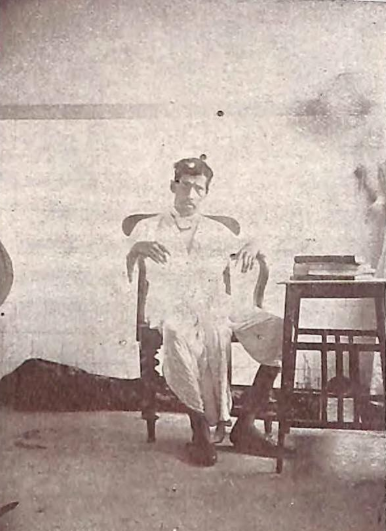
উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলা গানের ধারা আর বাংলা কবিতার ধারা খুব আলাদা করা যায় না। কারণটা অবশ্যই ঐতিহাসিক। প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য সংগীতের নিজস্ব চরিত্রগুলোকে ধারণ করেছিল। সুর, রাগ, তাল, ছন্দ– সবই নির্দেশিত থাকত সেই কাব্যে। চর্যাপদ, যা কিনা বাংলা ভাষানির্মিত সাহিত্যের ‘আদিতম’ নিদর্শন বলে গণ্য, সেগুলো আসলে ‘গীতি’। বড়ু চণ্ডীদাসের লেখার নামে আছে ‘কীর্ত্তন’। কৃত্তিবাস-কাশীরাম লিখেছেন ‘পাঁচালী’। মঙ্গলকাব্য গাওয়া হত সাপ্তাহিক আসরে। পদাবলীসাহিত্য সুর ছাড়া অকল্পনীয়। প্রাচীন এই গোষ্ঠীকেন্দ্রিক রীতিপদ্ধতিগুলো থেকেই তো আধুনিক সাহিত্যের বিবর্তিত ইতিহাস গড়ে উঠছিল। উনিশ শতকের কবিগানের মূলে আছে সুরসংযুক্ত কবিতা। ‘কবি’-‘গান’– এই যুগলসম্মিলনের অনিবার্যতা থেকে ঈশ্বর গুপ্তই কিন্তু বের করে এনেছিলেন কবিতাকে। সুর ব্যতিরেকে তাঁর খণ্ডকবিতা পাঠ করা যায়। পরে গড়ে উঠল আখ্যানকাব্যের নবীন ধারা। নতুন কবিদের লক্ষ্য– পাঠক ছিলেন শিক্ষিত আধুনিক নবীন মানুষেরা, যারা নতুন রুচির পন্থী। কিন্তু খেয়াল করুন, এই ধারা বড়ই ক্ষণস্থায়ী। আখ্যানকাব্যের স্রোত ফেলে পাঠককুল আবার খুঁজে নেয় নতুনতর পথ, যার নাম গীতিকবিতা।
বাংলা সংগীতের ক্ষেত্রে একদিকে ছিল নাট্যগীতি, অন্যদিকে মার্গসংগীত। যাত্রা-লীলা ইত্যাদিতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মতো নাটগীত, অন্যদিকে দরবারি রাগসংগীত। মনে রাখতে হবে, রাগসংগীতের মুখ্য অবলম্বন বাণী নয়, স্বরবিন্যাস, যদিও আমাদের অধিক পরিচিত উত্তর ভারতীয় ঘরানাপ্রধান রাগসংগীতের সঙ্গে দেশীয় রাগসংগীতের বহুল পার্থক্য ছিল। এরই মধ্যে আস্তে আস্তে পাঁচালি-কথকতা জনপ্রিয় আর্ট ফর্ম হিসেবে সমাদর পায়। এ-ও উল্লেখ্য, এই সাংগীতিক সংরূপগুলিতেও কিন্তু রাগসংগীত প্রথম থেকে স্বীকৃত। কিন্তু রাগসংগীতের আধারে মূল উদ্দেশ্য ছিল ওই ‘পদ’ বা ‘কাব্য’-এর উপস্থাপন। অতএব এই নতুন পর্যায়ের গানে রাগ-তালের পাশে জরুরি হয়ে গেল কাব্য। এই ফর্মটিকে যদি বলি ‘কাব্যসংগীত’, তাহলে হয়তো রাগসংগীতের সঙ্গে এর মূল তফাতটা বোঝা যাবে। উনিশ শতকের বাংলা গানে এই সমস্ত ঐতিহ্য মিলিত হল। তার সঙ্গে মিশল আরেক স্রোত। লোকায়ত ঝুমুর-পাঁচালীকে গ্রাস করে আখড়াই-হাফ আখড়াই-খেমটা-আড়খেমটার একটা অর্ধ-নাগরিক রূপ তৈরি হল। উনিশ শতকের পাশ্চাত্য সংস্কৃতির জলবায়ু যে ‘রুচি’র সংজ্ঞার্থ খাড়া করল, তাতে আর ধরানো যাচ্ছিল না এই দেশীয় সাংগীতিক বয়ানকে, লোকসংস্কৃতির স্বকীয় মর্যাদাও সেখানে ছিল না। শহুরে নব্যশিক্ষিত পরিবেশ উন্নাসিক প্রতিক্রিয়াতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে গড়ে নিলেন কিছু শীলিত পিউপাপ্রকোষ্ঠ। তৈরি হল নাগরিক ইন্টেলেকচুয়াল বাংলার কাব্যগীতি। রজনীকান্ত সেনের বেশিরভাগ গানকে আমরা অবশ্যই এই শাখার অন্তর্গত বলে মনে করি, কিন্তু তার মধ্যে তাঁর স্বতন্ত্র একটি অভিব্যক্তির ধরন, একটি বিশেষ কাব্যভাষা ও সাংগীতিক ভঙ্গি খুঁজে পাওয়া যায়।
গানের দু’টি দিক– কথা আর সুর। কথা বা বাণী অংশটিকে আমরা পোয়েট্রি নয়, ‘লিরিক’ বলে চিহ্নিত করি। গীতিকাব্যেরও ইংরেজি প্রতিশব্দ ‘লিরিক’। রজনীকান্তের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের নাম ‘বাণী’। রজনীকান্তের রচনা-সংকলনে ‘বাণী’-র যেসব লেখাকে ‘গান’ বলছি আমরা, তার সব কি সত্যিই গানপদবাচ্য?
‘যে দিন উপজিবে শ্বাসকষ্ট; বায়ু-পিত্ত-কফের নাড়ী হয়ে ক্ষীণ,
হবে নিজ নিজ স্থান-ভ্রষ্ট।
ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া থাকবে না হাত-পায়ে,
রসনা হবে আড়ষ্ট;
যকৃৎ, প্লীহা, হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী,
মূত্রাশয় হবে দুষ্ট…’
একে বড়জোর ডাক্তারি কাব্য-আমোদ বলা যায়, গান ভাবতে গেলেই বরং কষ্ট হয়! অথচ নিচে লেখা আছে বসন্ত মিশ্র– একতালা। সম্ভবত, স্বভাবকবি স্বভাবগায়ক হিসেবে সত্যিই এই বিচিত্র কবিতাগুলিতে সুর-টুর দিয়ে শোনাতেন রজনীকান্ত। এরকম অজস্র পঙ্ক্তির হদিশ পাচ্ছি দ্বিতীয় বই কল্যাণীতেও। জীবদ্দশায় প্রকাশিত তৃতীয় বই ‘অমৃত’ রবীন্দ্রনাথের কণিকার আদলে লেখা ছোট ছোট কবিতারই বই। কিন্তু ‘বাণী’, ‘কল্যাণী’, বা ‘শেষ দান’ আসলে কী? একাধারে গান ও কবিতার সংকলন? ঠিক প্রাগাধুনিক কাব্যেরই মতো?

একথা বুঝতে গেলে একটু অন্য প্রসঙ্গও টানতে হয়। রজনীকান্ত এন্ট্রান্স পাশ করেছেন ১৮৮২-তে। সে বছরেই তাঁর বিবাহ হিরন্ময়ী দেবীর সঙ্গে। ১৮৮৫-তে যখন ফার্স্ট আর্টস দিচ্ছেন রজনীকান্ত, তখনও বাবা, জেঠা জীবিত। পরের বছর দু’জনেই কয়েকদিনের ব্যবধানে মারা যান। আর এ সময় সপরিবার রজনীকান্তের ভরণপোষণ করেন জেঠতুতো দাদা উমাশঙ্কর। ইনি মারা যান ১৮৯৭-এ, ক্যানসার। তার মধ্যে রজনীকান্তের বিএ বিএল পাশ করা হয়ে গেছে, রাজশাহীতে ওকালতির পসার বেড়েছে। ইংরেজি ও সংস্কৃত– দুটোই ভালো জানতেন রজনীকান্ত। স্কুলজীবনে এমনকী, ইংরেজিতে লেখা সাহিত্যের জন্য পুরস্কারও পেয়েছেন। কিন্তু তিনি সাহিত্য রচনা করলেন নিখাদ বাংলাতেই। উপনিবেশের বাসিন্দা হিসেবে এমন কোনও অনর্থক হীনম্মন্যতা কাজ করল না তাঁর মধ্যে, যার জন্য শুধু ইংরেজি কপচে বাংলা ভুলতে হয়, বাংলার শেকড় ভুলতে হয়। একে ‘ব্যতিক্রম’ বলছি না, কিন্তু একজন গ্রামীণ মধ্যবিত্ত মানুষ, যাঁর বিরাট বংশকৌলীন্য বা বিপুল সামাজিক প্রতিপত্তি নেই, তার পক্ষে এই পদক্ষেপ যথেষ্ট সাহসী। বিশ শতকের ট্যাঁশগরু কলোনি সম্বন্ধে ভালোরকমের বিরাগ ছিল রজনীকান্তের। ‘বাণী’ বইয়ের ‘প্রলাপে’ আর ‘বৈয়াকরণ’ উপাধ্যায়ে দ্বিজেন্দ্রলাল-অনুসারী প্রচুর ব্যঙ্গকাব্য তথা ব্যঙ্গগীতি লেখেন তিনি। একটির নমুনা দিচ্ছি–
যেহেতু আমরা ‘হ্যাটে’ ঢাকি টিকি,
সাদা জামা রাখি শরীরে;
আর ‘শ্যান্টপো’ বলি ‘শান্তিপুর’কে,
‘হ্যারি’ বলে ডাকি ‘হরি’রে;
যেহেতু আমরা ছেড়েছি একান্ত,
কীট-দষ্ট বাতুলতা বেদ-বেদান্ত,
(মোদের) অস্থিমজ্জাগত সাহেবী দৃষ্টান্ত
দেখ না অমুক বাঁড়ুয্যে।
পরের বই ‘কল্যাণী’-তেও এমন উদাহরণ সুলভ। নিজে ইংরেজি-প্রভাবিত যুগের মানুষ হলেও মেকি মুখোশের প্রতি বিতৃষ্ণাকেই প্রকাশ করেছেন বেশি। ওকালতি-পেশার উপযুক্ত নব্যসভ্যতার পালিশ আদপেই নেই সেখানে। উল্লেখ্য, এই ‘গান’গুলিরও প্রায় সবেরই নাম আছে। দেওয়ানি হাকিম, ডেপুটি, নব্য বাবু, উঠে পড়ে লাগ্, উকিল– কবিতা হিসেবেই পাঠ্য বলে এই নামকরণ। সুরারোপ ঘটলেও এদের প্রাথমিক পরিচয় কবিতা।
বাংলার নিজস্ব পারিবারিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক গতি, আবহমান বাংলার সাংগীতিক স্রোত থেকেই একমাত্র সাহিত্যের উপাদান নিয়েছিলেন রজনীকান্ত। রবীন্দ্র-সমসাময়িক যে তিন সংগীতকারের নাম একসঙ্গে উচ্চারিত হয়, তাঁদের থেকে এখানেই তিনি একটু আলাদা। ‘পাশ্চাত্য-প্রভাবিত’ বা ‘বিলাতি সুর ভাঙা’ কোনও গান লেখেননি তিনি। জনপ্রিয় ‘থিয়েটারি গান’ লেখেননি। দ্বিজেন্দ্রলাল বা অতুলপ্রসাদ রজনীকান্তের তুলনায় অনেক বেশি নাগরিক পরিমণ্ডলে থেকেছেন, নব্য আধুনিক সংস্কৃতির সংসর্গ করেছেন, আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাও তাঁদের স্পর্শ করেছে বেশি। রজনীকান্তের কাব্যে বা গীতবাণীতে যে পুরাতনের আমেজ, যে সারল্যের আনন্দ, সত্যি কথা বলার যে স্বস্তি, তা তাঁর একান্ত নিজেরই।
তুমি আমার অন্তস্তলের খবর জান,
ভাব্তে প্রভু, আমি লাজে মরি!…
কিংবা,
তারে যে ‘প্রভু’ বলিস, ‘দাস’ হলি তুই কবে?
তুই মেটে গর্বে ফেটে মরিস্, তোর বিভবের গৌরবে!…
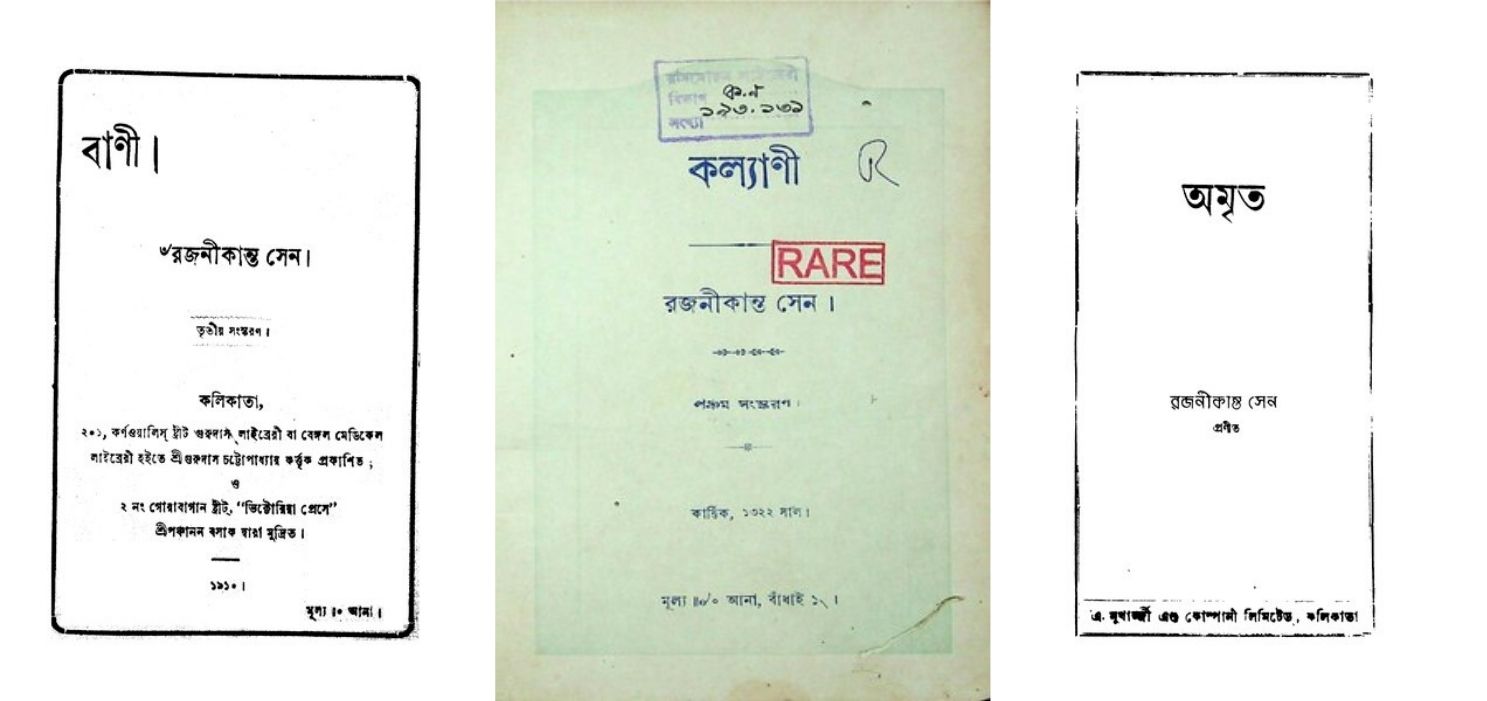
সে যুগের বিমিশ্র ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক চলনের মধ্যেও খুব স্বাভাবিক সহজ মনোভঙ্গিতে রজনীকান্তের কবিতা ও গান একজন ‘তুমি’-কে সম্বোধন করেছে। সেই ‘তুমি’ কোনও এক দয়াল, বা প্রভু, বা মা। যাঁর কাছে শেষ পর্যন্ত আশ্রয় নেওয়া যায়। ‘তপ্ত মলিন চিত’ নিয়ে এই দগ্ধভূমি থেকে চলে যাবেন কোনও এক পরম শান্তিনীড়ে, এ রজনীকান্তের আজীবনলালিত স্বপ্ন। ১৮৯০-এ ‘আশালতা’ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথম কবিতায় লিখেছিলেন–
কি এক রাক্ষসী মায়া, নয়নমোহন-রূপে,
ভুলায়ে আনিয়ে মোরে ফেলে গেল মহাকূপে!
শ্রমে অবসন্ন কায় কন্টক বিঁধিছে তায়,
বৃশ্চিক দংশিছে, অনিবার!
মাত্র ২৫ বছর বয়সে তাঁর এই অনুভব। আরও ১২ বছর পরে প্রথম বই বের করলেন রজনীকান্ত। সেখানেও এভাবেই এল সংসারের কণ্টকজ্বালা, এলো অসংখ্য ‘হে’, অজস্র ‘গো’-র আকুতি।
আর কতদিন ভবে থাকিব মা?
পথ চেয়ে কত ডাকিব মা?
তুমি দেখা তো দিলে না, কোলে তো নিলেনা,
কি আশে পরাণ রাখিব মা?
রজনীকান্তের কাছে একথা স্পষ্ট ছিল যে, তিনি বাসনার পাঁকে আকণ্ঠ ডুবে আছেন। তিনি পাতকী, মোহগ্রস্ত, পতিত, ক্ষুদ্র, দীন, তুচ্ছ। ধুলোমাখা ছেলেকে পায়ে ঠেলে দেবেন প্রভু, তাই অনবরত স্বীকারোক্তি আর অনন্ত অভিমান। এই সারল্যের সুরে, ভৈরবী-ইমন-বেহাগ-খাম্বাজ-ভূপালীর এই আরোহণ-অবরোহণে রবীন্দ্রনাথ মনে পড়ে না। বিপদে রক্ষা না করার আবেদন যে জানাতে পারে, তার মতো ঋজুতা নয়, রজনীকান্তের গানে আছে এক ভীত আপন্ন মানুষ, যে কাঁদতে চায়, কথা বলতে চায়, উদ্ধার পেতে চায়। এর সঙ্গে অনেক বেশি সম্বন্ধ বৈষ্ণব-শাক্ত গানের ভক্তির। পান্নালাল ভট্টাচার্যের শান্তমধুর কণ্ঠে যখন শুনেছিলাম সেই বিখ্যাত গান–
আমি সকল কাজের পাই হে সময়,
তোমারে ডাকিতে পাইনে,
আমি চাহি দারা-সুত-সুখসম্মিলন,
তব সঙ্গসুখ চাইনে।
তখন একে রামপ্রসাদ-পদ বলেই ভেবে ফেলেছিলাম। অনেক পরে জেনেছি, এটি ১৯০৫-এ প্রকাশিত ‘কল্যাণী’ বইয়ের গান। আদপেই এ গান শ্যামাসংগীত নয়, গানের কোথাও ‘মা’ সম্বোধনও নেই। রবীন্দ্রনাথের ‘তোমার কথা হেথা কেহ তো বলে না’-র সুরছকে গাওয়ার কথা এই গান। দীর্ঘযুগ ধরে একে শ্যামাসংগীত বলে মনে হওয়ার নেপথ্যে আমাদের অনভিজ্ঞ পাঠ ও শ্রবণ যেমন দায়ী, তেমনই রজনীকান্তকাব্যের পুরাতনী রূপ ও রংও অবশ্যই দায়ী। প্রাগাধুনিক কাব্যের মতোই রজনীকান্ত বহু কবিতার শেষে ভণিতা ব্যবহার করতেন। কল্যাণীর ‘আর কেন’ গানের শেষে লেখেন ‘কান্ত বলে, সব ফেলে দিয়ে তুলে নে কম্বল লোটা’; ‘আনন্দময়ী’ বইয়ের এক গানের শেষে লেখেন– ‘কান্ত কয় ভাই নগরবাসী, তোদের সপ্তমীতে পৌর্ণমাসী/ দশমীতে অমাবস্যা তোদের পঞ্জিকায়।’
………………………
রজনীকান্তের কাছে একথা স্পষ্ট ছিল যে, তিনি বাসনার পাঁকে আকণ্ঠ ডুবে আছেন। তিনি পাতকী, মোহগ্রস্ত, পতিত, ক্ষুদ্র, দীন, তুচ্ছ। ধুলোমাখা ছেলেকে পায়ে ঠেলে দেবেন প্রভু, তাই অনবরত স্বীকারোক্তি আর অনন্ত অভিমান। এই সারল্যের সুরে, ভৈরবী-ইমন-বেহাগ-খাম্বাজ-ভূপালীর এই আরোহণ-অবরোহণে রবীন্দ্রনাথ মনে পড়ে না। বিপদে রক্ষা না করার আবেদন যে জানাতে পারে, তার মতো ঋজুতা নয়, রজনীকান্তের গানে আছে এক ভীত আপন্ন মানুষ, যে কাঁদতে চায়, কথা বলতে চায়, উদ্ধার পেতে চায়।
………………………
প্রাচীনকে আঁকড়ে থাকার এই ক্ষমতা দুর্লভ। যে বিশ্বাস অর্জন করেছিলেন রজনীকান্ত, বহু বেদনায়, বহু ক্লেশে, তা অবিশ্বাস্য। জীবনের শেষ প্রান্তে, মৃত্যুযন্ত্রণার ভয়াবহতার মধ্যে মনে করেছিলেন, তাঁর দয়াল তাঁকে ব্যাধির আগুনে পুড়িয়ে আরও শুদ্ধ করে তুলছেন। ঈশ্বরকে কি আর অমনিই পাওয়া যায়? আনন্দময়ের কাছে পৌঁছতে গেলে সবার আগে নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। সেই প্রস্তুতিপথেই আছেন তিনি–
সেই আনন্দ-মন্দির মাঝে,
আনন্দ-সঙ্গীত বাজে,
নাহি ব্যথা, অশ্রু, বিষাদ,
(সে) সদানন্দ নিকেতনে।
দেখ্ কেমন তার ভালবাসা,
মিটায় আনন্দ-পিপাসা,
আগে, না পোড়ালে খাদ রয়ে যায়,–
সে আনন্দ পাবে কেমনে?

আজ থেকে ১৬০ বছর আগের ২৬ জুলাই পাবনার ভাঙ্গাবাড়িতে জন্মেছিলেন রজনীকান্ত। শ্রাবণপ্রকৃতির উচ্ছ্বাস তাঁর সৃষ্টিতে এল না, তার বদলে এল শ্রাবণের মেঘক্লান্ত আলো, ভিজে নরম মাটি। সেখানে দুর্দম আবেগ নেই, আছে বেপরোয়া বিশ্বাস।
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
