
স্বদেশি আন্দোলনের ছায়ায় বেড়ে উঠেছেন সরলা, ঠাকুরবাড়ির রাজনৈতিক পরিমণ্ডল তাঁকে গড়ে তুলেছে। মা স্বর্ণকুমারীর সঙ্গে মিলে ‘ভারতী’ পত্রিকা সম্পাদনা করছেন, নিজে স্বদেশি গান রচনা ও সুরারোপণ করছেন, মামা রবীন্দ্রনাথের গানে সুর পর্যন্ত দিচ্ছেন (এ কী লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ)। ঠাকুরবাড়ির পারিবারিক ঘেরাটোপের ভিতর থেকে শিল্প-সাহিত্য-রাজনীতি চর্চার ঐতিহ্য ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের রয়েছে, সেই পথেই হাঁটতে পারতেন সরলা। কিন্তু আলাদা হয়ে গেলেন দুই জরুরি মাপকাঠিতে।

ঠাকুরবাড়ির ছাদে-অলিন্দে রঙিন ছায়া হয়ে হেঁটে বেড়াতেন তাঁরা। জুঁই ফুলের সুবাস, পানের রেকাবি আর নকশা তোলা সুজনি দিয়ে সাজানো নান্দনিক ঘরোয়া আসরে হয়ে উঠতেন নবীন কবির নতুন কবিতার প্রেরণা। স্বামী-শ্বশুরের সস্নেহ প্রণোদনায় পোশাকে আনতেন প্রগতিশীল বৈচিত্র, কখনও বা ঘোড়ায় চড়ে হাওয়া খেতে বেরিয়ে সভ্য সমাজে হইচই ফেলে দিতেন। ঘরোয়া পত্রিকায় বেরত তাঁদের লেখা, ঘরোয়া নাটকে মঞ্চাভিনয়ের সুযোগ মিলত, মিলত প্রশংসাও। বিশ্ববরেণ্য কবির প্রতিভাবলয়ে তাঁরা কখনও ‘মিউজ’, কখনও পদাঙ্ক-অনুসারী, কখনও-বা তাঁর পরম্পরাকে এগিয়ে নিয়ে চলার কারিগর।
বাংলার ভাবনাজগতে ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের নিয়ে আলোচনা এই কয়েকটি নির্দিষ্ট ছকের মধ্যেই ঘোরাফেরা করে সাধারণত। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, কাদম্বরী দেবী, স্বর্ণকুমারী, প্রতিভা, ইন্দিরা থেকে রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী মৃণালিনী বা স্নেহের পুত্রবধূ প্রতিমা– প্রত্যেককেই মোটামুটি একটু টেনে একটু ছেড়ে এই ছকের ভিতর পুরে ফেলা যায়। খুব সহজ, সুন্দর ছক। এখানে হয় তাঁরা আক্ষরিকই দেবী– কবির মানসপ্রতিমা, অনুপ্রেরণাস্বরূপ (কাদম্বরী, জ্ঞানদানন্দিনী)। নয়তো বাড়ির দুর্বার প্রতিভাবান পুরুষদের উৎসাহ ও আশীর্বাদ নিয়ে শিল্প-সাহিত্য জগতে নিজেদের স্বাক্ষর রাখছেন (স্বর্ণকুমারী, প্রজ্ঞাসুন্দরী)। কখনও-বা তাঁদের শিল্পচিন্তার সুযোগ্য ধারক-বাহক হয়ে উঠছেন (প্রতিমা দেবী)। আর এইসব ঘিরেই যে কাজ তাঁদের সবার জন্য অব্যাহত থাকছে, তা হল পরিবারের খ্যাতিমান, প্রতিভাবান পুরুষদের সেবা ও সহায়তা, নিজের স্ত্রীধনের বিনিময়েও (মৃণালিনী দেবী)।
……………………………..
তাঁর স্বদেশি রাজনীতি ঘোষিতভাবেই চরমপন্থী ধারার, যা বারবার বিব্রত করছে রবীন্দ্রনাথকে। ভারতীর পাতায় স্বদেশচেতনা ও আত্মাভিমান জাগিয়ে তোলা রক্ত গরম করা একের পর এক লেখা লিখে চলেছেন তিনি, তাঁর সরাসরি প্রেরণায় তৈরি হচ্ছে ব্যায়াম সমিতি, যুব বিপ্লবী দল, যাদের হাতে লাল সুতো বেঁধে স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষা দিচ্ছেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভ্রাতৃত্যবোধের ধারণার থেকে এই রাজনীতির সুর অনেক বেশি চড়া, অনেক বেশি উত্তেজক– যার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ সরাসরি কলম পর্যন্ত ধরছেন (সরলার ‘বিদেশি ঘুষি দেশি কিল’ প্রবন্ধের উত্তরে রবীন্দ্রনাথের ‘ঘুষাঘুষি’)। ভাগ্নিকে আবেগপ্রবণ, চরমপন্থী হিসেবে দেখেছেন তিনি, ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে তাঁকে ‘মিশনারি’-দের সঙ্গে তুলনা করেছেন।
……………………………..
এই শান্ত-সুন্দর সরোবরে সরলা দেবী চৌধুরাণী যেন হাত ফসকে এসে পড়া বেয়াড়া ঢিল। তাঁকে নিয়ে কী করা যায়, তা খোদ রবীন্দ্রনাথই ভেবে উঠতে পারেননি, তো উত্তরকালের রবীন্দ্রগবেষকমণ্ডলীকে আর কী দোষ দেব?

স্বদেশি আন্দোলনের ছায়ায় বেড়ে উঠেছেন সরলা, ঠাকুরবাড়ির রাজনৈতিক পরিমণ্ডল তাঁকে গড়ে তুলেছে। মা স্বর্ণকুমারীর সঙ্গে মিলে ‘ভারতী’ পত্রিকা সম্পাদনা করছেন, নিজে স্বদেশি গান রচনা ও সুরারোপণ করছেন, মামা রবীন্দ্রনাথের গানে সুর পর্যন্ত দিচ্ছেন (এ কী লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ)। ঠাকুরবাড়ির পারিবারিক ঘেরাটোপের ভিতর থেকে শিল্প-সাহিত্য-রাজনীতি চর্চার ঐতিহ্য ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের রয়েছে, সেই পথেই হাঁটতে পারতেন সরলা। কিন্তু আলাদা হয়ে গেলেন দুই জরুরি মাপকাঠিতে।
প্রথমত, তাঁর স্বদেশি রাজনীতি ঘোষিতভাবেই চরমপন্থী ধারার, যা বারবার বিব্রত করছে রবীন্দ্রনাথকে। ভারতীর পাতায় স্বদেশচেতনা ও আত্মাভিমান জাগিয়ে তোলা রক্ত গরম করা একের পর এক লেখা লিখে চলেছেন তিনি, তাঁর সরাসরি প্রেরণায় তৈরি হচ্ছে ব্যায়াম সমিতি, যুব বিপ্লবী দল, যাদের হাতে লাল সুতো বেঁধে স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষা দিচ্ছেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভ্রাতৃত্যবোধের ধারণার থেকে এই রাজনীতির সুর অনেক বেশি চড়া, অনেক বেশি উত্তেজক– যার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ সরাসরি কলম পর্যন্ত ধরছেন (সরলার ‘বিদেশি ঘুষি দেশি কিল’ প্রবন্ধের উত্তরে রবীন্দ্রনাথের ‘ঘুষাঘুষি’)। ভাগনিকে আবেগপ্রবণ, চরমপন্থী হিসেবে দেখেছেন তিনি, ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে তাঁকে ‘মিশনারি’-দের সঙ্গে তুলনা করেছেন। পারিবারিক রাজনৈতিক চেতনার গণ্ডি থেকে যাত্রা শুরু করেও তাঁর এই অন্যস্বর গ্রহণের প্রবণতা তাঁকে আলাদা করেছিল। আর সেই আলাদা হয়ে যাওয়ার একাকিত্ব বাড়িয়েছিল তাঁর ভিন্নস্বরের ধরনটি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তথা রবীন্দ্রানুরাগী মহলের অস্বস্তি।
সেই অস্বস্তির শিকড় হয়তো নিহিত দ্বিতীয় মাপকাঠিটিতে। সরলার ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক অবস্থান ঠাকুরবাড়ির পরিচিত নারীত্বের খোপের অনেকটা বাইরে দিয়ে চলেছে। পরিবারনির্দিষ্ট গণ্ডির ভিতরে নিজের রাজনৈতিক বোধকে বেঁধে রাখেননি বলেই নয়। পরিবারে প্রথম একা একা চাকরি নিয়ে মহীশূরে পড়াতে চলে গিয়েছেন। রাজনৈতিক কার্যকলাপে নেপথ্যচারিণী ‘অনুপ্রেরণা’ হিসেবে নয়, সরাসরি নেত্রী হিসেবে লোকসমক্ষে এসে দাঁড়িয়েছেন বারবার। এবং সোজাসুজি স্পষ্টভাবে রাজনীতিতে নারীর নিজের জায়গার নির্মাণ করার কথা বলেছেন, সেই জায়গা তৈরি করেও দেখিয়েছেন।
ভারতের নারীবাদী আন্দোলন তাঁকে তেমন মনে রাখেনি, কিন্তু ভারতের প্রথম সর্বভারতীয় নারী সংগঠন ‘ভারতীয় স্ত্রী মহামণ্ডল’ তৈরি করেন তিনিই। নানা রঙের রাজনৈতিক আন্দোলনের ভিতর থেকে নারীর নিজস্বরে তৈরি করা নিজস্ব রাজনৈতিক সক্রিয়তার পক্ষে সরাসরি সওয়াল সেই প্রথম। ১৯১০ সালে সেই সংগঠন প্রতিষ্ঠার ভাষণে একটা বেশ চমকে দেওয়ার মতো কথা বলেছিলেন তিনি: ‘দ্য উইমেন্স কজ ইজ দ্য মেন্স কজ।’ নারীর লড়াই পুরুষদের লড়াইও বটে। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যখন আমরা আলোচনা করছি পিতৃতন্ত্র কীভাবে পুরুষদেরও খোপে বেঁধে রাখছে, পিতৃতন্ত্রবিরোধী লড়াই কীভাবে বৃহত্তর উপনিবেশ-বিরোধী তথা পুঁজিবাদবিরোধী লড়াইয়ের সঙ্গে একসূত্রে বাঁধা, তখন শতাধিক বছর আগের এই উচ্চারণ ভাবতে বাধ্য করে বটে।
এটুকুতেই যদি থেমে যেতেন সরলা, তবে হয়তো তাঁকে ঠাকুরবাড়ির চেনা দেবীত্বের খোপে আবারও চেপেচুপে ঢুকিয়ে যেওয়া যেত কোনওমতে। নারী অধিকারের লড়াইয়ে পুরুষকে অংশীদার হতে আহ্বান করছেন তিনি, পুরুষের সক্রিয়তা দাবি করছেন। তখনও পর্যন্ত ভারতে নারী অধিকার আন্দোলনের মুখ তো পুরুষরাই– রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার থেকে তাঁর মামা রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত। সেই পুরুষালি সক্রিয়তার ছায়াসঙ্গী হয়েও যদি তিনি থেকে যেতে পারতেন!
কিন্তু সে তাঁর দ্বারা হয়নি। ১৯৩১ সালে কলকাতায় মহিলা কংগ্রেসের অধিবেশনে একদম চাঁচাছোলা ভাষায় নারী রাজনীতিতে পুরুষের পৃষ্ঠপোষকতার বাস্তব মেলে ধরছেন সরলা। বলছেন, আইনভঙ্গের আন্দোলনের সময় মেয়েদের ডাক পড়ে দল ভারি করতে, কিন্তু আইন গঠনের কাজে মেয়েদের ডাকা হয় না। তাঁর পরিবারের মেয়েদের বিপ্লব যেখানে পোশাকের প্রগতিশীলতা, ব্যক্তিগত শিল্পসাহিত্য চর্চার স্বাধীনতা ইত্যাদির আঙিনায় ঘোরাফেরা করেছে, সেখানে নারী অধিকার সুনিশ্চিত করতে সরাসরি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাবি তুলছেন সরলা। পিতৃদত্ত সম্পত্তি ও স্বামীর উপার্জনে মেয়ে, বোন ও স্ত্রীদের অধিকার, সন্তানের ওপর সমানাধিকার, পুরসভা-আইনসভায় নারী প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত করা– এইসব দাবি তুলছেন তিনি।
আবার আরও পরে, সভা-সমিতিতে আসন সংরক্ষণের বাস্তব নিয়েও তিক্ততা ঢাকছেন না তিনি। কাউন্সিল ইত্যাদিতে মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত আসন নিয়ে কাড়াকাড়ির প্রেক্ষিতে নিজের অসমাপ্ত আত্মজীবনী ‘জীবনের ঝরাপাতা’-তে চরম খেদের সঙ্গে লিখছেন, ‘‘…মেয়েরা যদি পুরুষ দেবতাকেই বলে বসেন, ‘তোমার সিংহাসনটাই আমায় ছেড়ে দাও না ভাই’– তা হলেই বিপদ, তা হলেই পুরুষের পৌরুষ বেরিয়ে পড়ে চোখ রাঙা করে বলে, ‘কভি নেই’।” আপাতভাবে নারী অধিকার সুনিশ্চিতকরণের একটা হাতিয়ার কীভাবে নারীতে-নারীতে বিভেদ তৈরির কাজে লাগছে, সেটা তাঁর চোখ এড়াচ্ছে না। নারীচেতনা ও রাজনৈতিক চেতনা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রূপ বদলাচ্ছে তাঁর, আরও শাণিত হচ্ছে তাঁর বিশ্লেষণ।
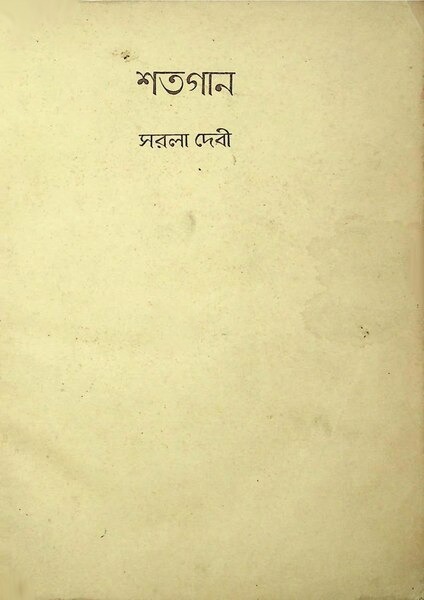
আর এইভাবেই তাঁর সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নারীর একটা মূলগত তফাত তৈরি হয়ে যাচ্ছে– যে তফাত একশো বছর পার করা আধুনিক ভারতীয় নারীবাদে আজও বিদ্যমান। একদিকে পিতৃতন্ত্রনির্দিষ্ট, বর্ণ-শ্রেণি-নির্দিষ্ট ঘেরাটোপের ভিতর থেকে গড়ে ওঠা উচ্চবিত্ত-উচ্চবর্ণ নারীবাদ– যা পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোটি বজায় রেখেই তার ভিতরে সুবিধা চায় কিছু মূলত। কাঠামোর ভিতরেই নারীর জন্য নির্দিষ্ট আছে কিছু কর্তব্য, কিছু আচরণ– যা পালনের শর্তে নারীর ‘মর্যাদা’ ও ‘অধিকার’ স্বীকৃত হয়। রবীন্দ্রনাথের নিজের নারীচেতনাও এই ধাঁচা ধরে চলে; উপন্যাসের নায়িকার চরিত্রায়ণ (‘শেষের কবিতা’-র লাবণ্য, ‘গোরা’-র সুচরিতা) থেকে ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের আলাপচারিতা, সর্বত্রই নারীর কল্যাণী মূর্তিকেই আদর্শ ধরেছেন তিনি। তাঁর নারী আদর্শ অবিচারের প্রতিবাদ করেছে, কিন্তু কখনও পুরুষের ‘সিংহাসন’ ধরে টান দেয়নি। আর তাঁর নারীভাবনার সূত্র ধরেই অতএব ঠাকুরবাড়ির নারীমহল নিয়ে প্রায় প্রতিটি আলোচনাতেই সে-বাড়ির নারীদের সামাজিক-রাজনৈতিক কার্যকলাপের পাশাপাশি নাছোড়বান্দা হয়ে বসে থাকে তাঁদের সেবাপরায়ণতা, তাঁদের সাংসারিক গুণপনা, রন্ধনপটুত্বের কাহিনি।
তার উল্টোদিকে থেকে যায় সরলার অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ভিত্তিমূলে নাড়া দেওয়া নারীবাদ। ‘স্ত্রীর পত্র’-র মৃণালের মতো সংসারত্যাগিনী প্রতিবাদী তিনি নন, সংসারের ভিতরে সমানাধিকার কড়ায়-গন্ডায় বুঝে নেওয়ার কথা বলছেন তিনি। নারী ক্ষমতায়ন করতে গেলে পুরুষকে যে আগে ক্ষমতার মৌরসিপাট্টা থেকে সরতে হবে, ক্ষমতাকাঠামোর ভিতরে নারী-পুরুষের আলাদা আলাদা পূর্বনির্দিষ্ট ভূমিকা বজায় রেখে যে আদৌ নারীর ক্ষমতায়ন সম্ভব নয়, হাল আমলের এই নারীবাদী ভাবনার ছায়া ধরা পড়ে তাঁর লেখায়। কাঠামোর ভিতরে চেপেচুপে জায়গা করে না নিয়ে কাঠামোটিকেই ঢেলে সাজার কথা বলে তাঁর লেখা। বলাই বাহুল্য, এই দ্বিতীয় ধরনটির গ্রহণযোগ্যতা সেকালেও ছিল না, একালেও তেমন নেই।
যৌবন থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত সরলার সমস্ত জীবনটা যেন এক মোড়ক উন্মোচনের খেলা। ঔপনিবেশিক রাজধানীর প্রসিদ্ধ উচ্চবিত্ত-উচ্চবর্ণ পরিবারের শিক্ষিত কন্যা পারিবারিক প্রগতিশীলতার উপহার কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করে না নিয়ে সাহস করছেন সেই উপহারের নির্দিষ্ট ঘেরাটোপের বাইরে পা বাড়ানোর। আর সেই যে বাইরে একবার তাঁর পা পড়ছে, তা আর কখনও পিছনে ঢুকে আসছে না। শেষ জীবনে এসে লড়াই করে ক্লান্ত সরলা যখন স্বেচ্ছা-নির্বাসন নিয়েছেন জনজীবন থেকে, রবীন্দ্রনাথ তথা ঠাকুরবাড়ির রাজনৈতিক চেতনা এবং নারীভাবনা– দুই থেকেই তাঁর দূরত্ব বহু যোজনের।
ঠাকুরবাড়ির নারীদের নিয়ে উত্তরকালের শত কৌতূহলী চর্চার ভিড়ে তাই তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায় না। দেবীত্বের মোড়ককে নিজের জীবন দিয়ে তিনি বর্জন করেছেন বারবার, তাই দেবীত্বের বিড়ম্বনাও তাঁর ইতিহাসকে ভারাক্রান্ত করেনি– যেমনটা হয়তো-বা করেছে কাদম্বরী বা জ্ঞানদানন্দিনীর ক্ষেত্রে। সরলা দেবী চৌধুরাণীকে নিয়ে এত বিস্মৃতির মাঝে সেটুকুই হয়তো আশার কথা।
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
