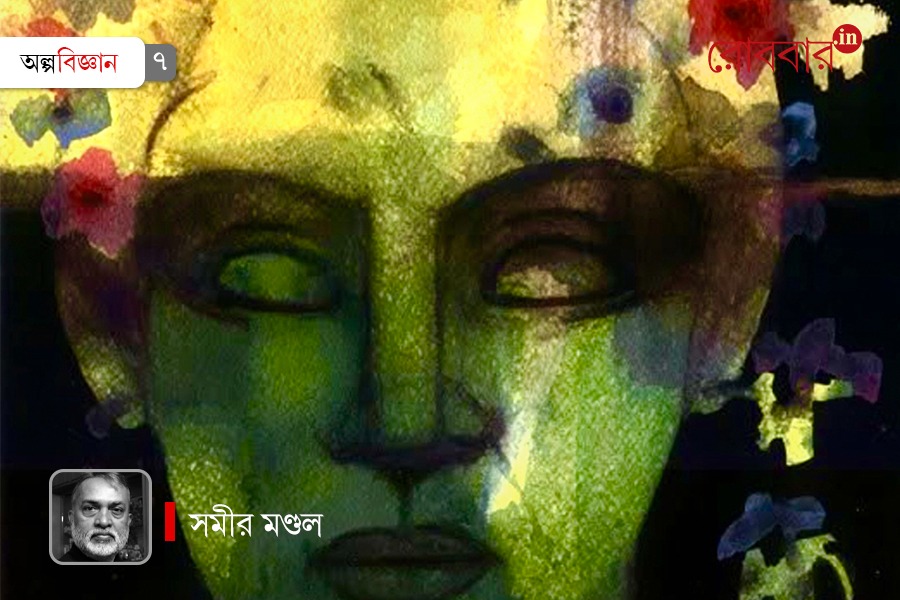
রং চলে যায়। কিন্তু ফিরিয়েও আনা যায় রং। পৃথিবীর রঙ্গ এমনই। ছবি, যা প্রায়শই হয়ে ওঠে বেরং, সেই রং ফিরিয়ে আনা যায় কোন পথে? ছবির ইতিহাস ফিরিয়ে আনা, সেই রেস্টোরেশন বা পুনরুদ্ধার কীভাবে হয়? এদেশে এখনও সে কাজের পরিসর রয়েছে? প্রযুক্তি?

৭.
আগের পর্বে বলেছিলাম পৃথিবীর রং বদলে যাচ্ছে। বলেছিলাম, পরের পর্বে রং বদলের আরও অনেক গল্প আছে। লক্ষ করছি, অনলাইনে ধারাবাহিক লেখার আরও একটা মজা হল, পাঠকের প্রতিক্রিয়া খুব তাড়াতাড়ি জানা যায়। কিছু কিছু মন্তব্য এমনই যে, পাঠক যেন বিষয়টার সঙ্গে বা ঘটনার সঙ্গে মিশে গিয়ে নিজেও রচনায় অংশগ্রহণ করছেন। কিছু মন্তব্য আবার এত সুন্দর এবং যুক্তিপূর্ণ, তা থেকে আমিও শিখছি নতুন করে। আগের পর্বের পাঠকদের দু’-একটা মন্তব্য এখানে শোনাই।
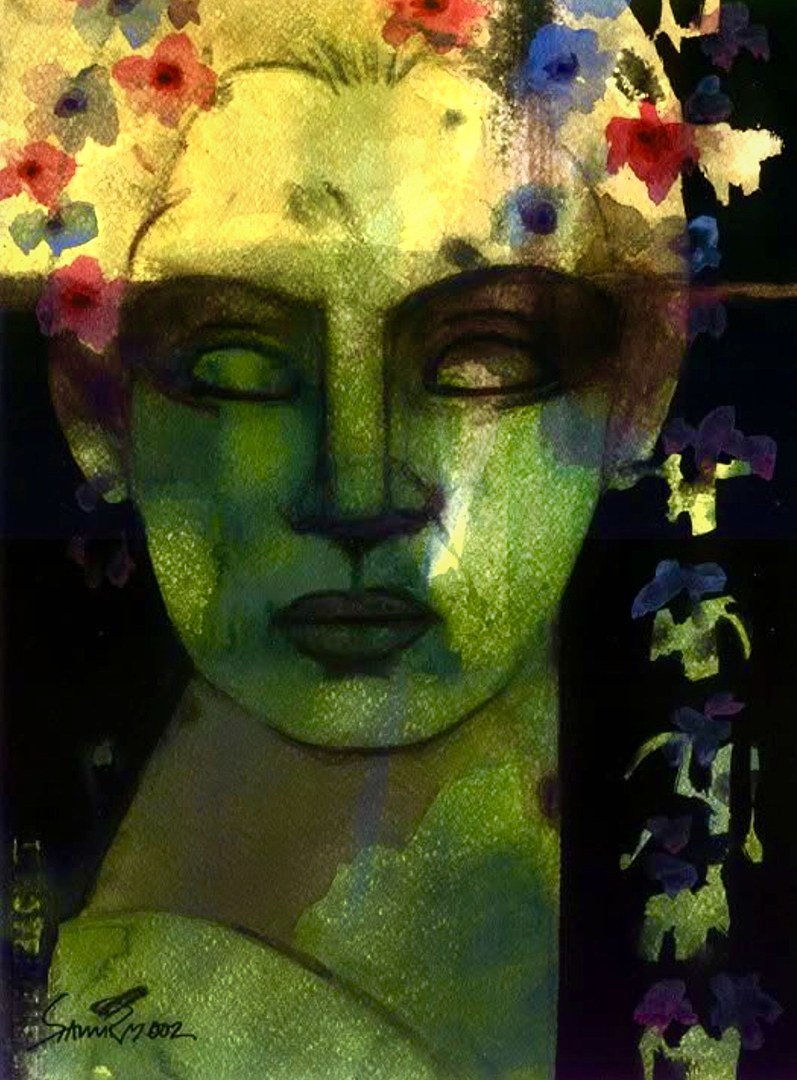
দক্ষিণ কলকাতা থেকে সুলেখক সিদ্ধার্থ মজুমদার বলছেন, ‘‘চমৎকার লেখা। কেন চমৎকার, দু’এক কথায় বলি তাহলে।… কী ভার্সেটাইল এই লেখা! প্রথমে বুঝতে পারছিলাম না, লেখাটির অভিমুখ নিয়ে। পৃথিবীর রং ও রূপ নিয়ে বলতে বলতে ধাঁধা, কুইজ, মুকুল শর্মা, মানচিত্রের রঙে চার না পাঁচ– গল্পবলিয়ে যাদুকরের মতন পাঠককে হাত ধরে ধরে যেন এইসব কিছু ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন ‘অল্পবিজ্ঞানের গল্পশিল্পী’! তারপর, গল্প গড়াতে গড়াতে পৃথিবীর রঙে এসে মিশে গেল কখন। এল, রঙের বৈচিত্র… জীব বৈচিত্র। শেষে পরিবেশ দূষণ , ইকোলজি, বাস্তুতন্ত্র… সতর্কবার্তা। অথচ উপদেশের মত জ্ঞানগর্ভ গুরুগম্ভীর কথা নয় একটিও। সবই কথায় কথায়… গল্প বুনতে বুনতে।’’
চিত্রশিল্পী, সঞ্জয় ব্যানার্জির মন্তব্য, ‘লেখা এবং ছবি যতটা অনবদ্য, পৃথিবীর পরিবেশ পরিবর্তন ততটাই চিন্তাজনক, কিন্ত সাধারণ মানুষের এতে ভূমিকা খুব সামান্য।’
জয়ন্ত হালদার, রামপুরহাট থেকে লিখছেন, ‘বিশ্বচরাচরের এত অব্যক্ত বেদনা কি শুধু রংবিহীন ধূসরতায় সীমাবদ্ধ থাকবে? আমরা কি রঙের মর্ম বুঝব না! এত আছে বলেই কি এত অপচয়?’
এখানে বেশিরভাগ মন্তব্যে লক্ষ করছি পাঠক ভীত, চিন্তিত। তবে এটা আমার একটা একপেশে গল্প। রংবদলের গল্প মানে সবসময় ভয়ের, তা নয়। রঙের বদল মানে পরিবর্তন। কখনও অসুস্থতার, কখনও সতর্কতার আবার কখনও কখনও সেটা রূপ বদলের, আনন্দের এবং খুশির।
গল্প শুনতে আমরা প্রত্য়েকেই ভালোবাসি। সেখানে ছোট-বড় খুব একটা ভেদাভেদ থাকে না। এখানে ছোটদের জন্য একটা গল্প প্রথমে বলি, তারপর বড়দের গল্প।
আমার ছেলে ও মেয়ে– শাপলা, ঝিনুক তখন খুব ছোট। মাঝে মাঝে আমি ওদের ঘুমপাড়ানি গল্প শোনাতাম। রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর আমি ওদের বলতাম, চল, একটা গল্প বলি। সঙ্গে সঙ্গে ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বন্ধ করে নড়েচড়ে শুয়ে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে একেবারে তৈরি হয়ে যেত গল্প শোনার জন্য।
লক্ষ করেছি, ছোটবেলায় গল্প শোনার একটা প্রবণতা, মানে সরল ইচ্ছা সব বাচ্চাদেরই থাকে। এখন মনে হয় বড়দেরও আছে। এক একটা গল্প কতবার যে বলেছি, তার ঠিক নেই। ওদের কোনও আপত্তি নেই। হয়তো একই গল্প শুনতে শুনতে নিজের মনে কল্পনায় অন্যরকম ভাবে ছবি তৈরি করে ওরা! একটা বাঘের গল্প বলতাম প্রায়ই। বাঘটার ডাকনাম, ‘বাঘু’। যখনই বলেছি ওই গল্পটা, তখনই ওরা একই রকম মন দিয়ে শুনেছে, কেন জানি না। গল্পটা আপনারাও শুনুন।
বাঘু, বয়সে কিন্তু বেশি বড় নয়, তবে ওর স্বাস্থ্যটা ভালো বলে অল্পবয়সেই একটা বিশাল চেহারা। সারাদিন খেলে বেড়ায় যেখানে খুশি। জঙ্গলে, কাদা মাটিতে, ধুলোয়। চান করে না সবদিন, মাঝে মাঝে করে। একদিন একটা পুকুরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল সে। চকচকে আয়নার মতো জল। সেখানে নিজের ছায়া জলের মধ্যে দেখে চমকে গেল বাঘু! দেখল, তার গায়ের সব রং উঠে গেছে। ঝকঝকে হলুদ তার ওপরে কুচকুচে কালো ডোরাকাটা ডিজাইন, সেগুলো কেমন একরঙা হয়ে গিয়েছে। কেমন যেন ধুলোর মতো ধূসর। খুব মন খারাপ হয়ে গেল বাঘুর। দু’-তিনদিন সে আর ভালো করে খেলাধুলো করতে পারছে না। তার শরীরের রং উঠে গিয়ে তাকে কেমন যেন একটা দেখাচ্ছে।
একদিন মাথায় এল, এটা বোধহয় একটা ভীষণ বড় রকম অসুখ। ডাক্তার দেখানো দরকার। জঙ্গলের কাছাকাছি লোকবসতি যেখানে, সেখানে ছিল এক ডাক্তারবাবুর বাড়ি। একদিন রাত্রিবেলা চুপিচুপি ওই ডাক্তারবাবুর বাড়িতে গেল বাঘু। থাবা দিয়ে দরজায় থপথপ করে আওয়াজ করতে লাগল। ডাক্তারবাবু দরজা খুলেই চমকে গেলেন। বিশাল বড় সাইজের একটা বাঘ। কিন্তু ডাক্তারবাবু ভয় পেলেন না। জঙ্গলের পাশে থাকতে থাকতে তিনি খুব সাহসী। বললেন, ‘কী চাই?’ বাঘু হাতজোড় করে বলল, ‘ডাক্তারবাবু, আমার ভীষণ অসুখ করেছে।’ ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ‘কী অসুখ?’ বাঘু বলল, ‘আমার গায়ের সব রং উঠে গেছে।’ ডাক্তারবাবু দেখে বললেন, ‘একটু দাঁড়াও আমি তোমায় ওষুধ দিচ্ছি’, বলে উনি দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ভেতরে চলে গেলেন। একটু পরে ফিরে এসে দরজা খুলে একটা চৌকো মতো জিনিস বাঘুর হাতে দিয়ে বললেন, ‘এইটা ওষুধ। তবে এটা কিন্তু খেয়ে ফেলো না, এটা হচ্ছে গায়ে লাগানোর ওষুধ। কাল সকালে চানের আগে এটা সারা গায়ে ভালো করে মেখে চান করবে।’
যথারীতি পরদিন সকালে বাঘু সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই পুকুরে নেমে গেল চান করতে এবং চৌকো জিনিসটা সারা গায়ে মেখে চান করল। ভিজে সারা গায়ে আবার মাখল, আবার চান করল। তারপর পুকুরের ওপরে উঠে বসে রইল রোদে গা শুকোতে। যখন শুকিয়ে গেল তখন গা-টা ঝেড়ে সে লোমগুলোকে ছাড়াছাড়া করল। জলের ধারে গিয়ে নিজের ছায়ায় দেখতে চাইল রংয়ের কোনও বদল হয়েছে কি না।
দেখে তো অবাক! ডাক্তারের ওষুধ ভীষণ ভালো কাজ করেছে, সারা গায়ে পরিষ্কার রং। ঝকঝকে হলুদ আর তার ওপরে কালো কালো ডোরা কাটা।
এই পর্যন্ত বলে আমি জিজ্ঞেস করতাম, ডাক্তারবাবু আসলে কী ওষুধ দিয়েছিল জানিস তো? ওরা সমবেত কণ্ঠে বলত, ‘সাবান’। গল্পটা আমি কোথায় পেয়েছিলাম আমার এখন আর ঠিক মনে নেই, তবে অনেক বাচ্চার কাছে এই গল্পটা প্রয়োগ করেছিলাম।
গল্পটা ভালো না? ছোটদের এই গল্প থেকে বড়দের গল্পে যাওয়ার আগে এর দুটো বিষয়কে আমি হাইলাইট করি– ১. রং যে বদলে যায় তার কিন্তু পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থাও আছে।
২. এই পুনরুদ্ধারের কাজ করার জন্য কোনও আজগুবি আয়োজন অথবা মন্ত্র-তন্ত্র নয়, অসুখ নিরাময়ের জন্য একজন সঠিক ডাক্তারের প্রয়োজন।
রঙের গোড়ার কথা হল, আলো। মানে, আলো ছাড়া রঙের কোনও অস্তিত্বই নেই। আলো মানে শক্তি। যখন সে শক্তি, বস্তু, বাতাস, জল কিংবা আমাদের শরীরের ওপরও ক্রিয়া করে, তখনই শুরু হয় রং বদলের গল্প। ক্ষয়ে যাওয়া, ঘষে যাওয়া, চটে যাওয়া বা ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া কিংবা কালচে অন্ধকারাচ্ছন্ন– সবই আসলে পদার্থের আর আলোর এক অন্তহীন কারসাজি।
রং আসলে আলোর প্রতিফলনের ফল। বস্তু যে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো প্রতিফলিত করে সেটাই আমরা সেই বস্তুর রং হিসেবে দেখি। আবার আলো যে রঙের প্রধান উৎস, সেই আলোই রং নষ্টের শত্রু। সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি কোনও বস্তুর অণুর গঠন ভেঙে দেয়। এই প্রক্রিয়াকে বলে, ফোটোডিগ্রেডেশন। আলোর দ্বারা রঙের অণু-ভাঙন। জীবনদায়ী যে অক্সিজেন, সেও রঙের সঙ্গে বিক্রিয়া করে তার রসায়ন বদলে দেয়।
তবে আগেই বলেছি, রং ফিকে হয়ে যাওয়া মানে শেষ নয়। অনেক সময় রং পরিবর্তন মানে নতুন কিছুর শুরু। বেশি ভালো করে বুঝতে পারি ঋতু পরিবর্তনের সময়। অনেক গাছের পাতা সবুজ থেকে হলুদ, হলুদ থেকে কমলা, লাল হয়ে বাদামি রঙে পরিবর্তিত হয়। প্রকৃতির এই প্রক্রিয়ায় আমরা খুশি হই, পরিবর্তন উপভোগ করি। এটা কোনও ক্ষয় নয়, জৈবচক্রের এক স্বাভাবিক পরিণতি।

আমরা যারা ছবি আঁকি তাদের কাছে রং হল বন্ধু, আমাদের আত্মীয়। আবার এই আত্মীয়কে নিয়ে ভোগান্তিরও শেষ নেই। পেশাদার শিল্পী হিসেবে আমাকেও ভুগতে হয়েছে। আজগুবি এক খবর ছড়িয়ে আছে ছবির বাজারে। জলরঙের ছবির রং নাকি টেকে না। খুব তাড়াতাড়ি ফিকে হয়ে যায়, তাই ছবির দামও কম। অদ্ভুত! তবে কাগজের ওপর জলরং হোক আর ক্যানভাসের ওপরে তেলরং, যত্নের অভাবে আমাদের ছবির আরও নানা রকমের অসুখ-বিসুখ হয়।
পৃথিবীর তাবড় তাবড় মিউজিয়ামগুলোতে রেস্টোরেশন, মানে ছবির রঙের পুনরুদ্ধার এবং কনজারভেশন, মানে শিল্পকর্মের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ নিয়ম করে হচ্ছে। নেট ঘাঁটলে অবাক করা নানা গল্প, ছবি ইত্যাদি সবাই দেখতে পাবেন। কিন্তু আমাদের একেবারে হাতের কাছেও যে এরকম কিছু কাজের ব্যবস্থা আছে, সেই খবরটা সবার কাছে নেই। সেই গল্পটাই বরং করব আজ।

সত্যি কথা বলতে কী, তেলরঙের ক্ষেত্রে যা হোক আছে, পেপার রেস্টোরেশন মানে কাগজের ছবির চিকিৎসার ডাক্তার আমাদের দেশে প্রায় নেই বললেই হয়। আমাদের দেশে শিল্পকর্মের অসুস্থতা যত বেড়েছে বা বাড়ছে দিনকে দিন, সেই তুলনায় ডাক্তারের সংখ্যা কিন্তু নিতান্তই কম, হাতে গোনা।
আমাদের দেশে একেবারেই বড় বড় কয়েকটি মিউজিয়ামে এই ব্যবস্থা আছে, যার মধ্যে সবচেয়ে পুরনো, দিল্লির ‘ন্যাশনাল গ্যালারি অফ মডার্ন আর্ট’। নিজস্ব বিশাল শিল্প ভাণ্ডারের রক্ষণাবেক্ষণ এবং চিকিৎসা ছাড়াও এখানে বিষয়টি শেখানোরও ব্যবস্থা রয়েছে। এইখানে এক সময় ইন্দিরা গান্ধীর পুত্রবধূ সনিয়া গান্ধী, রেস্টোরেশনের ছাত্রী ছিলেন। শিক্ষক, বাঙালি শিল্পী, সুকান্ত বসু।

সুকান্ত বসু-ই প্রথম রেস্টোরেশন ডিপার্টমেন্টে ১৯৫৯ সালে অফিশিয়ালি জয়েন করেন এবং ওঁর অবসর গ্রহণের ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত একটানা ‘ন্যাশনাল গ্যালারি অফ মডার্ন আর্ট’-এ ছিলেন। শিল্পী সুকান্ত বসুর সেকালের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা ছিলেন সোমনাথ হোড়, দিলীপ দাশগুপ্ত, বীরেন দে এবং বম্বের গায়তোন্ডে, তায়েব মেহতার মতো শিল্পীরা। বিদেশে রেস্টোরেশন এবং কনজারভেশন নিয়ে শিক্ষালাভ করেছেন। দেশে বহু বিখ্যাত শিল্পীর শিল্পকর্মের রেস্টোরেশন করেছেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, অমৃতা শেরগিল, যিনি ভারতের জাতীয় শিল্পী হিসেবে স্বীকৃত নবরত্নের একজন। নবরত্নের অন্যরা– রাজা রবি বর্মা, রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নিকোলাস রৈরিখ, নন্দলাল বসু, যামিনী রায় ও শৈলজ মুখার্জী।

এবার আসি আমাদের কলকাতার গল্পে। কলকাতার শিল্পকর্মের রেস্টোরেশনের অভিজ্ঞতা আর অনুভূতির গল্প শুনব দিবাকরের মুখে। আমাদের অনুজ শিল্পীবন্ধু দিবাকর কর্মকার এ-বিষয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল-এ কর্মরত একজন একনিষ্ঠ রেস্টোরার। কাগজের ছবি, তেলরং, মিনিয়েচার পেইন্টিং, মিউরাল বা ভিত্তিচিত্র ইত্যাদির স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে ওর ঝুলিতে ২৫ বছরের অভিজ্ঞতা। কলকাতার অন্যান্য মিউজিয়ামে রেস্টোরেশন বিভাগ থাকলেও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, এই ব্যাপারে খুবই বিখ্যাত। আর হবে না-ই বা কেন, সারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মের সংগ্রহশালা যে এটা। সেটা ভেবে আপনারা সহজেই আন্দাজ করতে পারেন, তাদের রক্ষণাবেক্ষণের কতটা দায়দায়িত্ব।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল বললেই একটা সম্ভ্রম, একটা স্মৃতির জায়গা ছাড়াও ব্যাপক সাইজের সংগ্রহশালা। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, স্মৃতিসৌধ নিজেই এক বিশাল শিল্পকর্ম। এত বিশাল এলাকা জুড়ে, মানে ৬৪ একর জমির ওপরে এত আশ্চর্য সুন্দর এই স্মৃতিসৌধ জগতে বিরল। আরও একটা কারণে আমাদের শিহরন জাগায়, গর্বিত হই ভেবে, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের নির্মাণের কাজ করেছিলেন ‘মার্টিন অ্যান্ড কোম্পানি’র স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি। স্যর বীরেন মুখার্জির পিতা এবং আমাদের অতি পরিচিত প্রিয়জন, লেডি রানু মুখার্জির শ্বশুরমশাই।
ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে আরও একজন, আমাদের কলেজেরই সিনিয়র দাদা, অরুণ ঘোষ, দীর্ঘদিন রেস্টোরেশনের কাজ করেছেন। নামী পত্র-পত্রিকায় শিল্প সমালোচকের কাজও করতেন অরুণদা। পরবর্তীকালে দিবাকর কর্মকারই বিশেষ দায়দায়িত্ব নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ রেস্টোরেশনের কাজকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

দিবাকরের মুখে বিভিন্ন কাজের পদ্ধতির বিস্তারিত বর্ণনা শুনে অভিভূত হয়েছি। আমাদের এখানে উপযুক্ত সরঞ্জামের এবং আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব। সেগুলোকে বাদ দিয়ে কীভাবে একটা বিশাল কাজ, আন্তর্জাতিক মানের কাজ করছে ওরা, শুনলে অবাক হবেন।
এখানে স্বল্প পরিসরে দুটো ছবির রেস্টোরেশনের কথা বলব। একটা, ‘দিল্লি দরবার’ অন্যটা, ‘জয়পুর শোভাযাত্রা’। দুটো ছবিই আমরা সাতের দশকে, ছাত্রজীবনে দেখেছি। পরবর্তীকালে দীর্ঘদিন দর্শকরা আর দেখতে পাননি। অবাক হয়েছিলাম শুধুমাত্র সাইজের বিশালত্ব আর কাজের দক্ষতা দেখে। ছবির অন্তরালের কোনও তথ্য জানা ছিল না সেই সময়।
দিল্লি দরবার। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দ্বিতীয় বৃহত্তম ছবি। একখানা ক্যানভাস ১১ ফুট বাই ১৭ ফুট। শিল্পকর্মটির রং এবং শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে যায়। তৈলচিত্রটি পরিষ্কার করে, অন্ধকারাচ্ছন্ন চেহারা কাটিয়ে আবার আগের মতো রঙে ফিরে যাওয়ার বা পুনরুদ্ধার কাজের একটা কমিটি তৈরি হয়। সেই কমিটিতে ইউরোপের বিশেষজ্ঞ ছাড়াও আমাদের দেশ থেকে ছিলেন সুকান্ত বসু, অরুণ ঘোষ এবং অন্য মিউজিয়ামের আরও অনেকে। দীর্ঘদিনের এই কাজটা শুরু হয় অরুণদার তত্ত্বাবধানে। ওঁর অবসরের পর দায়িত্বে আসে দিবাকর।
এই ধরনের কাজ করার বেশ কয়েকটা ধাপ থাকে। প্রথমত, একেবারে ওপরের ধুলো-ময়লা পরিষ্কার করা। দ্বিতীয় ধাপে আসে ভার্নিশের স্তর। যেখানে ছবির কাজের শেষে দেওয়া হয় একটা স্বচ্ছ কঠিন স্তর। যেমন আমরা ছবিতে কাচ দিয়ে বাঁধাই করি, তেমনই তৈলচিত্রে ছবি শেষ হয়ে যাওয়ার পর ভার্নিশের স্তর, যেটা ছবিকে দেয় ঔজ্জ্বল্য এবং ধুলো, ধোঁয়া থেকে সুরক্ষা করে। রেস্টোরেশনের কাজে ভার্নিশের স্তরটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ওই স্বচ্ছ স্তরই আমাদের চোখের ক্যাটারাক্টের মতো ঘোলাটে হয়ে ছবির রংকে দেখতে দেয় না। ভাগ্যি ভালো, তাতে ছবির রং সুরক্ষিত থাকে। সেটিকে সরিয়ে রঙের স্তরে পৌঁছনো যায়।

স্টুডিওতে যথাযথ টেবিল নেই যেটাতে ছবিকে শুইয়ে রেখে কাজ করা হবে। মেঝেতে কাঠের একটা তক্তপোশের মতো অল্প উঁচু টেবিল বানানো হল। দ্বিতীয় বিপত্তি হল, অত বড় ছবিটা শুয়ে আছে তার পাশ থেকে যতদূর হাত যায় তাতে সমস্ত ছবিটাতে কাজ করা অর্থাৎ, ছবির মাঝখানে কাজ করার খুব অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে। এখানে একটা কথা বলে রাখি, এই পরিষ্কার করার কাজ বা যা কিছু অন্য কাজ কিন্তু চটজলদি বড় ব্রাশ দিয়ে, জোরালো হাওয়া মেরে কিংবা কাপড় দিয়ে করা হয় না। খুব যত্ন করে, অনেক সময় নিয়ে, ছোট ছোট অংশ পরিষ্কার করতে হয়। একেবারে মিলিমিটার মিলিমিটার করে এগতে হয়।
বড় ছবির ওপরে বসে কাজ করা যায় না বলে বানানো হল ছবির চেয়ে বড় লম্বা বেঞ্চির মতো একটা বসার জায়গা। বেঁটে পায়ার সেই বস্তুটা তৈরি হল একটা ব্যবহৃত বাঁশের মই, পরিত্যক্ত কিছু কাঠের টুকরো, ফোম এবং আরও কিছু দিয়ে। সেই বেঞ্চির ওপরে বসে নিচের ছবিতে কাজ করা। একেবারে ‘বাংলা স্টাইল’। কাহিনি অনেক লম্বা। নষ্ট কাঠামো, ক্যানভাস এবং ছবির রঙের পুনরুদ্ধার মিলিয়ে দারুণ ঝুঁকি! শেষ পর্যন্ত দীর্ঘদিনের পরিশ্রমে সফল হয় সেই কাজ। দিবাকরদের চরম তৃপ্তি, সাফল্যর দারুণ সংবাদ নিয়ে তৈরি হয় প্রামাণ্যচিত্র, যা দেশ-বিদেশে যথেষ্ট প্রশংসিত।
এবারে আসি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের সবচেয়ে বড় ছবিটার কথায়। ‘জয়পুর শোভাযাত্রা’। ১৯ বাই ২৪ ফুটের একখানা ক্যানভাসে আঁকা তৈলচিত্রটি সারা পৃথিবীর বৃহত্তম তৈলচিত্রের দু’-একটার মধ্যে একটা। আমাদের হাতের নাগালেই এই বিশেষ শিল্পকর্ম রয়েছে ভাবলেই গা শিরশির করে না? বিশাল মাপের এই ছবিটি যখন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে আসে সেই দিন থেকে আজ অবধি দেওয়ালে একই জায়গায় লাগানো আছে। এত বড় এবং ভারী ছবিকে নড়াচড়া করে, তার সম্পূর্ণ রেস্টোরেশন প্রায় অসম্ভব! দেওয়ালে ডিসপ্লেতে রেখেই যা করার করা। অক্লান্ত পরিশ্রমে সেই বিশাল তৈলচিত্রের ওপরে ১০০ বছরের ধুলোর স্তর পরিষ্কার করতেই কেটে গিয়েছে বহুদিন। ফিরে এসেছে ছবির অনেকটাই আসল রং।

রাশিয়ান চিত্রশিল্পী, ভ্যাসিলি ভেরেশচাগিনের আঁকা, ১৮৭৬ সালের জয়পুর প্রেক্ষাপটের এই চিত্রকর্মটি প্রিন্স অফ ওয়েলসের ভারতীয় উপমহাদেশ ভ্রমণের একটি মুহূর্তকে মূর্ত করে তুলেছে। খুবই গুরুত্বপূর্ণ, পুরনো নগর জয়পুরের মধ্য দিয়ে এক রাজকীয় রাষ্ট্রীয় সফর। মানুষজন, হাতি-ঘোড়া ইত্যাদি নিয়ে বিশাল আয়োজন। বাড়িঘরের স্থাপত্য এবং রাস্তাঘাট, পোশাক-আশাক, অস্ত্র-শস্ত্র আর যাঁরা প্রতিনিধিত্ব করছেন ওই যাত্রায় সেইসব মানুষের প্রতিকৃতি। সবই নিখুঁত ভাবে আঁকা হয়েছে ছবিখানিতে।
জীবনের শেষ দশকে ইউরোপ এবং আমেরিকায় ৩০টিরও বেশি একক প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করলেও তুলনামূলকভাবে অজ্ঞাত, ভেরেশচাগিন ছিলেন একজন সৈনিক, ভ্রমণকারী, লেখক এবং প্রতিভাবান শিল্পী। ওঁর বেশিরভাগ কাজ মস্কো এবং সেন্ট পিটার্সবার্গের মিউজিয়ামে সংরক্ষিত।
বর্তমানে ‘জয়পুর শোভাযাত্রা’ আপনাদের দেখার জন্য রাখা আছে কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের, রয়্যাল গ্যালারিতে। চলুন, প্রিন্স অফ ওয়েলসের রাজকীয় শোভাযাত্রার ছবিটা এই যাত্রা দেখে আসি, পৃথিবীর এক অবিস্মরণীয় শিল্পের সামনে শিহরিত হতে, ইতিহাসের সাক্ষী হতে।
রেস্টোরেশনের ছবিঋণ: দিবাকর কর্মকার
…পড়ুন অল্পবিজ্ঞান-এর অন্যান্য পর্ব…
পর্ব ৬: বিসর্জনের মতোই একটু একটু করে ফিকে হয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর রং ও রূপ
পর্ব ৫: জীবন আসলে ক্যালাইডোস্কোপ, সামান্য ঘোরালেই বদলে যায় একঘেয়ে নকশা
পর্ব ৪: কুকুরেরই জাত ভাই, অথচ শিয়াল সম্পর্কে আমরা কতটুকু জানি?
পর্ব ৩: অন্ধকারে অল্প আলোর মায়া, ফুরয় না কোনওদিন!
পর্ব ২: বজ্রবিদ্যুৎ ভর্তি আকাশে ঘুড়ি উড়িয়ে আমাদের চিরকালের নায়ক হয়ে আছেন বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
