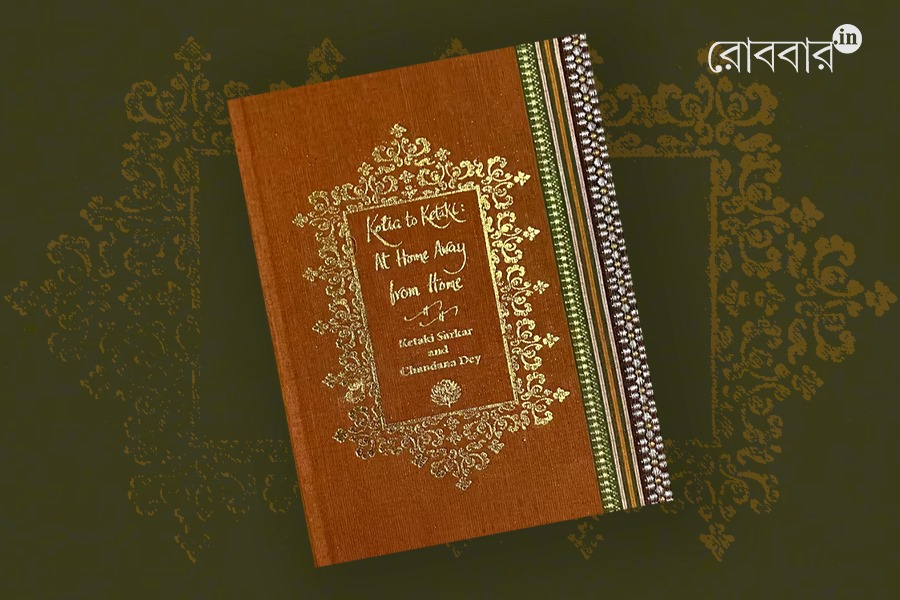
পরাধীন কলকাতার অস্থিরতা ছেড়ে শান্তিনিকেতনকেই নিজের জায়গা হিসেবে পছন্দ করে নেন কেতকী। সেখানে ইন্দিরা গান্ধীকে (তখন নেহেরু) ফ্রেঞ্চ ভাষা ঝালাতে সাহায্য করেন, কৃষ্ণ কৃপালিনীকে রাশিয়ান শেখান। রোজ সকালে গুরুদেবকে কবিতা পড়ে শোনান। ওঁর কাছে নতুন নাম পান কেতকী। ছেলেমেয়েকে রবীন্দ্রনাথের আদেশ মেনে শান্তিনিকেতন পাঠ ভবনে ভর্তি করেন। ওখানেই বাড়ি বানিয়ে শেষ জীবনটা কাটান নিতাইয়ের সঙ্গে।

কেতকী সরকার এবং চন্দনা দে-র বই ‘Kotia to Ketaki: At Home Away from Home’ শিক্ষিত, অভিজাত, উচ্চমহলের এক স্মৃতি কাহিনি। ১৯০৭-এর মস্কোতে কোটিয়া জোনাস উরফ কেতকী সরকারের জন্ম এক রুশ ইহুদি পরিবারে। ১৯৩০-এ তিনি বাঙালি ডাক্তার নিতাই সরকারকে বিয়ে করে পরবর্তীকালে কলকাতা চলে আসেন। শেষ জীবন কাটান শান্তিনিকেতনে।
ইউরোপ এবং ভারতের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক মুহূর্তগুলোর সাক্ষী কোটিয়া– প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, রুশ বিপ্লব, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বাংলার মন্বন্তর ও ভারতের স্বাধীনতার লড়াই। সেই সঙ্গে অন্তঃস্রোতে চলেছে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইউরোপে ইহুদি হওয়ার অস্থিরতা। তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হয়তো তাঁর বন্ধুত্ব এবং মেলামেশা পরাধীন শান্তিনিকেতনের সাংস্কৃতিক অভিজাত মহলের সঙ্গে, যেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর নামকরণ করেছিলেন কেতকী।
বইটার প্রথম ভাগ কেতকীর লেখা চিঠি তাঁর দুই সন্তানকে, মায়া এবং নন্দন। সাবলীল ভাষায় নিজের জীবনের গল্প লিখে গেছেন চিঠির আকারে। বাবা ডেভিড জোনাস বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী একজন উকিল। তাঁর ছিল চার ভগবান– শেক্সপিয়র, নিৎশে, কার্ল মার্কস এবং ওয়াগনার। মা ভারাভারা জোনাস মস্কো ইউনিভার্সিটিতে ডাক্তারি পড়েছিলেন, যাতে গুপ্ত বিপ্লবের কাজে যুক্ত হতে পারেন। তবে বিয়ের পর টালমাটাল রাজনৈতিক ও পারিবারিক পরিস্থিতিতে সংসার সামলাতে মন দেন।
চার ছেলেমেয়ের তৃতীয় জন কোটিয়া। যখন তাঁর তিন বছর বয়স, ডেভিড স্বপরিবারে সুইজারল্যান্ডের এক বড় খামারবাড়িতে বসবাস শুরু করেন। এখানে পাঠকের পরিচয় হয় জোনাস পরিবারের বাকি সদস্যের সঙ্গে। প্রত্যেকেই বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের গুরুত্বপূর্ণ পদে। কেউ প্যালেস্তাইনের প্রথম ইহুদি ঔপনিবেশিক বসতি স্থাপনকারীদের একজন এবং আধুনিক হিব্রু ভাষার সৃষ্টিকর্তা, তো কেউ আমেরিকাতে টমাস এডিসনের অ্যাসিস্ট্যান্ট। কেউ ডাক্তার, কেউ ভাষাবিদ, কেউ কলা ও সংগীতের সঙ্গে যুক্ত। শিক্ষা, সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ এক পারিবারিক মহলে বেড়ে ওঠা কোটিয়ার, যেখানে সকালে পড়াশোনা ও রাতে বড়দের মুখে কমিউনিজম, সমাজতন্ত্র, বিপ্লবের আলোচনা শোনা। পরে আবার মস্কোতে থাকাকালীন শহরের ঐতিহাসিক বলশোই অপেরা হাউসে ডেভিডের নামে একটা বক্স বছরভর রিজার্ভ করা থাকত। সপ্তাহে দু’বার পাশ্চাত্য শাস্ত্রীয় সংগীত শুনতে যেতেন স্বপরিবারে।
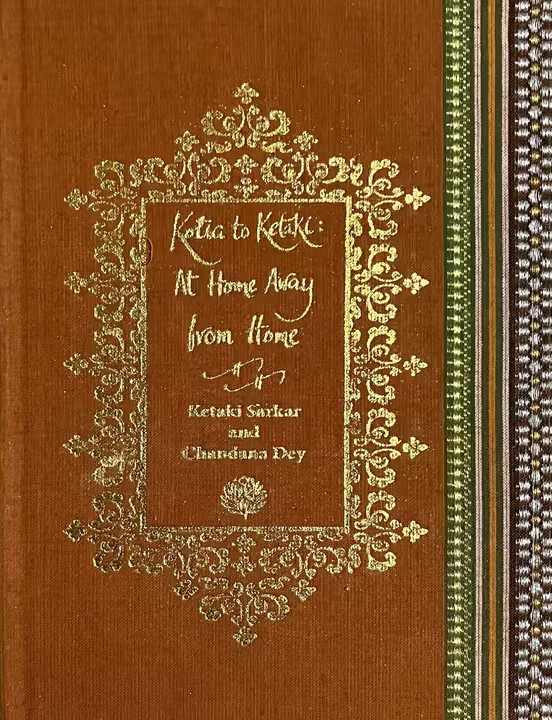
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বেশি প্রভাব পড়েনি মস্কোতে। ১৯১৭-এর রুশ বিপ্লবের সময় ১০ বছরের কোটিয়া দেখেন তাঁর বাবা মায়ের উচ্ছ্বাস। তবে সমস্যা শুরু হয় শীঘ্রই। খাবারের টানাপোড়েন। ডেভিডের এক মক্কেল নিজের গ্রামের বাড়িতে তাঁদের থাকার জায়গা করে দেন। ভারাভারা চার ছেলেমেয়ে নিয়ে ছোট্ট একটা ‘ইসবা’-তে (রুশ কুঁড়েঘর) গ্রাম্য জীবন শুরু করেন। এইখানে লেখিকার চিঠি পড়ে মন জুড়িয়ে যায়। রাশিয়ার গ্রাম, সেখানকার জীবন ও পোশাকের এক অনন্য বর্ণনা পায় পাঠক। বিপ্লব পরবর্তী অস্থিরতার ছোঁয়া নেই এই গ্রামে। সকাল থেকে চাষের জমিতে খেটে, খড় বানিয়ে খাবার জোগাড় করা, সন্ধেবেলায় রুশ লোকগীতি শোনা। কিন্তু শান্তি ক্ষণস্থায়ী। আবার ফিরতে হয় মস্কোতে। সেখান থেকে ছোটবেলার বাড়ি এবং স্মৃতি পিছনে ফেলে যাত্রা লিথুয়ানিয়ায়। পিসির বাড়িতে আশ্রয়।
অনেক ঘোরা, বাড়ি বদলের পর স্থায়ী জায়গা হয় জেনেভা। এখানেই ১৯২৯-এ ইউনিভার্সিটিতে কোটিয়ার আলাপ কলকাতা থেকে ডাক্তারি পড়তে আসা নিতাই দে সরকারের সঙ্গে। আজকেও যেমন আমরা প্রথম আলাপেই কাউকে মনের মানুষ ভেবে নিই, প্রায় ১০০ বছর আগেও আবেগগুলো একইরকম ছিল। প্রথম আলাপে এক ঘণ্টা কথা বলেই বন্ধুর কাছে কোটিয়া ঘোষণা করেন, এই ছেলেই নাকি তাঁর জীবনসঙ্গী হবে। ১৯৩০-এ তা হলও। বিয়ে করে সুইজারল্যান্ডের এক গ্রামে সংসার শুরু তাঁদের। নিতাই সেখানে ডাক্তারি করতেন। কোটিয়ার চিঠিতে সেই ডাক্তারি এবং হাস্যকর কিছু কাহিনির মাধ্যমে সুইজারল্যান্ডের এক অন্যদিক উঠে আসে পাঠকের কাছে। বিশেষ করে সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্যজ্ঞানের অভাব, যা আমরা সাধারণত পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে সমার্থক করি না।
সুইস সরকার বিদেশি বলে নিতাইকে সুইজারল্যান্ডে প্র্যাকটিস বন্ধ করার আদেশ দেওয়ার ফলে কোটিয়াকে ১৯৩৪-এ আবার চেনা মানুষ, জায়গা, দেশ ছেড়ে পাড়ি দিতে হয় সুদূর কলকাতাতে। এক বছরের মেয়ে নিয়ে পরাধীন ভারতে এসে পড়েন যেখানে বহু জায়গায় তাঁর প্রবেশের অনুমতি থাকলেও, স্বামীর ছিল না।
নিতাই সরকারের পরিবার বিভিন্নভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ওঁর মামা তুষারকান্তি ঘোষ, অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক। তাছাড়া তাঁদের বন্ধু ও চেনা বৃত্তে সেই সময়ের বিখ্যাত ব্যক্তিদের নাম উল্লেখ করে গিয়েছেন কোটিয়া। অনিল চন্দ, রানি মহালানবিশ, নন্দলাল বসু, বিনোদবিহারি মুখার্জি এবং আরও অনেকে।
পরাধীন কলকাতার অস্থিরতা ছেড়ে শান্তিনিকেতনকেই নিজের জায়গা হিসেবে পছন্দ করে নেন। সেখানে ইন্দিরা গান্ধীকে (তখন নেহেরু) ফ্রেঞ্চ ভাষা ঝালাতে সাহায্য করেন, কৃষ্ণ কৃপালিনীকে রাশিয়ান শেখান। রোজ সকালে গুরুদেবকে কবিতা পড়ে শোনান। ওঁর কাছে নতুন নাম পান কেতকী। ছেলেমেয়েকে রবীন্দ্রনাথের আদেশ মেনে শান্তিনিকেতন পাঠভবনে ভর্তি করেন। ওখানেই বাড়ি বানিয়ে শেষ জীবনটা কাটান নিতাইয়ের সঙ্গে।
কোটিয়ার এক সমৃদ্ধ স্মৃতি পাই এই বইয়ে– এক রুশ ইহুদি মহিলা, যার জীবন দুটো মহাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। পাঠক হয়তো আশা করবেন এরকম রাজনৈতিক তাৎপর্যপূর্ণ সময়ের কোনও প্রতিফলন উঠে আসবে তাঁর লেখায়। কিন্তু শেষে এসে আশাহত হতে হয়। চূড়ান্ত কমিউনিস্ট রাজনৈতিক চর্চার পরিবারে বেড়ে ওঠা সত্ত্বেও কোটিয়ার লেখাতে, ভাবনাচিন্তাতে সেই আভাস পাওয়া যায়নি। উনি উল্লেখ করেছেন সব রাজনৈতিক ঘটনা। কিন্তু গভীরে গিয়ে নিজের জীবনে বা চেতনায় সেই ঘটনাগুলোর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কথা তাঁর লেখায় নেই। তবে সেটা আসাও মুশকিল। ছোট থেকে যখনই কোনও সমস্যা দেখা দিয়েছে, খুব তাড়াতাড়ি সেগুলোর সমাধানও হয়েছে।
বিপ্লবের পর খাবার নেই, গ্রামে বাড়ি, চাষের ব্যবস্থা পাওয়া গিয়েছে। দেশ ছাড়ার পর বড়লোক আত্মীয়ের বাড়ি ঠাঁই পাওয়া গিয়েছে। ভারতে এসে একই গল্প। অভিজাত পরিবারে বিয়ের সূত্রে যখনই কলকাতায় সমস্যা দেখা দিয়েছে, শান্তিনিকেতনে জায়গা পেয়েছেন। ১৯৪৬ সালে কলকাতায় ভয়াবহ দাঙ্গা। গঙ্গার রং লাল। তখন এক ডাক্তার বন্ধুর বাড়িতে, তৎকালীন Galstaun Mansion-এ (এখন নিজাম প্যালেস) নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছেন।
শান্তিনিকেতনে যেসময় ছিলেন তখন বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী ওখানে থাকতেন, কাজ করতেন। শিল্প, সংগীত, সংস্কৃতির চর্চার মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরোধিতা করতেন। সেই চর্চার কোনও প্রভাব কোটিয়ার জীবনে পড়েছে কি না, তা পাঠক জানতে পারলেন না। তুষারকান্তি ঘোষের স্ত্রী তাঁকে পাশে বসিয়ে পুজো করতেন বলে তাঁর মনে হয়েছিল, এক ধাক্কায় ওঁরা জাতিবিভেদ ধ্বংস করেছেন। ১৯৩৪-৩৫-এ প্রত্যেক দিন বাড়ির গৃহ পরিচারককে এক টাকা দিয়ে বাজারে পাঠাতেন। তাঁর ইতিহাস এক অভিজাত পরিবারের ইতিহাস। আমাদের পড়া ইতিহাসের সঙ্গে কোটিয়ার রাশিয়া ও কলকাতাকে মেলাতে অসুবিধা হয়।
আর এই আভিজাত্যের বড় প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর নাতনি চন্দনা দে-র লেখাতে। বইটির দ্বিতীয় ভাগে চন্দনা, জোনাস-সরকার পরিবারের ইতিহাস, এবং তার সঙ্গে সমসাময়িক রাজনৈতিক সামাজিক ইতিহাসও তুলে ধরেছেন। সেখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন কলকাতার কথা বলার সময় চন্দনা লেখেন, জাপানি বোমা, মন্বন্তর, দাঙ্গা সত্ত্বেও তাঁদের পরিবারের জন্য এই সময়টা ইতিবাচক ছিল। কর্মসংস্থান এবং নিরাপত্তা ছিল তাঁদের জীবনে।
বইয়ের দ্বিতীয় অংশে চন্দনা যখন জোনাস পরিবারের ইতিহাস লিখছেন তখন তার সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রসঙ্গগুলো তথ্যমূলক। ইউরোপে ইহুদি সম্প্রদায়ের মধ্যে দেশ ও সমাজ অনুযায়ী পরিবর্তনগুলো আকর্ষণীয়, ইতিহাসের পাঠকের কাছে। তবে হৃদয় কেঁপে যায় এটা জেনে যে, আজকের প্যালেস্তাইনের ধ্বংসাবশেষের আয়োজনের উৎসে ছিল এই পরিবারের শিকড়।
বইটির প্রথম অংশের স্মৃতিচারণা অনুভূতিকে অনেকটা নাড়া দেয়। কিন্তু দ্বিতীয় অংশ বিশ্লেষণহীন তথ্যপূর্ণ রচনা। তাই দুটো ভাগের মধ্যে কিছুটা দূরত্ব তৈরি হয়েছে। তবে এই বইটি থেকে পাঠক একটি পরিবারের হাত ধরে বিস্তৃত এক ইতিহাসের স্বাদ গ্রহণ করতে পারবেন।
Kotia to Ketaki: At Home Away from Home
কেতকী সরকার, চন্দনা দে
মনোগ্রাফ
৮০০/-
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
