
সত্ত্বগুণের প্রতীক হিসেবে বিরসাইয়তরা সাদা জামাকাপড় পরেন। সপ্তাহে একদিন মাংস খান। বিরসাইয়তরা বিশ্বাস করেন, বিরসা বিরসাইয়তদের মধ্যেই আবার জন্ম নেবেন। বিরসাইয়তরা যদি ধর্মপালন না করেন তবে বিরসা ফিরে আসবেন না। বিরসা ফিরে এসে বিরসা-রাজ কায়েম করবেন। বিরসাইয়তরা তাই সাদা পোশাক পরেন, মদ খান না, একটার বেশি বিয়ে করেন না। শিকারে খুব একটা মন নেই বরং চাষে মন। বাড়িতে গরু পুষতে চেষ্টা করেন। নাচগান, হুল্লোড় খুব একটা করেন না। সত্ত্বগুণান্বিত হতে হলে যা-যা করতে হয়।
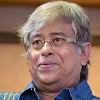
২০.
আমি তখন চাইবাসায়। রেডিও-তে। চক্রধরপুরের একজন সরকারি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল আমার এলাকার স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে। উনি ঝাড়খণ্ডের বাঙালি। বলছিলেন একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখেছি এখানে, হো আর মুন্ডাদের মধ্যে অম্বলের ব্যারাম নেই! অনেকেই সকালে খালিপেটে হাড়িয়া খেয়ে নেয়, বাসি তেলেভাজা খায়, অনেক সময় না খেয়েও থাকে, কিন্তু অ্যাসিড অম্বলের রোগী পাই না। অথচ বাঙালিদের ঘরে ঘরে গ্যাস-অম্বল! মাহাতোদের পরিবারেও অ্যাসিডিটি দেখেছি, কিন্তু হো-মুন্ডাদের গ্যাস্টিক আলসার পাইনি। এটা কিন্তু একটা গবেষণার বিষয় হতে পারে।
হাঁড়িয়ার গুণাগুণ নিয়েও কথা হচ্ছিল। ভাতের ফার্মেন্টেশন হলে কিভাবে ভিটামিন বি তৈরি হয়, মেঠো ইঁদুর, পিঁপড়ের ডিম কীভাবে প্রোটিনের চাহিদা মেটায় ইত্যাদি নানা কথার মাঝে পোলিও প্রসঙ্গটাও এসে যায়। উনি বলেছিলেন: পোলিও প্রজেক্টটা মোটামুটি সাকসেসফুল। প্রথমদিকে অল্প কিছু এলাকায় পোলিওর টিকা খাওয়াতে গেলে বাধা পেতে হত। কারণ একটা গুজব ছড়িয়েছিল যে, শিশু বয়সে বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা নষ্ট করে দেওয়ার চক্রান্ত এটা। কিছু মোল্লা মৌলবি এটা প্রচার করত। সেটা সামলানো গেছে। কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে কয়েকটা গ্রাম থেকে। জঙ্গলের ভিতরে ওই সব গ্রাম। এই তো গতকালই আমাদের টিম ‘লাংগি’ নামে একটা গ্রাম থেকে লেঙ্গি খেয়ে ফিরে এল। ওরা আমাদের টিমকে বলেছে, ‘সুঁই ফুঁড়ে দিন আপত্তি নেই কিন্তু মুখে কিছু খাওয়াতে দেব না।’ কী আশ্চর্য! আমাদের টিমে হিন্দি জানে সবাই, একজন ওঁরাও ছেলেও আছে। কিন্তু গ্রামের মুন্ডারা মুন্ডারিটাই বোঝে শুধু, হিন্দি বোঝে না, আবার ওঁরাও ছেলেটা মুন্ডারি বোঝে না। সুতরাং, ওরা অ্যাকচুয়ালি কী বলতে চায়, কেন পোলিও খাবে না আমরা বুঝতে পারলাম না। শুধু লাংগি নয়, এরকম অনেকগুলো। গ্রামেই এই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে আমাদের। ব্যাপারটা কিছুতেই মাথায় ঢুকছে না। ইনজেকশনে আপত্তি নেই, ওষুধে আপত্তি।

বিরসা মুন্ডা আর ওদের উলগুলান নিয়ে রেডিও ডকুমেন্টারি করতে গিয়ে সিংভূমের নানা প্রান্তে ঘুরতে হয়েছিল। চালকাদ, উলিহাতু, ডোম্বরাবুরু, শঙ্করপুরা, জামকোপাই– এরকম নানা জায়গায় বিরসার কর্মকাণ্ড ছড়ানো ছিল। ১৯০০ সালের মার্চ মাসে জামকোপাইয়ের জঙ্গলে বিরসাকে ব্রিটিশ পুলিশ গ্রেফতার করে। বিরসাকে নিয়ে নানারকম লোককথা, গান, কাহিনি প্রচলিত আছে। জামকোপাই অঞ্চলে বিরসার আত্মগোপন এবং গ্রেফতারি নিয়ে কোনও কাহিনি আছে কি না, জানতে গিয়েছিলাম। থাকলে রেকর্ড করে নিতাম। আমার সঙ্গে একটি ছেলে ছিল, সে হিন্দি, মুন্ডারি, হো– তিনটি ভাষাই জানত। জামাকোপাই-এর কাছাকাছি যে গ্রামগুলো আছে, দেখলাম পুরুষেরা সবাই সাদা পোশাক পরে। তখন শীতকাল। পুরুষেরা ধুতি এবং সাদা জামা। যারা জামা গায়ে দিতে পারেনি, ওরা গেঞ্জির উপর সাদা চাদর। মেয়েরা রঙিন শাড়ি পরলেও চাদরটা সাদা।
এরকম সাদা পোশাকের কিছু রিকশাওয়ালা দেখেছিলাম রাঁচির পথে। মাথায় সাদা পাপড়িও ছিল। ওরকম একটা রিকশায় উঠে আমি একবার বলেছিলাম, কোনও ‘দারু ক দুকান’-এ নিতে যেতে। সে হিন্দিতে বলেছিল– ‘দারুকা দুকানে সে নিয়ে যেতে পারবে না।’ কোনও জায়গায় ছেড়ে দেবে, তারপর নিজেকে খুঁজে নিতে হবে। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, দারুর দোকান কি চেনো না? ও বলেছিল, ‘চিনি জরুর, কিন্তু নিয়ে যাব না। বিরসা ভগোয়ানের নিষেধ আছে।’

ব্যাপারটা বুঝিনি তখন। আমি সেই রিকশায় চাপিনি। তবে পরে আস্তে আস্তে ব্যাপারটা বুঝি। জানতে পারি, যাঁরা বিরসা মুন্ডাকে ধর্মগুরু বলে মানে, তাঁরা হল বিরসাইয়ত। অন্য একজন রিকশাওলা, সেও বিরসাইয়ত, আমাকে অনেক কথা বলেছিল, সে সব পরে বলা যাবে। আজ বরং পোলিও সম্পর্কেই বলি। তবে তার আগে কয়েকটা কথা বলতেই হবে, নইলে পোলিও-র টিকা না খাওয়ানোর কারণ বোঝা যাবে না।
বিরসা মুন্ডাকে আমরা যোদ্ধা হিসেবেই জানি। ওঁর দৃপ্ত ভঙ্গীর মূর্তি দেখতে পাওয়া যায় বিভিন্ন জায়গায়। কিন্তু বিরসাইয়তদের কাছে বিরসা হলেন ধর্মগুরু। বিরসা মুন্ডা সমাজের একটা বড় ধরনের সংস্কার করতে চেয়েছিলেন। হাড়িয়া, মহুয়ার নেশা ছাড়াতে চেয়েছিলেন এবং নিজেদের জাতির অস্মিতা বোধ জাগাতে চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন সবার অন্তত অক্ষর পরিচয় হোক। রোমান অক্ষরেই মুন্ডা ভাষা শিখুক, জীবন সংযত হোক, নিজেদের মধ্যে হানাহানি, মারামারি বন্ধ হোক, দিকুদের বিরুদ্ধে মুন্ডারা ঐক্যবদ্ধ হোক। এরকম ভেবে বিরসা কিছু নির্দেশিকা দিয়েছিলেন। এই নির্দেশ যাঁরা পালন করেন, তাঁরাই বিরসাইয়ত।
বিরসার বাবা খ্রিস্টধর্ম নিয়েছিলেন এবং বিরসাকে চাইবাসায় একটা মিশনারি স্কুলে ভর্তি করানো হয়েছিল। ফলে ফাদারদের কাছ থেকে খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি হয়। সেই স্কুলের জনৈক ফাদার আদিবাসীদের সম্পর্কে কটূক্তি করেছিলেন বলে বিরসার সঙ্গে তাঁর ঝগড়া হয় এবং বিরসা ফাদারের গায়ে হাত তোলেন বলে শোনা যায়। যেমন শোনা যায় নেতাজি সুভাষ বসু এবং অধ্যাপক ওটেনকে নিয়ে। বিরসাকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। তখনকার দিনে মিশনারি স্কুলের ক্লাস এইটের ছাত্রকে শিক্ষিত মানা হত। চাকি নামে একটা এলাকা আছে, সেই চাকির জমিদারের প্রধান মুন্সী ছিলেন আনন্দ পাঁড়ে। আনন্দ পাঁড়ে সহকারী হিসেবে ইংরিজি জানা, পাটিগণিত জানা বিরসাকে নিয়োগ করেন। পাঁড়েজির কাছ থেকে বিরসা নিষ্কাম কর্ম, কর্মযোগ, দেহাত্মা ও পরমাত্মা, জন্মান্তর– এইসব হিন্দু ধর্মীয় জ্ঞান সংগ্রহ করেন। এছাড়া ওদের, নিজেদের শরনা ধর্ম, যেখানে মূর্তিপূজা নেই, প্রকৃতিকে সম্মান করার একটা ধারণা আছে, সেটা বিরসার রক্তেই ছিল, এই তিনধর্মকে মিলিয়ে বিরসা একটা নতুন ধর্মমত তৈরি করেন, যাকে নির্দেশিকাই বলা যায়। বিরসার প্রচুর অনুগামীও জুটে যায়। এবং এদের নিয়েই ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। যদিও যুদ্ধ পরিচালনা বিরসা নিজে করেননি। মুন্ডারা শোচনীয় ভাবে হেরে যায়। সেটা অন্য কথা। বলতে চেয়েছিলাম পোলিও-র টিকা।
খ্রিস্টানদের নির্দেশিকায় প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ভাব রাখা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এতে একটা এলাকা সংঘবদ্ধ থাকে। সত্য কথা বলা, নির্যাতন না করা– এসব সব ধর্মেই থাকে, কিন্তু খ্রিস্টধর্মে অনুশোচনা বা দোষ স্বীকার করা একটা বড় ব্যাপার। বিরসা তার নির্দেশিকায় এগুলোই করতে বলেছিল। সেই সঙ্গে সপ্তাহে একদিন বিশ্রাম করতে বলেছিলেন। এবং সেইদিন ওরা গাছের কোটরে মুখ রেখে নিজেদের দোষগুলো বলে দেয়। এবং ভবিষ্যতে না করার অঙ্গীকার নেয়। আনন্দ পাঁড়ে নিরামিষাশী ছিলেন। মুন্ডাদের পক্ষে নিরামিষাশী থাকা সম্ভব নয়, কিন্তু বিরসা যতটা সম্ভব মাংস কম খেতে বলেছিলেন। আসলে পাঁড়ের কাছ থেকে সত্ত্বগুণের ধারণা পেয়েছিলেন। সেজন্যই মদ খাওয়া নিষেধ করেছিলেন। উদ্দামতা সংযমিত করার কথা বলেছিলেন। বিলাস কম করতে বলেছিলেন।
সত্ত্বগুণের প্রতীক হিসেবে বিরসাইয়তরা সাদা জামাকাপড় পরেন। সপ্তাহে একদিন মাংস খান। বিরসাইয়তরা বিশ্বাস করেন, বিরসা বিরসাইয়তদের মধ্যেই আবার জন্ম নেবেন। বিরসাইয়তরা যদি ধর্মপালন না করেন তবে বিরসা ফিরে আসবেন না। বিরসা ফিরে এসে বিরসা-রাজ কায়েম করবেন।
বিরসাইয়তরা তাই সাদা পোশাক পরেন, মদ খান না, একটার বেশি বিয়ে করেন না। শিকারে খুব একটা মন নেই বরং চাষে মন। বাড়িতে গরু পুষতে চেষ্টা করেন। নাচগান, হুল্লোড় খুব একটা করেন না। সত্ত্বগুণান্বিত হতে হলে যা-যা করতে হয়। ফলে বিরসাইয়তরা ভাবতে থাকেন অন্যান্য মুন্ডার তুলনায় ওরা শ্রেষ্ঠতর মানুষ। হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণরা যেমন ভাবেন।
………………………………..
ফলো করুন আমাদের ওয়েবসাইট: রোববার ডিজিটাল
………………………………..
লাংসি গ্রামের লোকজন বলেছিল, ওরা যদি হাটে যায়, হাটের চিড়েমুড়ি ছাড়া অন্য রান্না খাবার কিনে খায় না। টিউবয়েলের জলে চিড়ে ভিজিয়ে নেয়, গুড় বা বাতাসা দিয়ে খায়। কারণ এসব যারা রান্না করে তারা নিচু জাত। নিচু জাতের রান্না করা খাবার কি করে খাবে? ওরা তো বিরসাইয়ত, উঁচু জাতের মুন্ডা। আর পোলিও-র টিকা তো মুখেই দেয় না। কোন জাত না কোন জাতের লোক খাওয়াচ্ছে ঠিক নেই। জাত যাবে না!
এই লাংগি গ্রাম চক্রধরপুর থেকে যে রাস্তাটা রাঁচি গেছে, সেই রাস্তার মাঝামাঝি জায়গা থেকে বাঁ-দিকে ঘণ্টাখানেক জিপগাড়িতে গিয়ে, পায়ে হেঁটে দুটো পাথুরে নদী পেরিয়ে চার কিলোমিটারের মতো হেঁটে যেতে হয়। এই গ্রামের ৫০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের বৃত্তে একটাও ব্রাহ্মণ নেই, কিন্তু দেখুন ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র কীভাবে আছে!
দেখুন কী শক্তি তার।
…পড়ুন ব্লটিং পেপার-এর অন্যান্য পর্ব…
১৯: ধোঁয়া আর শব্দেই বুঝে গেছি আট-তিন-পাঁচ-দেড়-দেড়!
১৮: নামের আগেপিছে ঘুরি মিছেমিছে
১৭: টরে টক্কার শূন্য এবং ড্যাশের সমাহারে ব্যাঙের ‘গ্যাগর গ্যাং’ও অনুবাদ করে নিতে পারতাম
১৬: ছদ্মবেশী পাগলের ভিড়ে আসল পাগলরা হারিয়ে গেল
১৫. ধূমপান নিষেধের নিয়ম বদলান, আকাশবাণীর স্টেশন ডিরেক্টরকে বলেছিলেন ঋত্বিক ঘটক
১৪. এমএলএ, এমপি-র টিকিট ফ্রি, আর কবির বেলা?
১২. ‘গাঁধী ভগোয়ান’ নাকি ‘বিরসা ভগোয়ানের পহেলা অবতার’
১১. কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্টের চক্করে বাঙালি আর ভোরবেলা হোটেল থেকে রওনা দেয় না
৫. তিনটে-ছ’টা-ন’টা মানেই সিঙ্গল স্ক্রিন, দশটা-পাঁচটা যেমন অফিসবাবু
৪. রাধার কাছে যেতে যে শরম লাগে কৃষ্ণের, তা তো রঙেরই জন্য
৩. ফেরিওয়ালা শব্দটা এসেছে ফার্সি শব্দ ‘ফির’ থেকে, কিন্তু কিছু ফেরিওয়ালা চিরতরে হারিয়ে গেল
২. নাইলন শাড়ি পাইলট পেন/ উত্তমের পকেটে সুচিত্রা সেন
১. যে গান ট্রেনের ভিখারি গায়কদের গলায় চলে আসে, বুঝতে হবে সেই গানই কালজয়ী
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
