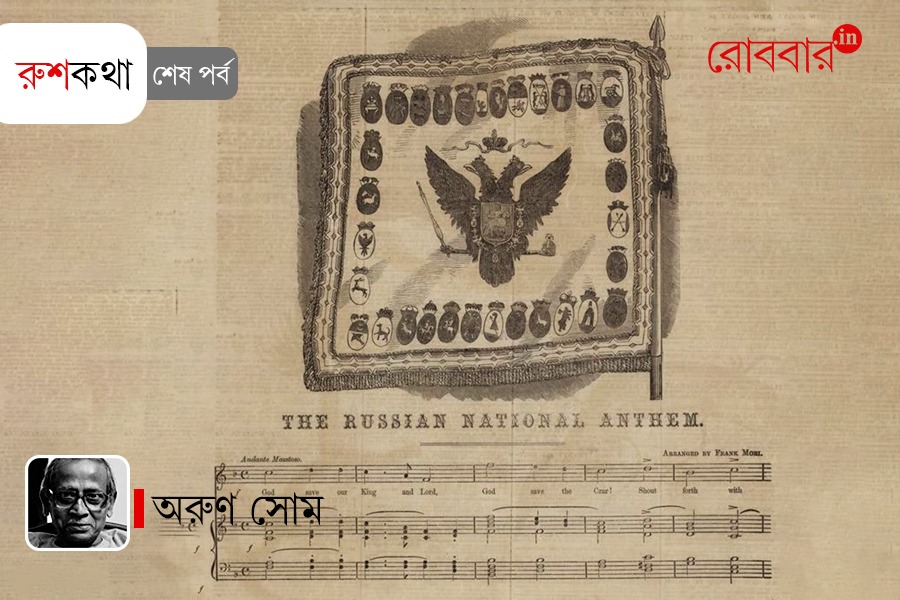
১৯৯৩ সালে (১৪ জানুয়ারি) জাতীয় সংগীতের কথা রচনার জন্য একটি কমিশন গঠিত হয়। সেই কমিশনের সভাপতি পদে নির্বাচিত হলেন সেই সের্গেই মিখাল্কোভ্, যিনি ১৯৪৪ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় সংগীতের কথা রচনা করেছিলেন। তখন তিনি ছিলেন তরুণ। ১৯৭৭ সালে তার সংশোধিত পাঠও রচনা করেছিলেন সেই তিনি। এখন তাঁর বয়স আশি। সেই সময় তিনি তাঁর রচনার জন্য ‘সমাজতান্ত্রিক শ্রমবীর’ অর্ডারে ভূষিত হয়েছিলেন, সুরকার আলেক্সান্দ্র আলেক্সান্দ্রভ্ ‘লেনিন অর্ডার’ পেয়েছিলেন। এবারে ওরকম কোন পুরস্কার প্রাপ্তির সম্ভাবনা কারও নেই। পাঠ মনোনীত হলে তার রচয়িতার নগদ অর্থপ্রাপ্তি ঘটবে।

শেষ পর্ব
অন্য কথা, সুর এক
রাশিয়ার জাতীয় সংগীত প্রসঙ্গে
১৯ ডিসেম্বর, ২০০০
শেষ পর্যন্ত বহু তর্কবিতর্কের অবসান ঘটিয়ে রাশিয়ার নতুন জাতীয় সংগীত অনুমোদিত হল। ফিরিয়ে আনা হল কথা পালটে এবং নতুন কথার দু’-এক জায়গায় সুরের সামান্য পরিবর্তন ঘটিয়ে পুরনো সোভিয়েত জাতীয় সংগীত যা ১৯৪৪ সালের ১ জানুয়ারি সে দেশের জাতীয় বেতারে প্রথম সম্প্রচারিত হয়েছিল। নববর্ষে দেশবাসীকে স্তালিনের উপহার। সুরকার আলেক্সান্দ্র আলেক্সান্দ্রভের রচিত এই সুরটি স্তালিন ব্যক্তিগতভাবে নির্বাচন করেছিলেন।
এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ইতিপূর্বে ১৯১৮ থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত সোভিয়েত রাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত হিসেবে ইন্টারন্যাশনাল প্রচলিত ছিল।
জাতীয় সংগীতের সুরটি যেহেতু একসময় স্তালিনের নির্বাচিত ছিল সেই জন্য রাশিয়ার বর্তমান রাষ্ট্রপ্রধান এবং সে দেশের দুমা-র (সংসদের উচ্চকক্ষ) তা পুনর্বহালের সিদ্ধান্ত দেশের কোনও কোনও সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মহলের বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিল।
সংগীতের ক্ষেত্রে এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সংগীতের ব্যবহার সম্পর্কে স্তালিন একেবারে অজ্ঞ ছিলেন না। বস্তুত তাঁর অবসর বিনোদনের একটা প্রিয় উপায় ছিল গ্লিন্কা অথবা রিঙ্স্কি-কর্সাকভের অপেরা অথবা চাইকোভ্স্কির ব্যালে অনুষ্ঠান দেখা। ক্ল্যাসিকাল সংগীত সম্পর্কে তাঁর ভালো জ্ঞান ছিল। নিজে তিনি ভালো গাইতে পারতেন। ধর্মীয় সেমিনারিতে পড়ার সময় গির্জার প্রার্থনা সংগীতও তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল।

জাতীয় সংগীতের সুর নির্বাচনে স্তালিনের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল কতকটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। সুর নির্বাচন উপলক্ষে যে প্রতিযোগিতার আহ্বান জানানো হয়েছিল সেখানে দ্মিত্রি শস্তাকভিচ্ ও আরাম খাচাতুরিয়ানের মতো বিশ্ববিখ্যাত সুরকারদের রচনাও ছিল। তাঁদের রচনার মৌলিকতার সর্বোচ্চ মূল্য ও মর্যাদা দেওয়া সত্ত্বেও স্তালিন শেষকালে একটি সহজ-সরল সুর বেছে নিয়েছিলেন। স্তালিন জানতেন মৌলিকতা বা উৎকর্ষ নয়, জাতীয় সংগীতের প্রধান গুণ হওয়া উচিত তার চমৎকারিত্ব ও মনোগ্রাহিতা। তাঁর কথায় ‘সুর এমন হওয়া উচিত যাতে একজন পাইওনিয়র থেকে পেনশনার পর্যন্ত সকলে সঙ্গে সঙ্গে তা মনে রাখতে পারে।’
ঠিক এই গুণগুলিই সুরকার আলেক্সান্দ্র আলেক্সান্দ্রভের সুরে ছিল, তাই তা ১৯৯০ সাল পর্যন্ত রাশিয়ার জাতীয় সংগীত হিসাবে চলে আসছিল। পুরনো জাতীয় সংগীত অনুমোদনের পক্ষে দুমার সামনে আসলে আরেকটি বড় সমস্যা জাতীয় সংগীতের অস্বস্তিকর কথাগুলি। মূল যে লিরিক তার যুগ্ম রচয়িতাদের মধ্যে একজন ছিলেন তখনকার দিনের উদীয়মান তরুণ কবি ও শিশু সাহিত্যিক সের্গেই মিখাল্কোভ, (১৯১৩ -২০০৯) অন্যজন এল্ রেগিস্তান (১৮৯৯-১৯৪৫)। স্তালিন নিজের হাতে এর পাঠ সম্পাদনা করেছিলেন। এতে সেই সময় স্তালিন প্রশস্তিও ছিল।
এই পাঠ সম্পর্কে বিখ্যাত সামরিক ঐতিহাসিক দমিত্রি ভল্কগোনভের মন্তব্য: ‘স্তালিন ব্যক্তিগতভাবে জাতীয় সংগীতের পাঠ সম্পাদনা করেছিলেন। এই পাঠে পিতৃভূমির ভাগ্যনির্ধারণে তাঁর যে ভূমিকা তার প্রতিফলন ঘটেছে।’ তৃতীয় স্তবকের তৃতীয় ও চতুর্থ পঙক্তিতে ‘মানুষের প্রতি আনুগত্যের শিক্ষায় আমাদের প্রতিপালন করেছেন স্তালিন, তিনি আমাদের শ্রমের প্রেরণা দিয়েছেন, মহৎ কীর্তি সাধনের প্রেরণা দিয়েছেন।’
সের্গেই মিখাল্কোভ ও এল্ রেগিস্তান ‘নেতার’ আজ্ঞাক্রমে জাতীয় সংগীতের পাঠ প্রস্তুত করে তাঁর কাছে নিয়ে যান। স্তালিন সেই পাঠের কিছু কিছু জায়গা সংশোধন করেন। স্তালিনের আর্কাইভে এই সংশোধনের ‘চিহ্ন’ সংরক্ষিত আছে।

মূল পাঠে যেখানে ছিল ‘স্বাধীন জাতিসমূহের সুমহৎ সঙ্ঘ’, সেখানে স্তালিন সংশোধন করে লিখলেন: স্বাধীন প্রজাতন্ত্রসমূহের অবিনশ্বর সঙ্ঘ। (সংগীতের সূচনাই এই কথাগুলি দিয়ে)।
দ্বিতীয় চতুষ্টয়ে বড় রকমের পরিমার্জনা ঘটালেন। আদিতে ছিল: ‘বজ্রনির্ঘোষ ভেদ করে আমাদের আলোকে উদ্ভাসিত করে তুলছে স্বাধীনতার সূর্য, লেনিন আমাদের ভবিষ্যতের পথকে আলোকিত করেছেন, আমাদের প্রতিপালন করেছেন স্তালিন– যিনি আমাদের জাতির মনোনীত; তিনি আমাদের শ্রমের প্রেরণা দিয়েছেন,
মহৎ কীর্তি সাধনের প্রেরণা দিয়েছেন।’ পাঠের ওপর স্তালিনের পেন্সিল চালনার পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণটি দেখতে অন্যরকম হল: ‘মহান লেনিন আমাদের ভবিষ্যতের পথকে আলোকিত করেছেন, মানুষের প্রতি আনুগত্যের শিক্ষায় আমাদের প্রতিপালন করেছেন স্তালিন।’ ‘জাতির মনোনীত’ কথাটি স্তালিনের কেন যেন পছন্দ হয়নি, যদিও অবশ্য ভালো করে ভেবে দেখতে গেলে সত্যিই তো, জাতি তাঁকে ‘মনোনয়ন’ করেনি। তিনি তাঁদের মনোনীত না হয়েই এক বিপুল জাতির নেতা অধিনায়ক ও হর্তাকর্তা বিধাতা হয়ে দাঁড়ান। তাঁর এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিমার্জনায় শুধু মিখাল্কোভ এবং এল্ রেগিস্তানই নন, ১৯৪৩-এর ২৮ অক্টোবর সন্ধ্যায় সেদিন স্তালিনের কক্ষে উপস্থিত মোলতভ্, ভরশিলভ্, বেরিয়া, মালেনকভ্ ও শ্চের্বাকভ– এঁরা সকলেই এতে সম্মতি প্রদান করেন। রচয়িতারা এই গীতির একটা ধুয়াও রচনা করেছিলেন: ‘যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাক, সমাজতন্ত্রের দেশ, আমাদের ধ্বজা বিশ্বশান্তি বহন করুক। বেঁচে থাক, দৃঢ় হও যশস্বী স্বদেশ। আমাদের মহান জনগণ তোমাকে রক্ষা করছে।’ স্তালিন সঙ্গে সঙ্গে এই অংশটি বাতিল করে দেন, কেন যেন তাঁর পছন্দ হয়নি। সম্ভবত ‘বিশ্বশান্তি’ কথাটি তাঁর মনে ধরেনি।
জাতীয় সংগীতে পার্টি সম্পর্কে একটি কথাও ছিল না, কিন্তু ‘অধিনায়ক’ বড়ই ‘প্রয়োজনীয়’ হয়ে দেখা দিয়েছিল। ধীরে ধীরে সোভিয়েত মানুষের মনের মধ্যে এই ধারণাই দৃঢ়বদ্ধমূল হল যে স্তালিন শুধু পার্টিরই অধিনায়ক নন, সমগ্র জনগণের অধিনায়ক। এই ধারণারই ঘনীভূত রূপ প্রকাশ পেয়েছিল ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বরে সারা ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর সদস্য খ্রুশশ্যোভের প্রকাশ্য ভাষণে: ‘সোভিয়েত ইউনিয়নের সকল জাতির মানুষই স্তালিনের মধ্যে তাদের বন্ধু পিতা ও অধিনায়ককে দেখতে পান। স্তালিন তাঁর সরলতার গুণে জনগণের বন্ধু। স্তালিন জনগণের প্রতি তাঁর ভালোবাসার জন্য জনগণের পিতা। স্তালিন জাতিসমূহের সংগ্রাম পরিচালনায় তাঁর প্রতিভার জন্য তাদের অধিনায়ক।’ (ইওসিফ স্তালিনের ৬০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে, মস্কো ১৯৪০, দ্মিত্রি ভল্কগোনভ্: ‘বিজয় ও ট্র্যাজিডি’ পৃষ্ঠা ৯৩-১০২)।

জাতীয় সংগীতের এই পাঠটি পরবর্তীকালে তুলে নেওয়া হয়। স্তালিনের মৃত্যুর পর থেকে ১৯৭৭ সালে যতদিন পর্যন্ত না স্তালিন প্রশস্তির অংশ বাদ দিয়ে তার ঈষৎ সংশোধিত পাঠ প্রকাশিত হয়, ততদিন সোভিয়েত জাতীয় সংগীত ‘বাক্যহারা’ হয়ে ছিল। শুধু সংগীতই বাজানো হত। এই নতুন সংশোধিত পাঠেরও রচয়িতা ছিলেন সের্গেই মিখাল্কোভ। সুর অপরিবর্তিত রেখে জাতীয় সংগীতের নবপর্যায়ের এই সংশোধিত পাঠের অভিনবত্ব এখানেই যে পূর্ববর্তী পাঠের তৃতীয় স্তবকের শেষ দুই ছত্রে যে স্তালিন প্রশস্তি ছিল এতে তা নেই। পরিবর্তে সেখানে যে গুণ স্তালিনের ওপর আরোপিত হয়েছিল অনেকটা তাই আরোপিত হয়েছে লেনিনের ওপর: ‘ন্যায়সঙ্গত কাজে আমাদের উদ্দীপিত করেছেন তিনি, আমাদের শ্রমের প্রেরণা দিয়েছেন, মহৎ কীর্তি সাধনের প্রেরণা দিয়েছেন।
দ্বিতীয়ত পূর্ববর্তী পাঠে ‘পার্টি’ ও ‘কমিউনিজমের’ কোনও উল্লেখ ছিল না। এখানে তা আছে। যেখানে ছিল: ‘সোভিয়েতের ধ্বজা, জনগণের ধ্বজা আমাদের এক বিজয় থেকে আরেক বিজয়ের পথে পরিচালনা করুক।’ ‘লেনিনের পার্টি– জনগণের শক্তি কমিউনিজমের বিজয়ের পথে আমাদের পরিচালনা করে।’
তৃতীয়ত পঞ্চম চতুষ্টয়টি একেবারেই বর্জিত। সেখানকার পাঠে ছিল: ‘আমরা আমাদের বাহিনীকে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বড় করে তুলেছি নীচাশয় হানাদারদের আমরা পথ থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করছি, আমরা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রজন্ম প্রজন্মান্তরের ভাগ্য নির্ধারণ করি, আমরা আমাদের পিতৃভূমিকে গৌরবের পথে পরিচালনা করব।’ কিন্তু এখানে তার জায়গায় আছে: ‘কমিউনিজমের শাশ্বত ভাবাদর্শের বিজয়ের মধ্যে আমরা আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ দেখে থাকি, আমাদের গৌরবময় পিতৃভূমির রক্তপতাকায় চিরকাল আমাদের নিঃস্বার্থ বিশ্বাস থাকবে।’
কিন্তু কথা জুগিয়ে দেওয়ার পরও সোভিয়েত জাতীয় সংগীত প্রায় ‘বাক্যহারা’ই রয়ে গিয়েছিল। বিশেষ গাওয়া হত না, সুরটাই বরাবর ধ্বনিত হত। তবে সে তো ওই একই সুর– স্তালিনের অনুমোদিত সুর!

পেরেস্ত্রৈকার আমলে এ সংগীত এক্কেবারেই নির্বাক হয়ে গেল, যদিও সোভিয়েত ইউনিয়ন তখনও ছিল। কিন্তু ১৯৯০ সালে রুশ সোভিয়েত ফেভারেটিভ প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট ইয়েল্ৎসিন তাঁর হুকুমনামাবলে জাতীয় সংগীতের অন্য একটি সুর অনুমোদন করেন– সেটা ছিল উনবিংশ শতাব্দীর খ্যাতনামা সুরকার গ্লিন্কার একটি অসমাপ্ত রচনার ভিত্তিতে ১৯৪৪ সালে সুরকার ও পরিচালক মিখাইল বাগ্রিনভ্স্কির একটি দেশাত্মবোধক গীতির সুর। গ্লিন্কার দেশাত্মবোধক সংগীতের সুরটিকেই প্রজাতন্ত্রের জাতীয় সংগীতরূপে তিনি ঘোষণা করলেন। অন্যদিকে, সমান্তরালভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় সংগীতের সুর অপরিবর্তিতই রয়ে গেল। তখনও সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল, কিন্তু রাশিয়া তার স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করে; অতএব তারও একটি জাতীয় সংগীত প্রয়োজন। অবশ্য রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ প্রজাতন্ত্রের সেই নতুন সুরেও কোনও কথা ছিল না। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের ফলে আবারও জাতীয় সংগীতকে কেন্দ্র করে অনিশ্চিত অবস্থার সৃষ্টি হল। প্রায় বছর দুয়েক এই অবস্থা চলার পর ১৯৯৩ সালের শেষে নতুন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ইয়েল্ৎসিন তাঁর নিজের নির্বাচিত সংগীতটিকেই হুকুমনামা বলে নতুন রাশিয়ার জাতীয় সংগীত রূপে ঘোষণা করলেন, যদিও পার্লামেন্টে তখনও তা অনুমোদিত হয়নি। রেডিয়ো টেলিভিশনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এবং স্টেডিয়ামে এই সুরই জাতীয় সংগীত হিসেবে বাজতে শুরু করল। কিন্তু এই সুরের মুখে ভাষা ত জোগানো গেলই না, এমনকী অনেকে এমন অভিযোগ করল যে এ সুর বড় জটিল এবং মনে রাখা দুঃসাধ্য।
১৯৯৩ সালে (১৪ জানুয়ারি) জাতীয় সংগীতের কথা রচনার জন্য একটি কমিশন গঠিত হয়। সেই কমিশনের সভাপতি পদে নির্বাচিত হলেন সেই সের্গেই মিখাল্কোভ্, যিনি ১৯৪৪ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় সংগীতের কথা রচনা করেছিলেন। তখন তিনি ছিলেন তরুণ। ১৯৭৭ সালে তার সংশোধিত পাঠও রচনা করেছিলেন সেই তিনি। এখন তাঁর বয়স আশি। সেই সময় তিনি তাঁর রচনার জন্য ‘সমাজতান্ত্রিক শ্রমবীর’ অর্ডারে ভূষিত হয়েছিলেন, সুরকার আলেক্সান্দ্র আলেক্সান্দ্রভ্ ‘লেনিন অর্ডার’ পেয়েছিলেন। এবারে ওরকম কোন পুরস্কার প্রাপ্তির সম্ভাবনা কারও নেই। পাঠ মনোনীত হলে তার রচয়িতার নগদ অর্থপ্রাপ্তি ঘটবে।
কোন কোন মহলের অদ্ভুত আবদার ছিল জারের আমলের জাতীয় সংগীতকে ফিরিয়ে আনার। কিন্তু সেটা কোনমতেই সম্ভব নয়– সেখানে ছিল রাজ প্রশস্তি। সেটা করতে গেলে কালানুচিত হত।

১৮৩৩ সালে জার প্রথম নিকলাইয়ের নির্দেশে সেই রাজপ্রশস্তিমূলক সংগীতের বাণী রচনা করেছিলেন তৎকালীন বিশিষ্ট কবি ভাসিলি জুকোভ্স্কি। সুর দিয়েছিলেন সুরকার আ. ফ. ল্ভোভ্। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে জার প্রথম পিয়োত্র ও সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় য়েকাতেরিনার আমলে নির্দিষ্ট সে রকম কোনও জাতীয় সংগীত ছিল না। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রকম গুরুগম্ভীর ক্লাসিক সংগীত বাজিয়ে সেই কাজটি সারা হত। ১৮১৬ সাল থেকে সরকারি ভাবে জাতীয় সংগীত হিসেবে ঘোষিত হয় ইংলন্ডের জাতীয় সঙ্গীত ‘God save the King’। ইংল্যান্ডের এই রাজপ্রশস্তির একটি রুশপাঠ অবশ্য ১৮১৬ সালে বিখ্যাত রুশ কবি পুশ্কিন রচনা করেছিলেন। কিন্তু রুশদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে প্রচলিত সংগীতের কথাগুলি রচনা করেছিলেন জুকোভ্স্কি। প্রথম ধ্বনিত হয় ১৮৩৩ সালের ১১ ডিসেম্বর বলশয় থিয়েটারে। কথাগুলি ছিল:
O God, save the Czar/Strong and powerful/Reign
over us in glory, in glory/Strike fear into the
hearts of our enemies.
মানতেই হবে যে কথাগুলি বর্তমান রাশিয়ার ভাবমূর্তি সম্পর্কে বিশ্বাসীর কাছে সঠিক বার্তা বহন করে না।
১৯৯৩ সাল থেকে শুরু করে প্রায় ৭ বছর জাতীয় সংগীতের কথা ও সুর নিয়ে উপরের মহলে যখন তর্কবিতর্ক চলছে সেই সময়ের মধ্যে জনসমীক্ষায় দেখা গেছে দেশের অধিকাংশ মানুষেরই পুরনো সুর সম্পর্কে কোনও আপত্তি তো নেই-ই বরং তাঁরা মনে করেন ওই সুর গুরুগম্ভীর অনুষ্ঠানে বাজানোর খুবই উপযোগী। এখানে আরও উল্লেখযোগ্য এই যে পুরনো সুর পুনঃপ্রতিষ্ঠার পক্ষে ছিলেন যুব সম্প্রদায়ভুক্ত সেই সমস্ত ক্রীড়াকুশলী, যাঁরা ২০০০ সালের সিডনি ওলিম্পিক্সে যোগ দিয়েছিলেন, সেখানে প্রেসিডেন্টের অনুমোদিত সুরে তাঁরা উৎসাহ পাননি।
অবশেষে ঘুরে ফিরে সেই পুরনো সুর। কিন্তু কথা? হ্যাঁ, কথা অন্য বটে, কিন্তু সেই কথা ঘুরে ফিরে বলছেন সেই একই ব্যক্তি– ইতিমধ্যে ৮৭ বছর বয়সে পদার্পণ করেছেন। সেই সের্গেই মিখাল্কোভ্– ‘স্বাধীন প্রজাতন্ত্র সমূদ্রের অবিনশ্বর সঙ্ঘ’-এর রচয়িতা।
এটাও দেশবাসীর কাছে নববর্ষের একটি উপহার। তবে প্রেসিডেন্ট পুতিনের উপহার– ২০০১ সালের নববর্ষের প্রাক্কালে– এর ঠিক এক বছর আগে প্রেসিডেন্ট ইয়েল্ৎসিন তাঁর হাতে ক্ষমতা প্রদান করে অবসর গ্রহণ করেছেন।
২০০০ সালের ২৯ ডিসেম্বর রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে সম্প্রচারিত হল এই সংবাদ। নতুন পাঠের প্রথম স্তবকটি পড়ে শোনালেন স্বয়ং তার রচয়িতা সের্গেই মিখাল্কোভ্।
সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় সংগীতে ভ্রাতৃপ্রতিম সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র সমূহের অবিনশ্বর সঙঘের কথা ছিল। নতুন রাশিয়ার এই জাতীয় সংগীতেও জাতিসমূহের অবিনশ্বর সঙঘের উল্লেখ আছে– যদিও বলাই বাহুল্য, রুশ ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত জাতিসমূহের। এই নতুন সংগীতের বিশেষভাবে দক্ষিণের সাগর-উপসাগর (কাসপিয়ান সাগর ও কৃষ্ণসাগর) থেকে উত্তরের মেরুপ্রান্ত পর্যন্ত দেশের বিপুল বিস্তার, সারা দুনিয়ায় তার অদ্বিতীয় ও অনবর্ত অবস্থানের জন্য স্লাঘার প্রসঙ্গ আসে। তবে এখানে দেশের জনগণের মাথার ওপর কোনও অধিনায়ক নেই– বিধাতাই তার রক্ষাকর্তা।

মিখাল্কোভ্ এই প্রসঙ্গে বললেন যে এই নতুন কথা লেখার জন্য তিনি গর্বিত। ‘আজ অবশ্যই বিগত দিনগুলির কথা আমার মনে পড়ছে। সেগুলি আমার কাছে পরম আদরের, বড়ই আপনার। কিন্তু আমি বুঝি যে দেশ বদলে গেছে। রাশিয়া তা পথ বেছে নিয়েছে। এখন আমি যা লিখেছি তা আমার হৃদয়ের খুবই কাছাকাছি কারণ আমি অন্তর থেকেই লিখেছি এবং যা লিখেছি তা আমি বিশ্বাস করি।’
আশ্চর্য। ১৯৯১ সালের আগস্টে (১৯-২১ আগস্ট) মস্কোয় কমিউনিস্টরা যে ব্যর্থ অভ্যুথান ঘটিয়েছিলেন এই সের্গেই মিখাল্কোভ্ সেদিন দ্বিধাহীন কণ্ঠে প্রকাশ্যে তা সমর্থন করেছিলেন।
আসলে এটাই বোধহয় সাধারণভাবে রাশিয়ার সর্বকালের বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা– শুধু রাশিয়ার বললে ভুল হবে, সর্বকালের সর্বদেশের বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা এবং সর্বত্রই তাঁরা যা করেন অন্তর থেকেই করেন।
কিন্তু না, মিখাল্কোভ্ তো একদিক থেকে নিজের সাফাই গাইতেই পারেন এই বলে যে মতাদর্শ পাল্টালেও দেশ তো দেশই আছে, আর তিনি তো সেই দেশেরই বন্দনা করছেন– কোনও বিশেষ ভাবাদর্শের নয়। এতে অন্যায়ের কী আছে? এ প্রশ্নও খতিয়ে দেখার মতো।
সবচেয়ে বড় কথা, রাশিয়া আছে– রাশিয়া রাশিয়াতেই আছে, জার পিয়োত্র-র ঐতিহ্য, লেনিনের উত্তরাধিকার নিয়ে আছে, স্তালিনের ‘সুকৃতি’ ‘দুষ্কৃতি’ নিয়ে আছে– থাকবেও, আরও বহু বছর থাকবে। এছাড়া তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার অন্য কোনও উপায় নেই।
আজকের পুঁজিতান্ত্রিক রাশিয়ার সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের কোনও কোনও ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার যে প্রয়াস চলছে তাকে সমাজতন্ত্র পুনরুদ্ধারের প্রয়াস বলে চালানো ঠিক হবে না। সমাজতন্ত্র থেকে পাঠ নিতে তার কোনও কোনও সুকৃতিকে কাজে লাগিয়ে গরিবগুর্বোদের জন্য কিছু সুযোগ-সুবিধা দিয়ে তথাকথিত ‘জনকল্যাণ মূলক’ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের ভিত শক্ত করাই এর মূল উদ্দেশ্য।
পরন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন গড়ে তোলা না গেলেও এই অবকাশে জাতীয়তাবাদের জিগির তুলে ইউনিয়নের নামে রুশ সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধার সাধনও যে অসম্ভব, এমন নয়।
…………………………… সমাপ্ত ……………………………
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
