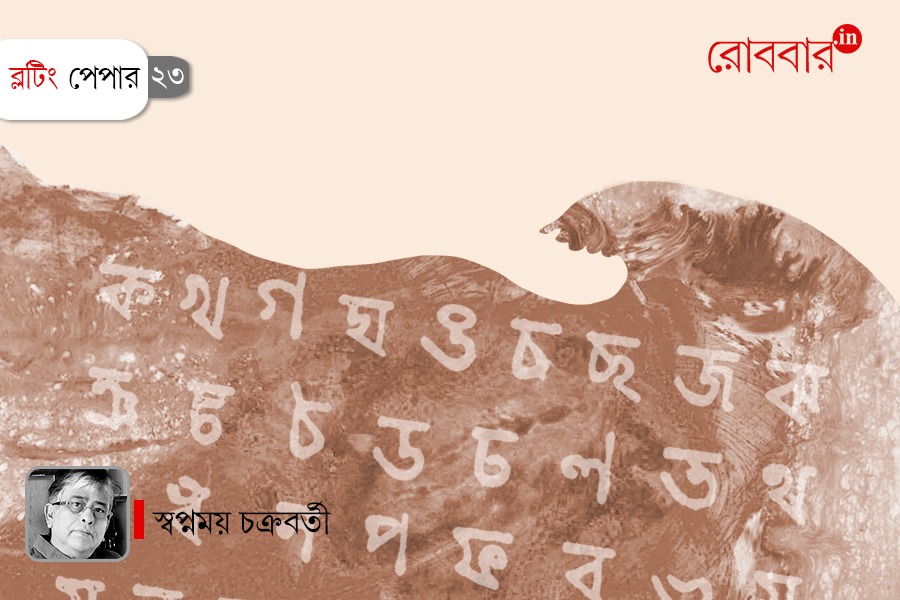
সেই ছোটবেলায় আমাদের ভাড়াবাড়ির একতলায় একটা কলতলা ছিল। চৌবাচ্চার জলে আমরা মগ ডুবিয়ে গায়ে জল ঢালতাম। মেয়েদের জন্য একটা আড়াল-ঘর ছিল। সেই কলতলা ‘কলঘর’ হল। কলঘরের প্রথম প্রমোশন হল ‘বাথরুম’। বাথরুমে দুটো কল থাকত, শাওয়ারও। বাথরুম প্রমোশন পেয়ে হয়ে গেল ‘টয়লেট’। টয়লেটে একটা বেসিন থাকত– কমোড। এটার আরও একধাপ উন্নতি হয়ে ‘ওয়াশরুম’ হল। উন্নতি বিষয়ে বিশদ ধারণা নেই। উন্নতি হলে নাম পাল্টে যায়। ঘুষ ‘কাটমানি’ হয়, স্পিডমানি হয়। দালাল ব্রোকার হয়, আরও পরে এজেন্ট হয়। এজেন্টও কিছু একটা হয়, সঠিক জানি না।
প্রচ্ছদে ব্যবহৃত হয়েছে উইলিয়াম বোল্টসের বাংলা হরফ। ১৭৭৩
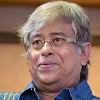
২৩.
শিমলা গিয়েছিলাম বছর পাঁচেক আগে। গিন্নির পেটের গন্ডগোল। ভ্রমণ সংস্থার খাবার চলবে না। ভাবলাম, চিঁড়ে ভিজিয়ে নুন-লেবু দিয়ে ওর লাঞ্চ হবে। চিঁড়ের জন্য বাজারে গেলাম। দোকানে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘চিঁড়া হ্যায়?’
‘চিঁড়া’ শুনে একজন বলল, ‘ক্যায়া চিজ?’
শুনেছিলাম হিন্দিতে ‘চুড়া’ বলে। তাই বললাম, ‘চুড়া, চুড়া…।’
–চুড়া ক্যায়া?
কী করে বোঝাই! আমার ‘বাঙালি হিন্দি’-তে বলি, ‘চাউল, চাউল হ্যায় না? সেই চাউল চিপকে এইসা করকে…’ মুকাভিনয়ে চিঁড়ে বোঝানো যোগেশ দত্তর পক্ষেও সম্ভব ছিল না!
এই চিঁড়ে প্রসঙ্গে আমার পিতামহর একটা অভিজ্ঞতার কথা শুনেছিলাম। সে সময়ের পূর্ব-পাকিস্তান থেকে শরণার্থী হয়ে আসা তিনি বাগবাজার অঞ্চলে একটা ঘরভাড়া নিয়েছিলেন। মুদির দোকানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ‘চিঁড়া আছে?’ দোকানদার বলেছিলেন, ‘চিঁড়া নেই, চিঁড়ে আছে। ঠিকভাবে বলবেন। কথাটা চিঁড়া নয়, চিঁড়ে।’
পিতামহ তখন বলেছিলেন, ‘আধ সের চিঁড়ে দ্যান তবে, আর এক পোয়া গুড়ে।’

বলছিলাম সিমলা গিয়ে চিঁড়ে কেনার কথা।
চিঁড়ে বোঝানো যে কী সমস্যা…। ‘পেট কা বিমারি মে খায়া যাতা হ্যায়, দহি মিলাকে, চিঁড়া কা পোলাও ভি হোতা হ্যায়, কিসমিস-বাদাম মিলাকে, ঘিউ দিয়া করকে, এইসা এইসা করকে…’ কড়াইতে খুনতি নাড়ার অভিনয় করলাম। দোকানদার বলল, ‘পোহা বোলো, পোহা।’ একটা প্যাকেট দেখাল। হ্যাঁ, চিঁড়েই তো। ওটাকেই ‘পোহা’ বলে। বড়বাজার অঞ্চলে একটা দোকানে দেখেছিলাম। মেনুতে লেখা, ‘পোহা মিক্স্।’ পোহা-হালুয়া!
ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া বাঙালি-ঘরের ছেলে মাকে বলছে, ‘বিকেলে পোহা করে দেবে মা?’ বিয়েবাড়িতে খেয়াল করেছেন নিশ্চয়ই, ক্যাটারিংয়ের লোকেরা ভাত বলে না, বলে ‘রাইস’। রুটি তো কবেই ‘চাপাটি’ হয়ে গিয়েছে! এগুলো বোধহয় প্রমোশন। গরিব মধ্যবিত্তরা ঘরে পাউরুটি খায়, উচ্চবিত্ত হয়ে গেলেই ওটা হয়ে যায় ‘ব্রেড’!
সেই ছোটবেলায় আমাদের ভাড়াবাড়ির একতলায় একটা কলতলা ছিল। চৌবাচ্চার জলে আমরা মগ ডুবিয়ে গায়ে জল ঢালতাম। মেয়েদের জন্য একটা আড়াল-ঘর ছিল। সেই কলতলা ‘কলঘর’ হল। কলঘরের প্রথম প্রমোশন হল ‘বাথরুম’। বাথরুমে দুটো কল থাকত, শাওয়ারও। বাথরুম প্রমোশন পেয়ে হয়ে গেল ‘টয়লেট’। টয়লেটে একটা বেসিন থাকত– কমোড। এটার আরও একধাপ উন্নতি হয়ে ‘ওয়াশরুম’ হল। উন্নতি বিষয়ে বিশদ ধারণা নেই। উন্নতি হলে নাম পাল্টে যায়। ঘুষ ‘কাটমানি’ হয়, স্পিডমানি হয়। দালাল ব্রোকার হয়, আরও পরে এজেন্ট হয়। এজেন্টও কিছু একটা হয়, সঠিক জানি না।
ছোটবেলায় আমরা লজেন্চুস খেতাম। চুষে খেতে হয় বলে লেখার সময় লিখতাম– ‘লজেন্চুষ’। পরে জানলাম ওটা লজেন্স। আরও পরে, যখন নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্ত হলাম, তখন দেখলাম ওটা ‘টফি’ হয়ে গেল। কিন্তু গরিব ঘরের শিশুদের মধ্যে টফি আজও ‘লজেন’ হয়েই বেঁচে আছে।
আমেরিকায় প্রবাসী এক আত্মীয় আমাদের জন্য কিছু কুকিজ আর পারফিউম নিয়ে এলেন। কুকিজ যে প্রমোশন পাওয়া বিস্কুট, সেটা তখন প্রথম জানলাম। উনি বলেছিলেন, “তোদের জন্য কিছু ‘কুকিজ’ এনেছি রে…।” আমি হাবলার মতো তাকিয়ে। একটা কৌটো দিলেন, কৌটোর গায়ে আমাদের ‘বেকারি-বিস্কুট’-এর ছবি। আরও অনেক পরে ‘কুকি’র অন্য একটা অর্থও জানলাম। ইন্টারনেট থেকে যেসব তথ্য আহরণ করা হয়, তারমধ্যে কিছু জঞ্জাল থাকে, সেটার নামও নাকি ‘কুকি’!
গাঁ-ঘরের ‘ডিমভাজা’ শহুরে ঘরে হয়ে গেল ‘মামলেট’। বাড়িতে মামলেটই হত। রথের মেলায় চ্যাপটা কড়াইতে খুনতি দিয়ে আহ্বান-ধ্বনি তৈরি করে ডাকত– ‘মামলেট… মামলেট…’। পাড়ায় পাড়ায় ছোট ছোট চায়ের দোকান ছিল প্রচুর। ভিতরে ছ’-আট জন বসতেও পারত। ওইসব চা-দোকানের নাম হত– ‘শম্ভু কেবিন’, ‘জয় হিন্দ’। কেবিন ওরকম। দেওয়ালের কিছুটা জায়গায় কালো রং করা থাকত, ওখানে মেনু লেখা– টোস্ট, আলুর দম, মামলেট…। সেই মামলেট কী করে যেন ‘ওমলেট’ হয়ে গেছে! কোনও মেনুতেই মামলেট লেখা হয় না আর। ছোলা যখন ভাঙা থাকে, তখন ছোলার ডাল। পরে গোটা ছোলাটা চানা হয়ে গেল। তরকারি আগে সাঁতলানো হত। অল্প তেল দিয়ে হালকা করে ভাজাকে সাঁতলানো বলে। গাঁ-ঘরে এই সাঁতলানোকে বলত ‘ছ্যাঁকা’ দিয়ে নেওয়া। সেই ছ্যাঁকা এখন বড় প্রমোশন পেয়ে ‘সঁতে’ হয়ে গেছে। টিভি-তে শেফ বলে– ‘ব্রকোলি, বিনস, গাজর একটু সঁতে করে নিন।’ হ্যাঁ, রাঁধুনি প্রথম প্রমোশনে ‘কুক’ হয়েছেন, পরের বড় প্রমোশনে ‘শেফ’। রাঁধুনিরা ‘ছ্যাঁকা’ দিয়ে নেয়, শেফ ‘সঁতে’ করে। ‘সঁতে’ বোধ হয় ফরাসি শব্দ।
কৈশোরে ‘লাইন করা’ নামে শব্দবন্ধ ছিল, এখনও আছে, তবে তেমন নেই। ছেলে-মেয়ের তো প্রথমে ‘লাইন’ হত। পরে প্রেমও হতে পারত। এখন প্রেম না-হলেও সম্পর্ক তৈরি হয়, ওটার নাম ‘রিলেশনশিপ’। আগে প্রেম ব্যর্থ হলে ‘ল্যাং’ খাওয়া শব্দবন্ধ ব্যবহার হত। ল্যাং খাওয়া প্রমোশন পেয়ে ‘ব্রেক আপ’ হয়েছে। গাঁ-ঘরে মেয়েরা পোয়াতি হত। পোয়াতি প্রমোশন পেয়ে ‘প্রেগন্যান্ট’ হল। আজকাল ‘কনসিভ’ করে। মদ খাওয়াটা প্রমোশনে ‘ড্রিংক’ করা হয়েছে। মাল থেকে মদ, মদ থেকে ড্রিংক। আর মালের চাট হয়ে গেছে ‘সাইড ডিশ’, বা ‘ফুড’।
যখন প্রথম চাকরিতে ঢুকি, তখন দেখতাম পিওনরা ‘পরিবারের’ জন্য শখ করে কিছু কিনত। কেরানিদের স্ত্রীরা ছিল ওয়াইফ, অফিসারদের স্ত্রী বা মিসেস। আর পরিবারের অন্যদিক, মানে পুরুষেরা ‘ভাতার’, প্রমোশন পেয়ে ‘হাজব্যান্ড’, আরও পরে ‘লাইফ পার্টনার’ বা ‘হোমপার্টনার’, বা ‘বেটার হাফ’। ‘একটু মাঠ ফিরে আসি’ মানে হচ্ছে– ‘যাই, একটু পায়খানা করে আসি।’ ‘পায়খানা’র পূর্ববর্তী ধাপ ছিল হাগা। ওটাই হয়ে গেল ‘বড় বাথরুম’, আরও পরে ‘পটি’।

‘বই দেখা’ উঠে গিয়েছে। ‘যাই, হাতিবাগানে একটা বই দেখে আসি’– কেউ বললে আমাদের বুঝতে অসুবিধে হত না যে, উনি সিনেমা দেখতে যাচ্ছেন। আগে চলচ্চিত্র, ছিল সাহিত্যনির্ভর। বই মানে তাই সিনেমা। এখন সিনেমা নয় আর, মুভি। কিছুদিন আগে ফিল্ম দেখতে যাচ্ছি শুনতাম।
পুকুরে ঝপাং করে লাফিয়ে একটু সাঁতার দিয়ে উঠে আসা মানে ছিল ‘স্নান’। মেসবাড়িতে চৌবাচ্চায় মগ ডুবিয়ে গায়ে জল ঢালা, কিংবা কুয়োতে বালতি ডুবিয়ে গায়ে জল ঢালাও ছিল স্নান। স্নান উচ্চারণ করতে একটু অসুবিধে, তাই ছান বা ছ্যান। আমরাও ছান করতে কলতলায় যেতাম। কলতলা ‘বাথরুম’ হয়ে ‘ওয়াশরুম’ হয়ে গেল, আর ‘ছান করা’ হয়ে গেল ‘শাওয়ার নেওয়া’।
রুটি ক্রমশ চাপাটি হতে চলেছে। ছোলা হয়ে যাচ্ছে চানা। হলুদ হয়ে যাচ্ছে হলদি। এগুলো হিন্দি প্রভাব বটে, কিন্তু এই হীনম্মন্য বাঙালি সমাজে এই পরিবর্তন প্রমোশনের মতোই প্রায়।
…পড়ুন ব্লটিং পেপার-এর অন্যান্য পর্ব…
২১. বাঙালির বাজার সফর মানেই ঘ্রাণেন অর্ধভোজনম
২০. জাত গেল জাত গেল বলে পোলিও খাব না!
১৯: ধোঁয়া আর শব্দেই বুঝে গেছি আট-তিন-পাঁচ-দেড়-দেড়!
১৮: নামের আগেপিছে ঘুরি মিছেমিছে
১৭: টরে টক্কার শূন্য এবং ড্যাশের সমাহারে ব্যাঙের ‘গ্যাগর গ্যাং’ও অনুবাদ করে নিতে পারতাম
১৬: ছদ্মবেশী পাগলের ভিড়ে আসল পাগলরা হারিয়ে গেল
১৫. ধূমপান নিষেধের নিয়ম বদলান, আকাশবাণীর স্টেশন ডিরেক্টরকে বলেছিলেন ঋত্বিক ঘটক
১৪. এমএলএ, এমপি-র টিকিট ফ্রি, আর কবির বেলা?
১২. ‘গাঁধী ভগোয়ান’ নাকি ‘বিরসা ভগোয়ানের পহেলা অবতার’
১১. কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্টের চক্করে বাঙালি আর ভোরবেলা হোটেল থেকে রওনা দেয় না
৫. তিনটে-ছ’টা-ন’টা মানেই সিঙ্গল স্ক্রিন, দশটা-পাঁচটা যেমন অফিসবাবু
৪. রাধার কাছে যেতে যে শরম লাগে কৃষ্ণের, তা তো রঙেরই জন্য
৩. ফেরিওয়ালা শব্দটা এসেছে ফার্সি শব্দ ‘ফির’ থেকে, কিন্তু কিছু ফেরিওয়ালা চিরতরে হারিয়ে গেল
২. নাইলন শাড়ি পাইলট পেন/ উত্তমের পকেটে সুচিত্রা সেন
১. যে গান ট্রেনের ভিখারি গায়কদের গলায় চলে আসে, বুঝতে হবে সেই গানই কালজয়ী
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
