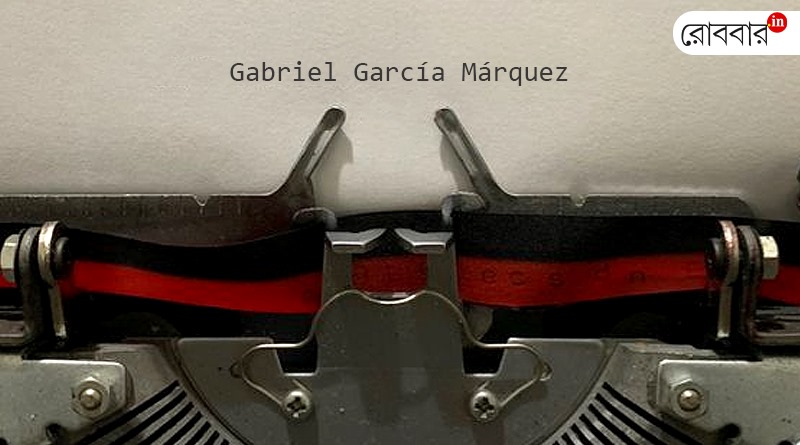
‘লেখক চাই’ নামে আরেকটা রিপোর্টাজে, সে-বছরই, ওই একই কাগজে শুনিয়েছেন টাইপরাইটার বেগড়বাঁই করার গল্প। মন্ট্রিয়লে গিয়ে যেমন তাঁকে নতুন টাইপরাইটার কিনতে হয়েছিল। কারণ তাঁর পুরোনো টাইপরাইটারটির সঙ্গে হোটেলের ভোল্টেজ মিলছিল না। ওই বছরই কুবাতে গিয়ে একই রকম ঝঞ্ঝাট পোহাতে হল। সেবার দু’-দুবার টাইপরাইটার বদলেও কাজ হচ্ছিল না। কেন-না মার্কেসের হাত একেবারেই চলছিল না নতুন যন্ত্র দুটোতে।

লেখককে স্বস্তি দেয় না সাদা পাতা। শক্তি চট্টোপাধ্যায় যেমন লিখেছেন, ‘শাদা পাতা। আক্রমণ করো।/ তীর যোথো কাঠের ধনুকে,/ পুরনো বিষাক্ত তীরে আক্রমণ করো–।’ আবার অতলান্তিকের ওপারে গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসকে যখন জিগ্যেস করা হয়েছিল সাদা পাতা তাঁকে কতটা আতঙ্কিত করে? জবাবে তিনি বলেছিলেন, শুধু আতঙ্কই নয়, একসময় সাদা পাতা দেখলে ক্লস্ট্রোফোবিয়া হত তাঁর। কিন্তু সাহিত্যজীবনে যাঁকে ‘ওস্তাদ’ বলে মেনে এসেছেন, সেই আর্নেস্ট হেমিংওয়ের একটা টোটকা ব্যবহার করে তিনি সে-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়েছেন। হেমিংওয়ে কোথাও বলেছিলেন, একবার লিখতে বসলে তখনই উঠবে যখন বুঝতে পারছ পরের দিন প্রথম লাইনটা কী লিখবে।
যে-বছর নোবেল পুরস্কার পেলেন গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস, সেই ১৯৮২-তেই প্লিনিয়ো আপুলেইয়ো মেন্দোসার সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ কথোপকথন ‘পেয়ারার গন্ধ’ নামে প্রকাশিত হয়। এ শুধু লেখক গার্সিয়া মার্কেসের পোশাকি সাক্ষাৎকার নয়, বরং তাঁর অন্তর্জগতেরও অনেকটা ফুটে উঠেছে বইটিতে। কেবল লেখককে খুশি করার মতো প্রশ্ন নয়, মেন্দোসা এমন প্রশ্ন করেছেন যেখানে গার্সিয়া মার্কেসের স্ববিরোধী মন্তব্যও আছে। আর মার্কেস উত্তরও দিয়ে গিয়েছেন রাজার মতো মেজাজে। যেমন সংশোধন-কাটাকুটির প্রসঙ্গ। মার্কেস বলছেন, অল্পবয়সে একটানে গোটাটা লিখে ফেলতেন। তারপর আবার একবার কপি করতেন। প্রয়োজনে ফের একবার। কিন্তু পঞ্চাশ-উত্তীর্ণ বয়সে তিনি লাইন ধরে ধরে সংশোধন করতে করতে এগোন। যাতে দিনের শেষে অন্তত একটা নিখুঁত পাতা হাতে থাকে। কোনও কাটাকুটি, ঢ্যাঁড়া মেরে বা তারা চিহ্ন দিয়ে অন্য জায়গায় লেখা পাণ্ডুলিপি নয়। একেবারে ছাপতে পাঠিয়ে দেওয়ার মতো একটা পাতা। আর এই করতে গিয়ে গুচ্ছের কাগজ নষ্ট হয় তার। স্রেফ ছিঁড়ে ফেলে দেন অপছন্দের কাগজ। এরপরই মেন্দোসা কথার সুতো ধরে তাঁকে সরাসরি প্রশ্ন করেন, ‘তুমি হাতে লেখো না? সবসময় টাইপ করো না কি?’ সপাটে উত্তর দেন মার্কেস, ‘সবসময়। বিশুদ্ধ ইলেকট্রিক টাইপরাইটারে। টাইপ করতে করতে যখন মনে হয় ঠিক এগোচ্ছে না লেখাটা, বা জায়গাটা তেমন জমল না, কিংবা টাইপ করতে গিয়ে কোনও ভুল বোতামে হাত দিয়ে ফেলেছি তখন কাগজটা ছিঁড়ে ফেলে নতুন কাগজ লাগিয়ে নিই টাইপরাইটারে।’ মেন্দোসা ফের খোঁচান, ‘কিন্তু বহু লেখকেরই টাইপরাইটারে অ্যালার্জি আছে যে !’ মার্কেস ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে বলেন, ‘টাইপরাইটারের সঙ্গে আমার বহুকালের প্রেম। এখন ইলেকট্রিক টাইপরাইটার ছাড়া আমি আর লিখতেই পারি না। আসলে কী জানো দোস্ত, জৈবিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে বৈরাগীর মতো এক কাপড়ে, না খেয়ে-দেয়ে, দারিদ্রে ধুঁকতে-ধুঁকতে মহান সাহিত্য রচনা করার রোম্যান্টিক ধারণায় আমার আদৌ কোনও বিশ্বাস নেই’। উলটে তাঁর মনে হয় পেটে খাদ্য, হাতের কাছে উত্তম পানীয় আর একটা ইলেকট্রিক টাইপরাইটার থাকলেই লেখা ভালো হয়।

মার্কেসের লেখায় টাইপরাইটারের খোঁজ করতে গিয়ে সবচেয়ে পুরনো যে, উল্লেখ চোখে পড়ছে সেটা ১১ এপ্রিল ১৯৫০ সালে বাররানকিয়ার ‘এল এরাল্দো’ পত্রিকায় প্রকাশিত লেখা, ‘বিষয়ের সন্ধানে’। মার্কেসের তখন ২৩ বছর। এর ঠিক মাসদুয়েক আগে তাঁর জীবনযাত্রা ও অর্থনীতি কেমন ছিল তার বিস্তৃত বিবরণ আছে আত্মজীবনী ‘গল্পটা বলব বলেই তো বেঁচে আছি’-র শুরুর দিকের কয়েকটি পাতায়। তখন তাঁর আক্ষরিক অর্থে ‘ভোজনং যত্রতত্র শয়নং হট্টমন্দিরে’। হট্টমন্দির, কারণ কবে কোথায় সন্ধে নামে কে জানে? ততদিনে ছয় সিমেস্টার আইনের ক্লাস করে পড়াটা চিরকালের মতো ছেড়ে দিয়ে কোর্টে যাওয়ার সাঁকো পুড়িয়ে দিয়েছেন। পরনে জিনসের প্যান্ট, ফুল ফুল ছাপ দেওয়া শার্ট আর পায়ে তীর্থযাত্রীদের মতো চটি। নিজের জীবনটা বইয়ে দিচ্ছেন বাররানকিয়া আর কার্তেহেনা দি ইন্দিয়াসের মধ্যে। দিনে ৬০টা সিগারেট ফোঁকেন, দু’-বার গনোরিয়ার ছোবল সামলেছেন। ‘এল এরাল্দো’তে দৈনিক ধারাভাষ্য লিখে তিন পেসো করে পেতেন। আর কোনও স্টাফ রিপোর্টারের অনুপস্থিতিতে সম্পাদকীয় লিখতে হলে চার পেসো। যদিও পত্রিকা দপ্তরে তখনই তাঁর ৫০ পেসো ধার হয়ে আছে। এইরকমভাবেই জীবন ইয়ার্কি করছিল তাঁর সঙ্গে।
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
মার্কেসের লেখায় টাইপরাইটারের খোঁজ করতে গিয়ে সবচেয়ে পুরোনো যে উল্লেখ চোখে পড়ছে সেটা ১১ এপ্রিল ১৯৫০ সালে বাররানকিয়ার ‘এল এরাল্দো’ পত্রিকায় প্রকাশিত লেখা, ‘বিষয়ের সন্ধানে’। মার্কেসের তখন ২৩ বছর। এর ঠিক মাসদুয়েক আগে তাঁর জীবনযাত্রা ও অর্থনীতি কেমন ছিল তার বিস্তৃত বিবরণ আছে আত্মজীবনী ‘গল্পটা বলব বলেই তো বেঁচে আছি’-র শুরুর দিকের কয়েকটি পাতায়। তখন তাঁর আক্ষরিক অর্থে ‘ভোজনং যত্রতত্র শয়নং হট্টমন্দিরে’।
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
‘বিষয়ের সন্ধানে’ নামে লেখাতে এই জীবনেরই ছায়া। রাতে বসে পরদিনের লেখার বিষয় খোঁজা। পাগলের মতো সিগারেট খাওয়া। ছটফট করা। আত্মকথনের ঢঙে লেখা সে-রিপোর্টাজের শেষ দিকে এসে বলছেন, ‘‘আরেকটা সিগারেট জ্বালিয়ে ভয়ে ভয়ে আবিষ্কার করুন যে এটাই প্যাকেটের শেষ সিগারেট। এবং দেশলাইয়ের কাঠিটাও শেষতম। রাত নামছে, ঘড়ির কাঁটা দুটো দু’-হাত ছড়িয়ে ঘুরছে তো ঘুরছেই, ক্যালিবানের মতো নেচেই চলেছে সারাক্ষণ। এবার কী হবে? একজন মাঝারিমানের মুষ্টিযোদ্ধার মতো তোয়ালেটা মেঝেতে আছড়ে ফেলুন। সাংবাদিকতার সঙ্গে মুষ্টিযুদ্ধের মিল সব থেকে বেশি কি না। কেবল বাড়তি হল এই যে, আপনার টাইপরাইটারটি সব সময় জেতে, আর মুশকিল হল আপনাকে আদৌ মেঝেয় তোয়ালে আছড়াতে দেওয়া হবে না। হায় রে, জিরাফের মতো লম্বা কোনও কলাম আপনার আর লেখা হয়ে উঠল না।’’ আসলে টাইপরাইটারটি তাঁর কাছে শরীরের অংশের মতোই ছিল। বাইরে থেকে চাপানো কিছু নয়। পরম বন্ধুর মতো। যার কাঁধে বিষণ্ণ মুখ ঘষা যায়।

এর অনেক পরে ১৭ এপ্রিল ১৯৮২-তে মাদ্রিদের ‘এল পাইস’ পত্রিকায় তিনি লিখছেন ‘আমার অন্য আমি’ নামে একটি রিপোর্টাজ। যেখানে চতুর্দিকে তারই সমনামী লোকজনের কথা, যারা নাকি তাঁর নাম ভাঁড়িয়ে বক্তৃতা করে– সাক্ষাৎকার দেয়– বন্ধুর বাড়ির বইয়ের তাকে গার্সিয়া মার্কেস হয়ে সইও করে থাকে। এমনকী, মার্কেস দম্পতির যে এতকালের সাধ একটি কন্যাসন্তানের– সেই কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হবার ভুল খবরও ছড়ায়। এরপরই অভিমানী মার্কেস লেখেন, ‘সে নিজের কাল্পনিক অস্তিত্ব নিয়েই মশগুল থাকবে, উজ্জ্বল এবং উদ্ভট, নিজের ব্যক্তিগত প্রমোদ তরণী বা ব্যক্তিগত বিমান নিয়ে কিংবা তার রাজকীয় প্রাসাদে রমণীয় শ্যাম্পেন-স্নানে ব্যস্ত থাকবে নিজের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীকে ধরাশায়ী করতে। সে আমার কিংবদন্তি আরও বাড়িয়ে চলবে, বিরাট বড়লোক হবে, চিরযৌবন লাভ করবে এবং শেষ অশ্রুবিন্দুটি গড়িয়ে পড়ার আগে পর্যন্ত খুশি থাকবে। এদিকে আমি বিবেকদংশনে পীড়িত হতে হতে এই বিভ্রম ও অতিরেক থেকে দূরে নিজের টাইপরাইটারটির সামনে বুড়ো হব। প্রত্যেক রাতে আমার চিরকেলে বন্ধুদের সঙ্গে চেনা মদ খেতে যাব এবং সান্ত্বনাবিহীন ভাবে পেয়ারার গন্ধের অভাববোধে তাড়িত হব। কারণ সবচেয়ে অন্যায় ব্যাপারটা হল: আমার অন্য আমিটাই যত খ্যাতি উপভোগ করে আর জীবনের যত ঝঞ্ঝাট সামলাতে হয় আমাকে।’ সেই একা হওয়ার মুহূর্তে, অক্ষরপ্রেমিকের শেষ অবলম্বন একখানি টাইপরাইটার। যা একই সঙ্গে তাঁর প্রেম ও পরিত্রাণ। বেরঙিন সকাল আর উচ্ছ্বল রাতের অবলম্বন। একা একা কথা বলার সঙ্গী। যে হাত ধরে টেনে বসায় লেখার টেবিলে। রাজ্যের ক্লান্তিতে যখন হাই ওঠে ক্রমাগত, তখন ম্যাজিকের মতো লেখায় ফেরায়। টাইপরাইটারেরও মন আছে। মেধাবী সে তো বটেই।
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
আরও পড়ুন: মার্কেজের শেষ আলো
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
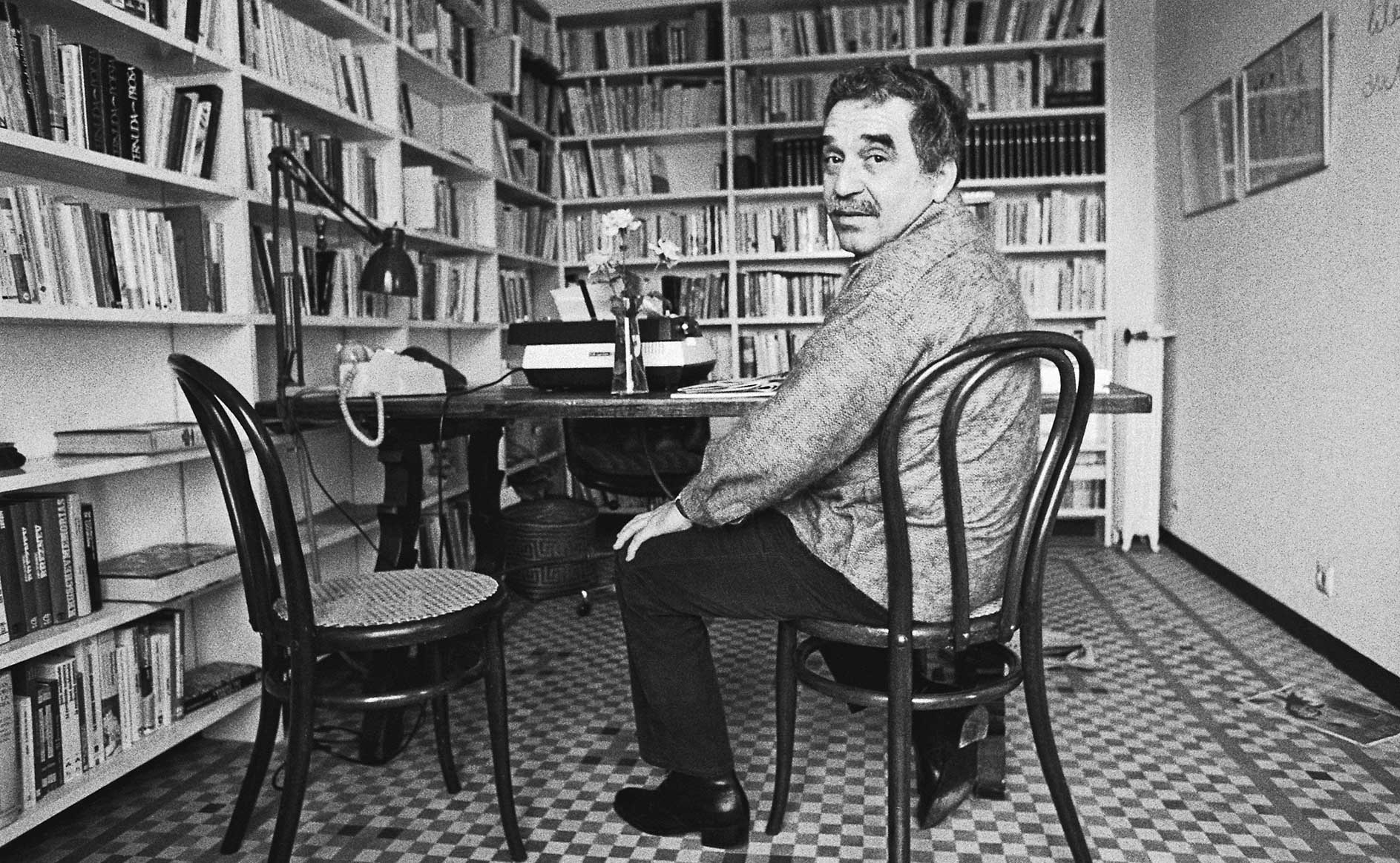
কিন্তু শুধুই ‘নমো যন্ত্র নমো যন্ত্র’ গেয়ে পঞ্চভূত বেঁধে ফেলা ইন্দ্রজালতন্ত্রের কথা বলে গেলেই তো চলে না। যন্ত্রের যন্ত্রণা নেই ? ‘লেখক চাই’ নামে আরেকটা রিপোর্টাজে, সে-বছরই, ওই একই কাগজে শুনিয়েছেন টাইপরাইটার বেগড়বাঁই করার গল্প। মন্ট্রিয়লে গিয়ে যেমন তাঁকে নতুন টাইপরাইটার কিনতে হয়েছিল। কারণ তাঁর পুরোনো টাইপরাইটারটির সঙ্গে হোটেলের ভোল্টেজ মিলছিল না। ওই বছরই কুবাতে গিয়ে একই রকম ঝঞ্ঝাট পোহাতে হল। সেবার দু’-দুবার টাইপরাইটার বদলেও কাজ হচ্ছিল না। কারণ মার্কেসের হাত একেবারেই চলছিল না নতুন যন্ত্র দুটোতে। শেষে ওরা তাঁকে একটা ইলেকট্রিক টাইপরাইটার এনে দেয়। কিন্তু সে যন্ত্রের কায়দা-কানুন এতই আধুনিক যে, শেষমেশ তিনি আরাকাতাকার প্রাইমারি স্কুলবেলায় যেমন চৌখুপ্পি কাটা কাগজে হাতের লেখা অভ্যেস করতেন, ঠিক সেরকম কাগজে লিখতে বাধ্য হন।
তবে আজীবন তারুণ্যে ভরপুর মার্কেস কখনও কম্পিউটারে হাত দেননি তা নিশ্চয়ই নয়। টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয় ৪০টা প্যাকিং বাক্স-ভরতি তাঁর ব্যবহৃত যেসব জিনিস ২২ লাখ মার্কিন ডলারে কিনে রেখেছে সেখানে পাণ্ডুলিপি, ছবির অ্যালবাম, স্ক্র্যাপবুক, কম্পিউটারের সঙ্গে একখানা টাইপরাইটারও আছে। জানি না, সে-ঘরে রাতে ‘পেয়ারার গন্ধ’ পাওয়া যায় কি না, গভীর রাতে এখনও ঝড় ওঠে কি না দশ আঙুলে।
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
