
গাছের প্রাণ আছে একথাটা আমরা কেবল মুখস্থ করি। বিজ্ঞান হয়ে ওঠে ‘সংকলিত তথ্যের ভিড় শুধু’। বিজ্ঞান হয়ে ওঠে কিছু সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য মুখস্থ করার একেকটা বই। তেমনভাবে আলোচিত হয় না আন্তঃসম্পর্কের কথা। গোপালচন্দ্র সারাজীবন কাটিয়েছেন এই আন্তঃসম্পর্ককে বুঝতে। অপরকে জানব বলেই বেঁচে থাকা। না-জানা থেকে হয় ভালোবাসার অভাব। ভালোবাসার অভাবে ধ্বংস। আমাদের মনে তাই অজস্র না জানা, ভয়, ভালোবাসার অভাব। খেতখামারের বেশিরভাগ পোকাকেই আমরা বলি ‘পেস্ট’ বা ফসল বিনষ্টকারী পোকা। গোপালচন্দ্রের সময়েও তাই ছিল। কানকোটারির জীবন কথায় দেখা যায় বাগানের মালিকেরা মনে করে কানকোটারি পোকাই সব ফুল ফল ছিদ্র করে নষ্ট করেছে এদিকে গোপালচন্দ্র দেখেন পোকার পেটে যারা রয়েছে তারা সবাই ফসলখেকো। অর্থাৎ ‘কানকোটারি’ সেই অর্থে মালিকের বন্ধু।

রাতে ফোটা ফুলের মুখে চড়া হ্যালোজেনের আলো জ্বেলে রাখেন ফুলের সৌন্দর্যপ্রিয় মালিক। প্রবল আলোকদূষণে ভালো করে চাঁদ-তারা দেখতে না-পেয়ে জলে-স্থলে দিশা হারায় কচ্ছপ, গুবরে পোকা, তিমিদের মতো প্রাণীরা; প্রজনন ব্যহত হয় জোনাকিদের। গুরুত্বপূর্ণ পরাগমিলনকারী স্তন্যপায়ী প্রাণী বাদুড় বিপন্ন হয়ে পড়ে। নিটোল ও প্রচুর ফলনের আশায় খেতজুড়ে মনস্যান্টো, সিঞ্জেন্টা, শেল, বায়ার, কারগিল কোম্পানির পতঙ্গনাশক বিষ ছড়ানোর ফলে মারা যায় প্রচুর পাখি, মৌমাছি, প্রজাপতি, মথ ও অন্য নানা প্রাণী। এরই মাঝখানে প্রণম্য বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের জন্মদিবস আজ। তাঁর আর কোনও বইয়ের নাম আমরা জানি বা না-জানি, ‘বাংলার কীটপতঙ্গ’ বইটার কথা অনেকেই জানেন।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যর লেখালিখি শুধু বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও ঘটনাবলির নীরস বিবরণ হয়ে থাকেনি। দিনের পর দিন মাঠ-ঘাট ঘুরে, বহু বিনিদ্র রাত গবেষণাগারে কাটিয়ে গবেষণালব্ধ ফল ব্যবহার করে যা লিখেছেন– তা উচ্চমানের সাহিত্য হয়ে উঠেছে। উক্ত বইয়ের একটা অধ্যায়ের নাম, ‘ভীমরুলের রাহাজানি’। নাম শুনলে বোঝা যায়, বেজায় রসিক ছিলেন আমাদের গোপালবাবু। পিঁপড়েদের দলের কাছে বসে থেকে এক ব্যাঙের মাথামোটা সৈনিক পিঁপড়ে শিকার থেকে শুঁয়োপোকা-বোলতার দ্বৈরথ হয়ে সে লেখা চলে যায় একেবারে বোলতার চাকে পুত্তলী বা পিউপা শিকার করতে আসা ভীমরুলের আক্রমণ বর্ণনায়। এমন নিঁখুত ও রোমাঞ্চকর সেই বর্ণনা যে, পড়তে পড়তে আসন থেকে উঠে আসবে আমাদের শরীর।
প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় আজীবন বিজ্ঞানচর্চা করে দেখিয়ে গেছেন গোপালবাবু। প্রজাপতির নাম দিয়েছেন ‘দুধলতা’ অথবা ‘লৌ-ফোঁট’ প্রজাপতির বাংলা নাম দিয়েছেন ‘রক্ততিলক’। এই দুই নামই দুই প্রজাপতির জন্মবৃত্তান্ত, আচার-আচরণ বা আত্মরক্ষা করার কৌশলের সঙ্গে যুক্ত। আমরা মানুষ– স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে একটা প্রজাতি, কিন্তু নিজেদের প্রজাতি হিসাবে ভাবার চেয়ে আমরা ‘Race’ হিসাবে ভাবতে পারি বেশি। ধর্ম, ভাষা, বর্ণ, শ্রেণিভেদে আমাদের বিভাজনের শেষ নেই। গোপালচন্দ্র পৃথিবীর অন্যান্য সমাজবদ্ধ জীব, যেমন– মৌমাছি, বোলতা, ভীমরুলদের জীবন নিয়ে গভীরভাবে চর্চা করে গিয়েছেন। এবং তার পাশাপাশি মানুষের সমাজ ও সমাজবদ্ধতাকে রেখে প্রশ্ন করেছেন, মানুষের সমাজ কি মৌমাছি বা পিঁপড়েদের সমাজের মতোই না অন্যরকম? গোপালচন্দ্র আধুনিক মানুষের অহং নয়, স্পিসিজ বা প্রজাতির চোখ, কৌতূহল ও প্রশ্ন নিয়ে গিয়েছেন অন্যান্য স্পিসিজ বা প্রজাতির কাছে। মৌমাছি, বোলতা, ভীমরুল, গুবরেপোকা– এরা প্রত্যেকে মানুষের চেয়ে বয়সে অনেক বড়। প্রত্যেকেই ভূতাত্ত্বিক সময়রেখার দীর্ঘ স্মৃতি বহন করছে। সেই স্মৃতির মধ্যেই আছে তাদের ও তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছুর বিবর্তনের ইতিহাস। যেমন মৌমাছিদের আবির্ভাব, গুপ্তবীজী উদ্ভিদ ও বিশ্বজুড়ে তাদের নানা বর্ণ, আকার, ঘ্রাণের ফুলের আবির্ভাব, ফুল ও মৌমাছিদের সম্পর্ক ও সহ-অভিযোজন।
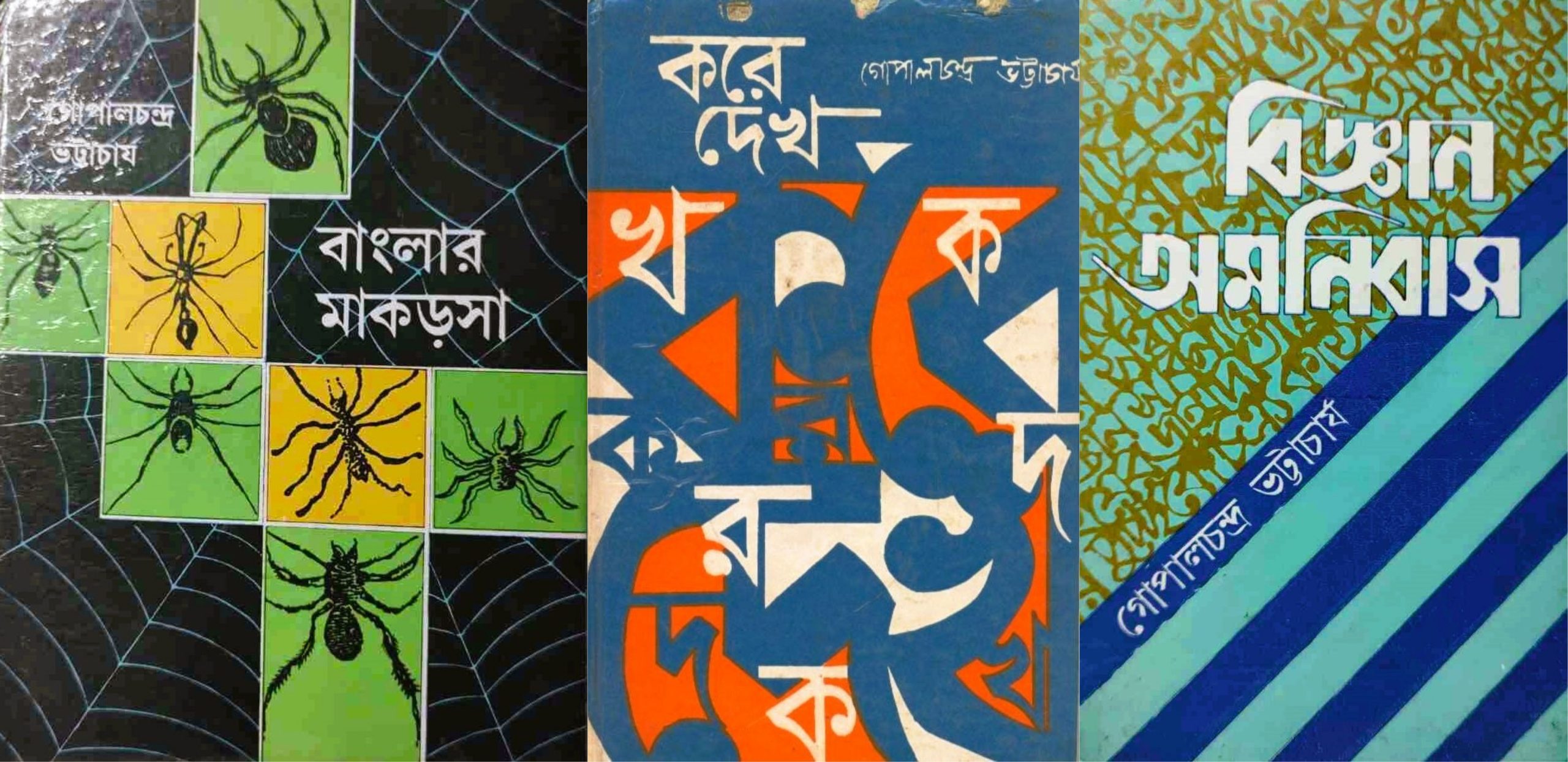
একলা মানুষ অপার বিস্ময়ে চলতে চলতে দেখছেন নালসো পিঁপড়েদের জীবনবৃত্তান্ত ও আচার আচরণ। পিঁপড়ে, মৌমাছি, বোলতাদের সমাজবদ্ধ জীবন দেখতে দেখতে তাঁর মনে পড়ছে রাজতন্ত্র, দাসপ্রথা ও পুঁজিবাদী সমাজে মানুষের অবস্থা। এক অধ্যায়ে তিনি লিখেছেন:
‘মানুষেরা বুদ্ধিমান এবং কৌশলী হলেও পিঁপড়ে অথবা মৌমাছির মতো সুনিয়ন্ত্রিত একটা পাকাপোক্ত সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে নি। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি এবং ব্যক্তিগত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। প্রত্যেকেই সুবিধামত সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে থাকে। তার ফলেই দাসত্ব প্রথা, বাধ্যতামূলক বেগার খাটা এবং অন্যান্য দুর্নীতিমূলক প্রথার উদ্ভব ঘটেছিল।’ (শ্রমিক পিঁপড়ের জন্ম রহস্য, বাংলার কীটপতঙ্গ)।
অন্যান্য সমাজবদ্ধ জীবদের জীবন ও সমাজবদ্ধ মানুষের জীবন পাশাপাশি রেখে গোপালচন্দ্র আমাদের সামনে রেখে গিয়েছেন মানবিক কিছু প্রশ্ন। পিঁপড়ে, মৌমাছিদের কাছ থেকে শিখতে পারলে মানুষের ভালো হত।
গাছের প্রাণ আছে একথাটা আমরা কেবল মুখস্থ করি। বিজ্ঞান হয়ে ওঠে ‘সংকলিত তথ্যের ভিড় শুধু’। বিজ্ঞান হয়ে ওঠে কিছু সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য মুখস্থ করার একেকটা বই। তেমনভাবে আলোচিত হয় না আন্তঃসম্পর্কের কথা। গোপালচন্দ্র সারাজীবন কাটিয়েছেন এই আন্তঃসম্পর্ককে বুঝতে। অপরকে জানব বলেই বেঁচে থাকা। না-জানা থেকে হয় ভালোবাসার অভাব। ভালোবাসার অভাবে ধ্বংস। আমাদের মনে তাই অজস্র না-জানা, ভয়, ভালোবাসার অভাব। খেতখামারের বেশিরভাগ পোকাকেই আমরা বলি ‘পেস্ট’ বা ফসল বিনষ্টকারী পোকা। গোপালচন্দ্রের সময়েও তাই ছিল। ‘কানকোটারির জীবনকথা’য় দেখা যায় বাগানের মালিকেরা মনে করে কানকোটারি পোকাই সব ফুল-ফল ছিদ্র করে নষ্ট করেছে। এদিকে গোপালচন্দ্র দেখেন পোকার পেটে যারা রয়েছে তারা সবাই ফসলখেকো। অর্থাৎ ‘কানকোটারি’ সেই অর্থে মালিকের বন্ধু। এই না-বোঝার জন্যেই কোটি কোটি মৌমাছি-ব্যাং-সাপ-প্যাঁচা-ইঁদুর মারা যায়। ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয় আর বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য হারিয়ে গিয়ে বিপদ ঘটে।
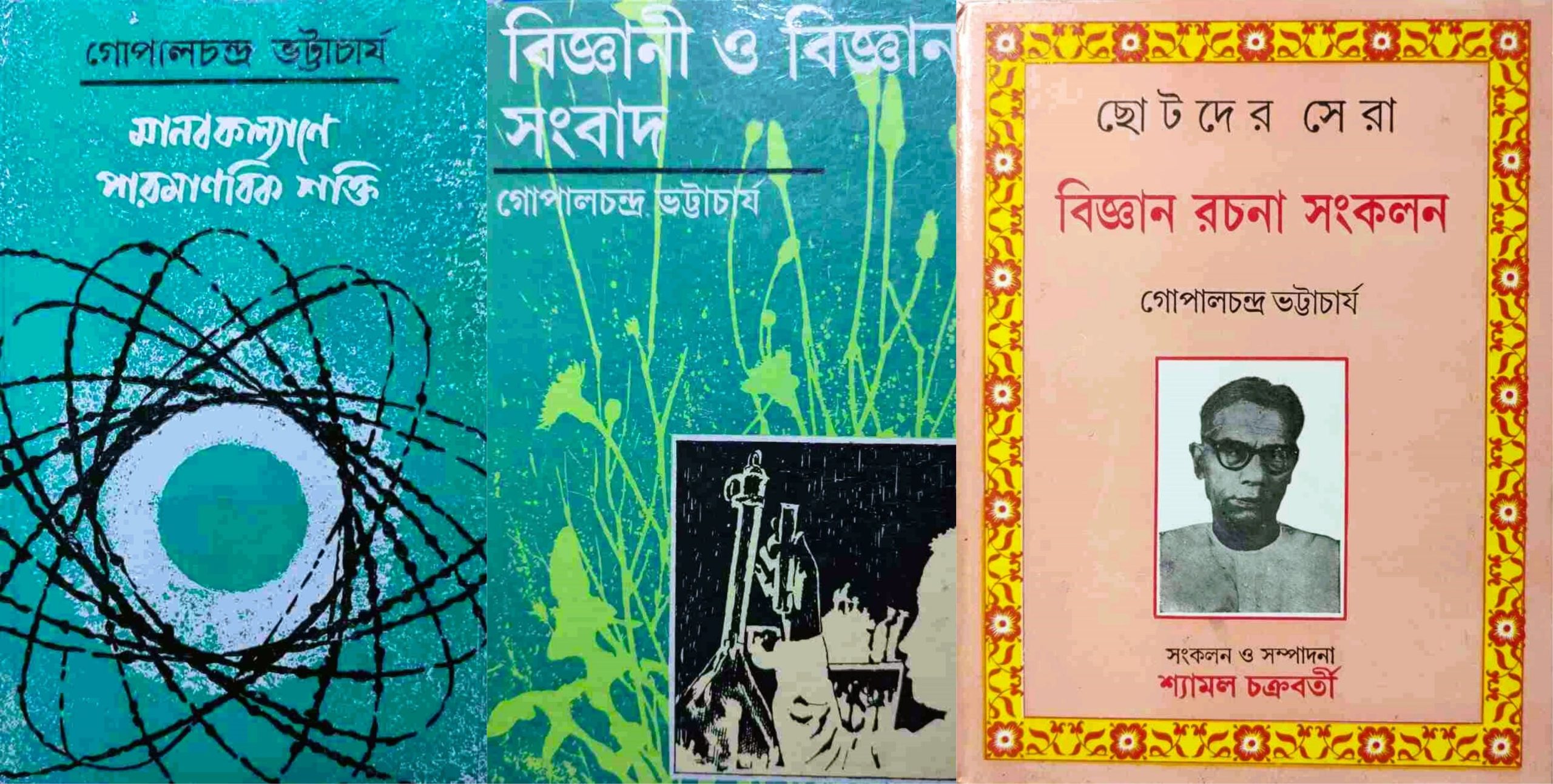
গোপালচন্দ্র এমন করে ভালোবাসতে পেরেছিলেন জীবনকে। ‘Utilitarian Abuse’-এর বাইরে গিয়ে সহজেই দেখতে পেয়েছিলেন দুনিয়াটাকে। তাই হ্যারিকেনের আলোয় বসে আনন্দে ডানা নাড়াতে থাকা স্ত্রী ও ঘুরে ঘুরে শব্দ করে চলা মিলনোন্মুখ পুরুষ কানকোটারির সংগীতকে শুনে তাঁর মনে হয়েছিল এই হল তাদের পূর্বরাগ।
সমস্ত লেখা ঘুরে টেলিমাইক্রোস্কোপ, আতশকাচের মতো সামান্য দু’-চারটে যন্ত্রের নামই পাওয়া যায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছেন গভীর গভীরতর পর্যবেক্ষণে। তাক লাগানো সেই পর্যবেক্ষণ থেকে কত যে নির্ভুল বোঝাপড়া তার হয়েছে। তিনি ঠিক বুঝেছেন প্রহরী মৌমাছিরা তাদেরই চাকের মৌমাছিদের পরখ করে গায়ের গন্ধ দিয়ে। গন্ধ চেনা হলে তবেই সে সহকর্মীদের চাকে প্রবেশ করতে দেয়।
মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার সঙ্গে সঙ্গে আপ্রাণ আজীবন যা করে গেছেন, তা হল সকলের জন্য বিজ্ঞানচর্চা করার উৎসাহ প্রেরণ করা। বিজ্ঞান কি শুধু সে-ই জানবে, যে জুলজি, বটানি, এন্টোমোলজি পড়বে স্কুল কলেজে? বাকিরা তাহলে স্কুল কলেজে না-পড়লে জানতে পারবে না? কোনও সুস্থ সমাজে এমন হওয়ার কথা না-হলেও আজ এই বৈষম্য বাড়তে বাড়তে এক সর্বনাশের দিকে গিয়েছে। জনজীবন বিচ্ছিন্ন এক জ্ঞানচর্চার পরিবেশ তৈরি হয়েছে ফলে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক, প্রাকৃতিক জ্ঞান, বিভিন্ন প্রাকৃতিক বা জলবায়ুগত সমস্যাকে বুঝতে বেশ অসুবিধা হচ্ছে। সমাধান হিসাবে যা ভাবা হচ্ছে তা খণ্ডজ্ঞান থেকে আসার ফলে সমাধানের হাত ধরে নতুন ও গুরুতর সমস্যা এসে উপস্থিত হচ্ছে।
ঘরে ফেরার রাস্তাটাই সবচেয়ে কম চিনি। তাকিয়ে থাকি কিন্তু দেখা হয় না। অটোমেশন ও প্রশ্নহীনতা আমাদের নিয়ে যাচ্ছে এজন্মের অমূল্য সম্পদ বিস্ময় থেকে পাকাপাকিভাবে আমাদের বিচ্ছেদ ও আত্মার মৃত্যুর দিকে। এখান থেকে ঘুরে দাঁড়াতে, মন থেকে ‘আনন্দরূপমৃতম যদ্বিভাতি’ কথাটা বলতে আজ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের মনন, দর্শনকে জানার, তাঁর লেখাগুলিকে পড়ার অত্যন্ত দরকার হয়ে পড়েছে।
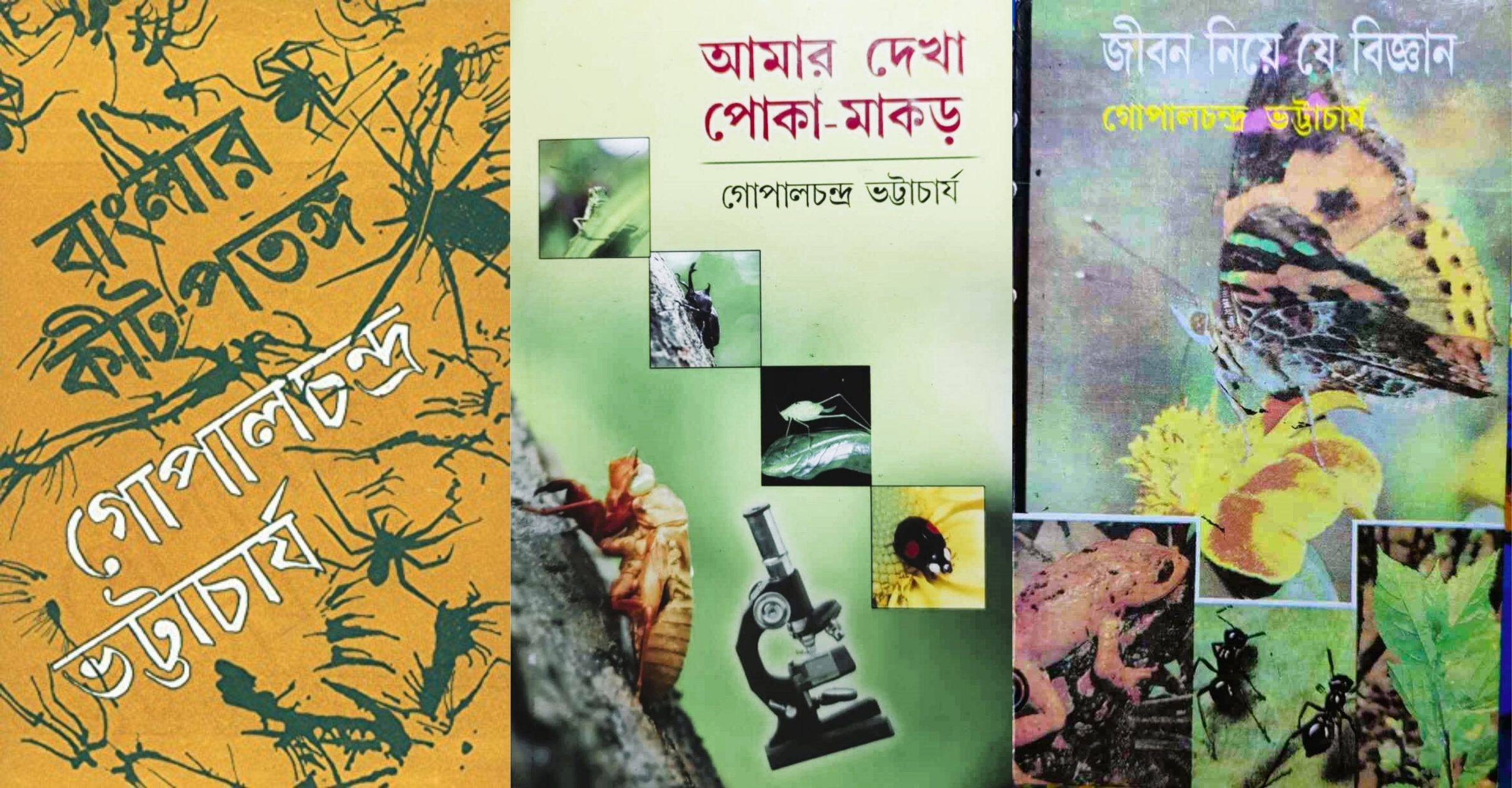
১৪ বছর আগে গোপালচন্দ্রের সাধের বোস ইন্সটিটিউটে এক সেশনে অধ্যাপক পুনর্বসু চৌধুরী এক বিজ্ঞানীর ছবি দেখিয়ে তাঁর নাম জানতে চেয়েছিলেন। ৯৪ জন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে থেকে পিনপতনের নৈঃশব্দ্য ভেঙে সুন্দরবন থেকে সদ্য কলকাতায় পড়তে আসা এক ছাত্র বলে উঠেছিলো, ‘আমি চিনি। ওঁর নাম গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য।’
আজ এইদিনে সেই বৃত্ত সম্পূর্ণ হল।
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
