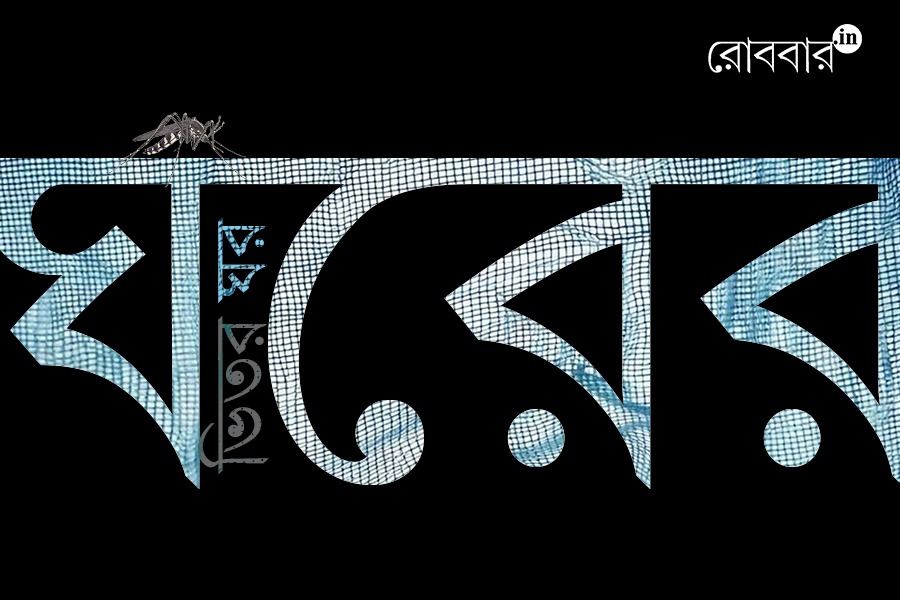
মেসজীবন কিংবা ছাপোষা মধ্যবিত্ত ঘরে মশারির ব্যবহার আমরা বাংলা গল্পে, সিনেমায় বা আত্মজীবনীতেও পাই। কিন্তু শহুরে ধনীরা মনে হয় মশারি থেকে বাঁচতে চাইছিলেন অনেক দিন ধরেই। উনিশ শতকের প্রেক্ষাপটে লেখা ‘সেই সময়’ উপন্যাসে নবীন কুমার ওরফে কালীপ্রসন্ন সিংহ মশা তাড়ানোর পরিকল্পনা করেন। সাহেবদের অনুকরণে শয়নকক্ষের জানলায় তিনি লাগান মশারির মতো সূক্ষ্ম তারের জাল।
গ্রাফিক্স: দীপঙ্কর ভৌমিক

সম্প্রতি জনৈকা বিদেশিনীর এক লেখায় ভারত-সম্পর্কিত একটি বিচিত্র তথ্য উঠে আসে। তিনি ভারত ভ্রমণ সেরে স্বদেশে ফিরে জানান যে, এখানকার কোনও হোটেলে থাকাকালীন তিনি মশারির সুব্যবস্থা পাননি। অন্যান্য ট্রপিকাল দেশে অতিথি আপ্যায়নের ব্যবস্থা দেখে তাঁর অভিযোগ– কেন দিল্লি, ওড়িশা বা পণ্ডিচেরির হোটেলগুলিতে মশারি লাগানো হবে না! প্যারিস বা লন্ডনে নিশ্চয়ই কেউ মশারি প্রত্যাশা করে না, কিন্তু তা বলে ভারতীয়রাও পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ করবে? ব্রিটিশরা এসেও যে ম্যালেরিয়া থেকে বাঁচার জন্য মশারি ব্যবহার করেছে ৩০০ বছর আগে! ‘মিসিং দ্য মসকুইটো নেট’ নামক এই ভ্রমণ অভিজ্ঞতা পড়তে পড়তে ভাবছিলাম যে, মশারি আর ওরিয়েন্টাল ইমেজারি (প্রাচ্যের অবয়ব) কীভাবে মিলেমিশে যায়!

আমরা, ভারতীয়রা, যাকে অতি সাধারণ, ‘দৈনন্দিন’ জিনিস ভাবি, তা নিয়ে সাহেবসুবোদের মধ্যে বেশ একটা উত্তেজনা রয়েছে; যেমন ধরুন– গামছা, রান্নার মশলা বা মশারি। ভারতের বাইরেও তো মশারি ব্যবহারের নজির মেলে, বিশেষ করে প্রাচীন মিশর এবং মেসোপটেমিয়া সভ্যতায়। এই নিয়ে সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে পেয়ে গেলাম, ইংল্যান্ডের বিখ্যাত মেডিকেল জার্নাল ‘দ্য ল্যানসেট’ পত্রিকার একটি প্রবন্ধ। ১৯২১ সালে অবসরপ্রাপ্ত এক সৈন্য, স্যর প্যাট্রিক জানাচ্ছেন যে পুণা, মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানে কর্মরত অবস্থায় তিনি মশারি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু ভারতে সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে কখনওই মশারির প্রচলন দেখেননি। রাজা বা জমিদাররা শৌখিন নকশা করা মশারি ব্যবহার করলেও (এক্ষেত্রে মনে পড়ে যায়, গুপী গাইন বাঘা বাইন সিনেমার দৃশ্য। আমলকি গ্রামে গুপিকে তাড়িয়ে দেওয়ার আগে, বিরক্ত রাজামশাই গুপির বেসুরো গান শুনে যখন খাট থেকে নামছেন, আগেই তার কাঠের পালঙ্ক থেকে নকশা করা মশারি হাত দিয়ে সরিয়ে নিচ্ছেন, সেই মশারি অবশ্যই আজকালকার নাইলন বা পলিয়েস্টারের তৈরি নয়, সাদা চিকনের সূক্ষ্ম কাজ, হয়তো ধনীরাই ব্যবহার করত সেকালে) গরিব চাষি বা মজুরের ঘরে মশারি মজুদ থাকার ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত মেলে না বলেই মনে হয়, অন্তত ব্রিটিশদের তাই মত। প্যাট্রিক সাহেব লিখছেন যে–
‘The natives of India has always used his Chadar (sheet) or other covering when they sleep to protect themselves from the attacks of mosquitoes.’

এমনকী, খুব গরমের দিনেও এখানকার ‘নেটিভ’রা নাকি মাথায় চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমায়– লিখছেন সেকালের ইংরেজরা। গ্রামের দিকে গোয়াল ঘর বা উঠোনে মশা তাড়ানোর পদ্ধতি ছিল আবর্জনা আর ভেজা কাঠ একসঙ্গে করে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া। এই প্রবন্ধেই তিনি জানাচ্ছেন, মশারি দিয়ে সর্বোপরি ম্যালেরিয়াকে ঠেকানো অসম্ভব, ইতিমধ্যে নাকি সরকারের পক্ষ থেকে বার্ষিক লক্ষাধিক টাকা খরচ করা হয় মশারির পিছনে, এবং সেগুলি দু’-তিন বছরের বেশি টেকেও না, তাই মশারির পরিবর্তে ‘wire gauze mosquito proof material’ ব্যবহার করাই বেশি কার্যকর হবে। মনে রাখতে হবে, এই প্রবন্ধটি লেখার সময়কাল ১৯২১ সাল, যখন প্রায় ২০০ বছরের বেশি সময় ধরে ইংরেজরা ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু বা মশারি নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে গিয়েছে।
শুধুমাত্র শাসকের বয়ানে নয়, মশারির কথা আমরা বাংলা পত্রপত্রিকাতেও পেয়ে থাকি। ১৯৩২-এর ‘মাসিক বসুমতী’ পত্রিকায় আমেরিকার হেনরি ফোর্ডকে নিয়ে একটি প্রবন্ধ লেখা হচ্ছে। সেখানে ফোর্ডকে ‘ধনকুবের’ আখ্যা দিয়ে তার ব্রাজিলে রবার চাষের বৃত্তান্ত লেখা হয়। লাতিন আমেরিকায় মশার উৎপাত খুব বেশি, কিন্তু ফোর্ড নাকি সেখানে মশারির ধার ধারেননি, বরঞ্চ আধুনিক কলাকৌশলে তৈরি করেছেন মজুর ও কেরানিদের জন্য সময়োপযোগী বাড়ি। তাদের ঘরগুলো জাল দিয়ে এমনভাবে ঘেরা যে, শুধু ম্যালেরিয়ার মশা কেন, কোনও কীটপতঙ্গই প্রবেশ করতে পারবে না! বসুমতি-র লেখক হয়তো তুলনা করে নিচ্ছিলেন ইংরেজ আমলে মশা-মাছি নিয়ে হাজার পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়াস আর অন্যদিকে আমেরিকার রাজা ফোর্ড তাদের নয়া উপনিবেশ ব্রাজিলে গিয়ে কত সহজেই না বিষয়টির সমাধান করেছেন।
ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে আর কী কী আধুনিক উপায় অবলম্বন করেছে আমেরিকাবাসী, আদৌ তারা মশারি ব্যবহার করে নাকি তা অনেক আগেই ‘সেকেলে’ হয়ে গিয়েছে? এমন খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে কাগজে লেখালেখি হত বিশ শতকের গোড়ার দিকে। সকলেরই যে মশারিতে আপত্তি ছিল তা নয়; ১৯১১ সালে আন্দামানের এক কলোনেল চিঠি লেখেন ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেটের সম্পাদককে। ব্রিটিশদের দ্বারা পরিচালিত এই জার্নালে ওরিয়েন্টাল রোগব্যাধি নিয়ে নানা লেখা পাওয়া যায়। কীভাবে সম্পূর্ণ ভিন্ন জলবায়ু থেকে এসেও ধীরে ধীরে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছিল সাহেবরা, সেই ‘বীর জয়গাথা’র কথা তাঁরা নিজেরাই লিখতেন এই পত্রিকায়। গেজেটের একটি সংখ্যায় এক সেনাধ্যক্ষ লিখছেন যে, হেরেডোটাসের লেখা পড়ে তিনি জানতে পেরেছেন সুপ্রাচীন কালে মিশরীয়দের মশারি ব্যবহারের কথা। তারা কিকি বা ক্যাস্টর অয়েল গায়ে মাখত, প্যারাফিনের উগ্র গন্ধে মশারা কাছে আসতে পারত না। এছাড়া সেখানকার সাধারণ মানুষ নেট বা জাল দিয়ে দিনের বেলায় মাছ ধরত নীলনদে, আর সেই জাল রাতে গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়ত মশার হাত থেকে বাঁচার জন্য।
এই তথ্যটি আবিষ্কার করতে পেরে আন্দামানের সেনাধ্যক্ষ বেশ গর্বিত হন যে, এমন মশারির ব্যবহার তারা নিজেদের কলোনিগুলোতেও করে থাকে। রস আইল্যান্ডে প্রশাসনিক দক্ষতায় মশার উপদ্রব কাটানো গিয়েছে এবং ব্যারাকে বা আর্মি ক্যান্টনমেন্টে মশারি ব্যবহারের কথা তো সকলেরই জানা। তবে ভারতে মশারি কখনওই ব্রিটিশদের হাত ধরে আসেনি। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে ‘চতুষ্কি’ বা ‘মশকহরি’ শব্দটি অনেক সময় মশা প্রতিরোধ করার পর্দা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থেও মঠের জীবনযাত্রা সম্পর্কে লেখার সময় মশা থেকে বাঁচতে নানা প্রকার আবরণ বা আস্তরণের উল্লেখ রয়েছে। ভারতের বাইরে দেখলে বার্মা, ইন্দোনেশিয়া এমনকী, জাপানেও মশারির ব্যাপক প্রচলন ছিল। এর প্রমাণ হিসেবে জাপানি কিছু চিত্রকলা রয়েছে, যেখানে বারবার বাড়ির অন্দরমহলে মশারি চিত্রিত হয়েছে।

এবারে যদি ঔপনিবেশিক বাংলার প্রসঙ্গে আসি, তাহলে প্রথমেই চোখে পড়ে মহেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা; তিনি সরাসরি মশারির কথা বলছেন না বটে কিন্তু তাঁর ছেলেবেলায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ যে খুব বেশি ছিল না, মশার উপদ্রব যে কলকাতাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠল, সেই স্মৃতি উঠে আসে। আগেও যেমনটা বলা হয়েছে যে, সেকালে গ্রামগঞ্জে ঘরে ঘরে মশারির ব্যবহারের নজির খুব একটা মেলে না।
১৯২০-’৩০-এর পর থেকে বাংলা সাহিত্যে অনেক সময় মশারির প্রসঙ্গ আসছে। বিনয় ঘোষ, তাঁর কালপ্যাঁচার নকশা বইতে হাস্যরসাত্মক ভঙ্গিমায় কলকাতার আনাচে-কানাচে বর্ণনা করেছেন। কালপ্যাঁচার কথা শুনলে অবশ্যই মনে পড়ে যায় ‘হুতোম প্যাঁচার নকশা’। ভোরের কলকাতার বর্ণনা দিতে গিয়ে কালপ্যাঁচা লিখছেন, শ্যামবাজার বা ভবানীপুরের কোনও এক কেরানিবাবু অফিসের হাড়ভাঙা খাটুনির পর ভোরের দিকে গভীর নিদ্রায় মগ্ন। ক্রমশই তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়ে উঠে নিজের গিন্নিকে হয়তো চায়ের ফরমায়েশ করছেন। কিন্তু গত রাতের ঘুমটা তার খুব একটা ভালো হয়নি, সারারাত মশার কামড় খাওয়ায় পর মনে পড়েছে কাল মশারিটা টাঙানো হয়নি। ফুলের মালা কিনে গত সন্ধেতে বাড়ি ফিরে বাবু দেখেছেন ঘরের একটি পেরেকও ফাঁকা নেই। চারটে লোহার হুকে কোনওটাতে বাজারের থলে আবার অপরটিতে খেলনা বেলুন, তাই অগত্যা তৃতীয়টিতে তিনি নিজেই মালাটি ঝুলিয়ে নিদ্রা গিয়েছেন। একেই তো ছোট ঘর, মেয়ে বউয়ের আসবাবপত্র, তার উপর এঁদো দেওয়ালে পেরেক পুঁতে টাঙাতে হবে মশারি, নিম্নমধ্যবিত্তের ঘুপচি ঘরে এ এক বিড়ম্বনা। তার থেকে মশার কামড়ই শ্রেয়, যা হবে দেখা যাবে।
এবার আসি মশারি টাঙাতে গিয়ে যার ভাগ্য খুলে গিয়েছিল উপকথার সোনার কুড়ুল পাওয়ার মতো। এখানে কোনও জলদেবতা যদিও কাঠুরিয়াকে সাহায্য করেননি, বরঞ্চ মশারি টাঙাতে গিয়ে ১০০টা সোনার গিনি পেয়েছিলেন ডমরুধর। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের গল্পের নায়ক ডমরু থাকেন কলকাতার এক ভাড়াবাড়িতে। কাজ করেন হরি ঘোষের কাপড়ের দোকানে। অল্প মাইনে, ছোট ঘর এবং পরিচারিকার রান্না করা অখাদ্য খাবার খেয়ে সেদিন চালায়। কিন্তু একদিন রাতে মশারি টাঙানোর জন্য, একটি পেরেক দেওয়ালে বিঁধতেই খুলে গেল তার বরাত। উদ্দেশ্য ছিল মশারি টাঙিয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে, সকালে আবার হরি ঘোষের দোকানে গিয়ে হাজিরা দেবে। কিন্তু হাতুড়ি ঠুকতেই পুরনো দেওয়ালের কিছুটা চটে গিয়ে বেরিয়ে আসল ১০০টা সোনার মুদ্রা। ডমরু বুঝতে পারল যে, তার পাশের ঘরে ভাড়া থাকেন সস্ত্রীক গোলক দে। নিশ্চয়ই এই গিনি তিনি লুকিয়ে রেখেছেন ভঙ্গুর দেওয়ালে। ডমরু আর ছাড়ে কেন! ১০০ স্বর্ণমুদ্রা কুক্ষীগত করে, সেই টাকা দিয়ে নিজের বিয়ে সেরে এবং বাকিটা গ্রামের বাড়িতে লুকিয়ে রেখে ডমরু হয়ে উঠলেন নামজাদা এক ভদ্রলোক। এমন ভাগ্য তো কালেভদ্রে কারও হয় না, তাই নাগরিক রূপকথার মতোই ত্রৈলোক্যনাথ দেখিয়েছেন শহরের না পাওয়া মানুষের হঠাৎ ধনী হয়ে ওঠার বিপুল আনন্দের ছবি।

মশা ও মশারি নিয়ে এমন আরও অনেক মজার গল্প আমরা বাংলা সাহিত্যে পাই। তারাপদ রায় তাঁর ছোট গল্প ‘ছারপোকার এপিটাফ’ বা ‘মশা ও লবণহ্রদ’-এ লিখছেন যে, শ্যামবাজার থেকে কালীঘাট, যাকে নাকি তিনি আসল কলকাতা বলে মনে করেন, সেখানে মশা সচরাচর জ্বালাতন করত না। তাই মশারির বিক্রিবাট্টাও বেশি ছিল না ওই অঞ্চলে। কেবল ধর্মতলার অনন্ত মল্লিকের দোকান কিংবা বউবাজারের বিছানা পট্টি এবং চেতলার হাটে মফস্সলে মশারি বিক্রির ব্যবস্থা ছিল। কিছু শৌখিন মানুষ মশারি কিনতেন, আর ধর্মতলায় গ্রামগঞ্জের লোকেরা এসে শখ করে মশারি কিনে নিয়ে যেতেন তাদের ‘দেশে’। খুব দুঃখ করে লেখক বলছেন, যেই এসপ্ল্যানেড বা কালীঘাটে তিনি মশার টিকিটুকুও দেখেননি, সল্টলেকে এসে তাকে ঢুকতে হল মশাদের খাস তালুকে। সেখানে ঈশ্বর গুপ্তর কবিতার মতো দিনে মাছি রাতে মশা শুধু নয়, দিন-রাত একাকার করে মশার চাষ হয়। এমন অবস্থায় তিনি এক ফন্দি আটলেন। শ্রীনিকেতনে একটি কবিতা উৎসবে যাওয়ার কথা, তাই ব্যাগপত্তর গোছাচ্ছেন। কিন্তু রোজকার মতো খাট থেকে নেমে মশারিটা তুলে ফেললেন না। বরঞ্চ একটু এলোমেলো অবস্থায় খাট আর মশারিটাকে রেখে কাদের যেন তিনি ধন্ধে ফেলতে চাইলেন যে, এখনও মানুষগুলো আরামে আবেশে ঘুমিয়েই রয়েছে। লেখকের বর্ণনায়, এরপরই ঘরের আনাচে-কানাচে থেকে সব মশা ছুটে এল মশারির ভেতর, আর তখনই মশারিটা টানটান করে গুঁজে দেওয়া গেল, যাতে একটিও বেরতে না পারে। তিনদিন মশারি বন্দি মশারা, লেখক ফিরে এসে দেখলেন অনেকে ইতিমধ্যে দেহত্যাগ করেছে, বাকিরা মৃতপ্রায় অবস্থায় মশারি থেকে দ্রুত বেরিয়ে যাচ্ছে, তারাপদ রায়ের ভাষায় ‘আর তারা ফেরেনি এবং এই দুর্বিপাকের কাহিনি শুনে অন্য মশারাও আমার ঘরে এগোতে সাহস পাচ্ছে না’।
মেসজীবন কিংবা ছাপোষা মধ্যবিত্ত ঘরে মশারির ব্যবহার আমরা বাংলা গল্পে, সিনেমায় বা আত্মজীবনীতেও পাই। কিন্তু শহুরে ধনীরা মনে হয় মশারি থেকে বাঁচতে চাইছিলেন অনেক দিন ধরেই। উনিশ শতকের প্রেক্ষাপটে লেখা ‘সেই সময়’ উপন্যাসে নবীন কুমার ওরফে কালীপ্রসন্ন সিংহ মশা তাড়ানোর পরিকল্পনা করেন। সাহেবদের অনুকরণে শয়নকক্ষের জানলায় তিনি লাগান মশারির মতো সূক্ষ্ম তারের জাল। সেই বইতেই আবার দেখতে পাই এক ফেরিওয়ালা কলকাতার রাস্তায় ঘুরে ঘুরে কয়লা বিক্রি করছেন আর হাঁকছেন–
‘কয়লার ধোঁয়ায় যে মশা মাছি পালায় সে খবর জানেন? পরীক্ষা প্রার্থনীয়!’ মশারির বিকল্প তাহলে কয়লা, গায়ে মাখার তেল বা হাল ফ্যাশনের জানলার নেট। অবশেষে মশারি বললে প্রিয় কবির দু’টি লাইন না-লিখে পারছি না, জীবনানন্দ দাশের ‘হাওয়ার রাত’ কবিতা:
‘গভীর হাওয়ার রাত ছিলো কাল– অসংখ্য নক্ষত্রের রাত;
সারা রাত বিস্তীর্ণ হাওয়া আমার মশারিতে খেলেছে;
মশারিটা ফুলে উঠেছে কখনো মৌসুমী সমুদ্রের পেটের মতো,
কখনো বিছানা ছিঁড়ে
নক্ষত্রের দিকে উড়ে যেতে চেয়েছে;
এক-একবার মনে হচ্ছিলো আমার– আধো ঘুমের ভিতর হয়তো–
মাথার উপরে মশারি নেই…
কাল এমন চমৎকার রাত ছিলো।’
জীবনানন্দ দাশের পক্ষেই হয়তো সম্ভব এমন প্রাত্যহিক তুচ্ছ কোনও বস্তুর সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া মহাজাগতিক বিস্ময়। যেখানে মশারি কেবল একটি মধ্যবিত্ততার প্রতীক হয়ে থাকে না, গার্হস্থ্য জীবনের খুঁটিনাটি পেরিয়ে তা হয়ে ওঠে দার্শনিক উপলব্ধির পথ।
………………………………
ফলো করুন আমাদের ওয়েবসাইট: রোববার ডিজিটাল
………………………………
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
