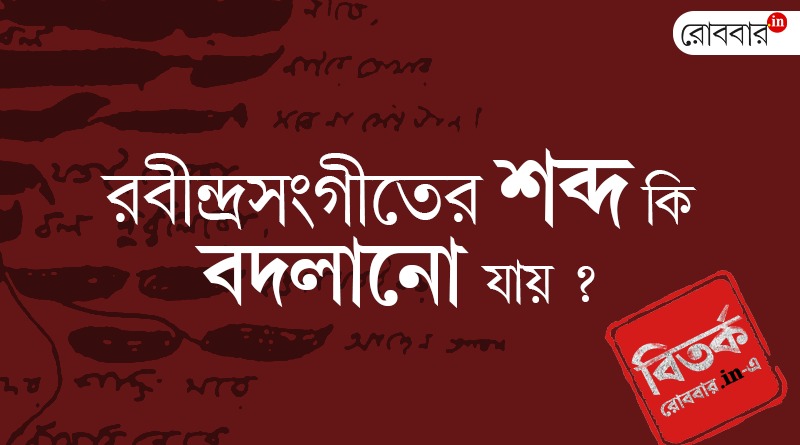
রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন সবই বদলে দেওয়া যায়, এমনকী, রবীন্দ্রনাথের গানও। কিছুই চিরায়ত নয়, প্রেম নয়, রবীন্দ্রনাথও নন। উল্টোদিকে, পূর্ণেন্দুবিকাশ সরকার বলছেন, রবীন্দ্রসংগীতের আসল সম্পদই তার নিখুঁত শব্দচয়ন। খোদার ওপর এই খোদকারিতে তাঁর কোনওরকম সায় নেই। হে তর্কশীল বাঙালি, পড়ুন, তর্ক করুন!
পক্ষে
রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
আমি অন্য সময়ের। টাইম মেশিনে ফিরে যাই ১৯৬০-এ। সেই সময়ের অবিকল্প স্কটিশ চার্চ কলেজ। ওই কলেজ থেকে আই.এ. পাশ করে ওই কলেজেই বি.এ. পড়ছি। ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে। আমাদের প্রিন্সিপাল ডক্টর হ্যারল্ড জন টেলর। তিনি বড্ড ইংরেজ। প্রথম দিনই বললেন, ‘আই অ্যাম দ্য ফার্স্ট অ্যান্ড লাস্ট ইংলিশ প্রিন্সিপাল অফ দ্য স্কটিশ চার্চ কলেজ। বিকজ, অল আদার হেডস অফ দিস কলেজ কেম ফ্রম স্কটল্যান্ড।’ (বিশাল হল-এ হাসি) ডক্টর টেলর হাসির শেষে, বললেন, ‘ইভন মিসেস টেলর ইজ ফ্রম স্কটল্যান্ড।’(আবার হাসি)। সেই সময়ে ইংরেজির হেড: মহীমোহন বোস (অক্সফোর্ড)। ইংরেজির অধ্যাপিকা ডক্টর কিটি স্কুলার, আর এক অক্সফোর্ড স্কলার, যিনি অম্লান দত্তকে বিয়ে করার পরে কিটি দত্ত, এবং যিনি আমাদের পড়ান মেটাফিজিকাল কবিতা, এবং অনন্য স্কলার দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় যাঁর ১৬ বছরের মেয়ে কলি, আমার প্রথম বউ– এঁরা প্রত্যেকেই বিশ্বাস করতেন, এবং অবশ্যই দর্শনের অধ্যাপক জন ওয়াকার এবং ডক্টর বিশ্বনাথ সেন, যে, সব কিছুই পরিবর্তন করা যায়, ‘নাথিং ইজ কনস্ট্যান্ট।’ সব কিছুই পরিবর্তনশীল।
আমার খুব ভাল লেগেছিল এবং এখনও লাগে, এই দৃষ্টিভঙ্গি– চেঞ্জ ইজ দ্য ওনলি কনস্ট্যান্ট! পরিবর্তনই চিরকালীন স্থিতিশীল সত্য! আজকের প্রেম, কালকের ঘৃণা। আজকের সংসার, কালকের মরুভূমি। আজকের ফুলশয্যা, কালকের শ্মশান!
১৯৬২ সাল। হ্যামলেট পড়াচ্ছেন আমাকে মহীমোহন তাঁর হরি ঘোষ স্ট্রিটের ‘ভূতের প্রাসাদ’-এ, বললেন, শেক্সপিয়র হ্যামলেটের মুখে বসিয়েছেন বটে, “Too too solid flesh will melt and thaw…!’’ আমি বদলে দিচ্ছি: “Too too ‘sullied’ flesh will melt and thaw!” কারণ ‘সলিড’ শব্দটা তেমন কিছু বলে না। শেক্সপিয়র ‘সলিড’ বলতে পারেন না। বলতে চেয়েছেন, ‘সালিড’– যার অর্থ, আমাদের এই ‘পাপক্লিষ্ট’, এই ‘অপবিত্র’ দেহ!’ সমস্ত মন আমার বলে উঠেছিল– আহা!
১৯৬২ সাল। ডক্টর কিটি স্কুলার (তখনও ‘দত্ত’ নন) জন ডান-এর ‘ফর গডস সেক হোল্ড ইওর টাং, অ্যান্ড লেট মি লাভ’-কে বদলে দিয়ে এক অপূর্ব বিকেলে বললেন, ‘ফর গডস সেক, ডোন্ট হোল্ড ইওর টাং অ্যান্ড লেট মি হেট!’ আমি নতুনভাবে জাগ্রত হলাম। দেবীপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়, ১৯৬৩ হবে হয়তো, আমাকে পড়াচ্ছেন তাঁর বাড়িতে শেক্সপিয়র, তাঁর ১৫ বছরের মেয়ে কলির সঙ্গে ২২ বছরের আমার প্রেম শুরু হয়েছে সবে– সেই পরম সময়ে দেবীপ্রসাদ কোনও এক সন্ধ্যায় হঠাৎ আবেগে বদলে দিলেন হ্যামলেট: টু লাভ অর নট টু লাভ, দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন।
আমি তীব্রভাবে প্রেমে পড়লাম কলির। বিয়ে করলাম তাকেই। কিন্তু বারবার প্রেমে পড়তেই থাকলাম। ‘চেঞ্জ ইজ দ্য ওনলি কনস্ট্যান্ট।’
রবীন্দ্রনাথও বদলে দেওয়া যায়, অবশ্যই যায়। আমি তো বদলে দিয়েছি, রবীন্দ্রনাথের একটি গান। ‘মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না?’
কী সর্বনাশ! চিরদিন! পাশ ফিরলেই তুমি! পাগল!
আমি বদলে করেছি, ‘মাঝে মাঝে যেন দেখা পাই, চিরদিন যেন পাই না।’ এই গান, আমার প্রিয় গায়ক ও বন্ধু ইমন গেয়েওছে! আহা! কী ভাল! চিরদিন কোনও কিছু ভাল কি আর থাকে!
…………………………………………………………………………………………………………………..
বিপক্ষে
ডা. পূর্ণেন্দুবিকাশ সরকার
রবীন্দ্রনাথের গানের শব্দ পরিবর্তন করার কি আদৌ কোনও প্রয়োজন আছে? আমার মনে হয় এটি একটি হাস্যকর আর অবাস্তব প্রস্তাব। এই ধরনের প্রচেষ্টা কোনও দিনই রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন পায়নি। তাঁর গানের কথা বা সুরের উপরে কোনও রকম হস্তক্ষেপ রবীন্দ্রনাথ কখনওই সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর বিপুল সৃষ্টিসম্ভারের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় ছিল গানগুলি। তাদের তিনি লালন করেছেন সন্তানস্নেহে। ছিল প্রচ্ছন্ন অহংকারও। একবার দিলীপকুমার রায় ‘তোমার বীণা আমার মনোমাঝে’ গানটিতে নিজেই সুরারোপ করতে চাইলে রবীন্দ্রনাথ ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলেন, ‘তুমি কি বলতে চাও আমার গান যার যেমন ইচ্ছা সে তেমনই ভাবে গাইবে? আমি তো নিজের রচনাকে সেরকম ভাবে খণ্ডবিখণ্ড করতে অনুমতি দেই নি। যে রূপ সৃষ্টিতে বাইরের লোকের হাত চালাবার পথ আছে তার এক নিয়ম, যার পথ নেই তার অন্য নিয়ম। আমার গানে আমি তো সেরকম ফাঁক রাখি নি যে, সেটা অপরে ভরিয়ে দেওয়াতে আমি কৃতজ্ঞ হয়ে উঠব।’ অর্থাৎ তিনি স্পষ্টভাবে বলে গিয়েছেন যে, তাঁর রচনায় অন্য লোকের ‘হাত চালানোর’ কোনও অধিকার নেই।
বিশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত পেশাদার উচ্চাঙ্গসংগীত শিল্পীরা রবীন্দ্রনাথের গানের কথা আর সুরকে বদলিয়ে নিয়ে নিজেদের খুশিমতো গাইতেন। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে বারেবারে তাঁর অসন্তোষ আর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। ১৯২০ সালে কে. মল্লিক গ্রামোফোন রেকর্ড থেকে ‘আমার মাথা নত করে দাও’ গানটি রেকর্ড করেছিলেন কথা এবং সুরের যথেচ্ছ পরিবর্তন করে। কবির কথায়, ‘সে গান শুনিয়া আমার মাথা সত্যই নত হইয়া গেল।’
রবীন্দ্রসংগীতের আসল সম্পদ তার কথা, তার নিখুঁত শব্দচয়ন। তাই গানের প্রতিটি বাণীই প্রাণকে স্পর্শ করে যায়, গভীর উপলব্ধিতে চেতনা ঋদ্ধ হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেকটি গানের অন্তরালে রয়েছে তার সুনির্দিষ্ট কথা আর সুরের চয়ন এবং বয়ন-কাহিনি। গানের কথাতেই উন্মোচিত হয় কবিমনের মানসপট, অন্তর্লোকের ভাব-কল্পজগৎ, বাহ্যিক ঘটনাক্রম আর অবচেতনার অভিঘাত। তাই গভীর অনুভূতি আর মনন থেকে রচিত রবীন্দ্রনাথের গানের প্রতিটি বাক্য শাশ্বত এবং কালোত্তীর্ণ। সেই বাক্যকে সামান্যতম বদল করার প্রচেষ্টা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকে আঘাত হানার স্পর্ধিত অহংকার। সেটি তখন আর রবীন্দ্রসংগীত থাকে না। খেয়া কাব্যগ্রন্থের ‘দিনের শেষে ঘুমের দেশে’ কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের অনুমতিক্রমে পঙ্কজকুমার মল্লিক সুরারোপ করলেও সেটি রবীন্দ্রসংগীতের তকমা পায়নি কিংবা গীতবিতানেও অন্তর্ভুক্ত হয়নি।
১৯৪০ সালে জোড়াসাঁকোর বিচিত্রা ভবনের এক অনুষ্ঠানে গভীর বেদনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ‘আমার গান যাতে আমার গান বলে মনে হয় এইটি তোমরা কোরো। আরো হাজারো গান হয়ত আছে, তাদের মাটি করে দাও-না, আমার দুঃখ নেই। কিন্তু তোমাদের গান যেন আমার গানের কাছাকাছি হয়, যেন শুনে আমিও আমার গান বলে চিনতে পারি। এখন এমন হয় যে, আমার গান শুনে নিজের গান কিনা, বুঝতে পারি না। নিজে রচনা করলুম, পরের মুখে নষ্ট হচ্ছে, এ যেন অসহ্য।’ শুধু রবীন্দ্রসংগীত কেন, কোনও শিল্পীর সৃষ্টিকে কাটাছেঁড়া করা বা তার উপরে কলম চালানোর অধিকার আমাদের কারও নেই।
রবীন্দ্রনাথ যখন নিজেই তাঁর গানের কথা বা সুরকে পরিবর্তন করবার অনুমতি দেননি, বরং বারবার আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন, তখন কেন এই ‘খোদার উপর খোদকারি’র চেষ্টা?
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
