
সব শ্মশানে শ্মশানকালীর পুজো না হলেও অনেক স্থানে শ্যামাপুজোর রাতে বা নির্দিষ্ট দিনে মৃণ্ময়ী মূর্তিতে পূজিত হন। সে মূর্তি বেশ স্বতন্ত্র। শিবের বুকে বাম পা দিয়ে এলোচুলে কালো কালী দাঁড়িয়ে। দু’-পাশে নরমাংস খাচ্ছে ভয়ংকরী ডাকিনী-যোগিনী। সঙ্গে শিয়াল। দেবীর পুজো করেন সাধারণত ‘শ্মশানে-বামুন’ বা অগ্রদানী। গ্রাম্য শ্মশান শুধু শবদাহের স্থান নয়। এখানে সমাধিও হয়। বিশেষ করে ‘কাঁচা ছেলে’ মারা গেলে তাকে দাহ করা হত না। শ্মশানের একপাশে কোমর-ভর খাল করে সমাধিস্থ করে। বড় কলসির মধ্যে ভরে মাটিতে পোঁতা নিয়ম।

ভয়ংকর শ্মশান!
বৃত্তাকারে শকুনের দল পাখা মেলে এগিয়ে যাচ্ছে নরমুণ্ডের দিকে। কখনও ধীর। কখনও দ্রুত লয়ে। অদূরে দুটো শিয়াল, কুকুর। তাক করে তাকিয়ে আছে নরমুণ্ডের দিকে। অতর্কিতে শকুনের ব্যূহ ভেদ করে শিয়াল আর কুকুর নরমুণ্ড অধিকার করে। চতুর্দিকে ছিটকে যায় শকুন।
দুই ঢাকিদার ঢাকের বাজনায় ফুটিয়ে তোলে শকুনদের সেই ছত্রভঙ্গের ছবি।
–ধাগ ধিনা ধিন/ ধাগ ধিনা ধিন/ ধাগ ধিনা ধিন/ ধা!
অসাধারণ কয়েকটা চিত্রমুহূর্ত। তারপর বোল-তাল চেঞ্জ! আক্রমণ প্রতি-আক্রমণে, অভিনয়ে, লোকজ নাচের মুদ্রায়, জমজমাট হয়ে ওঠে আবার শিয়াল-শকুনের লড়াই। একসময় শিয়াল-কুকুর তাড়িয়ে শকুনের দল নরমুণ্ড দখল করে। ভয়ংকরী কালো কালীর বেশে সজ্জিত কালকেপাতার দল। এরাই হয়েছিল শকুন। মুখে নরমুণ্ড আর হাতে রাম-দা নিয়ে ফিনিশিং নাচটি বীভৎস-সুন্দর!
ঢাকিদার মাতান বাজায়: ধাক ধিনা ধিন, ধিনাক তা/ নাক তিনা তিন, তিনাক তা।

শিয়াল-শকুনের এই প্রাচীন নৃত্যনাট্যটি ফি বছর অনুষ্ঠিত হয় শিবের গাজনে। ২৭ কিংবা ২৮ চৈত্র নিশিরাতে। ‘পোরোবোলান’ নামে বহুল প্রচলিত হলেও লোকে বলে, ‘শ্মশানে বোলান’।
গ্রাম্য বিশ্বাস, ‘শ্মশানে বোলান’ না হলে ‘গাজনশুদ্ধি’ হবে না।
শ্মশান! আদিতে শবের শয়ন স্থান। অর্থ– সমাধিক্ষেত্র। পরে মৃতদেহ দাহ করার রীতি প্রচলিত হলে শবদাহের স্থান। ভয়, দুঃখ, কান্না, শোক-বৈরাগ্য, জীবন-মৃত্যু সম্পর্কে উপলব্ধি যদি কোনও একটা শব্দে জমাট বেঁধে থাকে– সেটি শ্মশান। জীবনের শেষ পরিণাম একমুঠো ছাই! পঞ্চভূতের বিলীন-ক্ষেত্র। সুতরাং শ্মশান-সংস্কৃতি বহু বৈচিত্রময় বিষয় হবে, সন্দেহ নেই।
অধিকাংশ শ্মশান গঙ্গা বা নদীর ধারে অবস্থিত। সেই কারণে শ্মশানের অপর নাম ঝিল। গ্রামবাসীদের খুব আশা থাকে, অন্তিমে তার যেন ‘গঙ্গা চালান’ হয়। গ্রামে কেউ মারা গেলে আমন্ত্রণের কোনও ব্যাপার নেই। কান্নার আওয়াজ শুনে দলে দলে হাজির হয়ে যান।
একদিকে কান্না হাহাকার, অন্যদিকে নীরবে কর্মপ্রবাহ। কেউ বাঁশ কাটছেন। তৈরি হচ্ছে খাটুলি। কেউ খড় পাকিয়ে দড়ি প্রস্তুতিতে মগ্ন। ‘কেঁদো’র দলও হাজির। বামুন কায়েতের মরা হলে শ্মশান-কৃত্যের সঙ্গে মুখে একটুকরো সোনা ভরে চোখের জলে শেষ বিদায়।
–বলো হরি, হরি বোল!
ধনী বাড়ির বুড়ো মৃতদেহ হলে আরেকরকম। মরার খাটুলি রঙিন কাগজ দিয়ে সাজানো। মাটির ভাঁড়ে থাকা খুচরো পয়সা ছড়ায় নাতিপুতিরা। সঙ্গে হরিসংকীর্তন। শবযাত্রা নাকি শোভাযাত্রা ঠাওর করা দায়!
দাহ-কর্মের পর যখন বাড়ি ফেরে তখন সদর দরজায় নামানো থাকে আগুনের মালসা, আঁশবটি আর নিমপাতা। একটুকরো নিমপাতা মুখে দিয়ে আঁশবঁটি পার হলে শ্মশান-কর্মের সমাপ্তি। মরা বয়ে বয়ে কাঁধ ক্ষত-বিক্ষত হলে তখন তাদের নাম ‘কাঁধকাটা’। ‘হেড-কেঁদো’রা ‘শ্মশানে বোলান’ দলের ওস্তাদ।
উদ্ধারণপুরের মহাশ্মশান খুবই পুরনো। কথায় বলে, ‘যত মরা পুড়তে আসে উদ্ধানপুরের ঘাটে’। আদি নাম উধানপুর। ‘উধান’ শব্দের অর্থ শ্মশানের চুল্লি। পরে বৈষ্ণবসাধক উদ্ধারণ দত্তের শ্রীপাট গড়ে ওঠায় তাঁর নাম সাম্যে উধানপুর থেকে উদ্ধারণপুর।
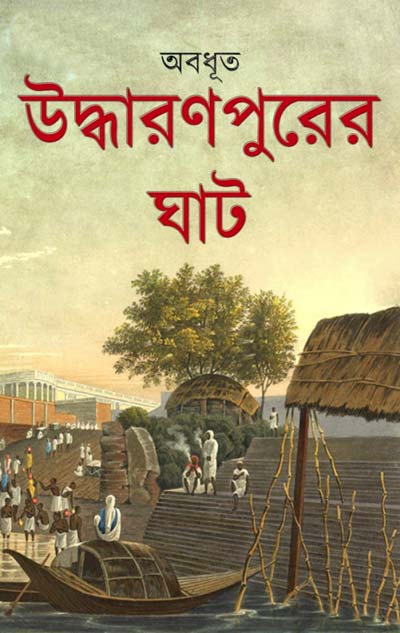
তখন ‘পা-গাড়ি’-ই ছিল ভরসা। শুধু বর্ধমান নয়, বীরভূম মুর্শিদাবাদের বহু দূরদূরান্ত থেকে কেঁদোরা মরা পোড়াতে আসতেন উদ্ধারণপুরে। আসা-যাওয়া পোড়ানো এসব ঝক্কি সামলাতে ১০-১২ দিন সময় লেগে যেত। অবধূতের লেখা ‘উদ্ধারণপুরের ঘাট’ উপন্যাসটি যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা সেসব কথা বিলক্ষণ জানেন।
প্রতিটি গ্রামে নিজস্ব শ্মশান আছে। সেই শ্মশানের মোটামুটি দু’টি ভাগ; একটি ব্যক্তিগত। অপরটি ‘সাজারে’ বা সর্বজনীন। ব্যক্তিগত শ্মশানে নির্দিষ্ট বংশ পরম্পরায় দাহ করা নিয়ম। সাজারে শ্মশানে গ্রামের সব শ্রেণির অধিকার। বিশেষ করে অপঘাতে বা আত্মহত্যা করলে সাজারে শ্মশানে ‘নমো নমো’ করে দাহ হয়। ইদানীং ছবিটা পাল্টালেও এখনও গ্রাম্য শ্মশানে দাহ করার বিষয়টি দক্ষিণ বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান বীরভূম প্রভৃতি জেলায় টিকে আছে।
ঐতিহাসিক তাম্রশাসনগুলি থেকে গ্রামের ভূমির চরিত্র, সীমানা নির্দেশ, মালিকানা, মূল্যমান ইত্যাদি সম্পর্কে বিচিত্র তথ্য মেলে। যেমন শুকো হাজা জমি, গো-পথ, বাথান, গো-ভাগাড় বা উপশল্য, শ্মশানভূমি ইত্যাদি। পূর্ববাংলা থেকে প্রাপ্ত খ্রিস্ট্রীয় পঞ্চম শতাব্দীর বৈন্যগুপ্তের তাম্রশাসনে গ্রামের নির্দিষ্ট শ্মশানভূমির উল্লেখ পাওয়া যায়।
গ্রাম্য-শ্মশান সাধারণত নদী, কাঁদর, পুকুরের গাবা বা বিলের ধারে এক খাবলা ঝোপঝাড় গাছপালার জটলা। মাটির ঢিপির ওপরে শ্মশানকালীর ‘মেড়’। আধপোড়া কাঠ, বালিশ-বিছানা, হাঁড়িকুঁড়ি যততত্র ছড়ানো। কোথাও বা বন-বিচুটির লতায় ঢাকা ছোট ছোট তুলসি মন্দিরের মতো সমাধি-স্মারক। টেরাবেঁকা আখরে লেখা, ‘শ্রীশ্রী হরি সহায়, ব্যোঁম পাল। ১৯৭২ সন। সাং-বরুন্দি।’

কোথাও শ্মশানের একপাশে সাবেকি সতীমন্দির। ভিতরে সমাধি-স্মারক। গোলাকার কয়েকটি রিঙের ওপরে শিবলিঙ্গের মতো গঠন। অনেক স্থানে সতীমন্দিরকে কেন্দ্র করে শ্মশানে মেলা বসে। আলকাপ শুনতে ঝেঁটিয়ে লোকজন জড়ো হয়। সধবা মেয়েরা লালপেড়ে শাড়ি-শাঁখা-সিঁদুর ইত্যাদি নৈবেদ্য সাজিয়ে সতীমায়ের পুজো দিতে যান।
সব শ্মশানে শ্মশানকালীর পুজো না হলেও অনেক স্থানে শ্যামাপুজোর রাতে বা নির্দিষ্ট দিনে মৃণ্ময়ী মূর্তিতে পূজিত হন। সে মূর্তি বেশ স্বতন্ত্র। শিবের বুকে বাম পা দিয়ে এলোচুলে কালো কালী দাঁড়িয়ে। দু’-পাশে নরমাংস খাচ্ছে ভয়ংকরী ডাকিনী-যোগিনী। সঙ্গে শিয়াল। দেবীর পুজো করেন সাধারণত ‘শ্মশানে-বামুন’ বা অগ্রদানী।
গ্রাম্য শ্মশান শুধু শবদাহের স্থান নয়। এখানে সমাধিও হয়। বিশেষ করে ‘কাঁচা ছেলে’ মারা গেলে তাকে দাহ করা হত না। শ্মশানের একপাশে কোমর-ভ’র খাল করে সমাধিস্থ করে। বড় কলসির মধ্যে ভরে মাটিতে পোঁতা নিয়ম।
প্রথাটি বহু পুরাতন। ঐতিহাসিকরা একে ‘কুম্ভসমাধি’ বলেছেন। বহু প্রত্নক্ষেত্র থেকে এই ধরনের কুম্ভসমাধির নজির মিলেছে যেমন মহারাষ্ট্রের ইনামগাওঁ, বর্ধমানের পাণ্ডুরাজার ঢিবি ইত্যাদি।
অনেক গ্রামে বৈষ্ণবদের ‘সমাজ’ও আছে। বর্তমানে বৈষ্ণবরা শবদাহ করলেও পূর্বে সমাজে বংশানুক্রমে সমাধি দিতেন। এখনও কেউ কেউ সমাজ নেওয়ার কথা উত্তরপুরুষদের কাছে বলে যান। সমাধি চত্বর বেশ বড় আকারের থান। চারপাশে প্রাচীর দেওয়া অথবা ফাঁকা আয়তাকার অথবা বর্গাকার ডাঙা। সমাধি স্মারক হিসাবে লাইন দিয়ে গোলাকার ছোট ছোট স্থাপত্য।
কেউ মারা গেলে সমাজ দেওয়ার পূর্বে মানুষ সমান খাল করে মৃতদেহকে স্নান করিয়ে নতুন বস্ত্র পরিয়ে মালা তিলক করেন। সমাধি গর্ভে আসন বিছিয়ে দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে পদ্মাসনে বসানো হয়। সামনে থাকে ১২টি ছোট আকারের ভোগের মালসা, পানপাত্র ইত্যাদি।
সমাধির ওপরে বাঁশের খাঁচা তৈরি করে মাদুর বিছিয়ে কয়েক ফুট মাটির আস্তরণ। পরে তার ওপর ইটের তৈরি গোলাকার স্থাপত্য নির্মাণ করে তিলক আঁকে। সমাজে ভূত-প্রেতের কোনও ভয় নেই। জন্ম বা প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে ভোগ নিবেদন করেন অনেকে। বাড়ির মহিলারা ধূপ-দীপ দান করেন সমাজে।

আরেক ধরনের সমাজ দেখা যায়, যেগুলির সঙ্গে যুক্ত বড় জমিদারদের স্মৃতি। যেমন, বর্ধমানের রাজাদের শ্মশানকর্ম হত প্রথমে ইন্দ্রাণী দাঁইহাটে, বর্গিহাঙ্গামার পর থেকে অম্বিকা কালনায়। গঙ্গার তীরে বিশেষ চিতায় শবদাহের পর চিতাভস্মের সমাধিতে তৈরি হত বিশেষ ধরনের চূড়া বা গম্বুজ যুক্ত স্থাপত্য। দাঁইহাট ও কালনায় সেই ‘সমাজবাড়ি’ আজও দেখার মতো পুরাকীর্তি।
গ্রাম্য সাধারণ্যের চোখে শ্মশান যেমন পবিত্র স্থান তেমনই ভয়ের ক্ষেত্র। সাধারণত শ্মশানের দিকে দুপুরে বা রাত্রে কেউ ভয়ে যায় না। হাতে মাদুলি-তাবিজ থাকলে তার কার্যকারিতা নষ্ট হয়। একে বলে ‘ওষুধ ছুটে’ যাওয়া। ব্যক্তিগত শ্মশানে কেউ কেউ কালীপুজোর আগে চতুর্দশীতে চোদ্দোপ্রদীপ জ্বালাতে যান।
পূর্বে ‘আঁতুরে -পোয়াতি’ ও শিশু মারা গেলে লোকবিশ্বাস হল শ্মশানে শাঁকচুন্নি হয়ে শনি মঙ্গলবারে মাঠময় মরার কানিচুনি পরে মৃত শিশুকে খুঁজে বেরয়। শঙ্খধ্বনির মতো কান্না। একবার খুঁচিয়ে দিলেই হল, কত যে শ্মশানের শাকচুঁন্নি পেতনির গপ্প শোনা যাবে, তার কোনও শেষ নেই।
শিবের সঙ্গে শ্মশানের গভীর সম্পর্ক। শিব শব্দের আদি অর্থ কী এনিয়ে বিতর্ক থাকলেও শবের সঙ্গে তার যোগ অচ্ছেদ্য। শবের ভস্ম মাখতে তিনি পছন্দ করেন। শবশিবা নামে দেবী মূর্তিতে শিব ও শব একাকার। সুতরাং শৈব আরাধনায় শব ও শ্মশানের সম্পর্ক সেই আদ্যিকালের।
উত্তর রাঢ় অঞ্চলে শিবের গাজনের সঙ্গে শুধু কালকেপাতার শ্মশানে বোলান নয়, ‘শ্মশান-জাগানো’ বা ‘শ্মশান চালানো’ নামে ভয়ংকর অনুষ্ঠান আছে। গভীর রাতে গাজুনে ভক্তরা ওস্তাদের নেতৃত্বে শ্মশান থেকে মড়ার মাথা সংগ্রহ করেন। সেই মড়ার মাথা গাছের মগডালে ঝুলিয়ে রাখেন।

দুপুরে ভক্তরা মরার খুলিতে সিঁদুর ইত্যাদি লেপন করে চালভাজা কলাইভাজা আর মদের নৈবেদ্য দিয়ে নানা ধরনের কৃত্যাদি করেন। নীলপুজোর রাতে নরমুণ্ডগুলিকে গাজনতলায় এনে নানা ধরনের প্রহেলিকাময় গান পরিবেশন করেন ঢাকের বাদ্যের সঙ্গে। একেই বলে শ্মশান-জাগানো বা শ্মশান চালানো।
অনেক স্থানে শ্মশানে পুজো পান হাজরা ঠাকুর। হাজরা, অর্থাৎ হাজার হাজার ভূত-প্রেতের ভয়ংকর অপদেবতা। চড়কের সময় হাজরা ঠাকুরের পুজো হয় শ্মশানের মধ্যে। শ্মশানের বাঁশ কাঠ জ্বেলে হাজরা দেবতার উদ্দেশ্যে শোলমাছ পুড়িয়ে ভোগ দেওয়া হয় নীলপুজোর রাতে। চব্বিশ পরগনা বা পূর্ব বাংলার চড়কপুজোর অন্যতম অঙ্গ হাজরাপুজো।
‘হাজরা-চালান’ নামেও তন্ত্রমন্ত্র ছড়া-কাটাকাটি নাচ-গান ইত্যাদি ভক্তরা পরিবেশন করেন। ভূত-প্রেত দেবতার রূপসজ্জা দেখার মতো জিনিস। হাজরা ঠাকুরের মূর্তিও অনেক শ্মশানে পূজিত হয়। চতুর্ভুজ শ্বেতবর্ণের মূর্তি। মাথায় জটাজুট। নিউটাউনের হাজরাতলায় হাজরা মন্দির ও মূর্তি আছে।

শ্মশান থেকে মাশান শব্দটি এলেও লোকবিশ্বাসে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। মশানে রাজ অপরাধীদের হত্যা করে দাহ করা হত। মশানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ব্রহ্মদৈত্য এবং মাশানদেবতার প্রসঙ্গ। মাশান ঠাকুর উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের পূজিত অপদেবতা বা উপদেবতা। মাশান ঠাকুরের পুজো হয় শনি মঙ্গলবার বা অমাবস্যায় কিংবা নির্ধারিত দিনে। মাশান-কাল্ট খুবই বৈচিত্রময়। প্রায় ২৩ ধরনের মাশানদেবতা আছেন যথা মুড়িয়ামাশান, জলুয়ামাশান শুকানমাশান ইত্যাদি।
মাশান ঠাকুর নিয়ে অদ্ভুত লোকপুরাণ আছে। কেউ বলেন কালী আর ধর্মরাজের বেটা হলেন মশান ঠাকুর। কেউ বলেন প্রাচীন যক্ষপুজোর স্মৃতি। আবার কেউ বলেছেন, শ্মশানচারী শিবের রকম ফের। আদিতে শ্মশানে পূজিত হলেও এখন লোকালয়ে ভয়ে ভক্তিতে পূজিত হন নানা আঙ্গিকে যেমন মূর্তিতে, প্রতীকে, মুখোশে।

মৃণ্ময় মূর্তির অনেক রকম রূপ। কোথাও পালোয়ানি চেহারার মাশানের এক হাতে গদা। কোথাও কবন্ধের মতো বুকে চোখ-মুখ-গোঁফ আঁকা। কাটা গলা থেকে উত্থিত ফণাধারী সাপ। কোথাও আবার পুরুষ কালীর মতো বিচিত্র গঠন।
শ্মশানের চিতা নিয়েও উৎসব কম নেই। আগুন যাতে চিৎ হয়, সেটি চিতা বা শ্মশান-চুল্লি। চিতাকে কেন্দ্র করে প্রাচীনকালে গড়ে উঠেছিল চৈত্য বা স্তূপ। গবেষকরা মনে করেন, এটি মূলত অস্ট্রিকদের কালচার। চিতা থেকে পোড়া হাড় সংগ্রহ করে সেখানে মাটির ঢপি বা পাথর বা গাছ দিয়ে চিহ্নিত করা হত।
কিংবা মাটির ঢিপির ওপর একটি গাছের চারা লাগানো হত। চিতা বা চিতা চিহ্নিত মাটির স্তূপ থেকে কালক্রমে দু’টি বড় লোক-উৎসবের জন্ম হয়। সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যে একে ‘চৈত্যমহ’ বা ‘স্তূপমহ’ বলা হয়েছে। এবং চিতা-চিহ্নিত বৃক্ষকে প্রাচীন সাহিত্যে ‘চৈত্যবৃক্ষ’ বলে।
যদিও পরবর্তীকালে শব্দটির অর্থান্তর ঘটেছে।
… পড়ুন শ্মশান-এর অন্যান্য লেখা …
নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী-র লেখা: শ্মশানের সঙ্গে বৈরাগ্যের কোনও সম্পর্ক নেই, তবুও প্রবাদের মতো সত্য শ্মশান-বৈরাগ্য
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
