
সকলের মতো আমিও টাইপ ইশকুলে ভর্তি হয়েছিলাম। টাইপ মেশিনের অক্ষরগুলির ওপর আমার আঙুল সেট করিয়ে দিয়েছিলেন এক দিদি। ওঁর চুল থেকে সুগন্ধি তেলের ঘ্রাণ পেতাম। তিনি বলেছিলেন, ‘সেটিংটাই আসল।’ টাইপ দিদিমণির সেই বাণী বড় অমোঘ। শুধু টাইপিংয়ের ক্ষেত্রেই নয়, জীবনের সর্বক্ষেত্রে সেটিংটাই আসল। আজকের জাবরকাটা টাইপ মেশিন নয়, টেলিগ্রাফের মেশিন। যাকে সহজে বলা হত ‘টরেটক্কা মেশিন’। টরেটক্কাটা শিখতে পারলে তখন পোস্ট অফিসে, রেলে, জাহাজে চাকরি হওয়ার সুযোগ তৈরি হত। বঙ্গতনয়গণ, যারা কেরানি হওয়ার জন্য বলিপ্রদত্ত ওরা টাইপ শিখতই আর একটু উচ্চাশা যাদের, তারা শর্টহ্যান্ডও শিখে নিত।
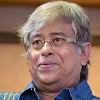
১৭.
আমরা যখন স্কুলের ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছি, গত শতাব্দীর ছয়ের দশকের শেষে, তখনও পরীক্ষার পর রেজাল্ট বেরনোর আগের তিন মাস আমাদের টাইপের ইশকুলে ভর্তি হতে হত। আমার দাদার বয়সি, কাকার বয়সি, বাবার বয়সি যাঁরা, সবাইকেই টাইপিং স্কুলে ভর্তি হতে হত। বাঙালি মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের যেমন দুটো নজরুলগীতি, দুটো রবীন্দ্রসংগীত, একটা শ্যামাসংগীত জানতে হত, একটু উলবোনা, ভাজা মাছ ওলটানো জানতে হত, ছেলেদের তেমনি টাইপ।
বাঙালি মোটামুটিভাবে কেরানি হওয়ার জন্যই জন্মায়। যদি কেরানির পরিবর্তে মাস্টারমশাই হয়, ডাক্তার হয়, রেলের গার্ড হয়– ভিতরে থাকা কেরানি মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসা বেশিরভাগ বাঙালিরই হয়ে ওঠে না। কেরানি মানসিকতাকে এক কথায় বলা যায়– ‘সব্বাই করে বলে সব্বাই করে তাই’ মার্কা গতানুগতিকতা।
…………………………….
এই যে ‘মর্স’ সাহেবের শব্দ ভাষা, এটা ১৮৩৫ থেকেই সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ততদিনে বিদ্যুৎও আবিষ্কার হয়ে গেছে। যখন যন্ত্রটার ওপরটা চেপে নিচের বোতামে স্পর্শ করা হত, তখন বিদ্যুৎ চালু হত, সেটা হল ডট্ বা টরে, ছেড়ে দিলেই বিদ্যুৎ বিযুক্ত হয়, এটা হল ড্যাস বা টক্কা। আজকের কম্পিউটারে যে অ্যালগারিদমের ভাষা, সেটাও ডট আর ড্যাসেরই খেলা।
…………………………….
যখন ‘ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি’ এল, ওদের ব্যবসার জন্য কেরানিদল দরকার পড়ল। এবং টাইপরাইটার মেশিনের। ১৮৮০ নাগাদ ইউরোপের বাজারে টাইপরাইটার মেশিন আসে। ভারতে তা ১৮৯০ সাল থেকে ব্যবহার হচ্ছে। তখন আর কোম্পানির আমল নেই, সরাসরি ব্রিটিশরাজের অধীনে চলে গেছে ভারত। রেমিংটন, পিটার– এসব কোম্পানির মেশিন ছিল, ভারতের গোদরেজ কোম্পানিও টাইপ-মেশিন তৈরি করত।
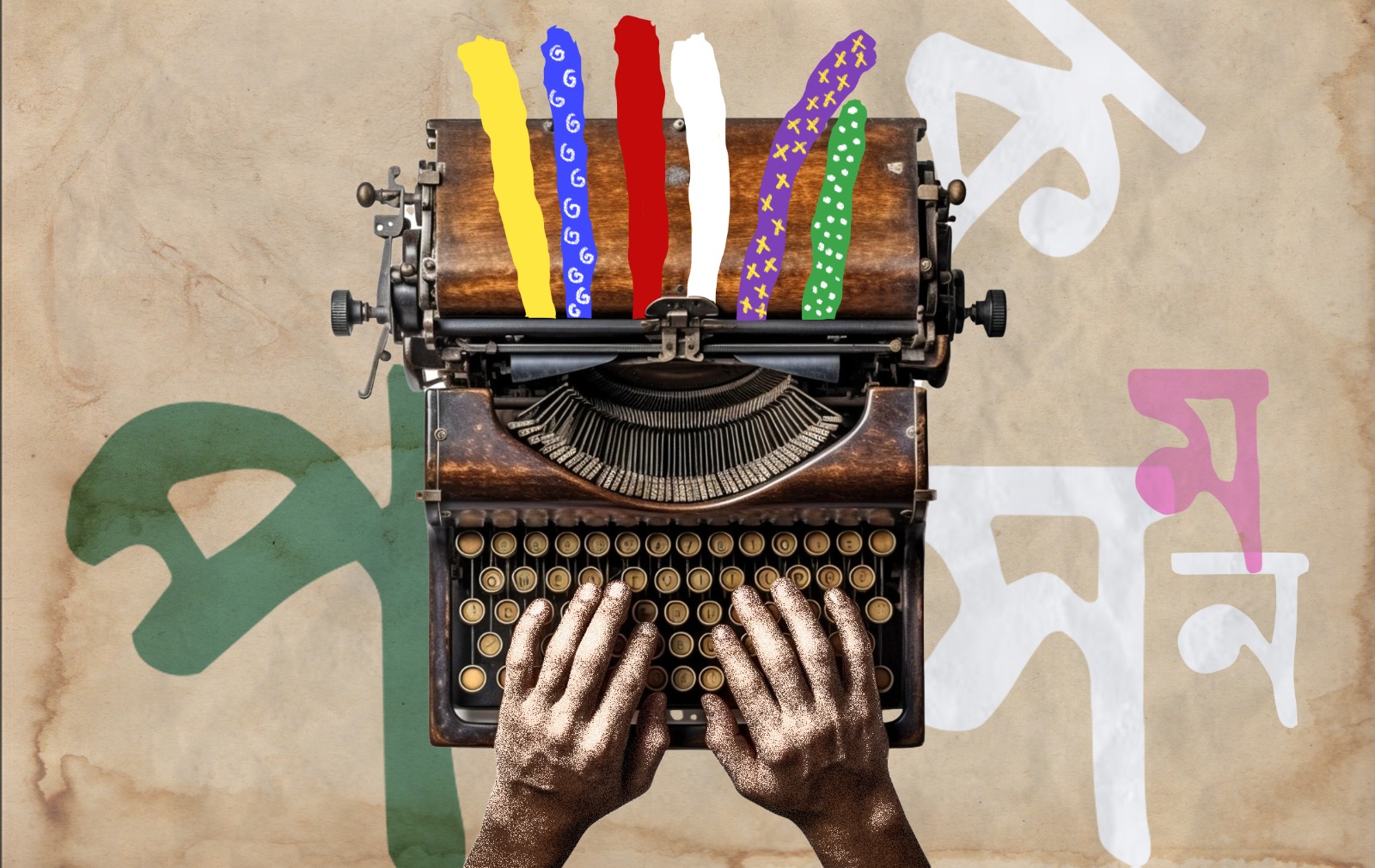
আমিও টাইপ ইশকুলে ভর্তি হয়েছিলাম। টাইপ মেশিনের অক্ষরগুলির ওপর আমার আঙুল সেট করিয়ে দিয়েছিলেন এক দিদি। ওঁর চুল থেকে সুগন্ধি তেলের ঘ্রাণ পেতাম। তিনি বলেছিলেন, ‘সেটিংটাই আসল।’ টাইপ দিদিমণির সেই বাণী বড় অমোঘ। শুধু টাইপিংয়ের ক্ষেত্রেই নয়, জীবনের সর্বক্ষেত্রে সেটিংটাই আসল।
আজকের জাবরকাটা টাইপ মেশিন নিয়ে নয়, টেলিগ্রাফের মেশিন নিয়ে। যাকে সহজে বলা হত ‘টরেটক্কা মেশিন’। টরেটক্কাটা শিখতে পারলে তখন পোস্ট অফিসে, রেলে, জাহাজে চাকরি হওয়ার সুযোগ তৈরি হত। বঙ্গতনয়গণ, যারা কেরানি হওয়ার জন্য বলিপ্রদত্ত– ওরা টাইপ শিখতই আর একটু উচ্চাশা যাদের, তারা শর্টহ্যান্ডও শিখে নিত। পিটম্যানের শর্টহ্যান্ড বই ছিল বিখ্যাত। শর্টহ্যান্ড জানা লোকদের বলা হত ‘স্টেনো’। উচ্চপদস্থরা ‘স্টেনো’-কে ডিকটেশন দিত। বড় বড় সাহেবদের একটা করে স্টেনো রাখার চল ছিল। ওরা শর্টহ্যান্ডে সাহেবের বক্তব্য লিখে নিয়ে টাইপ করে সাহেবের টেবিলে রাখলে সাহেব সই করতেন। যাদের সাহেবের লেজুর হওয়াটা ঠিক পছন্দ ছিল না, তারা টেলিগ্রাফ শিখত।
একটা ছোট্ট যন্ত্র, চাপ দিলে ‘খট্’ শব্দ করে নিচে নামে, ছেড়ে দিলে ওপরে উঠে যায়। কম সময়ের জন্য চাপ দিলে ‘টরে’ শব্দ হয়, একটু বেশি সময় চেপে ছেড়ে দিলে ‘টক্কা’ শব্দ হয়। এই টরে ও টক্কা দু’টি মাত্র শব্দের অক্ষরে তৈরি হয় টেলিগ্রাফের ভাষা। যখন টেলিফোন সহজলভ্য ছিল না, তখন টরেটক্কার সাংকেতিক ভাষায় খবর দেওয়া-নেওয়া হত। স্কুলজীবনে একটা গান অনুরোধের আসরে প্রায়ই শোনা যেত– ‘টক্কা টরে, টক্কা টক্কা টরে। খবর এসেছে ঘর ভেঙেছে দারুণ ঝড়ে/ তারের ভাষায় সংকেতে টক্কা টক্কা টরে…।’
এই যে ‘মর্স’ সাহেবের শব্দ ভাষা, এটা ১৮৩৫ থেকেই সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ততদিনে বিদ্যুৎও আবিষ্কার হয়ে গেছে। যখন যন্ত্রটার ওপরটা চেপে নিচের বোতামে স্পর্শ করা হত, তখন বিদ্যুৎ চালু হত, সেটা হল ডট্ বা টরে, ছেড়ে দিলেই বিদ্যুৎ বিযুক্ত হয়, এটা হল ড্যাশ বা টক্কা। আজকের কম্পিউটারে যে অ্যালগারিদমের ভাষা, সেটাও ডট আর ড্যাশেরই খেলা। ডট আর ড্যাশের সমাহারেই তৈরি হয় নানারকম সফ্টওয়ার। এর আদি রূপ ছিল মর্স কোড। আমরা পোস্ট অফিসে দেখতাম কেউ একজন ‘টরে টক্কা’ বাজিয়ে চলেছে। মানে টেলিগ্রাম পাঠাচ্ছে।
সে সময়ের অনেক গল্প-উপন্যাসে পাই– ‘তার আসিল যে আমার স্ত্রী একটি পুত্র সন্তানের জননী হইয়াছেন’ কিংবা ‘তোর মায়ের অসুখ, বাবাকে শীঘ্র তার করে দে’। আসলে টেলিগ্রাম করাকে ইংরেজিতে বলা হত ‘wire’। ‘wire’ মানে তো তারই হয়।
টেলিগ্রাম আসা মানে একটা কোনও বড় খবর। সুসংবাদের চেয়ে দুঃসংবাদই বেশি আসত। পিওন যখন হাঁকত– ‘টেলিগ্রাম টেলিগ্রাম’, বাড়ির লোকের বুক দুরু দুরু শুরু হয়ে যেত। টেলিগ্রামের ভাষাটা ছোট করতে হত। কারণ প্রতিটি শব্দের জন্য পয়সা দিতে হত। এমনকী, কমা ফুলস্টপের জন্যও। ফলে টেলিগ্রাফিক ল্যাঙ্গোয়েজ নামে একটা ভাষাশৈলী তৈরি হয়ে গিয়েছিল। ‘মাদার সিরিয়াস কাম সুন’ ধরনের তো ছিলই, অন্যরকমও ছিল।
নবনীতা দেবসেনের দশম বিবাহবার্ষিকীতে অর্মত্য সেন বিদেশ থেকে নবনীতাকে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন– ‘ট্রিট দিস পেপার অ্যাজ ফ্লাওয়ার।’ রেলস্টেশনের স্টেশনমাস্টারকেও ট্রেনের খবর দেওয়া-নেওয়ার জন্য টরে-টক্কা করতে দেখেছি। ‘পথের পাঁচালী’ ছায়াছবিটির সেই অপূর্ব দৃশ্যটির কথা মনে পড়ে, টেলিগ্রাফের পোস্টে অপু-দুর্গার কান পেতে দাঁড়িয়ে থাকা।

আমার ছোটকাকাকে দেখতাম আপনমনে ঘরে টরে-টক্কা প্র্যাকটিস করছেন। তখন টরে-টক্কা শেখানোর জন্য একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছিল ‘জর্জ টেলিগ্রাফ’। সেই প্রতিষ্ঠানটি আজও আছে, কিন্তু সেই আদিবিদ্যাটি শেখানো হয় না আর। অন্য নানা কিছু শেখানো হয় বোধহয়। আমার কাকা সেই প্রতিষ্ঠানেই টেলিগ্রাফি শিখতে যেতেন। টাইপ-শর্টহ্যান্ডের মতো টেলিগ্রাফিরও স্পিড বাড়াতে হত। স্পিড বাড়ানোর জন্য ক্রমাগত অনুশীলন করতে হত।
টেলিগ্রাফির একটু উন্নত সংস্করণ ছিল ‘রেডিও টেলিগ্রাফি’। এখানেও সেই একই মেশিন। উপরের হাতল নিচের বোতাম স্পর্শ করলে বিদ্যুৎ সংযোগ হত, তখন রেডিও তরঙ্গ নির্গত হত। ছেড়ে দিলে তরঙ্গ নির্গত হত না। যখন সংযোগ হত, তখন ‘ডা’ শব্দ হত, ছেড়ে দিলে ‘ডিট’। টরে-টক্কার মতোই ডা-ডিট। এখানেও সেই মর্স-প্রণীত সংকেত। শূন্য এবং ড্যাস-এর সমাহার। আমি ১৯৭৫ সালে ভূমি রাজস্ব দফতরের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে হাওয়া অফিস বা মেটেরোলজিকাল অফিসে ঢুকি। আবহাওয়ার যাবতীয় তথ্য পাঠানোর নিজস্ব ভাষা আছে। সেই ভাষা পাঠানোর জন্য কখনও রেডিও টেলিগ্রাফি করতে হত। যেমন তখন আন্দামানের সঙ্গে, আগরতলার সঙ্গে, ইম্ফলের সঙ্গে কলকাতার আবহাওয়ার তথ্য আদানপ্রদানের জন্য রেডিও টেলিগ্রাফি করতাম।
এখনও মনে আছে, A= . – B= –… C= –.–. D= –.. ইত্যাদি। S=… O= – – –। যখন কোনও জাহাজ থেকে ক্রমাগত ‘ডিট ডিট ডিট ডা ডা ডা’ ভেসে আসে, বুঝতে হবে এটা ‘SOS’। ‘SOS’-এর পুরো অর্থ হল– ‘Save Our Soul’, মানে চরম বিপদ। খুব বড় সাইক্লোনের সম্ভাবনায় আমরা ‘SOS’ পাঠাতাম। যখন আমি খুব ‘ডা-ডিট’ প্র্যাকটিস করে ‘ডা-ডিট’ আমার মননে ঢুকিয়ে নিয়েছি, তখন আমি ব্যাঙের ভাষা বুঝতে পারতাম। ব্যাঙের ‘গ্যাগর গ্যাং, গ্যাগর গ্যাং’-এর সমাহার ‘ডা ডিট’-এর মতো করেই অনুবাদ করে নিতে পারতাম। এবং বর্ষায় ব্যাঙের গলার শব্দে বুঝতে পারতাম ‘ওয়েটিং ফর ইউ ডিয়ার, কাম সুন।’ অনুবাদ করে নিতে পারতাম, ‘আই লাভ ইউ বিলিভ মি।’ পাখির শব্দেও ‘টিই টিট্ টিট্ টিই টিই’ অনুবাদ হয়ে যেত।
এখন টেলিগ্রাফ মেশিনটাকে আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। আর স্যামুয়েল মর্স-এর খোঁজ উইকিপিডিয়ায় পাওয়া যাবে শুধু। মর্স কোড আর কাউকেই শিখতে হয় না আর, এককালে যেটা ছিল চাকরির চাবিকাঠি।
১৯৮০ থেকেই এই টেলিগ্রাফের ব্যবহার কমতে থাকে। নয়ের দশক থেকে দ্রুত হারে। ১৯৯৭ সালে ফ্রান্সের নৌবাহিনী টেলিগ্রাফ যন্ত্রটি ব্যবহার করে শেষ যে মেসেজটি পাঠিয়েছিল, তার মর্মার্থ হল– চিরতরে থেমে যাওয়ার আগে এটাই আমার শেষ আর্তনাদ।
ভারতে ১৮৫০ সালে ‘টরে টক্কা’ চালু হয়। ১৬৩ বছর পর, ২০১৩ সালের ১৪ জুলাই শেষ টেলিগ্রামটি পোস্ট অফিসের বড়কর্তা পাঠিয়েছিলেন রাহুল গান্ধীকে।
…পড়ুন ব্লটিং পেপার-এর অন্যান্য পর্ব…
১৬: ছদ্মবেশী পাগলের ভিড়ে আসল পাগলরা হারিয়ে গেল
১৫. ধূমপান নিষেধের নিয়ম বদলান, আকাশবাণীর স্টেশন ডিরেক্টরকে বলেছিলেন ঋত্বিক ঘটক
১৪. এমএলএ, এমপি-র টিকিট ফ্রি, আর কবির বেলা?
১২. ‘গাঁধী ভগোয়ান’ নাকি ‘বিরসা ভগোয়ানের পহেলা অবতার’
১১. কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্টের চক্করে বাঙালি আর ভোরবেলা হোটেল থেকে রওনা দেয় না
৫. তিনটে-ছ’টা-ন’টা মানেই সিঙ্গল স্ক্রিন, দশটা-পাঁচটা যেমন অফিসবাবু
৪. রাধার কাছে যেতে যে শরম লাগে কৃষ্ণের, তা তো রঙেরই জন্য
৩. ফেরিওয়ালা শব্দটা এসেছে ফার্সি শব্দ ‘ফির’ থেকে, কিন্তু কিছু ফেরিওয়ালা চিরতরে হারিয়ে গেল
২. নাইলন শাড়ি পাইলট পেন/ উত্তমের পকেটে সুচিত্রা সেন
১. যে গান ট্রেনের ভিখারি গায়কদের গলায় চলে আসে, বুঝতে হবে সেই গানই কালজয়ী
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
