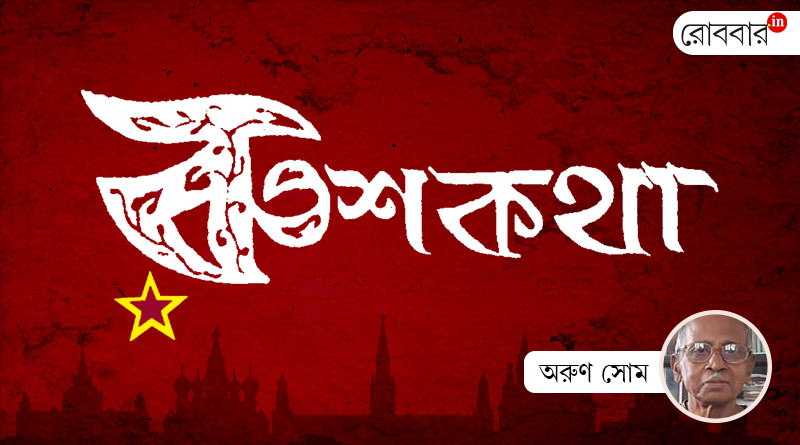
প্রগতির বাংলা বিভাগের প্রধান একজন রুশ ভদ্রমহিলা। ননীদা তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন, মামুলি দু’-একটা কথা হল তাঁর সঙ্গে। কিন্তু ওঁরা আমাকে নেবেন কি না বোঝা গেল না। রাইসা ভাসিলিয়েভ্না নামে ওই ভদ্রমহিলার তত্ত্বাবধানে পরবর্তীকালে দীর্ঘকাল আমি প্রগতিতে অনুবাদকের কাজ করি। তাঁর সঙ্গে বইপুথি নির্বাচনের ব্যাপারে আমার প্রায়ই খিটিমিটি বেঁধে যেত। এই নিয়ে স্থানীয় কর্মীদের মধ্যে একটা কথাই চালু হয়ে গিয়েছিল, ‘অরুণ যা চান, রাইসা ভাসিলিয়েভ্না তা চান না, রাইসা ভাসিলিয়েভ্না যা চান, অরুণ তা চান না।’

২২.
প্রগতির সঙ্গে প্রথম পরিচয়
ননীদার সঙ্গে কলকাতায় সাক্ষাৎ আর কথাবার্তার পরের বছর গ্রীষ্মকালে রুশ ভাষার শিক্ষকতার সুবাদে আবারও রুশ ভাষার শিক্ষকদের আন্তর্জাতিক সেমিনারে যোগদানের আমন্ত্রণ পেয়ে মস্কোয় যাওয়ার সুযোগ পাওয়া গেল। ভাবলাম, ভালোই হল, এবারে সঠিক জানতে পারব ‘প্রগতি প্রকাশন’ আমাকে কাজে নেবে কি না। মাঝখানে সভেত্লানা বৌদির একটা চিঠি পেয়েছিলাম। তাতে তিনি লিখেছিলেন, ‘এখনও সবই কেমন ভাসা ভাসা…’ ননীদাকে পত্রাঘাত করে আর বিরক্ত করিনি।
মস্কোয় আসার পর ননীদা আমাকে জানালেন যে আমার অনুবাদ করা নমুনাটা ওখানে এসে গেছে। একদিন উনি আমাকে নিয়ে ‘প্রগতি প্রকাশন’-এ যাবেন, কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন।
ননীদার কথামতো নির্ধারিত দিনে দুপুর ১২টা নাগাদ ওঁর বাড়ি এলাম। উনি আমায় সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন ‘প্রগতি প্রকাশন’-এর অফিসে। এবারেও আমার সেই একই ভুল: আমি হয়তো যথাসময়ের একটু আগেই পৌঁছে গিয়েছিলাম। ননীদার সবে ঘুম ভেঙেছে। বললেন, একটু ঘুরে ঘণ্টাখানেক বাদে আসতে। কী আর করি, বাইরে বেরিয়ে উল্টো দিকের বুলভারে একটা বেঞ্চিতে বসলাম। রাস্তায় দৃশ্য দেখে ঘণ্টাখানেক কাটানোর পর আবার কলিংবেল টিপলাম। এবারে ননীদা তৈরি। পরে বুঝতে পারি– আসলে এখানকার অনুবাদকরা যেহেতু বাড়িতে বসে কাজ করেন, অফিসে তাঁদের নিয়মিত হাজিরা দিতে হয় না সেই হেতু ওঁদের কাজের ধারাটাও অদ্ভুত। অনেকেরই সকাল শুরু হয় বেলা বারোটায়। তারপর সন্ধ্যা পর্যন্ত একটানা কাজ। কোনও কোনও সময় জরুরি কাজ থাকলে অবশ্য রাত জেগেও কাজ করেন। তা নইলে সন্ধ্যায় আড্ডা জমে, চলে রাতভোর।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে কয়েক মিনিটের হাঁটাপথ– তারপরই ইউনিভার্সিটি মেট্রো। সেখান থেকে ট্রেন ধরে ‘পার্ক কুলতুরি’ স্টেশন নেমেই জুবো্ভস্কি বুলভার– দু’পা হেঁটেই প্রগতির অফিস। এভাবে যাওয়াটাই তো সুবিধে। তা না করে ননীদা ধরলেন তুলনায় শম্বুকগতির এক যান– ট্রলিবাস। আমি কৌতূহল প্রকাশ করতে জানালেন পারতপক্ষে পাতালরেল এড়িয়ে চলেন তিনি। বললেন, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। কেবলই মনে হয় যেন পাতালে তলিয়ে যাচ্ছি। আশ্চর্য! এরকম অনুভূতি কখনও কারও হয়েছে বলে শুনিনি। পৃথিবীর সেরা ভূগর্ভ রেলপথ মস্কোর পাতাল রেলের প্রতিটি স্টেশনই প্রশস্ত, আলো-হাওয়ার কোনও অভাব নেই সেখানে। এমনকী লেনিনগ্রাদের মতো শহরের যে ভূগর্ভ রেলপথ, যেখানে অনেক সময় এসকালেটরের ওপরের সিঁড়ি থেকে ভূগর্ভ স্টেশন চোখেই পড়ে না, এমনকী স্টেশনের ভেতরেও লাইনের পাশে দেওয়াল দেওয়া, যাতে দরজাগুলো ট্রেন আসার সঙ্গে সঙ্গে কামরার খোলা দরজার গায়ে গায়ে লেগে খুলে যায়। এবং ট্রেন চলার সঙ্গে সঙ্গে যথারীতি বন্ধ হয়ে যায়– সেখানেও এরকম অনুভূতি আমার কখনও হয়নি। ননীদা বললেন লেনিনগ্রাদে পাতাল রেলে তিনি মাত্র একবারই চেপেছিলেন। আমি বললাম, ‘আপনি তো ইচ্ছে করলে গাড়িও কিনতে পারেন।’ উত্তরে তিনি বললেন, ‘তাহলে বলি, একটা দু’চাকার গাড়ি, মানে মোটর সাইকেল কিনেছিলাম। কিন্তু তোমার বৌদির তাড়নায় বছর ঘুরতে না ঘুরতে বেচে দিতে হল। তার সবসময় ভয় মাতাল অবস্থায় আক্সিডেন্ট না করে বসি। ছোটখাটো একটা দুর্ঘটনা ঘটেওছিল। অল্পের ওপর দিয়ে পার পেয়ে যাই। তবে ভাগ্যি ভালো যে মাতাল অবস্থায় নয়। পরে অবশ্য অভিজ্ঞতায় দেখেছি দুর্ঘটনা না ঘটিয়েও মাতাল অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে কেউ যদি ট্রাফিক পুলিশের হাতে ধরা পড়ে, তাহলে হাজতবাস ও জরিমানা ছাড়াও তার কঠোর সাজার ব্যবস্থা আছে। তাই কোনও মদ্যপই পারতপক্ষে নিজের গাড়ি নিয়ে সে ধরনের কোনও অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যায় না, গেলেও মদ ছোঁয় না। কিন্তু ননীদা সেদিন কথাপ্রসঙ্গে সেইরকমই এক হঠকারিতার কাহিনি আমাকে শোনালেন।

মস্কো রেডিওতে কাজ করতেন তাঁর এক ভারতীয় বন্ধু। ত্রিশের কোঠায় বয়স। গাড়ি কিনেছিলেন। রুশি প্রথা অনুযায়ী দামি কোনও জিনিস কিনলে লোকজন ডেকে ‘ধোয়াতে হয়’। ‘কী দিয়ে বুঝতেই পারছ’– হাসতে হাসতে ননীদা বলেন– অর্থাৎ কিনা কড়া পানীয় দিয়ে পার্টি দিতে হয়, তাও আবার মোটরগাড়ি বলে কথা। মস্কোতে যখন প্রাইভেট গাড়ি দুর্লভদর্শন ছিল, ভদ্রলোক পার্টি দিয়েছিলেন শহরের এক বড় রেস্তোরাঁয়। বাড়ি ফেরার পথে গাড়ি চালানোয় ক্ষমতা তাঁর ছিল না। গাড়ি চালানোর ভার স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যে রুশি বন্ধুটি নিলেন তাঁরও অবস্থা তথৈবচ। কিন্তু তিনি তা স্বীকার করলেন না। ননীদা ও সভেত্লানা সেদিন ভয়ে ওই গাড়িতে না চেপে ট্যাক্সি করে বাড়ির পথ ধরেছিলেন। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে তাঁরা সে যাত্রায় বেঁচে যান। মোটরগাড়িটি পথে এক ভারী পোস্টের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। গাড়ির মালিক-সহ আর যে দু’জন আরোহী ছিলেন, তাঁরা সকলেই প্রাণ হারান সে দুর্ঘটনায়। গুরুতর জখম হয়ে কোনওমতে প্রাণে বেঁচে যান চালকের আসনগ্রহণকারী রুশি বন্ধুটি। বিচারে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয় তাঁকে, তাঁর পার্টি সদস্যপদও খারিজ হয়ে যায়। ১৯৬২ সালের শীতকালে মস্কোর আউটার রিং রোডের ওপর এই দুর্ঘটনা ঘটে।
আমি চমকে উঠলাম। বললাম, সেই গাড়ির মালিকের নাম ইকবাল সিং নয়তো? ননীদা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুমি জানলে কী করে?’ আমি বললাম, ‘১৯৬৭ সালে মস্কোয় এক মনেস্টারি সংলগ্ন সমাধিক্ষেত্রে ঘুরতে ঘুরতে খ্যাত-অখ্যাত রুশিদের সমাধির মাঝখানে ওই ভারতীয় যুবকের সমাধি দেখতে পেয়ে আমি চমকে উঠেছিলাম। এখন জানা গেল তাঁর পরিচয়। যাঁর হঠকারিতায় ওই দুর্ঘটনা ঘটে, সেই রুশি ভদ্রলোকটি এককালে ছিলেন পেশায় ইঞ্জিনিয়ার, পরবর্তীকালে বাংলা ভাষাবিদ। এক সময় নাকি বিখ্যাত পরমাণু বিজ্ঞানী কুর্চাতভের অধীনেও কাজ করেন। ঘটনার সপ্তাহখানেক পরেই কলকাতার সোভিয়েত দূতস্থানের সংস্কৃতি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত কর্মী হয়ে তাঁর ভারতে যাওয়ার কথা ছিল। একটি ভুলের জন্য তাঁর কর্মজীবন ওলটপালট হয়ে যায়। কারাদণ্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তিনি ‘প্রগতি প্রকাশন’-এর বাংলা বিভাগে অন্যতম সম্পাদক (মূল রুশের সঙ্গে বাংলা মিলিয়ে দেখা যাঁর কাজ) হয়ে যোগ দেন। কর্মসূত্রে পরবর্তীকালে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল, আমার দু’-একটি অনুবাদের সম্পাদনার কাজও তিনি করেছিলেন। তাঁর স্বপ্নের দেশ ভারতবর্ষে আর কখনওই তাঁর যাওয়া হয়নি। পদোন্নতি ঘটার কোনও সম্ভাবনা নেই। দুর্ঘটনা থেকে তাঁর নিজের ও সভেত্লানার বেঁচে যাওয়ার প্রসঙ্গে ননীদা হাসতে হাসতে বললেন: রাখে হরি মারে কে?’
প্রগতির বাংলা বিভাগের প্রধান একজন রুশ ভদ্রমহিলা। ননীদা তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন, মামুলি দু’-একটা কথা হল তাঁর সঙ্গে। কিন্তু ওঁরা আমাকে নেবেন কি না বোঝা গেল না। রাইসা ভাসিলিয়েভ্না নামে ওই ভদ্রমহিলার তত্ত্বাবধানে পরবর্তীকালে দীর্ঘকাল আমি প্রগতিতে অনুবাদকের কাজ করি। তাঁর সঙ্গে বইপুথি নির্বাচনের ব্যাপারে আমার প্রায়ই খিটিমিটি বেঁধে যেত। এই নিয়ে স্থানীয় কর্মীদের মধ্যে একটা কথাই চালু হয়ে গিয়েছিল, ‘অরুণ যা চান, রাইসা ভাসিলিয়েভ্না তা চান না, রাইসা ভাসিলিয়েভ্না যা চান, অরুণ তা চান না।’ একদিন আমি ওঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ‘আচ্ছা, এ সমস্ত বই নির্বাচন কারা করেন?’ তিনি বললেন, ‘বাংলা বিভাগের তাতে কোনও হাত নেই। নির্বাচিত হয় আরও ওপর থেকে।’ আমার প্রশ্ন ছিল, ‘সেই ওপরওয়ালাদের কাছে গিয়ে কিছু অনুরোধ জানানো যেতে পারে না?’ তাতে তিনি বললেন, সেখানে যাওয়া সম্ভব নয়। আমি তখন হাসতে হাসতে তাঁকে বলেছিলাম: ‘তাহলে সোভিয়েত ইউনিয়নে ভগবান আছেন?’ এসব কটুকাটব্যের জন্য অবশ্য আমাদের মধ্যে কখনও মানোমালিন্য হয়নি। কাজের পরিবেশ বেশ সৌহার্দ্যপূর্ণ ছিল। এমনকী, রইসা ভাসিলিয়েভ্না একদিন কথায় কথায় ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে আমাকে এও বলেছিলেন যে, উনি আমাকে কাজে নেওয়ায় খুব একটা পক্ষপাতী ছিলেন না। সেটা অবশ্য আমি সেদিনই কিছুটা আঁচ করতে পেরেছিলাম।

সেদিন বাংলা বিভাগের ঘরে প্রগতির আরও কয়েকজন স্থানীয় কর্মী কাজ করছিলেন। রথীন চ্যাটার্জি নামে একজন বাঙালি যুবকও প্রগতিতে তখন প্রুফ রিডারের কাজ করতেন। তাঁকে আমি আগে থাকতে চিনতাম– ভূতত্ত্ব নিয়ে এদেশে পিএইচডি করেছেন, দেশে ফিরে যাওয়া তাঁর পক্ষে একটু অসুবিধাজনক, যেহেতু তাঁর স্ত্রী রুশি, ভারতে যেতে ঠিক রাজি নন। ফলে রথীনকে সহানুভূতির ভিত্তিতে এখানে কাজে বহাল করা হয়েছে। এখানে লেখাপড়া শেখার পর অনেকেই দেশে ফিরতে চান না, কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নে তাঁদের যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পাওয়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই। বিদেশিদের চাকুরির ক্ষেত্র ছিল সীমিত– হয় ‘প্রগতি’ ও ‘মির’-এর মতো প্রকাশনা সংস্থা, নয়তো মস্কো রেডিও। ভূতত্ত্ববিদ রথীনকে পরে শেষ পর্যন্ত স্থায়ীভাবে মস্কো রেডিওতে কাজ নিয়েই সারা জীবনের মতো থাকতে হয়েছিল। আমাদের জানাশোনার মধ্যে একমাত্র ডাঃ শান্তি রায়ই ওখানে হাসপাতালের ডাক্তার ছিলেন। উনি কলকাতার মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করা ডাক্তার। ছয়ের দশকের প্রথম দিকে কোনও এক সময় মস্কোয় এসেছিলেন চিকিৎসার জন্য আগত শ্রীরামপুরের কমরেড পাঁচু ভাদুড়ির সঙ্গী হয়ে। তারপর পাকাপাকি মস্কোয় থেকে যান।

রথীনকে দেখছি না কেন, জানতে চাইলে ওই কর্মীদের মধ্যেই একজন পরিষ্কার বাংলায় বলল, রথীন ছুটিতে আছেন। আমি চমৎকৃত হলাম। যুবকের ভাষায় সামান্য অবাঙালি টান আছে, যেমন আমাদের দেশের অন্য প্রদেশের কেউ কেউ পরিষ্কার বাংলা বললেও অনেক সময় তাদের কথার মধ্যে থেকে যায়। একেবারে ভারতীয় চেহারা। তাই আমার মনে হল, এ যুবক অবাঙালি হলেও, নির্ঘাত ভারতীয়। আলাপ হল– বলল ‘আমার নাম মির্জো।’ আমি শুনলাম ‘মির্জা’– ভাবলাম তাহলে তো ভারতীয়ই। কিন্তু সে হেসে বলল, ‘আমি তাজিকিস্তানের লোক’। অনেকেই আমাকে ভারতীয় বলে মনে করে, যেমন আপনার বন্ধু রথীনকে অনেকে সোভিয়েত দেশের উজবেক প্রজাতন্ত্রের লোক বলে ভুল করে। তার মুখেই শুনলাম, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগেও সে বছরখানেক ক্লাস করেছে। আচার্য সুনীতিকুমার নাকি তার বাংলা শুনে বলেছিলেন, ‘তুমি অনেক দূর যাবে।’ কিন্তু কতদূর আর সে যেতে পারল? সোভিয়েত ইউনিয়নের সেই একই কালব্যাধি– অতিরিক্ত মদ্যপান তাকে অকালে গ্রাস করল।
মির্জোর সঙ্গে পরে কাজ করার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল। আমার প্রথম অনূদিত গ্রন্থ ‘রুশ ইতিহাসের কথা ও কাহিনী’র সে সম্পাদনা করেছিল। অফিস তার প্রায়ই কামাই হত, অনেক সময় অমুক অনুবাদকের বাড়ি গিয়ে ওঁর অনুবাদ সম্পাদনা করছিলাম– এইরকম কোনও একটা কৈফিয়ত দিত, কোনও সময় বরফে পা পিছলে গিয়ে তার পা মচকে যেত, কখনও ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে অফিসে আসত, হয়তো বলে দিল কোন পাগল তাকে ল্যাং মেরে ফেলে দিয়েছে, কখনও দেখা যেত তার কপালে ইয়া বড় একটা ঢিবি। সবেরই কারণ আসলে সেই এক, কৈফিয়ত অনেকরকম। বিয়ে করেছিল এক লাটভীয় মেয়েকে। মস্কোয় আসার পর গ্রামে আর একবারও যায়নি, বলত সেখানে গেলে মসজিদে বিধিবদ্ধভাবে নিকাহ সম্পন্ন না করলে তাকে গ্রামে ঢুকতেই দেবে না। এক শীতের বিকেলে মস্কোর এক বন্ধুর ফ্ল্যাটে তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। সারারাত মদ্যপানের পর বন্ধুটি ওকে নিদ্রিত অবস্থায় ফ্ল্যাটে রেখে কাজে বেরিয়ে গিয়েছিল। পরে যখন সে কাজ থেকে ফিরে আসে, তার অনেক আগেই মির্জোর হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। তার বয়স তখন বড়জোর ৪০ হবে।
মৃতদেহ গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য মির্জোর বাবা আর ভাইয়েরা এসেছিলেন। নেহাতই গ্রামের খেটে খাওয়া চাষি শ্রেণির মানুষ– চেহারা দেখে তাই মনে হল। মির্জো অপরিমিত মদ্যপান করত এবং অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে মারা গেছে– একথা শুনে তো তাঁরা অবাক।
…পড়ুন রুশকথা-র অন্যান্য পর্ব…
পর্ব ২১। সোভিয়েতে অনুবাদকরা যে পরিমাণ অর্থ উপার্জন করত, সে দেশের কম মানুষই তা পারত
পর্ব ২০। প্রগতি-র বাংলা বিভাগে নিয়োগের ক্ষেত্রে ননীদাই শেষ কথা ছিলেন
পর্ব ১৯। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নাকি খুব ভালো রুশভাষা জানতেন, প্রমথনাথ বিশী সাক্ষী
পর্ব ১৮। লেডি রাণু মুখার্জিকে বাড়ি গিয়ে রুশ ভাষা শেখানোর দায়িত্ব পড়েছিল আমার ওপর
পর্ব ১৭। একদিন হঠাৎ সুভাষদা আমাদের বাড়ি এসে উপস্থিত ফয়েজ আহমেদ ফয়েজকে নিয়ে
পর্ব ১৬। মুখের সেই পরিচিত হাসিটা না থাকলে কীসের সুভাষ মুখোপাধ্যায়!
পর্ব ১৫। রুশ ভাষা থেকেই সকলে অনুবাদ করতেন, এটা মিথ
পর্ব ১৪। মস্কোয় ননীদাকে দেখে মনে হয়েছিল কোনও বিদেশি, ভারতীয় নয়
পর্ব ১৩। যিনি কিংবদন্তি লেখক হতে পারতেন, তিনি হয়ে গেলেন কিংবদন্তি অনুবাদক
পর্ব ১২। ‘প্রগতি’ ও ‘রাদুগা’র অধঃপতনের বীজ কি গঠনপ্রকৃতির মধ্যেই নিহিত ছিল?
পর্ব ১১। সমর সেনকে দিয়ে কি রুশ কাব্যসংকলন অনুবাদ করানো যেত না?
পর্ব ১০। সমর সেনের মহুয়ার দেশ থেকে সোভিয়েত দেশে যাত্রা
পর্ব ৯। মস্কোয় অনুবাদচর্চার যখন রমরমা, ঠিক তখনই ঘটে গেল আকস্মিক অঘটন
পর্ব ৮: একজন কথা রেখেছিলেন, কিন্তু অনেকেই রাখেননি
পর্ব ৭: লেনিনকে তাঁর নিজের দেশের অনেকে ‘জার্মান চর’ বলেও অভিহিত করত
পর্ব ৬: যে-পতাকা বিজয়গর্বে রাইখস্টাগের মাথায় উড়েছিল, তা আজ ক্রেমলিনের মাথা থেকে নামানো হবে
পর্ব ৫: কোনটা বিপ্লব, কোনটা অভ্যুত্থান– দেশের মানুষ আজও তা স্থির করতে পারছে না
পর্ব ৪: আমার সাদা-কালোর স্বপ্নের মধ্যে ছিল সোভিয়েত দেশ
পর্ব ৩: ক্রেমলিনে যে বছর লেনিনের মূর্তি স্থাপিত হয়, সে বছরই ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙার সূচনাকাল
পর্ব ২: যে দেশে সূর্য অস্ত যায় না– আজও যায় না
পর্ব ১: এক প্রত্যক্ষদর্শীর চোখে রাশিয়ার খণ্ডচিত্র ও অতীতে উঁকিঝুঁকি
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
