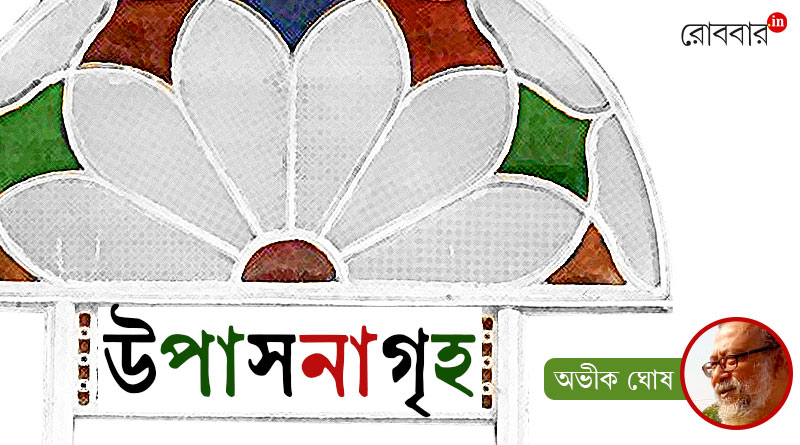
সাধক মানুষেরা, যাঁরা নিজের সমস্ত শক্তিকে পরমার্থ লাভের জন্যই প্রয়োগ করতে চান, তাঁরা অনেক সময় লোকালয় ছেড়ে নির্জন পর্বতে চলে যান। শক্তির অপব্যয় তাঁরা এড়াতে চান। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের স্পষ্ট উপলব্ধি, মানুষকে একেবারে ত্যাগ করে যাওয়া, মানুষের ধর্ম নয়। তাছাড়া, নির্জনতা বাইরে বাইরে খুঁজে পাওয়া নাই যেতে পারে। আরও বড় কথা হল, এই নির্জনতা আসলে আছে আমাদের অন্তরের মধ্যেই। অন্তরের মধ্যে এই নির্জনতা না থাকলে, কোনও পর্বতগুহা, সমুদ্রতীরে তাকে আমরা পেতে পারি না।

৮.
বসন্তোৎসবে শান্তিনিকেতনে বহু মানুষের সমাগম হয়। বিশ্বভারতী উৎসবের আয়োজন না করলেও দোলের দিনে শান্তিনিকেতনে আসাটা অনেক মানুষের কাছে যে কোনও কারণেই হোক, একটা আকর্ষণীয় ব্যাপার মনে হয়। সপ্তাহান্তের ছুটির সঙ্গে তারিখের সমাপতন হলে সেই সমাগম আরও বেশি। স্থানীয় বহু মানুষের উপার্জনের সুযোগ ঘটায় তাঁরা খুশি হন। যাঁদের সেই প্রয়োজন নেই, শান্তিনিকেতনের তেমন অধিবাসীরা নানান কারণেই নানারকম অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে বিরক্ত বোধ করেন। এবার সেই যুগপৎ উচ্ছ্বাস-বিরক্তির দিনগুলিতে রবীন্দ্রনাথের যে অভিভাষণটির কথা মনে হচ্ছিল, তার শিরোনাম ‘অন্তর বাহির’।
শুরুতে বলছেন, ‘আমরা মানুষ, মানুষের মধ্যে জন্মেছি। এই মানুষের সঙ্গে নানাপ্রকার মেলবার জন্যে, তাদের সঙ্গে নানাপ্রকার আবশ্যকের ও আনন্দের আদানপ্রদান চালাবার জন্যে আমাদের অনেকগুলি প্রবৃত্তি আছে।’
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
আমরা যখন সংসারে থাকি, এই প্রবৃত্তিগুলি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নানা দিকে নানারকম ভাবে মানুষের সঙ্গ বা সংসর্গের উত্তেজনায় নিজেকে জড়িয়ে রাখে। নানারকম দেখাশোনা, মেলামেশা, হাসিগল্প, আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণের মধ্যে এই প্রবৃত্তি নিজেকে প্রয়োগ করতেই থাকে, বিরামের কথা ভাবতেই পারে না।
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
আমরা যখন সংসারে থাকি, এই প্রবৃত্তিগুলি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নানা দিকে নানারকম ভাবে মানুষের সঙ্গ বা সংসর্গের উত্তেজনায় নিজেকে জড়িয়ে রাখে। নানারকম দেখাশোনা, মেলামেশা, হাসিগল্প, আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণের মধ্যে এই প্রবৃত্তি নিজেকে প্রয়োগ করতেই থাকে, বিরামের কথা ভাবতেই পারে না। লোক, লৌকিকতার বিচিত্র কৃত্রিম খেলায় মনকে মাতিয়ে রাখে এই প্রবৃত্তি, মনকে শান্ত করার সমস্ত প্রয়োজন, সুযোগ, সম্ভাবনা, জীবন থেকে হারিয়ে যেতে থাকে। সমস্ত উদ্যম তখন নতুন নতুন সামাজিক আমোদের সন্ধানে আর সৃষ্টিতে মেতে থাকে। এই প্রবৃত্তি নিয়মিত ইন্ধন আর চর্চায় যখন লাগামছাড়া বেড়ে ওঠে, তখন দিনরাত নতুন নতুন সমাজবিলাসের উন্মাদনায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে জীবন, জীবনের পথ চলার জন্য আর কোনও লক্ষ্য স্থির করার উপায় থাকে না।
মানুষের প্রতি মানুষের যে স্বাভাবিক প্রেম, এই চাঞ্চল্য আর উদ্যমের পিছনে সেই প্রেমই যে প্রাণিত করে তা নয়। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, ‘সামাজিক এবং প্রেমিক একই লোক নয়– অনেক সময় তার বিপরীতই দেখতে পাই। অনেক সময় লক্ষ্য করা যায় সামাজিক ব্যক্তির মনে গভীরতর প্রেম ও দয়ার স্থান নেই।’ অমিতব্যয়ী মানুষ যেমন অন্যের দুঃখ দূর করার জন্যই দান করেন, এমন নাই হতে পারে। নানারকম ভাবে খরচ করার খেলায় তাকে মাতিয়ে রাখে তার খরচের প্রবৃত্তি।
দান আর ব্যয়ের পার্থক্যের কথা মনে করেছেন রবীন্দ্রনাথ। ‘আমরা মানুষের জন্যে যা দান করি তা একদিকে খরচ হয়ে অন্য দিকে মঙ্গলে পূর্ণ হয়ে ওঠে, কিন্তু মানুষের কাছে যা ব্যয় করি তা কেবলমাত্রই খরচ। তাতে দেখতে পাই আমাদের গভীরতর চিত্ত কেবলই নিঃস্ব হতে থাকে, সে ভরে ওঠে না। তার শক্তি হ্রাস হয়, তার ক্লান্তি আসে, অবসাদ আসে– নিজের রিক্ততা ও ব্যর্থতার ধিক্কারকে ভুলিয়ে রাখবার জন্যে কেবলই তাকে নূতন নূতন কৃত্রিমতা রচনা করে চলতে হয়, কোথাও থামতে গেলেই তার প্রাণ বেরিয়ে যায়।’
এইজন্য সাধক মানুষেরা, যাঁরা নিজের সমস্ত শক্তিকে পরমার্থ লাভের জন্যই প্রয়োগ করতে চান, তাঁরা অনেক সময় লোকালয় ছেড়ে নির্জন পর্বতে চলে যান। শক্তির অপব্যয় তাঁরা এড়াতে চান। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের স্পষ্ট উপলব্ধি, মানুষকে একেবারে ত্যাগ করে যাওয়া, মানুষের ধর্ম নয়। তাছাড়া, নির্জনতা বাইরে বাইরে খুঁজে পাওয়া নাই যেতে পারে। আরও বড় কথা হল, এই নির্জনতা আসলে আছে আমাদের অন্তরের মধ্যেই। অন্তরের মধ্যে এই নির্জনতা না থাকলে, কোনও পর্বতগুহা, সমুদ্রতীরে তাকে আমরা পেতে পারি না।
রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ, অন্তরের সেই নিভৃত আশ্রয়টিকে চিনে নেওয়ার কাজে মন দিতে হবে। অন্তরের সেই নিভৃত আশ্রমে যাতায়াত বাড়িয়ে, নিয়মিত যাতায়াতের পথটি সহজ করে তুলতে হবে।
মানুষকে ছেড়ে যাওয়ার পথটিকে রবীন্দ্রনাথ মনে করছেন, ‘রোগের চেয়ে চিকিৎসাকে গুরুতর করে তোলা।’ সেইজন্য অনেক ধর্মলুব্ধ মানুষ মনে করেন, মনুষ্যত্বকে আনন্দহীন শুকনো করে তোলাই সিদ্ধিলাভের লক্ষণ। আমার নিজের খুব প্রিয় রবীন্দ্রনাথের পরামর্শটি, ‘মানুষকে সম্পূর্ণ সহজ হতে হবে; উদ্দামভাবে বেহিসাবি হলেও চলবে না, কৃপণভাবে হিসাবি হলেও চলবে না। এই মাঝখানের রাস্তায় দাঁড়াবার উপায় হচ্ছে– বাহিরের লোকালয়ের মধ্যে থেকেও অন্তরের নিভৃত নিকেতনের মধ্যে নিজের প্রতিষ্ঠা রক্ষা করা। বাহিরই আমাদের একমাত্র নয় অন্তরেই আমাদের গোড়াকার আশ্রয় রয়েছে তা বারংবার সকল আলাপের মধ্যে, আমোদের মধ্যে, কাজের মধ্যে অনুভব করতে হবে। সেই নিভৃত ভিতরের পথটিকে এমনি সরল করে তুলতে হবে যে, যখন-তখন ঘোরতর কাজকর্মের গোলযোগেও ধাঁ করে সেইখানে একবার ঘুরে আসা কিছুই শক্ত হবে না।’
এই ধাঁ করে ঘুরে আসার সাধনা জীবনে সহজ হয়ে উঠুক, এই প্রার্থনা। সমস্ত কলরবের মধ্যে সেই চিরস্থায়ী অবকাশটিকে যেন সঙ্গে রাখতে পারি। ‘এই অবকাশ তো কেবল শূন্যতা নয়। তা স্নেহে প্রেমে আনন্দে কল্যাণে পরিপূর্ণ। সেই অবকাশটিই হচ্ছেন তিনি যাঁর দ্বারা উপনিষৎ জগতের সমত্ত কিছুকেই আচ্ছন্ন দেখতে বলেছেন। ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।’
…পড়ুন উপাসনাগৃহ-র অন্যান্য পর্ব…
পর্ব ৭। সমগ্র অখণ্ড সৃষ্টির সৌন্দর্য একটি গানের মতো পূর্ণ
পর্ব ৬। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন উপনিষদ ভারতবর্ষের ব্রহ্মজ্ঞানের বনস্পতি
পর্ব ৫। ‘ঈশ্বর সর্বত্র আছেন’ কথাটা অভ্যাসের মতো হয়ে গেলে তার মধ্যে আর প্রাণ থাকে না
পর্ব ৪। আনন্দের ভাষা শেখাকেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন মুক্তির পথ
পর্ব ৩। সমগ্রের সঙ্গে যোগসাধনে আমাদের মঙ্গল
পর্ব ২। আমাদের চাওয়ার শেষ নেই, কারণ আমরা অনন্তকে চাই
পর্ব ১। ‘অসতো মা সদ্গময়’ মন্ত্রের অর্থ কৈশোরে বুঝিনি, শব্দগুলো ভালো লেগেছিল খুব
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
