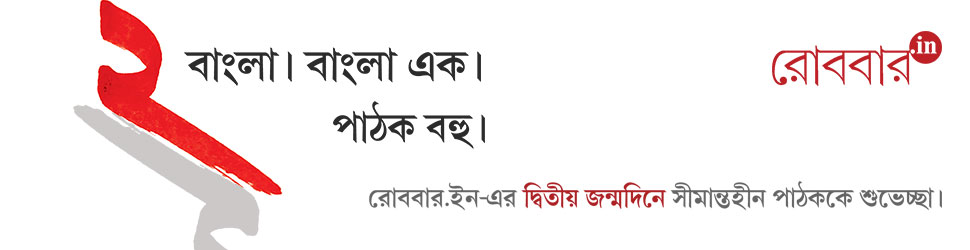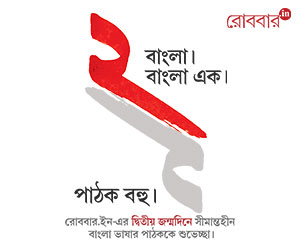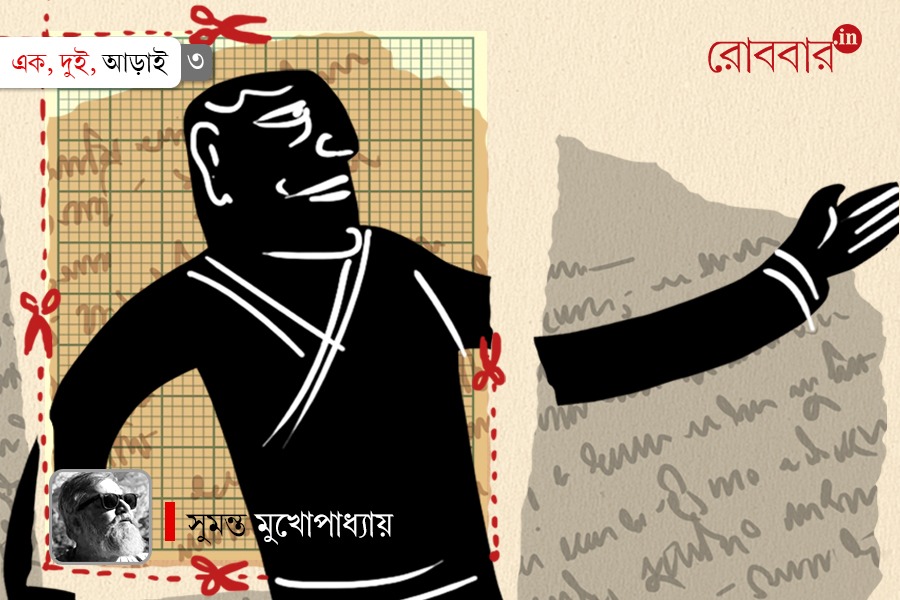
কবিতা হোক, উপন্যাস হোক আর নাট্যাভিনয়– সব কিছুর জন্যই নিজের শরীরটাকে আকাশছোঁয়া অনুভূতিতে বাড়িয়ে নেওয়া চাই। গুরুজনরা তাই বলে গেছেন। আমাদের রাজনীতি নড়ে না। আমাদের মেজাজ চড়ে না। সবই ভীষণ মাপে মাপে মন্টুর বাপের নন্দনতত্ত্বে নির্ভর করে চলেছে। এর মাঝে এক ঘর অন্ধকারে ভর করে যখন অন্ধ অভিনেত্রী বলে, ‘এ ঘরে কী একদিনও আলো জ্বলবে না?’ তখন আলো অন্ধকার নতুন মানে নিয়ে জেগে ওঠে। অন্ধ-মানুষের দৃষ্টিশক্তি নেই ঠিকই, কিন্তু বাকি চারটে ইন্দ্রিয় আমাদের আছে কই? হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করার কথা ছিল। স্পর্শ, গন্ধ, স্বাদ, শ্রবণ– আমাদের দৃশ্য এসে খেয়ে গেছে।

৩.
ঘোড়া দেখলেই সবার পায়ে বেমালুম বাত। কোনও কিছু লিখতে গেলে এই তেজি প্রাণীর চলাফেরা মনে আসে। সোজা গট গট করে কিছু যে বলে যাব, এমন কনফিডেন্স কস্মিনকালেও ছিল না। আড়ে আড়ে কোনাকুনি চলতে গিয়েও লজ্জায় মাথা কাটা যায়। তাই আড়াই চালে ভাবি। বাধা টপকে আদার ব্যাপারীও মোক্ষম ঘরটিতে গিয়ে বসতে পারে চোখের পলকে। কাটাকুটি– সে পরের কথা। তবে নিওলিথ স্তব্ধতায় না হোক মহীনের পোষা জীবটির আপন মনে ঘাস খাওয়ার দৃশ্য নিউটাউনেও দেখা যায়, সূর্যাস্তে, সন্ধ্যায়। স্যুররিয়াল। বিষাদ মন্থর। দিনশেষের লালচে আলোয় পিঠের ভাবনা-ক্ষতগুলো চিক চিক করে। কারও হাসি পায়, কারও চোখে জল আসে।
আলো অন্ধকার
গিরিশ মঞ্চে দর্শক আসনে অন্ধকারে চুপচাপ বসেছিলাম। রবীন্দ্রনাথের ‘রাজা’ নাটকটা সোজা এসে বুকে ধাক্কা মারল। অনেকদিন পরে বড় মঞ্চে সম্পূর্ণ নতুন করে নিজেদের পুরনো প্রোডাকশন ‘রাজা’ অভিনয় করছিল ‘শ্যামবাজার অন্যদেশ’। ‘শ্যামবাজার অন্যদেশ’ মূলত দৃষ্টিহীনদের দল, তবে কিছু সৃষ্টিছাড়া মানুষ আর ছেলেমেয়েও এদের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন দীর্ঘদিন। দীর্ঘদিন মানে, প্রায় ৩০ বছর। গত তিন দশকের নানা ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে এঁরা চলেছেন। কোভিডের সময় লকডাউনে দিব্যদৃষ্টির অধিকারে সবচেয়ে বিপজ্জনক অবস্থা পার হয়েছেন এই দলের কর্মীরা। দু’জন সহযোদ্ধা-কে হারিয়ে যেতে দেখেছেন। অন্ধদের নিয়ে নাট্যদল যখন গড়ে ওঠে, প্রথমে তার নাম ছিল ‘ব্লাইন্ড অপেরা’। তারপর বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে এই ‘অন্যদেশ’।

এতদিন ধরে এশিয়া মহাদেশের কোথাও দৃষ্টিহীনদের নাটকের দল টিকে আছে বলে শুনিনি। এই দলের চার-পাঁচজন মানুষের থিয়েটার করাই পেশা, অবসর পেলে অন্য কাজ করে থাকেন। এঁদের নিয়ে তিনটি ছোট ছোট ডকুমেন্টারি বানানো হয়েছে। দুটো বানিয়েছেন শোভন তরফদার, অন্যটা নীলাদ্রিশেখর দাশশর্মা। কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গের নানা জেলার মঞ্চে শুধু নয়, ‘অন্যদেশ’– দিল্লির ‘ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা’-র মঞ্চে অভিনয় করেও পুরস্কার জিতে নিয়ে এসেছে। এই পরিচয়টুকু বলে নিতে হল, কারণ এই দলের বেশিরভাগ অভিনেতা যেমন দেখতে পান না, তেমনই কলকাতা থিয়েটারের বেশিরভাগ দর্শক, বেশিরভাগ নাট্যকর্মী এঁদের কাজকর্ম দেখতে পান না। এও একরকম অন্ধত্ব!
অথচ কলকাতার বুকে নাটকের দলগুলোতেই শুধু তো নয়, আমাদের ছোটবেলায় থিয়েটারের আবহাওয়ায় চারিদিকের বাতাসে পুওর থিয়েটার, গ্রোটভস্কি, অগুস্ত বোয়াল, এরউইন পিসকাটোর, শতাব্দী, অঙ্গনমঞ্চ, পথনাটক– এইসব শব্দ উড়ে বেড়াত। ১৯৮৯-এর ১ জানুয়ারি ‘হল্লা বোল’ নাটক চলাকালীন সফদর হাশমি খুন হয়ে যান। সেই ছোট বয়সেও স্কুল-পাঠশালায় নাটক ভালোবাসতাম যারা, হাশমির কাজকর্ম নিয়ে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলাম সেদিন। মনে আছে, হাশমি-র লেখা নাটকের একটা বাংলা অনুবাদ সংকলন ছাপে বাংলার ‘নাট্য একাডেমি’, ১৯৮৯ সালের এপ্রিল মাসে। এখনও নিশ্চয়ই পাওয়া যায় সেই বই। বাদল সরকার, ‘ভুল রাস্তা’ লিখলেন ১৯৮৯ নাগাদই, মার্চ মাসে ‘শতাব্দী’ বোধহয় প্রথম অভিনয় করে নাটকটা।

‘ভুল রাস্তা’ ছাপা হয়েছিল ‘দেশ’ পত্রিকায়। পড়ার সেই শারীরিক অনুভূতি এখনও লেশমাত্র রয়ে গেছে। তারপর কার্জন পার্কে আমাদেরই ভেতর থেকে বন্ধুরা বেরিয়ে এসে চারদিক থেকে লোক ডেকে অভিনয় করে এল একদিন। আজকের ডিরেক্টর-অভিনেতা সুজন মুখোপাধ্যায় আর শিবপ্রসাদ-এর সেই উত্তেজিত লড়াকু নাট্যকর্মী চেহারাটা কে আর তেমন দেখেছে!
এসব প্রসঙ্গ আসছে কেন? আসছে কারণ, কীভাবে যেন বাংলা নাটক থেকে তার অন্তরের সবচেয়ে বড় জোরের জায়গাটা গত এক যুগে হারিয়ে যেতে দেখলাম। সেই জোর হল তার গভীরতর রাজনীতির জোর। এর জন্য দায়ী কে? নতুন জেনারেশন?
এক কবি একদিন কফি হাউসে বসে কফিতে দু’-চুমুক মেরে আমাকে বলেছিলেন, এ-হল পোস্ট-পলিটিকস যুগ। নতুন ছেলেমেয়েরা নাকি ভার্চুয়াল জগতের বাসিন্দা, কোনও কিছুতেই তাদের মন নেই। ভদ্রলোক যে এই পোড়া দেশে বেঁচে-বর্তে নিজের বস্তাপচা মাল এখনও গছিয়ে চলেছেন, সে ওই বাচ্চা ছেলেমেয়েদেরই দৌলতে। উমর খলিদ জামিন পায়নি ঠিকই, কিন্তু তার মতো ছেলেমেয়েদের উপস্থিতির ওপর ভর করেই পলিটিকস-এর যথার্থ ধারণা এখনও আমাদের কথায় উঠে আসতে পারছে।
‘পলিটিকস’ কথাটা ছোট করে ধরলে যা বোঝায়, সেসবের অবশ্য কোথাও কোনও খামতি নেই। মঞ্চ-নাটকে কী রাজনৈতিক কথাবার্তা আসছে না? আসছে। নানা ইস্যুতে রাস্তা জোড়া প্রতিবাদে নাটকের দলগুলোর ছেলেমেয়েরা ঝাঁপিয়ে পড়ছে না? পড়ছে বইকি! সমসাময়িকের খণ্ড, ইটের টুকরোর মতো ছিটকে আসছে মঞ্চ থেকে চারদিকে। ভাইরাল হয়ে উঠছে গান। নাম আছে, না কি নেই– তা নিয়ে বিতণ্ডা হচ্ছে দেখার মতো। ভাইরাল জিনিসটা ভালো হয় কি না, সেকথা জানি না যদিও। একে বলা যায় ছোট রাজনীতি ওরফে দুর্নীতির কথা। কিন্তু বড় করে যৌন নিগ্রহ এবং নাট্যদলে ক্ষমতার অপব্যবহার নিয়েও ছেলেমেয়েরা দিব্যি লড়ে চলেছে।

এ তো গেল প্রতিদিনের বাঁচা-মরার লড়াই। কিন্তু এর থেকে থিয়েটারের ভাষা তৈরি হতে পারে তখনই, যখন এই টুকরোগুলো জুড়ে জুড়ে একটা অভিমুখ পাওয়া যায়। যাকে রাস্তা বলতে পারি। নতুন সংকটে নতুন রাস্তা। বাকি সব পথ চলতে চলতে একটা গন্তব্য ঠিক করে নেয়। তখন হওয়ার আগেই সব হয়ে থাকে। এটাকেই বলছি রাজনীতিহারা বাংলা নাটক। ঠিক একই দশা বাংলার সুবেশ সুকেশ তেলচুকচুকে বেশিরভাগ লিটল ম্যাগাজিনের। তারও ভেতর সব ঠিক হয়ে আছে আগে থেকেই। কোথায় যেতে হবে, কেমন দেখতে হবে, ক’-পাতা বিজ্ঞাপন যাবে, কার নামে বিশেষ সংখ্যা করতে হবে, ক্রোড়পত্র ক’টা চাই, কাকে চাই– সব ঠিক করা আছে। এমনকী শিশুরাও জেনে গেছে এইসব কথা। আমাদের সংস্কৃতির সব থেকে জোরালো দুটো প্ল্যাটফর্ম নিয়ে ভাবলে আঁতকে উঠে, এই কথাটাই মনে হচ্ছে বারবার। সিনেমার দশা আর নাই বা তুললাম। লিটল ম্যাগাজিন প্রসঙ্গে সবিস্তারে ফিরে আসতে হবে আরেক দিন। পাঠক হিসেবে দর্শক হিসেবে আপাতত এগুলো বলা দরকার। কে কী ভাববে, কে কী বলবে– সেসব এহবাহ্য।
এখন রাজনীতি বলতে কী বুঝলাম? বুঝলাম, দাঁড়ানোর জায়গা। একটা নয়, অজস্র। এলোমেলো নয়– সমস্ত ইতিহাস আর বাস্তবটার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বদল সম্ভব দাঁড়ানোর জায়গা। যেখান থেকে চারপাশটাকে খানিক বুঝতে পারি। বদলে নিতে পারি নিজের কাজের ধারণা। ক’টা ছোট ছোট উদাহরণ টেনে আনা যাক। এই ক’দিন আগে বাস-অটো রিকশার পিছন ভাগে যেসব আজব কথা লেখা থাকে, তার একটার দিকে নজর পড়ল– ‘দেখা হলে বলে দিও আজও বেঁচে আছি।’ এখন এই কথাটার সেন্টিমেন্টাল দেবদাস-মার্কা বয়ান পোড়খাওয়া লোককে সবসময় টানে না। তবু ভাবছিলাম, আহা রে প্রেমিকটার কী কষ্ট! কার সঙ্গে কার কোথায় দেখা হবে? হলেই বা উদ্দিষ্ট মানুষটি সে বেঁচে আছে কি না, জানতেই বা চাইবে কেন? এইসব ভাবনার মধ্যেই দেখা গেল ম্রিয়মান কন্ডাকটরকে নামিয়ে নিয়েছে আমাদের সিভিক ভাই। অস্থানে-কুস্থানে ফাঁকা বাস নিয়ে হেঁচকি তোলার অপরাধে তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দূরবর্তী বুলেট আরোহী সার্জেনের দিকে। কলকাতার বাস পরিবহনের অবস্থাটা মুহূর্তে সব কিছু উল্টে দিল। এই ড্রাইভার কন্ডাকটর মিনি মিনি বাস বাস চোখ কান নাক মুখ রোগা রোগা চেহারার সব মানুষ কাদের যেন বলতে চাইছে, দেখা হলে বলে দিও, আজও বেঁচে আছি। আমাদের কবি, আমাদের নাট্যকর্মী, আমাদের লেখক, আমাদের অভিনেতা– সবাই যে যেখানে আছে, রাস্তায় যার সঙ্গেই দেখা হবে, বলে দেবে, আজও বেঁচে আছে।

এই রকমই একবার এক ছোট-হাতি ভর্তি মানুষ তাদের শ্রমিক সহকর্মীর মরদেহ নিয়ে ‘ইনকিলাব জিন্দাবাদ’-এর সুরে ‘বল হরি হরি বোল, রাম নাম সত্য হ্যায়’ বলতে বলতে মানিকতলা দিয়ে নিমতলার দিকে গেল। ভিঁয়ো, সেই কোন কালের ফরাসি কবি লিখেছিলেন– ‘মৃত্যু, আমি তোমার খরতা নিয়ে, প্রতিবাদে বিচার চাইলাম’। এই হল রাজনীতি। এই প্রতিবাদ, মৃত্যুর বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ, মালিকের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ– তফাত কীসে?
আর একটা গল্প শুনেছি অভিনেতা রাজেশ শর্মার মুখে। গেল শতাব্দীর নয়ের দশকে, ঊষা গাঙ্গুলির নাট্যদল ‘রঙ্গকর্মী’-র অন্যতম প্রধান এই অভিনেতা একটা ঘরোয়া আড্ডায় এই দেখার দৃষ্টি বদলের কাহিনি বলেছিলেন আমাকে। রাজেশ একবার উৎপল দত্তের সঙ্গে ওয়ার্কশপ করার কথা ভাবেন। তখন ঠিক ছাত্রদশা নয় তাঁর। উৎপলবাবু স্পষ্ট জানিয়ে দেন, আপনি চলে আসুন, সারাদিন কাটান, কথা বলি, এই-ই ওয়ার্কশপ। এইরকম কথাবার্তার একটি রাজেশ বলেছিলেন আমাকে।
–আপনি বাসে ট্রামে চড়েন?
উৎপলবাবুর প্রশ্নের উত্তরে সে-সময় সারাক্ষণের গ্রুপ থিয়েটারকর্মী রাজেশ জানাতে বাধ্য হন, আর তো কোনও উপায় নেই।
–আপনি কন্ডাকটরদের লক্ষ করেছেন? বাস আর ট্রামের কন্ডাকটরের তফাত খেয়াল করেছেন? সরকারি বাস আর পাবলিক বাস? দূরপাল্লা আর শহরের রুট? সব দেখেছেন? আলাদা হয়, তাই না?
রাজেশ অবাক হয়ে সেদিন বলেছিলেন– দেখব, দেখব স্যর।

দেখার এই ট্রেনিংটা অবস্থান থেকে আসে। সব সময় যে তা স্থির থাকে, তা তো নয়। তখন বদলে নিতে হয় চোখের চাহনি। চোখটা ধুয়ে আসতে হয় রাস্তা থেকে। অসংখ্যের স্রোত থেকে। এই দৃষ্টিপ্রদীপ বাংলার গোটা সংস্কৃতি হারাতে বসেছে। তাই একটা বদল, সার্বত্রিক বদল দরকার। থিয়েটারের দৃশ্যগুলো কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচা করে হাততালিতে হল ভরিয়ে ফেললেও কোনও পথ নিচ্ছে না। আমোদ-প্রমোদ প্রতিবাদের মতো একটা সত্যিকারের থিয়েটারের মিমিক্রি হয়ে থেকে যাচ্ছে। প্রায় চার দশকের থিয়েটার দর্শক হিসেবে এই আমার অভিজ্ঞতা। একই কথা কবিতা, গল্প, উপন্যাস নিয়েও বলা চলে। বেশিরভাগই, আনন্দবর্ধন যাকে ‘চিত্রকাব্য’ বলেছিলেন, সেই জিনিস। ঢেঁকি-ছাঁটা চালের মতো, পালিশ করা ‘ফিনিশড প্রোডাক্ট’। ‘ফিনিশড প্রোডাক্ট’-এর ভোগ্যপণ্য হয়ে ওঠা ছাড়া কোনও রাজনীতির কোনও দাঁড়ানোর জায়গা থাকতে পারে না।
কবিতা হোক, উপন্যাস হোক আর নাট্যাভিনয়– সব কিছুর জন্যই নিজের শরীরটাকে আকাশছোঁয়া অনুভূতিতে বাড়িয়ে নেওয়া চাই। গুরুজনরা তাই বলে গেছেন। আমাদের রাজনীতি নড়ে না। আমাদের মেজাজ চড়ে না। সবই ভীষণ মাপে মাপে মন্টুর বাপের নন্দনতত্ত্বে নির্ভর করে চলেছে। এর মাঝে এক ঘর অন্ধকারে ভর করে যখন অন্ধ অভিনেত্রী বলে, ‘এ ঘরে কী একদিনও আলো জ্বলবে না?’ তখন আলো-অন্ধকার নতুন মানে নিয়ে জেগে ওঠে। অন্ধ-মানুষের দৃষ্টিশক্তি নেই ঠিকই, কিন্তু বাকি চারটে ইন্দ্রিয় আমাদের আছে কই? হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করার কথা ছিল। স্পর্শ, গন্ধ, স্বাদ, শ্রবণ– আমাদের দৃশ্য এসে খেয়ে গেছে।
‘রক্তকরবী’ নাটক অনেক দেখেছি , কিন্তু অন্য দেশের ‘রক্তকরবী’ নাট্যে, লড়াইয়ের ডাক যেন এখনও কানে লেগে আছে। তিনজন নন্দিনীকে নিয়ে নির্দেশক শুভাশিস গঙ্গোপাধ্যায় এক নাট্যাভিনয় করান, যেখানে প্রতিটি নন্দিনীকে দেখে ভাবতে হয়– এদের কোনওদিন নন্দিনী হিসেবে ভেবেছে কেউ? এই শীর্ণ শরীর, যেন মিশে, দলে-যাওয়া সব মানুষের হয়ে চিৎকার করে বলছে– ‘রাজা, এবার সময় হয়েছে, তোমার সঙ্গে আমার লড়াই।’

এই অবস্থান, অনড় পাথর থেকে অতর্কিতে রবীন্দ্রনাথকে জাগিয়ে তুলেছিল সেদিন ‘রাজা’, ‘রক্তকরবী’ নাটকের কুশীলবরা। সেই রবীন্দ্রনাথ, যিনি আমাদের সব চেয়ে বড় জোরের জায়গা। সেই রবীন্দ্রনাথ যিনি আপাদমস্তক পলিটিক্যাল।
…………………………
রোববার.ইন-এ পড়ুন সুমন্ত মুখোপাধ্যায়-এর অন্যান্য লেখা
………………………….
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved