
২৫ মার্চ প্রয়াত হয়েছেন সন্জীদা খাতুন। শান্তিনিকেতনের এই আশ্রমকন্যা ক্রমে হয়ে উঠেছিলেন ভাষার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা বাংলাদেশের অভিমানের মুখ। রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী হিসেবে খ্যাত হলেও, তাঁর লেখালিখি একেবারেই উপেক্ষণীয় নয়। জীবনের একেবারে প্রথম ভাগ থেকেই নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলেছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করেছেন সেই মুক্ত যুক্তিবাদী দৃষ্টি দিয়েই, নির্ভয়ে। প্রয়াণ-পরবর্তী এই লেখায় রইল তাঁর প্রতি রোববার.ইন-এর শ্রদ্ধার্ঘ্য।

প্রথম বই লিখেছিলেন কবিতা নিয়ে। তা-ও আবার সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা। রবীন্দ্রসংগীতকে আত্মপরিচয় করে বাংলাদেশে বাংলা ভাষার লড়াইয়ের অন্যতম মুখ সদ্যপ্রয়াত সন্জীদা খাতুনের প্রথম বই ‘কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত’, প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল আজ থেকে প্রায় ৭০ বছর আগে, ১৯৫৮-র মে মাসে। সেই বই তখন বাংলা সাহিত্যের ছাত্রীর গবেষণার বই। বিশ্বভারতীর স্নাতকোত্তর পরীক্ষার গবেষণা-নিবন্ধ হিসেবে এ-বইয়ের মূল লেখাটি রচিত হয়েছিল। কিন্তু সেখানেও নিয়মরক্ষার মতো করে গবেষণা করেননি সন্জীদা, যেতে চেয়েছেন বিষয়ের গভীরে, নতুনভাবে চিন্তা করতে চেয়েছেন। বইয়ের পরিচিতিতে তাই প্রবোধচন্দ্র সেন লিখেছিলেন–
‘‘কিছুকাল পূর্বে হরপ্রসাদ মিত্রের ‘সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা ও কাব্যরূপ’ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থটি তৎপূর্বেই পরিকল্পিত ও সমাপ্ত হয়েছিল। বস্তুতঃ এটি রচনার সময়ে লেখিকার সামনে সত্যেন্দ্রসাহিত্য আলোচনার কোনো আদর্শ ছিল না। আর সত্যেন্দ্রসাহিত্য প্রকৃতি ও আকৃতিতে কোনো পূর্বতন কবিকীর্তির অনুকৃতিমাত্র নয় বলে তাঁর পক্ষে উক্ত আলোচনার পথও সুগম ছিল না। এই অবস্থায় হরপ্রসাদ মিত্রের মতো অভিজ্ঞ লেখকের গ্রন্থ প্রকাশের ফলে বর্তমান গ্রন্থটির প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যাবার খুবই আশঙ্কা ছিল। সুখের বিষয় লেখিকার সনিষ্ঠ সাহিত্যচর্চা ব্যর্থ হয়নি: ‘সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা ও কাব্যরূপ’ প্রকাশের পরেও এই পুস্তকের প্রয়োজনহানি অথবা মূল্যাবনতি ঘটেনি; বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণে ও তথ্য-সমৃদ্ধিতে এটির স্বাতন্ত্র্য ও প্রয়োজনীয়তা এখনও স্বীকার্য। বস্তুতঃ এটিকে হরপ্রসাদ বাবুর গ্রন্থের পরিপূরক হিসাবে গ্রহণ করলেই সত্যেন্দ্রসাহিত্য-চর্চার পথ সুগমতর হবে বলে মনে করি।’’

‘এটি রচনার সময়ে লেখিকার সামনে সত্যেন্দ্রসাহিত্য আলোচনার কোনো আদর্শ ছিল না।’– প্রবোধচন্দ্র সেনের এই কথাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা সাহিত্যের প্রথাগত প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণায় অনুকরণের ছড়াছড়ির এই সময়ে তরুণী সন্জীদার ওই সনিষ্ঠ কাজ দৃষ্টান্তের মতো হয়ে থাকে।
‘সনিষ্ঠ’ শব্দটা প্রবোধচন্দ্র সেন তাঁর লেখা সন্জীদার পরিচিতিতে ব্যবহার করেছিলেন। নিষ্ঠাটাই ছিল সন্জীদার পরবর্তী বইগুলোরও মূল পরিচয়। তাই দেশভাগের সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করছেন যখন তখন খুঁজে পেতে চাইছেন নতুন দিকচিহ্ন। বাংলা সাহিত্যে দেশভাগের যন্ত্রণার তেমন উপস্থিতি না-পাওয়ার কারণ হিসেবে, তাঁর মতে, ‘বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন এবং আটান্নর সামরিকশাসন জারিতে পূর্ব বাংলায় দেশবিভাগের গুরুত্ব অনেকটাই হ্রাস পেয়েছিল।’ আর সেখানেই, পূর্ব বাংলার অন্তত প্রথম দিকের বাংলা ছোটগল্পে দেশভাগের যন্ত্রণার থেকেও বড় হয়ে উঠেছিল ‘নবীন পাকিস্তানকে সব পেয়েছির দেশে পরিণত করার স্বপ্ন কল্পনা।’ পরে ভাষার ভিত্তিতে তৈরি হওয়া একটি রাষ্ট্রের অভিমানের একটি মুখ হয়ে উঠবেন যিনি তাঁর এই গভীর বিশ্লেষণ খেয়াল করার মতো।

সাহিত্যতত্ত্বে, কবিতার গঠনে তাঁর ছিল আজীবন মনোযোগ। কিন্তু সেই চর্চা গড় বাংলা সাহিত্যের অ্যাকাডেমিক চর্চা থেকে এইখানে আলাদা যে তা নানা বিষয়ে, এমনকী, বিজ্ঞানেও স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত বই ‘ধ্বনি থেকে কবিতা’-র বিষয় ছিল ধ্বনিশাস্ত্রের আলোয় কবিতাকে দেখা। সেই সময়ে দাঁড়িয়ে সে ছিল এক নতুন পথ। সে বইয়ে সন্জীদা লিখেছেন–
‘‘পদার্থবিদ Sir Richard Paget ‘Gesture-origin theory’ নামে একটি মতবাদ প্রচার করেছিলেন। ১৯৪৯ সালে Howard Peacy তাঁর The Meaning of Alphabet গ্রন্থে Paget-এর সকল বক্তব্য গ্রহণ না করলেও তাঁকে সমর্থন করে বলছেন যে, অক্ষর বা বর্ণধ্বনির যুক্তিগ্রাহ্য তাৎপর্য আছে, ধ্বনির মূলে নিহিত উচ্চারণপদ্ধতি বা বর্ণ-উৎপাদন-প্রক্রিয়ার ধারা থেকে সে-তাৎপর্য অনুধাবন করতে হবে। রামেন্দ্রসুন্দরের মতের সঙ্গে এর সাযুজ্য লক্ষ করি। Roman Jakobsonও তাঁর Selected Writing I গ্রন্থে ‘Tonality Features’ প্রসঙ্গে ধ্বনির গাম্ভীর্য অথবা তীব্রতা, প্রান্তিক মসৃণতা বা অমসৃণতা, সংহতিসৌষ্ঠব বা অসংহতির পিছনে উচ্চারণস্থলের পেশী-ব্যবহারমূলকতার বিজ্ঞানসম্মত বিবরণ দিয়েছেন।’’
তাঁর অন্যান্য বইপত্রও– যেমন ‘রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাবসম্পদ’, ‘তোমারি ঝর্ণাতলার নির্জনে’, রবীন্দ্রনাথ: বিবিধ সন্ধান’, ‘রবীন্দ্রনাথের হাতে হাত রেখে’, ‘বাংলাদেশের সংস্কৃতির চড়াই-উৎরাই’, ‘ধ্বনির কথা আবৃত্তির কথা’, ‘সংস্কৃতির বৃক্ষছায়ায়’ ধরে আছে এই গভীর, মুক্ত দৃষ্টিকেই। রবীন্দ্রসংগীতকে তিনি নতুন দৃষ্টিকোণে দেখেছেন। সেকালের প্রেক্ষিতে যথেষ্ট সাহসী সেই দৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের গানের প্রচলিত পর্যায় বিভাগকেই প্রশ্ন করেছেন তিনি। ‘রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাবসম্পদ’ প্রবন্ধে যেমন লিখছেন–
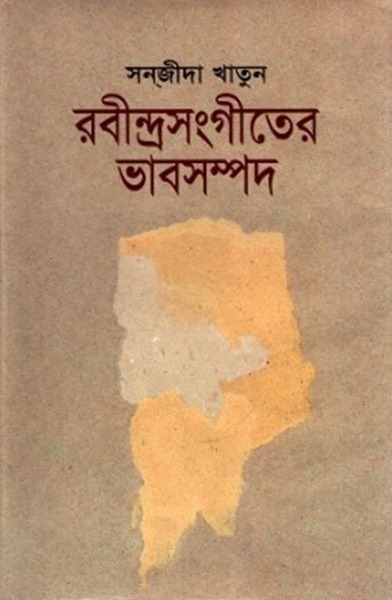
‘‘‘চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে’ রচনাটিকে প্রেমের গান বলা হয়েছে। ‘ফুলের বনে যার পাশে যায় তারেই লাগে ভালো’– ‘পাগল হাওয়া’র এই প্রণয়ভাবের জন্যে কি? না গানটিতে প্রেমের পরিবেশ-চিত্র রয়েছে বলে? প্রকৃতির বর্ণনাই এতে প্রধান বলে ‘প্রকৃতি’ পর্যায়ের প্রথম দিকে বিন্যস্ত সাধারণভাবে প্রকৃতি বিষয়ক নয়টি গানের দশম গানও এটি হতে পারত। এই গানে অভিব্যক্ত ‘পাগল হাওয়া’র প্রেমিক ভাবের সঙ্গে প্রকৃতিবিষয়ক অন্যান্য গানে ইতস্তত ব্যক্ত প্রণয়লীলার কল্পনার যোগ লক্ষ্য করা যায়। যেমন ‘পথ-ভোলা’ পথিক বসন্তের সঙ্গে সন্ধ্যাবেলার চামেলি, সকালবেলার মল্লিকা, আমের মঞ্জরী, মাধবী, তরুণ করবীর; মাধবী-মালতীর সঙ্গে পথিকরূপী বসন্তের; উতল হাওয়ার সঙ্গে প্রদীপ শিখার; ফাগুন সন্ধ্যার চাঁদের আলোর সঙ্গে তরুশাখা ও পল্লবের; বেণুর সঙ্গে দখিন হাওয়ার– এমন বহু প্রণয়লীলার কথা ‘প্রকৃতি’ পর্যায়ের গানে প্রকাশ পেয়েছে।’’
এই স্বকীয়, মুক্ত দৃষ্টিরই বড় আকাল এখন, যে দৃষ্টি যে-কোনও রকমের মৌলবাদকে প্রশ্ন করে।
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
