
‘দেহসম্পর্কহীন এই স্বামী ও স্ত্রীর হৃদয়ের বন্ধুতা’– এইরকম বাক্যবন্ধ দিয়ে কি আগে কখনও শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদার বৈবাহিক সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করা করেছে? পুরো বাক্যটি লেখার প্রবণতা লক্ষ করবার মতো। প্রথমেই ‘দেহসম্পর্কহীন’ শব্দটি বসে, তারপর সেখান থেকে ক্রমোত্তীর্ণ হয়েছে হৃদয়ের বন্ধুতায়। নিজের চেয়ে ২০ বছরের বড় স্বামীর সঙ্গে, (যার আগে খুব অসফল, অশান্তির বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল) বিয়ের পরে দেবারতির কী অভিজ্ঞতা হয়েছিল?

২০০৭ সালে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে দেবারতি মিত্র সরাসরি বলেছিলেন, ‘রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে শ্রীরামকৃষ্ণের মতো এত বড়ো কবির দেখা আজ পর্যন্ত পাইনি।’ ছয়ের দশকের বাংলা ভাষার একজন প্রতিনিধি-স্থানীয় কবি যখন মন্তব্যটি করেন, তখন তা আমাদের ভাবায় বইকি। এর আগে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ‘কবি শ্রীরামকৃষ্ণ’ নামের বইতে কবি হিসেবে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। রামকৃষ্ণকে কেন তিনি কবি বলতে চেয়েছেন, তার যুক্তি হিসেবে লিখেছেন: ‘কবিতা হচ্ছে একটা প্রকাশ, প্রস্ফুটন। অন্তরের ভাবকে রসে জ্বাল দিয়ে প্রতীকের সাহায্যে প্রকাশ করা। ছন্দ বা মিল, যতি বা ঝঙ্কার– এসব বসন ভূষণ মাত্র, প্রাণবস্তু নয়।’ বলা বাহুল্য এ সংজ্ঞার ভাষা কোনওভাবেই রবীন্দ্র-পরবর্তী মরবিড, সংশয়াচ্ছন্ন আধুনিক বাংলা কবিতার সংজ্ঞায়নের সঙ্গে যায় না। এই ভাষা একেবারেই ভাবজগতের। অচিন্ত্যকুমার কল্লোলের কবি হওয়া সত্ত্বেও শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে একাধিক বইপত্র লিখেছেন। সেই চর্চাই তাঁকে রামকৃষ্ণকে কবি হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য করেছিল। রামকৃষ্ণের কবি-প্রকৃতি সম্পর্কে বলেছেন, ‘শ্রীরামকৃষ্ণের কবিতার কাঠামো গদ্য। তা দূরবেধী। যা ব্যক্ত, তার সীমাকে ছাড়িয়ে নিজেকে উত্তীর্ণ করে গভীরের দিকে।’ অচিন্ত্যকুমারের ব্যাখ্যার একেবারে শেষ অংশের সঙ্গে উত্তরাধিকার সূত্রে দেবারতির ব্যাখ্যাও মিলে যায়। মা-সারদাকে নিয়ে সরাসরি কবিতা (‘সারদার সকাল’) লিখেছেন দেবারতি মিত্র। শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে সরাসরি নামাঙ্কিত কোনও কবিতা আছে কি না, জানা নেই। তবে রামকৃষ্ণ মিশন কামারপুকুর থেকে একটি সংকলন-গ্রন্থ বের হয়েছিল স্বামী শিবপ্রদানন্দের সম্পাদনায়– ‘শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবপ্রবাহ: মননভূমি ছুঁয়ে’ (প্রকাশ: ২০১৩)। সেখানে দেবারতি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলেন– ‘শ্রী রামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীতে কবিতা’। লক্ষণীয়, দেবারতি তাঁর লেখার ভাববীজটি নির্মাণ করতে চাইছেন কবিতা নিয়ে। কিন্তু রামকৃষ্ণ তো কবিতা লেখেননি। তাহলে? এই প্রবন্ধটি আমাদের জানায়, দার্শনিক রামকৃষ্ণের কথামৃতর টেক্সট কীভাবে দেবারতির কাছে প্রসাদগুণে কবিতা হয়ে উঠছে এবং হয়তো অজ্ঞাতেই সম্পর্ক-স্থাপন করছে তাঁর একনিষ্ঠ জীবনের ধ্রুবতারা মণীন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে। একটি নৈর্ব্যক্তিক প্রবন্ধের মধ্যে মিশে যাচ্ছে ব্যক্তিগত প্রবন্ধের দ্যুতি। একে দোষ না-বলে বরং দেবারতির মনোভঙ্গিমার অনিবার্যতা বলাই ভালো।
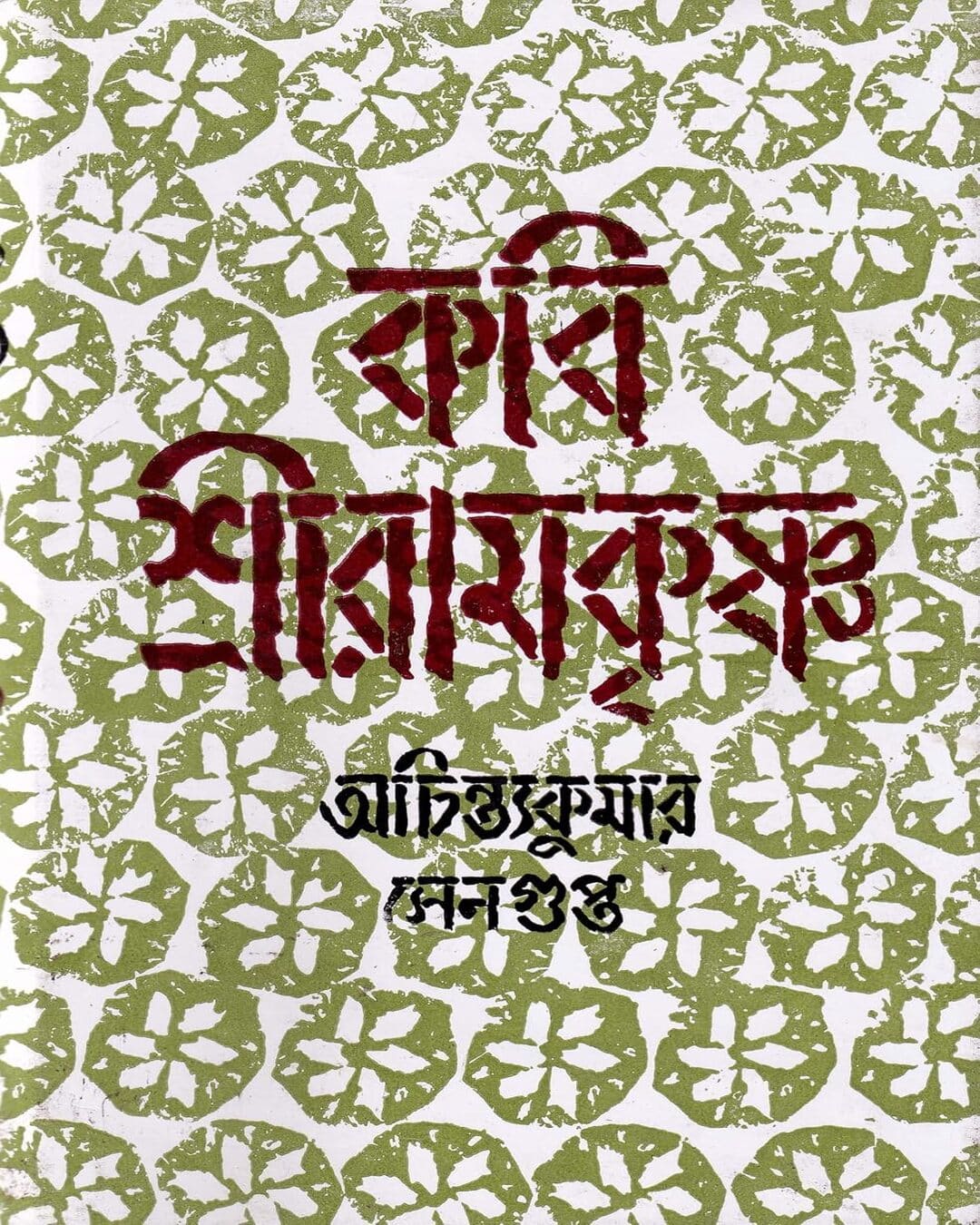
‘কবিতা যে কী তা বুঝিয়ে বলা শক্ত। চেনাজানা গণ্ডির বাইরে একটা ঘটনা বা চিন্তার উদ্ভাসকে বা হঠাৎ দেখা স্বপ্নের সত্য হয়ে ওঠাকেই কি কবিতা বলে?’– এখানে দেবারতি কিন্তু কবিতার চিরায়ত সংজ্ঞা দেওয়ার প্রবণতা থেকে দূরে সরছেন এবং ‘চেনাজানা গণ্ডির বাইরে একটা ঘটনা’ বলে নির্দিষ্ট করতে চাইছেন। অর্থাৎ এতকাল ধরে আমরা কবিতাকে যেভাবে দেখে এসেছি, তার থেকে বেরিয়ে কবিতার একটা প্রলম্বিত ব্যাখ্যা নির্মাণ করতে চাইছেন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকে সামনে রেখে। সেখানে দেবারতি হেঁটেছেন সূক্ষ্ম দড়ির ওপর দিয়ে, যার নাম অলৌকিকতা। রামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীতে ছড়িয়ে থাকা বিস্ময়কে তিনি কবিতার যোগসূত্র হিসেবে দেখতে চেয়েছেন– এ চাওয়া বিতর্কিত হতে পারে কারও-র কাছে, কিন্তু অভিনব তা নিয়ে সন্দেহ নেই। বিশেষত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পার করা এক অবদমিত মানবতার ইতিহাস যখন মুখ্যত সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যাতেই জীবনের অস্তিত্বের চেতনাকে খুঁজে পেতে চাইল, সেখানে নিখাদ আধ্যাত্মিকতার জায়গা কোথায়? বরং আধুনিকতার নামে সেই দৃষ্টিকোণকে বাতিল বলেই দাগিয়ে দেওয়া হল। দেবারতি সেই পরিত্যাজ্য হয়ে যাওয়া মাপকাঠিকে শুধুমাত্র স্বীকার করে নিচ্ছেন তাই নয়, তাকে ব্যবহার করছেন ঐতিহ্যকে স্মরণ করে আধুনিক বাংলা কবিতার সাপেক্ষেই।
দেবারতির দৃষ্টিতে দিব্যপুরুষ রামকৃষ্ণের কবিতা কী? প্রবন্ধে দেবারতি জানাচ্ছেন: ‘শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের আগে থেকেই তাঁকে ঘিরে এই কবিতার সূত্রপাত হয়েছিল।’ কীভাবে? কামারপুকুরের ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়কে দেব গদাধর দর্শন দিয়ে বললেন: ‘তোমার পুত্র হয়ে তোমার বাড়িতে গিয়ে জন্মাব, তোমার সেবা, তোমার আদর পেতে আমার বড় সাধ।’ ক্ষুদিরাম তাঁর দারিদ্রের কথা জানালে দেব জানালেন: ‘ভয় নেই, সে হয়ে যাবে’। এরপর ক্ষুদিরামের স্ত্রী চন্দ্রমণি বাড়ির পাশের শিবমন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে দেখলেন: ‘শিবের গা থেকে আলো বেরিয়ে এসে হাওয়ার মতো ঘুরতে ঘুরতে আচ্ছন্ন করে ফেলল’ তাঁকে, এবং তাঁর ‘শরীরের মধ্যে তীব্রবেগে ঢুকতে লাগল। মনে হল, তাঁর পেটে কেউ এসেছে।’ অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণর জন্মমুহূর্তের সঙ্গে শিবের যোগ তৈরি হল। বোঝা গেল তেমন কেউ আসতে চলেছেন। তিনি শিব-জাত, অর্থাৎ শিবের অংশ। রোমা রোঁলা-র লেখা রামকৃষ্ণের জীবনীতেও এই জন্মের ব্যাখ্যা রয়েছে একই ভঙ্গিতে:
‘Chandramani, dreamt that she had been possessed by a God. In the temple opposite her cottage the divine image of Shiva quickened to life under her eyes. A ray of light penetrated to the depths of her being. Under the storm Chandamani was overthrown and fainted. When the prey of God came to herself, she had conceived.’

শিব ছাড়াও বিশ্বাসীরা তাঁকে বিষ্ণুর অবতার বলে মানেন। অর্থাৎ রামকৃষ্ণের ব্যক্তিত্বের মধ্যে ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে একাধিক ঐশ্বরিক সত্তার সম্মেলন ঘটেছে। রামকৃষ্ণ নিয়ে নাস্তিকদের চর্চার ক্ষেত্র অবশ্য তাঁর সহজ ও গভীর দার্শনিক দিক। এ আলোচনায় সেই দিকটি খুব বিস্তারিত বলা প্রাসঙ্গিক হবে না। কিন্তু অবশ্যই এবার একথা স্মরণে আনতে হবে, মণীন্দ্র গুপ্তও কিন্তু দেবারতি মিত্রের কাছে শিবকল্প ব্যক্তি হিসেবে স্থান পেয়েছেন। কৃষ্ণবর্ণ মণীন্দ্র একদিকে ধূসর শিব ও কৃষ্ণরূপী নারায়ণ– উভয় আধারেই দেবারতি দ্বারা নির্মিত ও গৃহীত। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম ভাবসমাধিই হল দেবারতির চিহ্নিত সেই মাহেন্দ্রক্ষণ, যখন ‘সেই আদি কবির সঙ্গে সেই পরম কবির এইভাবে যোগাযোগ হল’। আদি কবি কে? ছয় বছর বয়সে ধানখেতে, আলের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে রামকৃষ্ণ দেখছেন, আকাশের দিকে কালো মেঘের গা ঘেঁষে একসারি বকের পাঁতি উড়ে যাচ্ছে। প্রকৃতির এই চলমান রূপকল্প রামকৃষ্ণের প্রথম ভাবসমাধি– যাকে দেবারতি বলতে চাইছেন কবিতা। আদি কবি প্রকৃতির সঙ্গে ‘পরম কবি’ রামকৃষ্ণের যোগাযোগ হল। বিশেষণের আগে বিশেষণ বসিয়ে রামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীকেই কবি হিসেবে দেখতে চাইলেন দেবারতি– এখানেই বিশ্লেষক হিসেবে তাঁর চিন্তার অভিনবত্ব। এই চিন্তা আরও অভিনব হয়ে তখন, যখন রামকৃষ্ণর জীবনের মধ্যে কবিতার ঐশ্বর্য খুঁজতে গিয়ে মণীন্দ্র গুপ্তের জীবনের প্রসঙ্গ মিলে যায়। শিবকল্প-চেতনায় রামকৃষ্ণ এবং মণীন্দ্র গুপ্ত একই বিন্দুতে চলে আসেন:
‘জন্মের পরেই আঁতুড়ে মায়ের কোলের কাছে তাঁর (রামকৃষ্ণ) অনুপস্থিতি কি কম আশ্চর্যের? সদ্য জন্মানো শিশুকে ধাই ধনী কামারনি খুঁজে বের করলেন ছাইগাদা থেকে, কখন সে যে গড়িয়ে সেখানে চলে গেছে এবং বেরিয়ে এসেছে ভস্মমাখা শিব হয়ে!’
এখানেই শেষ নয়। এরপর যাত্রার আসরে মাত্র আট বছর বয়সে শিবের ভূমিকায় তাঁকে দেখে ধন্য ধন্য করতে লাগল সবাই। দর্শক কী দেখল? ‘তাঁর চোখে আনন্দাশ্রু, বাহ্যজ্ঞান নেই, তিনি কি সমাধিস্থ?’ কেন একথা বলা হচ্ছে? রোমা রোঁলা জানাচ্ছেন সেই পালায় অভিনয়ের সময়, ‘suddenly his being was possessed by his hero; tears of joy coursed down his little cheeks; he lost himself in the glory of God;’ কথা হল, সমাধি কি শুধু এভাবেই হয়? ঐশিকতা মণীন্দ্র গুপ্তের কাছে অলৌকিকতা ছেড়ে হয়ে উঠেছে দর্শন। ‘অক্ষয় মালবেরি’ গ্রন্থে রয়েছে ‘শিববাড়ি’ নামে এক প্রান্তরের কথা। কীরকম সেই প্রান্তর?
‘অনেকখানি জঙ্গলাকীর্ণ জায়গা নিয়ে শিববাড়ি। মন্দিরহীন, মার্জনাহীন, শ্রীহীন এক বন্য দেবালয়। এলোমেলো গাছপালার মধ্যে একটি ছোট পুকুর, তার অনতিদূরে উদোম-খোলা একটা বড় চালাঘর। সেই চালার এক প্রান্তে একটু খুপরিমতো করা, সেখানে কষ্টিপাথরের এক বিশাল শিবলিঙ্গ।’
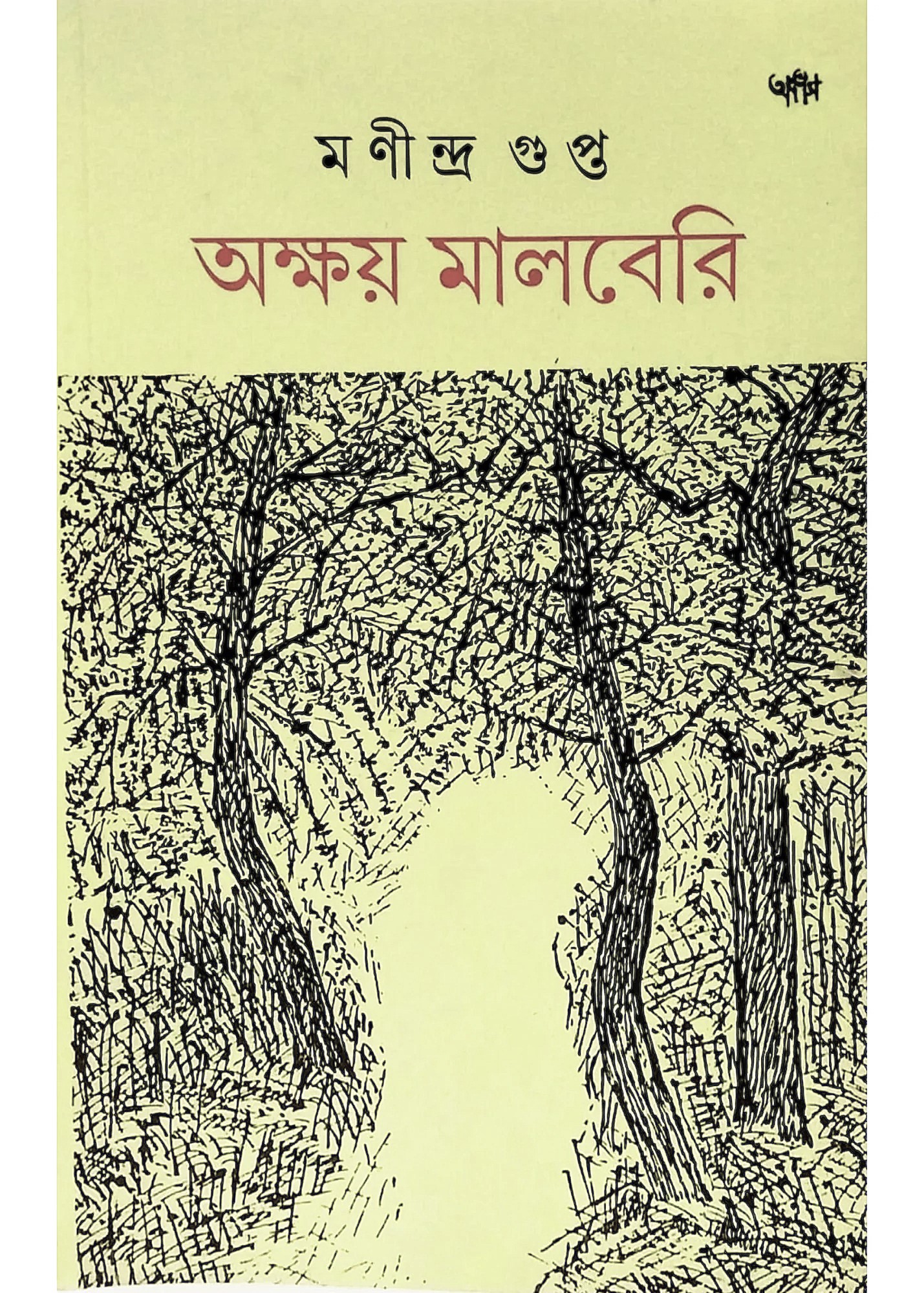
সেই জায়গায় গিয়ে মণীন্দ্র গুপ্ত প্রত্যক্ষ করছেন পশ্চিমা, হিন্দিভাষী সাধুসন্তদের। ছিলেন ভাও গিরি। যার মধ্যে নির্ভেজাল বৈরাগ্যকে দেখতে পেয়েছিলেন তিনি। এই জায়গায় দিনের পর দিন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে করতে কোন অনুভূতিতে পৌঁছচ্ছেন?
‘আমি ভাবতে ভাবতে চলেছি, আমার পায়ের তলার পৃথিবীটা যেন অলক্ষে সংকুচিত হয়ে ছোট হয়ে আসছে।’
যেন পার্থিব পৃথিবীর অস্তিত্ব গুটিয়ে ছোট হয়ে যাচ্ছে তাঁর আঙুলের তলায়। নিজের মধ্যে ভূমার অস্তিত্বকে অনুভব করার মধ্যে দিয়ে কি মণীন্দ্র গুপ্তের মধ্যেও ঈশ্বরের ভাব জেগে উঠছে না? মণীন্দ্র গুপ্ত ওই নির্জন, বুনো প্রান্তরে যে শিবলিঙ্গের অধিষ্ঠান আবিষ্কার করেন, অনেকটা তেমনই চোখের আড়ালে থাকা শিবলিঙ্গের অস্তিত্ব পাওয়া যায় দেবারতি মিত্রের লেখায়। তফাৎ এটাই, দেবারতির কবিতায় ওই হারিয়ে যাওয়া পরিত্যক্ত শিবমূর্তিটি স্বয়ং মণীন্দ্র গুপ্ত। ‘গাঁয়ের মন্দিরে’ নামের সেই কবিতা লেখা হচ্ছে মণীন্দ্র গুপ্তের মৃত্যুর বছর দুয়েক পর। সেখানেও এক পরিত্যক্ত মন্দিরে ঘেঁটুফুল, আগাছায় আগাছায় ভরে থাকা এক নির্জন শিবমূর্তি নির্মাণ করেছেন দেবারতি। যেন তিনিই একমাত্র ওই মন্দির ও তার মধ্যে ভেঙে পড়া শিবের অস্তিত্ব জানেন। সেখানে ধুঁধুল লতার মতো সাপ ঘোরে। কখনও চপল গরুরা এসে শিবের পাশে থাকা ষাঁড়টিকে চেটে দিয়ে যায়:
‘গাঁয়ের মন্দিরে ভাঙা শিব
ঘেঁটু ফুলে আগাছায় আগাছায় ঢেকে আছে।
ধুঁধুল লতার মতো সাপ ঘোরে আনাচেকানাচে,
চপল গরুরা এসে কখনো কখনো প্রেমভরে
পাথরের ষাঁড়টির গা চেটে দেয়।’
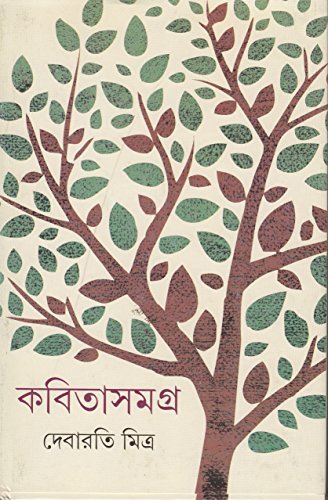
এরপরই এই কবিতায় এসে লাগে অলৌকিকের ঝাপট। এবার এই কবিতায় যে অতিবাস্তবতার সূচনা হয়, তা একান্তভাবেই দেবারতির মনোজগতের। চৈত্র সংক্রান্তির আবহে এক নিঃসঙ্গ মন্দিরের শিবমূর্তিকে ঘিরে শুরু হয় গাজনের উৎসব। সেই উৎসবের অলৌকিক বিবরণই দেবারতির ভাষায় কবিত্ব। এই বিদ্যুৎ চমকের সঙ্গে ঝড়বৃষ্টির বর্ণনা আসলে নিঃসঙ্গ শিবকে খুঁজে পেয়ে উমার নিঃসীম আনন্দ, যা আসলে স্বয়ং দেবারতিরই শরীরী-মৃত স্বামীর সঙ্গে মানসমিলনের অ-শরীরী উচ্ছ্বাস:
‘বর্ষাকালে কূলহারা মেঘমালা উমার অগাধ চুল,
দেবীর কানের দুল বিদ্যুৎঝলক,
কড়াৎ কড়াৎ বজ্রের মতন তাঁর ছদ্ম কোপ দেখে শিবঠাকুরের ঘোর লাগে, ভাব হয়।’
যেন সেই পরিত্যক্ত শিব আবার জেগে উঠেন অগাধ বিরহ পেরিয়ে ওই নির্জন মন্দিরে আসা উমার অতিস্পর্শে। পার্বতী শিবকে পেয়েছিলেন নিজের পরিবারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, কঠিন সাধনায়। এখানেও যেন উমাবেশে দেবারতি তাঁর পরলোকে উচ্চাসীন স্বামীকে পুনরায় ফিরে পেতে চেয়েছেন একটানা ঝিঁঝিঁরব, ব্যাঙের ডাক পেরিয়ে। কবিতাটি শেষ হচ্ছে ভাবসমাধি থেকে জেগে ওঠা জ্যান্ত শিবের অস্তিত্বে:
‘একটানা ঝিল্লিরব, ব্যাঙেদের ডাক,
এই অবিশ্রান্ত বৃষ্টি
ত্র্যম্বকের নাচগান, ডমরুর ধ্বনি’

মণীন্দ্র গুপ্তের ছেলেবেলার গ্রামে শিববাড়ির সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনও ছিল। সেখানে স্বামী পুরুষাত্মানন্দ কোনও আধ্যাত্মিক উপদেশ না-দিয়ে লাইব্রেরি থেকে ইলিয়াড, ওডিসি, বিভিন্ন পুরাণকাহিনির বই দিতেন। আবার মণীন্দ্র গুপ্তকে এও জিজ্ঞাসা করতেন, তিনি সাধু হতে চান কি না। এইভাবে কৈশোরে, যৌবনে সাধুসন্তের প্রভূত সাহচর্য, যে-অঞ্চলে বড় হয়েছেন, সেখানে হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান ধর্মের সহাবস্থান থাকবার ফল এটাই– মণীন্দ্র গুপ্তের মধ্যে সর্বধর্ম সম্পর্কে আগ্রহ তৈরি হয়েছিল। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাঁর পারিবারিক ধর্মাচরণের ইতিহাস। মণীন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন: ‘আমরা পিতৃকূল মাতৃকূল উভয় দিক থেকেই নিশ্ছিদ্র শাক্ত হওয়া সত্ত্বেও দিদিমা তাঁর বাড়িতে এক শব্দঘোর বৈষ্ণব উৎসব প্রবর্তন করলেন।… দাদু দিদিমার ইষ্ট ছিলেন শিব। রুপো আর ধূসর বর্ণের নুড়িতে তৈরি চমৎকার শিবলিঙ্গ দুজনেই পুজো করতেন।’ এখন, দেবারতি তাঁর জীবনে এই লিবারাল ভাববাদী মানুষটিকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন ঈশ্বরের মতোই স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে। স্বামীকে একইসঙ্গে সখা ও সন্তানরূপে পেতে চাওয়ার এবং তাকে সম্ভব করে তোলার মধ্যে দিয়েই একনিষ্ঠ পথে এগিয়েছে দেবারতির অস্তিক্যবোধ। ফলে কোনও দার্শনিক ব্যক্তিত্বের জীবন নিঃসৃত অলৌকিকতাকে তিনি মিলিয়ে ফেলেন ব্যক্তিগত জীবনের সম্পর্কের উত্তাপে।
শুধুমাত্র শিবের অনুষঙ্গে নয়, রামকৃষ্ণ-সারদার একত্রিত হওয়ার মধ্যে দিয়েও আত্মজীবনের প্রতিফলন চলে আসে অনায়াসে। রামকৃষ্ণের জীবন প্রসঙ্গে কিছু ঘটনার কথা বলতে বলতে দেবারতি আসেন বিয়ের প্রসঙ্গে। এই প্রসঙ্গ উদ্ধৃতি-পূর্বক আলোচনা জরুরি। রামকৃষ্ণ-সারদার সম্পর্ককে কীভাবে দেখেছেন দেবারতি?
‘দেহসম্পর্কহীন এই স্বামী ও স্ত্রীর হৃদয়ের বন্ধুতা, আত্মার মিল নিখাদ সোনার মতো, তাতে হয়তো গয়না গড়া যায় না, কিন্তু অখণ্ড জ্যোতির আভায় তা অনির্বচনীয়।’
শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাকে দেখতেন এই বলে:
‘যে-মা মন্দিরে আছেন, যে-মা নহবতে আছেন, তুমিও সেই মা। তুমি আমার আনন্দময়ী।’
মণীন্দ্র গুপ্ত মারা যাওয়ার পর ‘সবই অখণ্ড’ শিরোনামে দেবারতি মিত্র লিখছেন:
‘টুকরো-টুকরো করে কিছু দেখো না,
সবই অখণ্ড।
ভাগ-বিয়োগে কী লাভ?
যোগ আর গুণ অঙ্কেরই-বা কী দরকার?
এই যে আমরা দুজনে আছি,
সারাদিন গল্প করছি, এসব যথেষ্ট নয়!
সাইবেরিয়া থেকে একটা বিরাট হাঁস
পাশের পুকুরে এসে নেমেছিল।
যে যদি পরের বছর আর না আসে,
তখন কি পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসবে?
দেখো, অনন্ত চারিদিক ডগমগ করছে,
আমরা অখণ্ড–
তাছাড়া আর কিছু নই।’

শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদার যুগল-অবস্থাকে দেবারতি বলেছেন ‘শিব-পার্বতীর বিয়ের অনুষ্ঠান’ (লক্ষ করা ভালো, শিব-পার্বতীর অর্ধনারীশ্বর অবস্থা ও অবিচ্ছিন্ন অবস্থান কি দেবারতি-মণীন্দ্রর দাম্পত্যজীবনের পরম সত্য নয়?)। এবং সেই বিয়েতে যে অলক্ষণের বাধা আসছে, তাকেও কোনও দুর্লক্ষণ হিসেবে না দেখে মনে করা হচ্ছে বিশিষ্টতা। এয়োরা যখন সাতাশ কাঠি জ্বেলে বরকে প্রদক্ষিণ করছে, তখন বরের হাতে বাঁধা মাঙ্গলিক সুতো পুড়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাই বলে বিয়ে বন্ধ হচ্ছে না। এই ঘটনার তাৎক্ষণিক ফলশ্রুতি কী হয়েছিল, ওই বিবাহে উপস্থিত জনমানসে তা জানা না গেলেও এই ঘটনার তাৎপর্য সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দেবারতি দিয়েছেন, তাকে কোনওভাবেই নৈর্ব্যক্তিক বলা যায় না: ‘তাঁদের এই পুণ্য বিবাহকে কোনো প্রচলিত শব্দে বা ছন্দে বাঁধা যাবে না; সব প্রথা, নিয়মের বাইরে এ এক অভাবিত পবিত্র তুলনাহীন কবিতা।’ মনে হয় না, নিজের অজ্ঞাতে রামকৃষ্ণ-সারদার এই নিয়মহারা বিবাহের পবিত্রতা নির্ধারণ করতে গিয়ে নিজের বৈবাহিক জীবনের তাৎপর্য নির্ধারণ করে ফেলেছেন দেবারতি? ২৪ বছরের শ্রীরামকৃষ্ণ ও ৬ বছরের মা-সারদার বিবাহের মতোই মণীন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে দেবারতির বয়সের তফাৎ কুড়ি বছরের। এবার পুরাণ ও ইতিহাসের সঙ্গে এই দাম্পত্যের সম্পর্ক লক্ষ করা যাক। শিব-পার্বতীর বিবাহেও কিন্তু পার্বতীর বাবার মত ছিল না। তেমনই দেবারতি-মণীন্দ্রর বৈবাহিক জীবনেও ছিল না পারিবারিক সম্মতি। রামকৃষ্ণ-সারদার বিবাহে কোনও অসম্মতির প্রসঙ্গ না থাকলেও ওই বরের হাতে বাঁধা হলুদ মাঙ্গলিক সুতোর পুড়ে যাওয়ার মতো বাধার সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ শিব-পার্বতী হোক, শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা হোক কিংবা দেবারতি-মণীন্দ্র– এদের সবাইকেই একত্রিত হওয়ার আগে বাধা পেরতে হয়েছে। কিন্তু বাধা পেরনোর ফল হয়েছে মধুর। কেননা এই তিনটি দাম্পত্য সম্পর্কই স্বতঃসিদ্ধ। এর কোনও অন্যথা সম্ভব নয়। শিব-পার্বতী, রামকৃষ্ণ-সারদার মতোই যে তাঁদের দাম্পত্য সম্পর্কও অখণ্ডস্বরূপ– তা নিয়ে নিশ্চিত ছিলেন দেবারতি। টুকরো টুকরো পরিমাপ করে, জাগতিক হিসেব-নিকেশের প্যারামিটারে একে মাপা সম্ভব নয়। অঙ্কের হিসেব কষেও এই সম্পর্কের অভিন্নতাকে বোঝা যাবে না। এমনকী দৈহিক অনুপস্থিতিকেও এই সম্পর্কের তেজ অস্বীকার করে দিতে পারে। সাইবেরিয়া থেকে আসা বিরাট হাঁসটি আসলে মৃত মণীন্দ্র গুপ্তের মোটিফ। যে শরীর গেছে, সে আর সশরীরে ফিরবে না, কিন্তু তাই বলে কি সে আর কোথাও নেই। অনন্তের মধ্যে যে তরঙ্গ ডগমগ করছে, সেখানে তো চাইলেই তাকে পাওয়া যাবে। আমার মধ্যেই তো তোমার উপস্থিতি। এই কবিতা যখন লেখা হচ্ছে, দেবারতি তখন বেঁচে। মণীন্দ্র গুপ্তের মৃত্যুর শোককে সহ্য করতে করতে এই বিশ্বাসে চিরকাল স্থির থেকেছেন, মণীন্দ্র গুপ্ত আছেন। কেননা, দেবারতি আছেন বলেই মণীন্দ্র আছেন। সারদা আছেন বলেই রামকৃষ্ণ আছেন। পার্বতী আছেন বলেই শিব আছেন। সবাই অখণ্ড। সবই অখণ্ড। শিব-পার্বতীর যুগলকে মেনে রামকৃষ্ণ-সারদার বিবাহ দেবারতির কাছে কবিতা। তার মানে, এই প্রবন্ধের নিরিখে বাস্তবতা যাকে কোনওভাবেই স্পর্শ করতে পারে না, সেই অভাবনীয়তাও যেমন কবিতা, তেমনই যা-কিছু স্বতঃসিদ্ধ, তাও দেবারতির অন্তর্দৃষ্টিতে– কবিতাই। যাকে কোনওভাবেই খণ্ডন করা যায় না, যাবতীয় বাধা-বিপত্তিকে জয় করে যা উত্তীর্ণ হয়, সেই ধ্রুব সত্য দু’টি সত্তার মধ্যে অভেদরূপ নির্মাণ করে অখণ্ড শক্তির সৃষ্টি করে। আর এই সত্যি বুঝে গেলে আর জাগতিকভাবে কাউকে হারানোর বেদনা তেমন কাজ করে না। কিংবা কাজ করলেও তাকে অতিক্রম করবার একটা রাস্তা খুঁজে বের করা যায়। মণীন্দ্র গুপ্তকে হারাবার পর দেবারতি যে-রাস্তা প্রাণপণে খুঁজেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেয়েছিলেন কি? কিংবা আরও সঠিকভাবে বললে, পেতে চেয়েছিলেন কি?

রামকৃষ্ণকে নিয়ে এই প্রবন্ধ লেখা হচ্ছে আনুমানিক ২০১২-১৩ সালে। মণীন্দ্র গুপ্ত তখন জীবিত। আর উদ্ধৃত কবিতাটি যখন লেখা হচ্ছে, তখন তিনি আর জাগতিকভাবে নেই। যখন তিনি ছিলেন, চিন্তাজগতের পরিপার্শ্বে তাঁকে মিলিয়ে দেখার প্রবণতা কাজ করত। যখন তিনি রইলেন না, তখন আরও বেশি করে দায়িত্ব পড়ল, আরও আকুতি জন্মাল তাঁকে বাঁচিয়ে রাখবার। কেননা তিনি (মণীন্দ্র গুপ্ত) বাঁচলে তবেই দেবারতি বাঁচবেন। অথচ মর্মান্তিক জীবনসত্যের বাস্তব অভিঘাতকে তো আর উপেক্ষা করা যায় না। তাহলে উপায়? উপায় দেবারতির দেহাতীত অলৌকিকতার বিশ্বাস, উপায় উপনিষদের, ব্রহ্মাণ্ডের জগৎ, যার প্রতি স্বয়ং মণীন্দ্র গুপ্তের অটুট বিশ্বাস ছিল। বস্তুজগতের অভাব এইভাবে চিরকালীনতা পেল ভাবজগতে। সেই ভাবজগতের নির্মাণে এই প্রবন্ধের ভূমিকাকেও অস্বীকার করা যায় না। ‘দেহসম্পর্কহীন এই স্বামী ও স্ত্রীর হৃদয়ের বন্ধুতা’– এইরকম বাক্যবন্ধ দিয়ে কি আগে কখনও শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদার বৈবাহিক সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করা করেছে? পুরো বাক্যটি লেখার প্রবণতা লক্ষ করবার মতো। প্রথমেই ‘দেহসম্পর্কহীন’ শব্দটি বসে, তারপর সেখান থেকে ক্রমোত্তীর্ণ হয়েছে হৃদয়ের বন্ধুতায়। নিজের চেয়ে ২০ বছরের বড় স্বামীর সঙ্গে, (যার আগে খুব অসফল, অশান্তির বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল) বিয়ের পরে দেবারতির কী অভিজ্ঞতা হয়েছিল? আত্মজৈবনিক গ্রন্থ ‘জীবনের অন্যান্য ও কবিতা’-র ‘বিবাহ’ পরিচ্ছেদে লিখেছেন:
‘আমার স্বামীকে আমি পেয়েছিলাম ভাঙাচোরা অবস্থায়। তখন তাঁর রসকষ আর কিছু অবশিষ্ট ছিল না।’
এবং
‘বিয়ের প্রথম দিকে আমার স্বামী সমুদ্রের ধারে জেলেদের জাল শুকোবার কাঠের খুঁটির মতো নিষ্প্রাণ ও নির্বিকার হয়ে থাকতেন, আমি অনবরত ঢেউয়ে, কলরবে, উচ্ছ্বাসে ওঁর গায়ে ভেঙে পড়তাম।’
এই একমুখী জৈবী পিপাসা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। স্বামীর নিস্পৃহতা, অনাগ্রহ এই সম্পর্ককে অভাবিত অন্যতর মাত্রা এনে দেয়, যার বিপুল পরিধি তাঁদের দাম্পত্যের শেষদিন পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। দেবারতি এ-ও লিখেছেন:
‘বরং এভাবেই বলা ভালো– একটি আড়াই-তিন বছরের শিশুর মা-বাবা দুইই হয়ে তাকে দেখাশোনা করা ও তার রক্ষণাবেক্ষণ হয়ে দাঁড়াল আমার কাজ। আজও আমার স্বামীকে একটি ছোট বাচ্চা ছাড়া কিছু মনে করি না।’

এইভাবে দেহসম্পর্কের লগ্নতা থেকে সন্তানভাবে স্বামীকে দেখতে চাইলেন দেবারতি। অবশ্যই শ্রীরামকৃষ্ণের, মা-সারদাকে ১২৮০ বঙ্গাব্দের ফলহারিনী কালীপুজোর দিন মাতৃভাবে পুজো করবার সঙ্গে এর মনস্তাত্ত্বিক ও দর্শনগত পার্থক্য আছে। কিন্তু স্বাভাবিকতার ঊর্ধ্বে, প্রচলিত শব্দ ও ছন্দের বাইরে এই দাম্পত্যের অভিনব সংজ্ঞা নির্মাণের ক্ষেত্রে কি দেবারতির ভাষায় ‘সব প্রথা, নিয়মের বাইরে… এক অভাবিত পবিত্র তুলনাহীন কবিতা’ হয়ে থেকে যায়নি? ব্যক্তিগত জীবনে দেহাতীত সম্পর্কে বিশ্বাসী রামকৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিতত্ত্বকে ব্যাখ্যা করছেন ‘রমণ’ শব্দের সাবলীল ব্যবহারে। চতুর্দিকে শিব আর শক্তি। ‘শিব-শক্তির রমণ’-ই হল এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। ‘মানুষ, জীবজন্তু, তরু, লতা, সকলের ভেতরেই সেই শিব আর শক্তি। পুরুষ আর প্রকৃতি। এদের রমণ।’ মহাজাগতিক ঘটনাকে, তার কার্য-কারণকে, ক্রমবিবর্তনকে একজন ভারতবর্ষীয় শাক্ত সাধক বোঝাতে চাইছেন ‘রমণ’ শব্দের পরের পর সুচিন্তিত ব্যবহারে– এটাই আধুনিকতার সীমান্তে এসেও দেবারতির মতো একজন বাংলা ভাষার কবির কাছে চূড়ান্ত বিস্ময়ের কারণ। এই বিস্ময়কে তিনি মেনে নিচ্ছেন ‘কবিতা’ বলেই। প্রকৃত কবি শুধু অলৌকিকের দ্রষ্টা নন, ‘তাঁর মধ্যে একজন সরস দক্ষ কথাকারও লুকিয়ে থাকে।’ গল্পের মধ্যে দিয়ে বলা ওই কথনবিশ্ব নির্মাণও একজন কবির কাজ বলে দেবারতি মনে করছেন। বহুরূপধারী গিরগিটিকে দেখে একেকজন একেক বর্ণের বলে উল্লেখ করছে। তাদের মধ্যে কোনজন সত্য সেই নিয়ে তর্ক বাঁধলে, একটি লোক এসে বুঝিয়ে দিচ্ছে, তোমরা আসলে সবাই সত্যি বলছ। সত্যির এমনই বহুরূপ হয়ে থাকে। সৃষ্টির বিজ্ঞান এমনই পরিবর্তনশীল বহুরূপের বৃত্তান্ত। মুণ্ডকোপনিষদে আছে, সৃষ্টির জন্য ব্রহ্ম স্ফীত হন। তাঁর থেকে প্রকৃতি জাত হয়, প্রকৃতি থেকে মন, মন থেকে পঞ্চভূত, তা থেকে লোকসমূহ; লোকসমূহ থেকে কর্ম ও কর্মফল। সোজা কথায় সত্য উৎপত্তির ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে জড়িত। সত্য বহুরূপী অথচ স্থির– কেননা তা আছে। আর যা আছে, তাকে শুধু পুথি পড়ে জানা যাবে না। তাকে আকুল হয়ে ডাকতে হয়। মণীন্দ্র গুপ্ত মারা যাবার পরেই দেবারতি যে-সমস্ত কবিতা লিখেছিলেন সেখানে সদ্য স্বামী হারানোর যন্ত্রণা ছিল। ক্রমশ, স্বামীর অনুপস্থিতিকে ভাবসম্মেলনের মাধ্যমে দেবারতি কাছে নিয়ে আসেন। উভয়ের মধ্যে মানসলোকে আবার সাক্ষাৎ হয়। সে সাক্ষাতের ধরন কী রকম?
‘আমার চোখের সামনে
শুকনো কালো গাছটা সবুজ হয়ে গেল–
এক ঝাঁক টিয়াপাখির কলস্বর,
রোদবৃষ্টি, আলোছায়া
তবু আমি কি হাসব না, কথা বলব না আকাশের সঙ্গে?
তুমি আমাকে রাতদিন শেখাও
আলো যেমন সত্য, অন্ধকারও সত্য।
তোমার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ কখনো হবে না।
সবুজ শুকনো হয় না,
সবুজ মৃত্যু হয় না–
আবহমান কাল ধরে এই চলে আসছে।
বিশ্বাস রাখো, বিশ্বাস করো এই সৃষ্টিকে।’

ঈশ্বরকে শুভ ও অশুভ দুই-ই মনে করতেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বরই সাপ হয়ে খাচ্ছেন, আবার রোজা হয়ে ঝাড়ছেন। ‘তিনি বিদ্যা অবিদ্যা দুইই হয়ে রয়েছেন।’ নেতি নেতি করেই তো সাধককে সচ্চিদানন্দে পৌঁছতে হয়। সেই আনন্দের সমুদ্রে সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, জীবন-মৃত্যু সবই সমান। ঈশ্বরের জন্য যখন প্রাণ ‘আঁকুপাঁকু’ করবে, কিছুতেই স্বস্তি পাওয়া যাবে না। তখনই তাঁকে পাওয়া সম্ভব। দেবারতির প্রাণও তেমনই অস্থির হয়ে উঠেছিল সন্তানকল্প, যোগীকল্প স্বামীকে পাওয়ার জন্য। ভারত সেবাশ্রম থেকে দীক্ষা নেওয়ার পর দু’জনের নির্লোভ যৌথ কবিজীবনে দাঁড়ি পড়ল যখন, তখন দুই সাধকের মধ্যে একজনের ভার পড়ল অপরজনকে বাঁচিয়ে রাখবার। অন্ধকার আর আলো সমান সত্য– একথা যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে শিখেছিলেন দেবারতি, সেই শিক্ষাই ফিরে এল মরণোত্তর স্বামীর উপদেশ হয়ে। প্রেমের দু’টি লক্ষণের কথা রামকৃষ্ণ বলেছিলেন– ‘প্রথম, জগৎ ভুল হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত, নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিস, এর উপরও মমতা থাকবে না, দেহাত্মবোধ একেবারে চলে যাবে।’ ৩১ জানুয়ারি ২০১৮, মণীন্দ্র গুপ্ত চলে যাওয়ার পর থেকে সমস্ত জগৎ ভুলে গিয়েছিলেন দেবারতি। যা ভেবেছেন, যা লিখেছেন সব একটি মানুষকে ঘিরে। মৃত্যুর পরে আরও তীব্রভাবে মণীন্দ্র গুপ্ত হয়ে উঠেছিলেন দেবারতির মর্মজগৎ। শরীর কীভাবে ভাঙতে ভাঙতে নিজেকে নিঃশেষ করে ফেলেছিলেন অযত্নে অবহেলায়, যারা তাঁকে এইসময় দেখেছিলেন, জানেন। ‘ঈশ্বরদর্শন না হলে প্রেম হয় না’– শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন। দেবারতি মিত্রের কোনও অলৌকিক ঈশ্বরদর্শন হয়েছিল কি না, আমরা জানি না; তবে ঈশ্বরতুল্য এক জীবনসঙ্গী পেয়েছিলেন আজীবন।
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
