
সোশ্যাল মিডিয়াতে কোভিডের চেয়েও ভয়ানক ভাইরাস ঘুরে বেড়ায়। সেরকম ভাইরাল কিছু সূত্র থেকে জানা গেল, রামপ্রসাদ সেনই নাকি লিখেছিলেন, ‘এই জীবন ভরা ভুলের ডালি/ তোমার পায়ে দিলাম ঢালি,/ এখন তোমার কৃপায় অমৃত হোক্ ব্যথার গরল যত!’ ইউটিউব উপচে পড়ছে লাল-নীল জবার ইমোজিতে, ভুলেও গায়ক-গায়িকারা ভুল সংশোধন করছেন না। একটু সতর্ক থাকলেই বোঝা যেত, রামপ্রসাদ সেন উমার গান-শ্যামার গানের ভুবন ভরিয়ে দিলেও এই গান, এই বিশ শতক-ঘেঁষা শব্দ, এই সুরের ছক তাঁর নয়।
প্রচ্ছদ অর্ঘ্য চৌধুরী

পথের ধারে আলোর মালা, জানলায় রঙিন বাতি, আকাশে ফানুস, আর চোরাগোপ্তা দুম ফটাস্ আওয়াজের মতোই কালীপুজোর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ পান্নালাল। শানু-নাসিক সংস্করণ যতই বাজারে থাক, পান্নালালের ওই শান্তমধুর কণ্ঠের চিরকৈশোর সমস্ত প্রতিযোগিতার ঊর্ধ্বে। সেই কণ্ঠ শোনা যাবে না, এমন পুজো বিরল। আর কয়েকটা ঘণ্টার অপেক্ষা। অথবা বেশিরভাগ জায়গাতেই অপেক্ষা এখনই শেষ। শ্যামাপোকা-উপদ্রুত জানলার কাচ ভেদ করে আসছে অভিমানী শব্দগুচ্ছ, ‘যদি তোর ও মন্দিরের দ্বারে/ তোমার লাগি কাঁদি অঝোর ধারে/ যদি নয়ন হতে লুপ্ত ভুবন হয় সেই সে অশ্রুতেই/ তবে আমার কাছে আসবিনে, তোর এমন সাধ্য নেই।’
কার তৈরি এই শব্দমালা? এই সুরের মায়াই বা কার রচনা? আন্তর্জাল বলবে, ‘প্রচলিত’। কবে থেকে প্রচলিত? রামপ্রসাদ-কমলাকান্তের যুগ থেকে? কার নামে প্রচলিত? আঠারো শতকের কোনও সাধক ভক্তের নামে? দু’টিরই উত্তর– না। পান্নালাল ভট্টাচার্যই এই গানের প্রথম গায়ক। তাই তাঁর কণ্ঠেই ১৯৬০-এর দশকে এই গান প্রচলিত ও প্রচারিত হয়। কার নামে প্রচলিত, এই প্রশ্নের উত্তর গোলমেলে। কোথাও ‘প্রচলিত’-র বেশি কিছু বলাই হবে না, কোথাও আবোল তাবোল কিছু নাম দেওয়া থাকবে। একটি গানকে ‘প্রচলিত’ বলতে গেলে তা যতটা প্রাচীন হতে হয়, এই গান তা নয়; লোকপরম্পরায় বাহিত হয়ে উৎসনির্দেশ হারিয়ে ফেলার কথা নয়, কারণ এটি নগরসভ্যতার মূলস্রোতেই তৈরি হওয়া গান। অথচ দিনের পর দিন আমরা স্রষ্টাকে চেনার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করিনি। দীর্ঘদিন এই প্রমাদ চলার পরে রেকর্ড লেবেল সারেগামা প্রমাদ সংশোধন করে এই গানের গীতিকার-সুরকার হিসেবে নাম দেখিয়েছে দিলীপকুমার রায়। তথ্যগত ভুল এতে না থাকলেও তথ্যের অপূর্ণতা আছে। কারণ, বাঙালি সংগীতশ্রোতা দিলীপকুমার রায় বলতে প্রথমেই যাঁকে চেনে, তিনি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সুযোগ্য পুত্র, গায়ক, সংগীতজ্ঞ, সংগীতস্রষ্টা। এঁর চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম খ্যাত, কম প্রচারিত গায়ক, শিক্ষক ও সংগীতনির্মাতা ছিলেন তাঁরই সমনামী, রজনীকান্ত সেনের দৌহিত্র। পরিচয় উল্লেখিত না থাকায় এই গানকেও অনেকেই মন্টুবাবুর গান বলেই চিনে এসেছে, রীতিমতো তর্কাতর্কিও করতে হয়েছে ভুল ধরিয়ে দেওয়ার ফলে।
………………………….
দীর্ঘদিন এই প্রমাদ চলার পরে রেকর্ড লেবেল সারেগামা প্রমাদ সংশোধন করে এই গানের গীতিকার-সুরকার হিসেবে নাম দেখিয়েছে দিলীপকুমার রায়। তথ্যগত ভুল এতে না থাকলেও তথ্যের অপূর্ণতা আছে। কারণ, বাঙালি সংগীতশ্রোতা দিলীপকুমার রায় বলতে প্রথমেই যাঁকে চেনে, তিনি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সুযোগ্য পুত্র, গায়ক, সংগীতজ্ঞ, সংগীতস্রষ্টা। এঁর চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম খ্যাত, কম প্রচারিত গায়ক, শিক্ষক ও সংগীতনির্মাতা ছিলেন তাঁরই সমনামী, রজনীকান্ত সেনের দৌহিত্র।
………………………….
রেকর্ড কোম্পানির নির্দেশে, পান্নালাল ভট্টাচার্যের গাওয়ার জন্যেই দু’টি গান তৈরি করেছিলেন দিলীপ রায়, একটি ‘আমি মন্ত্র-তন্ত্র কিছুই জানিনে মা’, যার অন্তরা থেকে উপরের লাইনগুলি উদ্ধৃত, আরেকটি– অত্যন্ত জনপ্রিয় ‘আমি সব ছেড়ে মা ধরব তোমার রাঙা চরণ দুটি’। এ গানও, যথারীতি, কে বেঁধেছে, তা আমরা জানতে চাই না। সোশ্যাল মিডিয়াতে কোভিডের চেয়েও ভয়ানক ভাইরাস ঘুরে বেড়ায়। সেরকম ভাইরাল কিছু সূত্র থেকে জানা গেল, রামপ্রসাদ সেনই নাকি লিখেছিলেন, ‘এই জীবন ভরা ভুলের ডালি/ তোমার পায়ে দিলাম ঢালি,/ এখন তোমার কৃপায় অমৃত হোক্ ব্যথার গরল যত!’ ইউটিউব উপচে পড়ছে লাল-নীল জবার ইমোজিতে, ভুলেও গায়ক-গায়িকারা ভুল সংশোধন করছেন না। একটু সতর্ক থাকলেই বোঝা যেত, রামপ্রসাদ সেন উমার গান-শ্যামার গানের ভুবন ভরিয়ে দিলেও এই গান, এই বিশ শতক-ঘেঁষা শব্দ, এই সুরের ছক তাঁর নয়। রেকর্ড লেবেলগুলি গায়ক, বাদক, ধ্বনিগ্রাহক, চিত্রগ্রাহক, প্রত্যেকের নাম সযত্নে প্রকাশ করলেও অযত্নে এড়িয়ে যাচ্ছে স্রষ্টার পরিচয়। অথচ প্রথম প্রকাশের সময় তো বটেই, পরে ‘মায়ের পায়ের জবা’ নামের সংকলনেও সম্ভবত স্রষ্টার নাম উল্লেখিত ছিল।

শুধু দিলীপকুমারের ক্ষেত্রে নয়, তাঁর মাতামহ রজনীকান্তেরও এমনই ললাটলিখন! তাঁর বহুল প্রচলিত গান ‘মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়’-এর তো সুর-টুর বদলেই গেয়ে ফেলা হয়েছে। ভক্তিসংগীতের স্বত্বও ভাসমান। ‘আমি সকল কাজের পাই হে সময়, তোমারে ডাকিতে পাইনে’, রজনীকান্ত সেনের বিখ্যাত গান। না, কোনও খ্যাতনামা রেকর্ড লেবেলেই একে ‘রামপ্রসাদী’ বলা হয়নি, রজনীকান্তের নামই স্বীকৃত। বহু মঞ্চে অবশ্য ‘রামপ্রসাদী’ বলে গাইতে শুনেছি। কিন্তু ভালো করে পড়ে বা শুনে দেখি, এটি কি আদৌ শ্যামাসংগীত? গানে কোথাও শ্যামা, তারা, কালী দূরস্থান, মা সম্বোধনও নেই। রজনীকান্তের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ‘কল্যাণী’-র অন্তর্গত গান এটি। নিচে লেখা ছিল, গানটি গাওয়া হবে রবীন্দ্রনাথের ‘তোমার কথা হেথা কেহ তো বলে না’-র সুরে। যেমন ‘দাঁড়াও আমার আঁখির আগে’-র সুরে ‘শুনাও তোমার অমৃতবাণী’, ‘উঠ গো ভারতলক্ষ্মী’-র সুরে ‘আকুল কাতর কণ্ঠে’, তেমনই এক রচনা এটি। যদিও, রেকর্ডে গানটিকে যে সুরকাঠামোতে শোনা যায়, তার সঙ্গে উল্লেখিত গানটির সুরগত সাযুজ্য থাকলেও প্রভেদই বেশি। তবে তার চেয়ে বড় কথা, রজনীকান্তের ঈশ্বরবিষয়ক গানের ‘দয়াল’ বা ‘হরি’-র বদলে এই গানের ‘তুমি’-কে শ্যামা-তারা-কালী ভাবার কারণ কী? কারণ একমাত্র পান্নালাল ভট্টাচার্যের রেকর্ড।
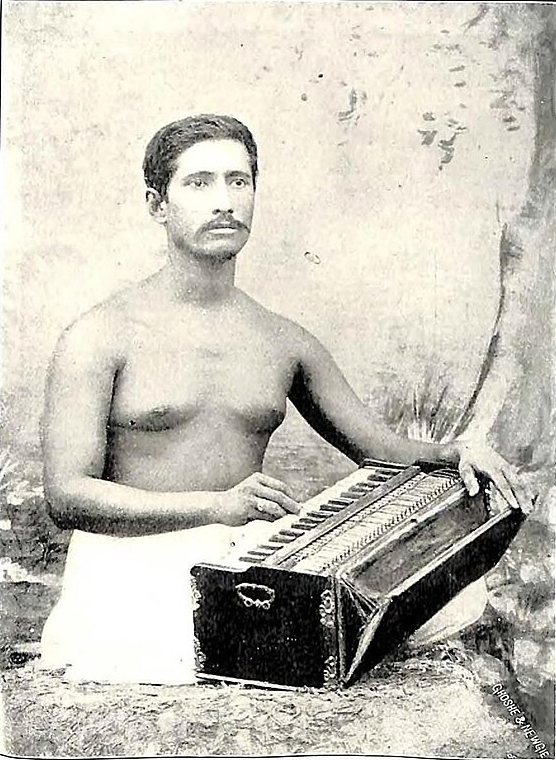
আসলে, যে গানগুলির উল্লেখ করেছি, তার বাণী ও সুরে পুরনো সময়ের গন্ধ বেশ প্রকট। বিশেষত, মাস্টারমশাই শ্রী দিলীপকুমার রায়ের কাছ থেকেই শোনা, শ্যামাসংগীত রচনার পূর্ব অভিজ্ঞতা বা আন্তরিক ভক্তি-তাগিদ, কোনওটাই না থাকায় তিনি প্রাচীন শাক্ত পদের মডেলগুলিকেই তখনকার মতো অবলম্বন করেছিলেন। ফলে কী হল? মধ্যযুগে যেমন অখ্যাত কবিরা জনপ্রিয় কবির ভণিতা বসিয়ে নিজের পদকে বাজারে চালিয়ে দিতেন, পান্নালাল-শানু-অনুরাধার শ্রোতারা বা অন্যান্য ‘রিমেক’ গায়কেরা চেনা বামুনের নামে গানগুলি প্রচার করে ফেললেন। অদীক্ষিত জনশ্রবণে খুব কিছু ধরা পড়ল না, কারণ গানের পরিমণ্ডল প্রায় সে যুগের।
এই বৃত্তে একেবারে নতুন স্বর ‘আমায় একটু জায়গা দাও, মায়ের মন্দিরে বসি’। ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত ‘মা আমার মা’ অ্যালবামের এই গান, এর সঙ্গে থাকা অন্যান্য গানও বহু যুগ ব্যবধানে মাতৃসংগীতের এক নতুন সম্ভাবনা দেখিয়েছিল। গুণাগুণের কথা বাদ দিয়েই বলা যায়, আঠারো শতকের প্রাচীন শাক্ত পদ, উনিশ শতকের অনুবর্তন, বা তার অনুসরণে রচিত বিশ শতকের গানের তুলনায় শতকশেষের এই গানগুলি কালের পার্থক্যকে অনেক স্পষ্ট করেছিল। ভিতরের ভাব একই, সেই পুরনো অভিমান, সেই আত্মসমর্পণ, সেই উদ্ধারের বাসনা, সেই অনর্গল মিনতি। কিন্তু যে ভাষাগত বদল ঘটে গিয়েছে, তা চোখে পড়তে বাধ্য। তবে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা এই গানগুলি শুনতে গেলে মাঝেমাঝে মনে হয়, শ্যামাসংগীত বানাবার ছলে কি ভবিষ্যতের ঘোষণা করেছিলেন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়? ‘জীবনটা মনে হয় ব্যর্থ আবর্জনা/ ভাবি গঙ্গায় ঝাঁপ দিই/ রেলের লাইনে মাথা রাখি’… গীতবাণী হিসেবে খুব উচ্চাঙ্গের একে কোনও দিনই মনে হয়নি, কিন্তু গান প্রকাশের ঠিক এক বছর পরে, ১৯৯৯ সালে যখন হুগলি নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, তখন নতুন করে ওই অ্যালবামের প্রতিটি গানকে তাঁর আত্মজৈবনিক উচ্চারণ হিসেবে পড়তে শুরু করি। গানগুলিতে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাক্ষর এতই তীক্ষ্ণ যে, তাকে চিনতে ভুল হয় না। অন্তত এখনও হয়নি। কিন্তু কয়েক শতাব্দী পর? যখন এই কবি-গীতিকারের বৈশিষ্ট্য, বা এই সুরস্থাপনার লক্ষণ সম্পর্কে ধারণা ফিকে হয়ে যাবে, তখন? পোস্ট-ট্রুথ পৃথিবীকে হরদম দেখতে দেখতে আশঙ্কা হচ্ছে, আজ থেকে ৩০০ বছর পর হয়তো ‘শুধু আরতি যখন করবে/ মার পূজাদীপ তুলে ধরবে/ আমাকে দেখতে দিও মায়ের একটু হাসি’ হয়ে যাবে কমলাকান্তের বাণী।
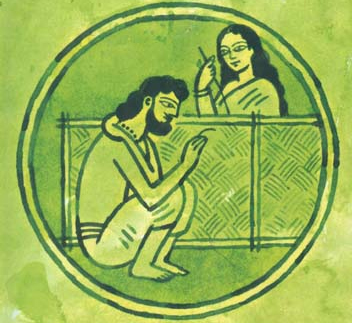
পৃথিবীর সব শ্যামাসংগীতকেই ‘রামপ্রসাদী’ বলে চালিয়ে দেওয়া তা বলে এতটাও সহজ নয়। উল্টোটাও ঘটে। রামপ্রসাদের নিজের গানের ক্রেডিটই তাঁর থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছে জেনারেশন জেড! সেই প্রবণতায় নবতম ও বিচিত্রতম সংযোজন ‘মন রে কৃষিকাজ জানো না’। নিজের চোখকানকে বিশ্বাস করতে না পারলেও দেখছিলাম, সংগীত প্রতিযোগিতার মিষ্টি প্রতিযোগী গানটি ‘কভার’ করে গীতিকারের নাম লিখেছেন শ্রীজাত। সুরকার? না, অরিজিৎ সিং নন, জয় সরকার। একটুও অতিরঞ্জন নয়, পরিস্থিতি এমনই অদ্ভুত।
………………………………………..
ফলো করুন আমাদের ফেসবুক পেজ: রোববার ডিজিটাল
………………………………………..
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
