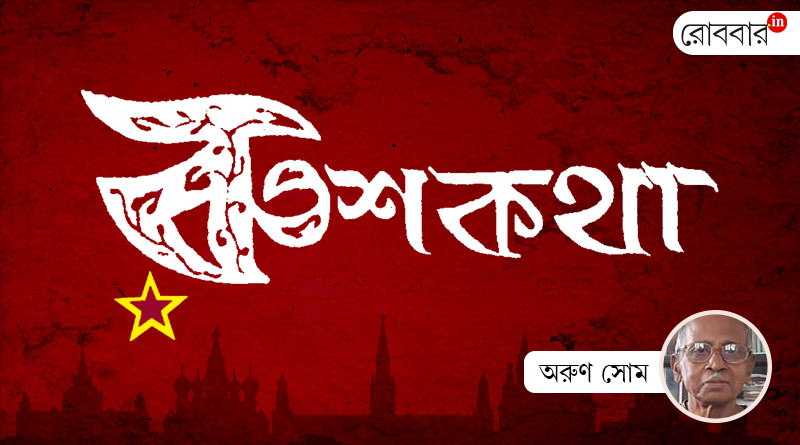
জ্লাতা আলেক্সেইয়েভনার বাড়িতে একবার সেই সময়কার বিখ্যাত লেখিকা আশা দেবীর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তাঁর স্বামী খ্যাতনামা লেখক ও অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের মাস্টারমশাই ছিলেন, কিন্তু আশা দেবীর সঙ্গে আলাপ ছিল না। তখনও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় জীবিত, নিজেদের সদ্যনির্মিত বাসভবনে যাননি। আশা দেবী সিটি কলেজে বাংলা পড়াতেন, ইলা মিত্রও সেখানে বাংলা পড়াতেন। ইলাদির সঙ্গে আমার ভালোই পরিচয় ছিল, সেকথা ওঠাতে বুঝতে পারলাম দু’জনের মধ্যে তেমন একটা সদ্ভাব নেই।

১৯.
কোনও এক দেশান্তরী রুশি পরিবারের কাহিনি
কলকাতায় আমার রুশ ভাষার শিক্ষিকা ছিলেন একজন দেশান্তরী রুশ মহিলা– জ্লাতা আলেক্সেইয়েভনা তিরতভা। তিনি ভারত সোভিয়েত সংস্কৃতিতে রুশ ভাষা শেখাতেন। ঘটনাচক্রে দেখা গেল পার্ক সার্কাসে আমাদের বাড়ির মাত্র কয়েক পা দূরে একটা ভাড়া বাড়ির একতলায় থাকেন। পরিবার বলতে স্বামী আর দুই ছেলে। বড়জনের বয়স তখন বছর বারো। ছোটটির বছর আষ্টেক, একটু জড়বুদ্ধি মতো। কিন্তু পাড়ায় তার ভারি খাতির– এর-ওর ফাইফরমাস খাটত। ভাঙা ভাঙা ইংরেজি বলত। রুশ ভাষা তেমন একটা জানত বলে মনে হয়নি। স্বামী ভদ্রলোক একটা জাহাজ কোম্পানিতে কাজ করেন। টাকা পয়সার তাই তেমন একটা অভাব ছিল না। বাড়িতে প্রশস্ত জায়গা– বিশেষত সামনে হলঘরের মতো জায়গাটা বড়ই আকর্ষণীয়। সেখানে ছুটির দিনগুলিতে, সন্ধ্যায়, অনেক সময় দিনে-দুপুরেও পাড়ার যত অ্যাংলো ইন্ডিয়ান, আর্মেনীয় সম্প্রদায়ের লোকজনের আড্ডা বসত। জ্লাতা আলেক্সেইয়েভনা ক্লাস নিতে যেতেন সন্ধ্যাবেলায়। একসময় গোলপার্কের রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউটেও রুশ ভাষার শিক্ষকতা করেছেন।
অতিথি অভ্যাগত, আহূত, অনাহূত, রবাহূত যাঁরাই তাঁর বাড়িতে আসতেন, তাঁদের অনেকেই সেখানে ডিনারও সারতেন। এ ব্যাপারে ভদ্রমহিলার যেমন কোনও কার্পণ্য ছিল না, তেমনই তিনি আবার অসাধারণ রন্ধনকুশলীও ছিলেন। বেশিরভাগ খাবারই হত রুশি খাবার। গৃহকর্তা কলকাতায় থাকলে আমার বেশিরভাগ কথাবার্তা তাঁর সঙ্গেই হত, বলাই বাহুল্য, রুশ ভাষায়। রসনা পরিতৃপ্তির সঙ্গে রুশ ভাষার চর্চা– এর চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে। প্রথম সোভিয়েত ইউনিয়নে গিয়ে সেদেশের খাবার নিয়ে তাই আমাকে এতটুকু সমস্যায় পড়তে হয়নি।
স্বামীর বাণিজ্য জাহাজে কাজের সূত্রে ওঁরা প্রথমে এসেছিলেন বোম্বাইতে, তারপর সেখানেই থেকে যান, কয়েক বছর বাদে কলকাতায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। এক পুরুষ আগে ওঁদের বাবা-মা বিপ্লবের পরপর দেশত্যাগ করে চিনের হার্ভিন প্রদেশে গিয়ে থাকতে শুরু করেন। সেখানে নাকি প্রবাসী রুশিদের একটা বিরাট কলোনি ছিল। দোকানপাটে রুশি পণ্যদ্রব্য, খাবার-দাবার পাওয়া যেত, রুশ ভাষায় লেখা সাইনবোর্ড যত্রতত্র দেখা যেত, রুশি স্কুলও ছিল, রাস্তা-ঘাটে সর্বত্র রুশি ভাষার এমন ছড়াছড়ি এবং রুশি লোকজনের এমন ভিড় থাকত যে, বিদেশ বলে মনেই হত না। প্রাক্তন শ্বেতরক্ষী অফিসারদের কোনও কমতি ছিল না, অনেক সময় জারের সেনাবাহিনীর উর্দি পরে সামরিক পদক বুকে বুলিয়ে তাঁদের ঘোরাফেরা করতেও দেখা যেত। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন বিপন্ন, তখন এঁরাই আবার সে দেশ রক্ষার জন্য নিজেদের সামরিক পদক বিক্রি করে এবং নানা উপায়ে চাঁদা সংগ্রহ করে সেখানে সাহায্য পাঠিয়েছিলেন। এই যুদ্ধ তাঁদের কাছেও ছিল ‘পিতৃভূমির মহাযুদ্ধ’।
বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা এই সমস্ত দেশান্তরী রুশিদের সোভিয়েত সরকার অনেক সময় সোভিয়েত নাগরিকত্বের প্রমাণ স্বরূপ সোভিয়েত ‘আন্তর্জাতিক’ পাসপোর্ট দিতেন বটে, কিন্তু সে পাসপোর্ট থাকলেই দেশে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাসের অধিকার পাওয়া যেত না। কেননা দেশের অভ্যন্তরেও একটা ‘অভ্যন্তরীণ’ পাসপোর্ট ব্যবস্থা ছিল এবং এখনও আছে। সেটা না থাকলে, উপরন্তু তার পরেও সে দেশের কোনও শহরে বসবাস করার রেজিস্ট্রেশন না থাকলে, দেশে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাসের অধিকার পাওয়া কোনওভাবেই সম্ভব নয়। আর, সোভিয়েত সংবিধান ছিল এতটাই মানবিক যে, কোনও নাগরিককে সে অধিকার দিতে গেলে সরকারের পক্ষে তার বাসস্থানের ব্যবস্থা ও কর্মসংস্থানও ছিল বাধ্যতামূলক। কোনও কোনও বিশিষ্ট দেশান্তরীর ক্ষেত্রে সরকার সেসব ব্যবস্থা করলেও সাধারণ দেশান্তরী নাগরিকের ক্ষেত্রে সেটা করা হয় না। ফলে কার্যত এদের পক্ষে দেশে ফেরা সম্ভব নয়। শুধু তা-ই নয়, সোভিয়েত দূতাবাস বা দূতস্থানের কোনও অনুষ্ঠানেও এরা কখনও আমন্ত্রিত হত না।
ওঁর স্বামীর কর্মসূত্রে প্রায়ই ওদেশে বা অন্যান্য সোভিয়েত বন্দরে যাতায়াত ছিল। ওসব জায়গায় গেলে স্থানীয় রুশিরা অনেকেই ওঁর মুখে রুশ ভাষা শুনে অবাক হয়ে বলত, ‘আপনি তো দিব্যি রুশিদের মতোই রুশ ভাষা বলেন।’ উনি বলতেন, ‘আমি তো রুশিই।’ তাতে ওরা আরও অবাক হয়ে যেত। ওঁর কথায়, ‘ওখানে সবই ভালো শুধু বড্ড বেশি নজরদারি’। সোভিয়েত ইউনিয়নের কোনও বিরূপ সমালোচনা ওঁদের দু’জনের কারও মুখ থেকে আমি কোনও দিন শুনতে পাইনি। তবে ওঁদের রুশভাষাটা একটা জায়গায় এসে থমকে গিয়েছিল। ঘটনাচক্রে আমার উপস্থিতিতেই সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে আগত রুশ ভাষার জনৈক শিক্ষকের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ ও বাক্যালাপ হয়েছিল। তিনি বললেন খাঁটি রুশ উচ্চারণ এবং শব্দপ্রয়োগও বিশুদ্ধ, কিন্তু আজকাল ঠিক এই ভাষায় লোকে কথা বলে না। প্রথমবার সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ফিরে আসার পর লক্ষ করেছি, বিশেষভাবে ভদ্রমহিলা, অনেক নতুন রুশ শব্দের সঙ্গে পরিচিত নন– শব্দগুলি যদি প্রযুক্তিবিদ্যা সংক্রান্ত হয় তাহলে তো কথাই নেই। যেমন ‘রেকর্ড প্লেয়ার’, ‘টেপ রেকর্ডার’ বা ‘ফ্রিজ’-এর রুশভাষার প্রতিশব্দ তাঁর জানা নেই– গ্রামাফোন পর্যন্ত জানা আছে। অন্যগুলির ইংরেজিই শুধু জানেন।
ওঁদের বাড়িতে রুশ গান বাজনার রেকর্ডের একটা বড় সংগ্রহ ছিল। সময় পেলে বাজিয়ে শুনতাম। এছাড়া ওদেশের ওপর নানা রকম ছবির বই দেখতাম, স্লাইড প্রোাজেক্টর দিয়ে ছবিও দেখতাম। তাই মস্কোতে যখন প্রথম যাই, তখন ক্রেমলিন থেকে শুরু করে সেখানকার রাস্তাঘাট, দর্শনীয় বস্তু, মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের দালান– কোনওটাই আমার কাছে অপরিচিত বলে মনে হয়নি।
জ্লাতা আলেক্সেইয়েভ্নার সঙ্গে মিলে বিভিন্ন বাণিজ্য সংস্থা, সরকারি ও বেসরকারি বেশ কিছু সংস্থার প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের রুশ থেকে ইংরেজি এবং ইংরেজি থেকে রুশ অনুবাদের কাজও করেছি।
তখন পর্যন্ত কোনও প্রকাশনালয় থেকে রুশ সাহিত্য অনুবাদের কোনও সুযোগই পাইনি। দেশে থাকতে সাহিত্যের অনুবাদ বলতে আমার মাত্র একটি অনুবাদই প্রকাশিত হয়েছিল, প্রকাশিত হয়েছিল স্থানীয় একটি সাহিত্যপত্রে– কিন্তু কোনও রুশ গল্পের নয়, সেটা ছিল চিন দেশের খ্যাতনামা লেখক ল্যু সুন-এর একটি গল্পের অনুবাদ, বলাই বাহুল্য, ইংরেজি থেকে।

জ্লাতা আলেক্সেইয়েভনার বাড়িতে একবার সেই সময়কার বিখ্যাত লেখিকা আশা দেবীর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তাঁর স্বামী খ্যাতনামা লেখক ও অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের মাস্টারমশাই ছিলেন, কিন্তু আশা দেবীর সঙ্গে আলাপ ছিল না। তখনও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় জীবিত, নিজেদের সদ্যনির্মিত বাসভবনে যাননি। আশা দেবী সিটি কলেজে বাংলা পড়াতেন, ইলা মিত্রও সেখানে বাংলা পড়াতেন। ইলাদির সঙ্গে আমার ভালোই পরিচয় ছিল, সেকথা ওঠাতে বুঝতে পারলাম দু’জনের মধ্যে তেমন একটা সদ্ভাব নেই।

সে যাই হোক, আশা দেবী বোধহয় কিছুদিন রুশ ভাষার পাঠ নিয়েছিলেন, সেই সূত্রে জ্লাতা আলেক্সেইয়েভনার সঙ্গে তাঁর পরিচয়। যে সময়কার কথা বলছি, তখন তিনি ওঁর কাছে আসতেন একটা অনুবাদের কাজ নিয়ে। ‘বিংশ শতাব্দী’ প্রকাশনালয় থেকে তিনি একটা বই রুশ থেকে মুখে মুখে ইংরেজিতে অনুবাদ করে যাচ্ছেন আর ওঁর মুখের কথা পড়তে না পড়তে আশা দেবীও তরতর করে তার বাংলা অনুবাদ লিখে যাচ্ছেন। এভাবে যে মূল থেকে অনুবাদ করা যায়, তা আমার ধারণায় ছিল না।

সম্প্রতি কোনও এক জনপ্রিয় বাংলা সংবাদপত্রের এক প্রতিবেদন থেকে জানতে পারলাম নারায়ণবাবু নাকি খুব ভালো রুশভাষা জানতেন। প্রমথনাথ বিশী মহাশয় তার সাক্ষী। এঁরা দু’জনেই আমার শিক্ষক। আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে এঁদের ছাত্র, তখন ঘুণাক্ষরেও এর আভাস পাইনি। পরবর্তীকালে আশা দেবীর এইভাবে বাংলা অনুবাদ করাটাও নিশ্চয়ই তার সাক্ষ্য বহন করে না। অথচ প্রতিবেদক লিখেছেন, একবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে নাকি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান একাডেমি থেকে রুশ ভাষায় লেখা একটি চিঠি এসেছিল, নারায়ণবাবু সঙ্গে সঙ্গে তার চমৎকার অনুবাদ করে দিয়েছিলেন, আর প্রমথনাথ বিশী মহাশয় নাকি তাতে ভারি চমৎকৃত হয়েছিলেন। এসব জনশ্রুতি ছাপার অক্ষরে যত কম প্রচারিত হয়, ততই ভালো নয় কি? নারায়ণবাবু নিজেও কি এমন কোনও দাবি কখনও করেছেন?

আমি কলকাতা ছেড়ে চলে আসার বছর তিনেক আগে আমায় শিক্ষিকার স্বামী মি. তিরতভ্ জাহাজ কোম্পানির চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁদের বড় ছেলেটিও অস্ট্রেলিয়ায় চলে গেছে। অবসর গ্রহণের স্বল্পকালের মধ্যেই মি. তিরতভ্ একটা চাকরি জুটিয়ে ফেললেন। ওড়িশার কেওনঝোর না কোথাকার কোনও এক মহারাজার খামারের ম্যানেজারির কাজ। শরীর অর্ধেক ধসে গেছে। মাথায় জীবিকার বোঝা। বড় ছেলে অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে কী করছে না করছে, কিছুই জানেন না। মাঝে মাঝে ছুটি নিয়ে ভদ্রলোক কলকাতায় আসতেন। বলতেন খাবার বলতে জোটে পুঁই ডাটার চচ্চড়ি আর ডাল ভাত। কলকাতার বাড়িতে অতিথি অভ্যাগতদের আর সেই রমরমা নেই। এক ছুটির দিনে ওঁর বাড়ি দিয়ে দেখলাম বাইরের বড় হলে তাঁর বেশ কিছু বান্ধবী এসে জুটেছেন। সকলে বিষণ্ণ ও গম্ভীর মুখে টেবিলের চারধারে বসে আছেন। তখন গ্রীষ্মকাল। শুনলাম মি. তিরতভ্ মারা গেছেন। প্রচণ্ড গরমে পুকুরে স্নান করতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে আর উঠতে পারেননি– ম্যাসিভ হার্ট আটক।
ঘনিয়ে এল চরম দুর্দশার কাল। বাড়িতে একা আর স্বল্পবুদ্ধি ছোট ছেলেটি। বাড়িভাড়া মেটাতে পারেন না। একসময় বাড়িওয়ালার নোটিশ এল, বাড়ি ছাড়তে হল। একদিন গিয়ে দেখি বাইরে থেকে তালা বন্ধ। দারোয়ান বলল মেমসাহেব পাশের গলিতে একটা বাড়িতে উঠে গেছেন। গিয়ে দেখলাম বাসা বলতে একটা একচিলতে ঘুপটি ঘর, আলো-হাওয়া ঢোকে না, বাইরে চটের পর্দা ঝুলছে।
এরপর তাঁর পরিচিত কে একজন শিয়ালদহের রেল কলোনির এক কামরার একটা ফ্ল্যাটে তাঁকে স্থান দিয়েছিলেন। স্থায়ীভাবে মস্কোয় চলে যাওয়ার আগে সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে গেলাম। মস্কো থেকে তাঁকে ওই ঠিকানায় একাধিক চিঠি লিখেছিলাম, সাড়া পাইনি।
তিন বছর বাদে গ্রীষ্মকালে ছুটিতে কলকাতায় আসার পর পার্ক সার্কাসে আমাদের পাড়ায় জ্লাতা আলেক্সেইয়েভ্নার সন্ধান করলাম। বেশি খুঁজতে হল না– পাড়ায় একটা দোকানের সামনে তাঁর ছোট ছেলের সন্ধান পেয়ে গেলাম। এবারে আশ্রয় নিয়েছেন ডাক্তার গণির বাড়িতে। ডাক্তার গণির মেয়ে, তখনকার এক বিশিষ্ট সমাজসেবী সাজেদা আসাদ, পাড়ার সকলের লিলিদি, তাঁদের বাড়ির চিলেকোঠায় তাঁকে আশ্রয় দিয়েছেন। লিলিদির সঙ্গে আমার অনেক আগে থাকতেই পরিচয়। গিয়ে সস্ত্রীক দেখা করলাম জ্লাতা আলেক্সেইয়েভনার সঙ্গে। ভারি খুশি হলেন। এবারে অতটা করুণ দেখাল না। ছেলে বলছে শিগগিরই ওঁদের অস্ট্রেলিয়ায় নিয়ে যাবে। যে ক’দিন কলকাতায় ছিলাম, প্রায়ই ওঁর বাসায় যেতাম। আমরা ওঁকে এক বোতল শ্যাম্পেন আর ওখানকার চকোলেট উপহার দিয়েছিলাম। সোভিয়েত শ্যাম্পেনের খালি বোতল আর চকোলেটের মোড়কটা পরে তিনি যত্ন করে রেখে দিয়েছিলেন। বললেন, এছাড়া ওদেশের আর কোনও স্মৃতিচিহ্ন তাঁর কাছে নেই। যা ছিল সব বিক্রি হয়ে গেছে। এবারে এতকাল পরে জানতে পারলাম ওর মা নাকি এতকাল জীবিত ছিলেন, হালে প্যারিসে এক বৃদ্ধাবাসে মারা গেছেন– বয়স হয়েছিল একশোর কাছাকাছি।
পরের বার ছুটিতে দেশে এসে শুনলাম ওঁরা অস্ট্রেলিয়ায় চলে গেছেন। ওখান থেকে চিঠি লিখে ওঁর থেকে কোনও সাড়াশব্দ পাইনি। খবরটা জানতামই না। আমার আসার খবর পেয়ে লিলিদি নিজেই আমাদের বাড়ি এসেছিলেন ওঁর কোনও সংবাদ আমি রাখি কি না, জানার জন্য। আমি বললাম আমার সঙ্গেও কোনও যোগাযোগ নেই। লিলিদির মুখেই পরে জানতে পারলাম ছোট ছেলেটি নাকি কলকাতায় আসার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল, কলকাতায় আসবে বলে টাকা সংগ্রহ করছিল। এতদূর মনমরা হয়ে পড়েছিল যে শেষ পর্যন্ত মারা যায়। শেকড় ছেঁড়ার যন্ত্রণার কি কোনও উপশম আছে?
…পড়ুন রুশকথার অন্যান্য পর্ব…
পর্ব ১৮। লেডি রাণু মুখার্জিকে বাড়ি গিয়ে রুশ ভাষা শেখানোর দায়িত্ব পড়েছিল আমার ওপর
পর্ব ১৭। একদিন হঠাৎ সুভাষদা আমাদের বাড়ি এসে উপস্থিত ফয়েজ আহমেদ ফয়েজকে নিয়ে
পর্ব ১৬। মুখের সেই পরিচিত হাসিটা না থাকলে কীসের সুভাষ মুখোপাধ্যায়!
পর্ব ১৫। রুশ ভাষা থেকেই সকলে অনুবাদ করতেন, এটা মিথ
পর্ব ১৪। মস্কোয় ননীদাকে দেখে মনে হয়েছিল কোনও বিদেশি, ভারতীয় নয়
পর্ব ১৩। যিনি কিংবদন্তি লেখক হতে পারতেন, তিনি হয়ে গেলেন কিংবদন্তি অনুবাদক
পর্ব ১২। ‘প্রগতি’ ও ‘রাদুগা’র অধঃপতনের বীজ কি গঠনপ্রকৃতির মধ্যেই নিহিত ছিল?
পর্ব ১১। সমর সেনকে দিয়ে কি রুশ কাব্যসংকলন অনুবাদ করানো যেত না?
পর্ব ১০। সমর সেনের মহুয়ার দেশ থেকে সোভিয়েত দেশে যাত্রা
পর্ব ৯। মস্কোয় অনুবাদচর্চার যখন রমরমা, ঠিক তখনই ঘটে গেল আকস্মিক অঘটন
পর্ব ৮: একজন কথা রেখেছিলেন, কিন্তু অনেকেই রাখেননি
পর্ব ৭: লেনিনকে তাঁর নিজের দেশের অনেকে ‘জার্মান চর’ বলেও অভিহিত করত
পর্ব ৬: যে-পতাকা বিজয়গর্বে রাইখস্টাগের মাথায় উড়েছিল, তা আজ ক্রেমলিনের মাথা থেকে নামানো হবে
পর্ব ৫: কোনটা বিপ্লব, কোনটা অভ্যুত্থান– দেশের মানুষ আজও তা স্থির করতে পারছে না
পর্ব ৪: আমার সাদা-কালোর স্বপ্নের মধ্যে ছিল সোভিয়েত দেশ
পর্ব ৩: ক্রেমলিনে যে বছর লেনিনের মূর্তি স্থাপিত হয়, সে বছরই ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙার সূচনাকাল
পর্ব ২: যে দেশে সূর্য অস্ত যায় না– আজও যায় না
পর্ব ১: এক প্রত্যক্ষদর্শীর চোখে রাশিয়ার খণ্ডচিত্র ও অতীতে উঁকিঝুঁকি
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
