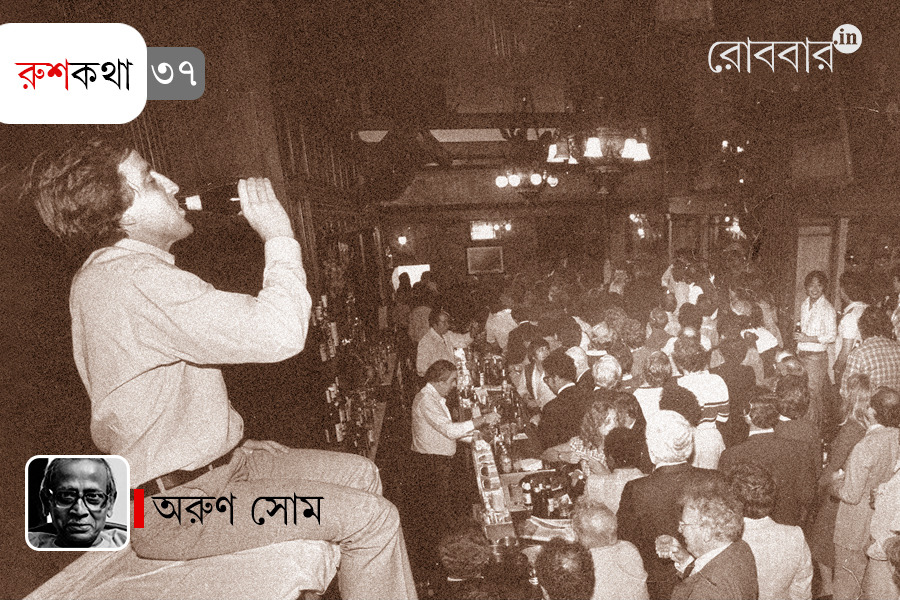
স্ত্রী-পুরুষের মেলামেশার ব্যাপারে আমাদের মতো সামাজিক সংস্কারাচ্ছন্ন দেশের লোকদের এটাই বিপদ। এদের অনেকে বিদেশে এসে অবাধ মেলামেশার সুযোগ পেয়ে মনে করে সেখানকার মেয়েরা সকলে নষ্ট চরিত্রের। রুশি মেয়েদের সম্পর্কে বিশেষভাবে এরকম ধারণাই প্রচার করে এসেছে এদেশে আগত আমাদের দেশের রক্ষণশীল মানুষেরা। কেউ কেউ এমনও প্রচার করেছে যে, একটা বিদেশি সাবানের বিনিময়েও নাকি এখানে নারীসঙ্গ উপভোগ করা যায়। নারীসঙ্গ খুব একটা দুর্লভ নয় ঠিকই, কিন্তু সেটা নেহাতই ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার, বোধহয় কোনও বিনিময়ের অপেক্ষা রাখে না।

৩৭.
আড্ডা অনেক সময় ঝামেলারও হত
মস্কোয় আমাদের আড্ডাগুলি যে সবসময় নির্দোষ হত, এমন নয়– আরও ভালো করে বলতে গেলে শুরুতে নির্দোষ হলেও অনেক সময় মদ্যপায়ীদের দৌরাত্ম্যে প্রায় ভণ্ডুল হয়ে যেত। আমার পরিচিত দু’-একজন রুশি মহিলা গোড়াতে আমাকে এই বলে সতর্কও করে দিয়েছিলেন যে, পানভোজনের আসরে রুশি ‘মুজিক’দের, অর্থাৎ মর্দগুলোকে যেন আমি বেশি প্রশ্রয় না দিই।
অবশ্য প্রশ্রয় না দিলেও বা আপ্যায়ন না করলেও এদের অনেকে যে নেশার ঝোঁকে গায়ে পড়ে নানা রকম হুজ্জোতি বাধাতে পারে, সে অভিজ্ঞতাও পরে আমার হয়েছে। একবার তো রাতের বেলায় বাড়ি ফেরার পথে ভারতপ্রেমে গদগদ এক নেশাখোর ‘মুজিক’ বাসস্টপেই যেচে এসে আলাপ করে হিড়হিড় করে তার বাড়ি টেনে নিয়ে গেল আপ্যায়ন করার জন্য। আবার এমনও হয়েছে যে, বিদেশি দেখে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় রাস্তায় ধূমপানের জন্য আমার কাছে সিগারেট চেয়ে বসেছে কোনও বিদেশি দামি ব্র্যান্ডের সিগারেটের প্রত্যাশায়, কিন্তু আমি দেশি সিগারেট বাড়িয়ে দিতে ছ্যা ছ্যা করে গালাগাল দিতে দিতে চলে গেছে।
নতুন যে পাড়ায় উঠে এলাম, সেখানে আমার পাশের ফ্ল্যাটের প্রতিবেশী ছিল একজন মহাকাশ পদার্থবিজ্ঞানী, মস্কোর কোন এক বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক। বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী তার অধীনে গবেষণা করে, এমনকী নিজেও বেশ কয়েকটা গবেষণাগ্রন্থের লেখক। সেসব বই স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাসই করতাম না। সুস্থ অবস্থায় তাকে খুব কমই দেখতাম। রুশ চরিত্রের এটাই অসঙ্গতি– কে মুজিক কে ভদ্রলোক– আচার-আচরণে অনেক সময়ই বোঝা ভার। লোকটা ভালো না মন্দ এককথায় বলা মুশকিল। দু’-একবার তার ডাকে সাড়া দিয়ে তার ঘরেও গেছি। ঘরে চোলাই মজুত। উৎসব-পার্বণ হলেই বড় বেশি বেসামাল হয়ে পড়ত। স্ত্রী তখন অনেক সময় বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র গা ঢাকা দিত।
তখনই হামলা হত আমাদের ওপর– তার ধারণা ওর স্ত্রীকে আমরা লুকিয়ে রেখেছি। একবার তো আমাদের ঘরে নাকি চরস-গাঁজার সেবন চলছে– এই মর্মে অভিযোগ করে থানা থেকে পুলিশই ডেকে এনেছিল। পুলিশ এসে সেসবের গন্ধমাত্র না পেয়ে আমাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে, ওকে ধমকধামক দিয়ে চলে গেল। দু’দিন পরে লিফটে দেখা হতে আমার সঙ্গে তখন স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা বলেছে, যেন সেদিন কিছুই হয়নি।
এই শ্রেণির লোকের সংস্পর্শে এসে এরকম ছোট-বড় অস্বস্তিকর ও অপ্রীতিকর ঘটনা প্রায়ই ঘটেছে। একবার শীতের ভরসন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার পথে মেট্রোর ট্রেনের কামরায় ঢুকতেই ভেতরে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক মাতাল হড়হড় করে আমার গায়ের ওপর তার পেটের খাবার উগড়ে দিল– মনে হল যেন আমার অপেক্ষাতেই ছিল। এদেশে এই ধরনের কাণ্ডকারখানার জন্য মাতালদের কেউ মারধর করে না, বড়জোর পুলিশ দেখতে পেলে ধরে নিয়ে যায়, থানায় আটকে রেখে জলথেরাপি করে ছেড়ে দেয়। মাতালদের ব্যাপারে ওরা বেশ সহিষ্ণু। যাত্রীরা শুধু একটু তফাত রেখে দাঁড়াল। আমার হতভম্ব ভাব দেখে একজন মহিলা দয়াপরবশ হয়ে হাত বাড়িয়ে আমার হাতের জিনিসপত্র ধরে নিয়ে একটুকরো খবরের কাগজ আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন– তাই দিয়ে যতদূর পারা যায় ওভারকোটটা সাফ করা গেল। মাতাল যথারীতি টলটলায়মান অবস্থায় দিব্যি খাড়া হয়ে রইল। শীতের রাতে বাড়ি গিয়ে ওভারকোট তো সাফ করলামই, নানা রকম লোশন দিয়ে সাফ করেও কোনওমতেই স্বচ্ছন্দ বোধ করতে পারলাম না। ওভারকোটটা শেষকালে বাতিলই করে দিতে হল।
আরেকবার, সেটা প্রথম বছরের ঘটনাই হবে, আমার তখনকার ফ্ল্যাটটা ছিল পাঁচতলা দালানের তিনতলায়, সেখানে লিফটের কোনও বালাই ছিল না। দোতলায় ওঠার মুখে এক মাতাল আমার পথ অবরোধ করে দাঁড়াতে আমি তাকে হাত দিয়ে একপাশে সরিয়ে দিতে গেছি, এমন সময় লোকটা হুড়মুড় করে গড়িয়ে সিঁড়ির চাতালে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। পড়ার সময় তার মাথাটা লোহার রেলিং-এ ঠুকে যেতে নারকেল ভাঙার মতো একটা আওয়াজ হল। আমি ঘাবড়ে গিয়ে চটপট ওপরে আমার নিজের ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়ে দরজা বন্ধ করে দিলাম। কিন্তু কিছু পরে কেমন যেন বিবেকে বাধল; লোকটার যদি কিছু হয়ে থাকে? বেঁচে আছে কি না কে জানে? একটা কিছু ব্যবস্থা করা দরকার। এই ভেবে যেই বেরিয়ে এসেছি, ওমনি দেখি লোকটা যেন কিছুই হয়নি এই ভাবে আমার ওপরের তলায় উঠে যাচ্ছে। যেন এক ধাক্কায় তার নেশা টুটে গেছে। পরে জানলাম এই বাড়িতে আমারই ওপরতলার একজন প্রতিবেশী। এই দুই অভিজ্ঞতার পর থেকে রাস্তায় ঘাটে মাতাল দেখলে আমি সাত হাত দূরে থাকি।

কিন্তু এদেশে অতিথি হয়ে এসে আমাদের দেশের ভদ্র সন্তানরা অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে যে ধরনের নোংরা ও অশালীন ব্যবহার করে থাকে, তার কোনও তুলনা নেই। একবার আমাদের দেশের খুবই নামজাদা এক যন্ত্রসংগীতশিল্পী খুব সম্ভবত ভারত উৎসবে অংশগ্রহণের জন্যই আমন্ত্রিত হয়ে দলবল নিয়ে মস্কোয় এসেছিলেন। একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমার এক বন্ধু পুরো দলটাকেই আমন্ত্রণ করে আমার বাসায় নিয়ে এলেন। কথা ছিল বাজনার আসর বসবে, কিন্তু দেখা গেল যন্ত্রপাতির কোনও বালাই নেই, সকলেই খালি হাতে এসেছে, কেবল বন্ধুটির হাতে কয়েক বোতল হুইস্কি। বাড়ির সকলে হতাশ ও বিরক্ত। ভদ্রতার খাতিরে আপ্যায়ন করতে হল। কিছুক্ষণ পরেই অতিরিক্ত পানের ফলে বিশিষ্ট যন্ত্রসংগীতশিল্পীটি নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে আমার স্ত্রীর শ্লীলতাহানির উদ্যোগ করতে আমি বাধ্য হয়ে বন্ধুকে ডেকে দলবল সমেত তাকে বিদায় করে দিলাম।
আসলে স্ত্রী-পুরুষের মেলামেশার ব্যাপারে আমাদের মতো সামাজিক সংস্কারাচ্ছন্ন দেশের লোকদের এটাই বিপদ। এদের অনেকে বিদেশে এসে অবাধ মেলামেশার সুযোগ পেয়ে মনে করে সেখানকার মেয়েরা সকলে নষ্ট চরিত্রের। রুশি মেয়েদের সম্পর্কে বিশেষভাবে এরকম ধারণাই প্রচার করে এসেছে এদেশে আগত আমাদের দেশের রক্ষণশীল মানুষেরা। কেউ কেউ এমনও প্রচার করেছে যে, একটা বিদেশি সাবানের বিনিময়েও নাকি এখানে নারীসঙ্গ উপভোগ করা যায়। নারীসঙ্গ খুব একটা দুর্লভ নয় ঠিকই, কিন্তু সেটা নেহাতই ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার, বোধহয় কোনও বিনিময়ের অপেক্ষা রাখে না। অমনিতেও পাওয়া যেতে পারে। আর বিদেশি জিনিসের প্রতি লোভ– সেটা তো অন্য প্রসঙ্গ। সে লোভ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে অধিকাংশ নাগরিকেরই ছিল। সেটা দেশের সমাজব্যবস্থার একটা বড় রকমের ত্রুটি, কিন্তু সে অন্য প্রসঙ্গ।
পেরেস্ত্রৈকার প্রথম বছরেই গর্বাচ্যোভের মদ্যপান বিরোধী প্রচারের ফলে মদ্যপায়ীরা সাময়িকভাবে বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিল। হোটেল-রেস্তোরাঁয় পর্যন্ত অ্যালকোহল দুর্লভ হয়ে পড়েছিল। সেই সময় কি উপলক্ষে ঠিক মনে নেই, কলকাতা থেকে ছেলেমেয়েদের একটি দল, সম্ভবত কোনও প্রতিযোগিতায় জয়লাভের পুরস্কার হিসেবে মস্কো সফরের সুযোগ পেয়েছিল। তাদের সঙ্গে কীভাবে কে জানে আমাদের দেশের তৎকালীন এক খ্যাতনামা প্রৌঢ় লেখককেও ভিড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। ওঁর নিজের নাকি অন্য কোনও একটা কর্মসূচি উপলক্ষে, বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের আসার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু কলকাতা থেকে কর্মকর্তারা ওঁকে বুঝিয়ে বলেছিলেন পেরেস্ত্রৈকার ডামাডোলে পড়ে কবে সেই সুযোগ আসবে বলা যায় না।
আপাতত এখানে একটা সিট খালি যাচ্ছে। অগত্যা তাতেই রাজি হতে হল। একটু ঘুরপথে তাশখন্দ হয়ে আসতে হয়েছিল। তাতে লেখক অত্যন্ত বিরক্ত; অযথা হয়রানি, তাশখন্দ বিমানবন্দরে শুল্ক দপ্তরের কর্মীরা কেন আর সকলকে ছেড়ে দিয়ে তন্নতন্ন করে তাঁর সুটকেস-হ্যান্ডব্যাগ এমনকী দেহ পর্যন্ত তল্লাশি করেছিল। লেখার মাধ্যমে ওঁকে অবশ্যই চিনতাম, কিন্তু দেশে থাকতে ওঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষ আলাপের সৌভাগ্য হয়নি। মস্কোতে ওঁর সঙ্গে দোভাষী হিসাবে স্থানীয় যে ব্যক্তিকে দেওয়া হয়েছিল, তিনি আমাদের প্রকাশনালয়েরই তামিল বিভাগের একজন ইংরেজি জানা সম্পাদক। আমার বিশেষ পরিচিতও বটে। হোটেলে উঠে প্রথম দিনের সন্ধ্যাতেই লেখকের মনমেজাজ বিগড়ে গেল। গর্বাচ্যোভের দৌরাত্ম্যে হোটেলে আপাতত মদ সরবরাহ বন্ধ, কাউন্টারে বিক্রিও বন্ধ। কলকাতায় থাকতে মস্কোয় বসবাসকারী কোনও ভারতীয়ের সঙ্গে যোগসূত্র হিসাবে এখানে পাঠরত এক বাঙালি সাহিত্যপ্রেমী ছাত্রের ফোন নাম্বার অবশ্য তিনি জোগাড় করেছিলেন। কিন্তু তালেগোলে হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁর দোভাষীও সেই ব্যক্তির হদিশ দিতে পারলেন না, শুধু বললেন এখানে বাঙালি বলতে তিনি একমাত্র আমাকেই চেনেন। অগত্যা তাঁর কাছ থেকে আমার ফোন নম্বর নিয়ে তিনি আমাকেই ফোন করলেন, নিজের পরিচয় দিয়ে আমার কাছ থেকে সেই সাহিত্যপ্রেমীটির ফোন নম্বর জানতে চাইলেন। আমার কাছে তখন ওর ফোন নম্বর ছিল না। এবারে তিনি তাঁর আসল সমস্যাটা আমাকে খুলে বললেন: কলকাতায় সন্ধ্যার সময়টাতে তিনি রোজই দু’-এক পেগ হুইস্কি সেবন করে থাকেন, কিন্তু এখানে সেসবের কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না– আমি এই ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করতে পারি কি না।
আমি আমার অপারগতার কথা জানাতে তিনি আর কথা না বাড়িতে কতকটা বিরক্ত হয়েই ফোন ছেড়ে দিলেন।
পরদিন ভারত উৎসব উপলক্ষে মস্কোর ভারতীয় দূতাবাসে রবিশঙ্করের বাজনার একটা অনুষ্ঠান ছিল। লেখকও সেখানে উপস্থিত। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হল। তিনি যার সন্ধান করছিলেন, সৌভাগ্যবশত সেও সেখানে উপস্থিত। তাঁকে দেখে লেখকের বোধহয় ধড়ে প্রাণ এল।
যা হোক, দিন দুয়েক বাদে ওই সাহিত্যপ্রেমীর উদ্যোগেই কোনও এক বাড়ির, একটি ফ্ল্যাটে লেখককে নিয়ে একটি সাহিত্যবাসরের আয়োজন করা হয়েছিল। আমাদের মতো স্থানীয় বাঙালিরা অনেকেই আমন্ত্রিত হয়েছিল। অনেকেরই আশা ছিল লেখকের কাছ থেকে সাহিত্য সম্পর্কে দু’-চারকথা শোনা যাবে। যথারীতি পানভোজনের ব্যবস্থা ছিল। রান্নার ভার আমার ওপর ছিল।
এককালে বামপন্থী ছিলেন, বামপন্থী পত্রপত্রিকায় লিখেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন, বেশ কিছুকাল হল অবশ্য একালের আরও অনেক বামপন্থী কবি সাহিত্যিক বা বুদ্ধিজীবীর মতো তিনিও বামপন্থা থেকে সরে এসেছিলেন। অন্তত তাঁর সেই সরে আসার নেপথ্য কাহিনিও শুনতে পাব– এমন একটা ক্ষীণ আশাও মনে ছিল। কিন্তু হা হতোস্মি! দু’-এক পেগ পেটে পড়তেই তিনি উল্টোপাল্টা বকতে শুরু করে দিলেন। গোর্কি সম্পর্কে দু’-চার কথা বলতে গিয়ে সব গুলিয়ে ফেললেন। অবশ্য বাঁচোয়া এই যে যারা উপস্থিত ছিলে, তাদের অনেকেই গোর্কির ওই সব লেখার একটাও পড়া তো দূরের কথা, এমনকী নাম পর্যন্ত শোনেনি। এরপর কী কথায় কী কথায় যেন ‘ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ’ বলে উদ্বাহু হয়ে এক পাক নেচেও নিলেন। তিনি এদেশের সাধারণ মানুষের তাঁদের নিজেদের দেশের শিল্পী সাহিত্যিকদের সম্পর্কে অজ্ঞতার দৃষ্টান্ত হিসেবে বললেন; “এরা ‘ডস্টায়ভোস্কি’ নাম পর্যন্ত শোনেনি, আমি আমার দোভাষীর কাছে ‘ডস্টায়ভোস্কির মিউজিয়াম’ কোথায় জানতে চাইলে তিনি হাঁ করে আমার দিকে চেয়ে রইলেন”। তাঁর কথা শুনে উপস্থিত সকলে তো থ। আমি প্রতিবাদ করে বললাম, ‘ডস্টায়ভোক্সি নয়– দস্তইয়েভ্স্কি– ওরকম ভুল উচ্চারণে তাঁর নাম করলে কোনও রুশির সাধ্য নেই তাঁকে শনাক্ত করে’। তাতে তিনি কেন যেন তেড়েফুঁড়ে এসে আমার গলা টিপে ধরলেন।
আমি কোনওমতে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এক পাশে তাঁকে সোফার ওপর শুইয়ে দিলাম। সেই যে শুলেন, তারপর গভীর ঘুমেই ঢুলে পড়লেন, আর তাঁকে চাঙ্গা করে তোলা গেল না। বলাই বাহুল্য, খাদ্য ও পানীয়ের আমরাই সদ্ব্যবহার করলাম। লেখককে কোনওমতে গাড়িতে তুলে হোটেলে দিয়ে আসা হল।
…পড়ুন রুশকথা-র অন্যান্য পর্ব…
পর্ব ৩৬। মস্কোর ঠান্ডায় লঙ্কা গাছ দেখে পি.সি. সরকার বলেছিলেন, ‘এর চেয়ে বড় ম্যাজিক হয় নাকি?’
পর্ব ৩৫। রুশদের কাছে ভারত ছিল রবীন্দ্রনাথের দেশ, হিমালয়ের দেশ
পর্ব ৩৪। সোভিয়েত শিক্ষায় নতুন মানুষ গড়ে তোলার ব্যাপারে একটা খামতি থেকে গিয়েছিল
পর্ব ৩৩। দিব্যি ছিলাম হাসপাতালে
পর্ব ৩২। মস্কোর স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে সাধারণ ডাক্তাররা অধিকাংশই মহিলা ছিলেন
পর্ব ৩১। আমার স্ত্রী ও দুই কন্যা নিজভূমে পরবাসী হয়ে গিয়েছিল শুধু আমার জন্য
পর্ব ৩০। শান্তিদা কান্ত রায়ের প্রিয় কাজ ছিল মস্কোয় ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের কমিউনিজম পড়ানো
পর্ব ২৯। পেরেস্ত্রৈকার শুরু থেকেই নিরাপত্তার অভাব বোধ করছিলেন গোপেনদা
পর্ব ২৮। দেশে ফেরার সময় সুরার ছবি সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি পাননি গোপেনদা
পর্ব ২৭। বিপ্লবের ভাঙা হাট ও একজন ভগ্নহৃদয় বিপ্লবী
পর্ব ২৬। ননী ভৌমিকের মস্কোর জীবনযাত্রা যেন দস্তইয়েভস্কির কোনও উপন্যাস
পর্ব ২৫। ননীদা বলেছিলেন, ডাল চচ্চড়ি না খেলে ‘ধুলোমাটি’র মতো উপন্যাস লেখা যায় না
পর্ব ২৪। মস্কোয় শেষের বছর দশেক ননীদা ছিলেন একেবারে নিঃসঙ্গ
পর্ব ২৩। শেষমেশ মস্কো রওনা দিলাম একটি মাত্র সুটকেস সম্বল করে
পর্ব ২২। ‘প্রগতি’-তে বইপুথি নির্বাচনের ব্যাপারে আমার সঙ্গে প্রায়ই খিটিমিটি বেধে যেত
পর্ব ২১। সোভিয়েতে অনুবাদকরা যে পরিমাণ অর্থ উপার্জন করত, সে দেশের কম মানুষই তা পারত
পর্ব ২০। প্রগতি-র বাংলা বিভাগে নিয়োগের ক্ষেত্রে ননীদাই শেষ কথা ছিলেন
পর্ব ১৯। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নাকি খুব ভালো রুশভাষা জানতেন, প্রমথনাথ বিশী সাক্ষী
পর্ব ১৮। লেডি রাণু মুখার্জিকে বাড়ি গিয়ে রুশ ভাষা শেখানোর দায়িত্ব পড়েছিল আমার ওপর
পর্ব ১৭। একদিন হঠাৎ সুভাষদা আমাদের বাড়ি এসে উপস্থিত ফয়েজ আহমেদ ফয়েজকে নিয়ে
পর্ব ১৬। মুখের সেই পরিচিত হাসিটা না থাকলে কীসের সুভাষ মুখোপাধ্যায়!
পর্ব ১৫। রুশ ভাষা থেকেই সকলে অনুবাদ করতেন, এটা মিথ
পর্ব ১৪। মস্কোয় ননীদাকে দেখে মনে হয়েছিল কোনও বিদেশি, ভারতীয় নয়
পর্ব ১৩। যিনি কিংবদন্তি লেখক হতে পারতেন, তিনি হয়ে গেলেন কিংবদন্তি অনুবাদক
পর্ব ১২। ‘প্রগতি’ ও ‘রাদুগা’র অধঃপতনের বীজ কি গঠনপ্রকৃতির মধ্যেই নিহিত ছিল?
পর্ব ১১। সমর সেনকে দিয়ে কি রুশ কাব্যসংকলন অনুবাদ করানো যেত না?
পর্ব ১০। সমর সেনের মহুয়ার দেশ থেকে সোভিয়েত দেশে যাত্রা
পর্ব ৯। মস্কোয় অনুবাদচর্চার যখন রমরমা, ঠিক তখনই ঘটে গেল আকস্মিক অঘটন
পর্ব ৮: একজন কথা রেখেছিলেন, কিন্তু অনেকেই রাখেননি
পর্ব ৭: লেনিনকে তাঁর নিজের দেশের অনেকে ‘জার্মান চর’ বলেও অভিহিত করত
পর্ব ৬: যে-পতাকা বিজয়গর্বে রাইখস্টাগের মাথায় উড়েছিল, তা আজ ক্রেমলিনের মাথা থেকে নামানো হবে
পর্ব ৫: কোনটা বিপ্লব, কোনটা অভ্যুত্থান– দেশের মানুষ আজও তা স্থির করতে পারছে না
পর্ব ৪: আমার সাদা-কালোর স্বপ্নের মধ্যে ছিল সোভিয়েত দেশ
পর্ব ৩: ক্রেমলিনে যে বছর লেনিনের মূর্তি স্থাপিত হয়, সে বছরই ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙার সূচনাকাল
পর্ব ২: যে দেশে সূর্য অস্ত যায় না– আজও যায় না
পর্ব ১: এক প্রত্যক্ষদর্শীর চোখে রাশিয়ার খণ্ডচিত্র ও অতীতে উঁকিঝুঁকি
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
