
টুওয়ার্ডস ইক্যুয়ালিটি রিপোর্ট প্রকাশের পর কেটে গিয়েছে অর্ধশতক। দেশের শহরাঞ্চলে ২০০৪-০৫ থেকে ২০১৯-২০’র মধ্যে মহিলাদের শ্রমের বাজারে যোগদানের হার রয়ে গিয়েছে একই জায়গায়, ১৭ শতাংশের আশপাশে। উন্নত দেশগুলির তুলনায় তো বটেই, উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যেও এ দেশের মহিলাদের কর্মনিযুক্তির হার শোচনীয়। এর কারণ খুঁজতে অনেক গবেষণাই হয়েছে, তবে পরিবারের অন্দরে গৃহকাজে শ্রমের অসম বণ্টনের কথা বলেছেন বেশির ভাগ গবেষক। শুধু অসংগঠিত ক্ষেত্রে নয়, সংগঠিত ক্ষেত্রেও রয়ে গিয়েছে মজুরির অসাম্য। কাজের বাজারে লিঙ্গ সাম্যের কারণ বুঝতে, এবং তা কমানোর লক্ষ্যে ঠিকঠাক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে আজও বার বার ফিরে যাওয়া দরকার টুওয়ার্ডস ইক্যুয়ালিটি রিপোর্টে।



শেষ পর্ব
১৯৭৫ সালকে ‘আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ’ হিসাবে ঘোষণা করে রাষ্ট্রপুঞ্জ। সেই প্রেক্ষিতে ভারত সরকার দেশের মহিলাদের অবস্থা সম্পর্কে জানতে একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটিতে ছিলেন ফুলরেণু গুহ, মণিবেন কারা, সাবিত্রী শ্যাম, নীরা ডোগরা, বিক্রম মহাজন, লীলা দুবে, সাকিনা হাসান, ঊর্মিলা হাকসর, লতিকা সরকার এবং বীণা মজুমদার। এই কমিটি ১৯৭৪ সালে জমা দেয় ৪০০ পাতার একটি প্রতিবেদন, যার নাম ‘টুওয়ার্ডস ইক্যুয়ালিটি রিপোর্ট’।
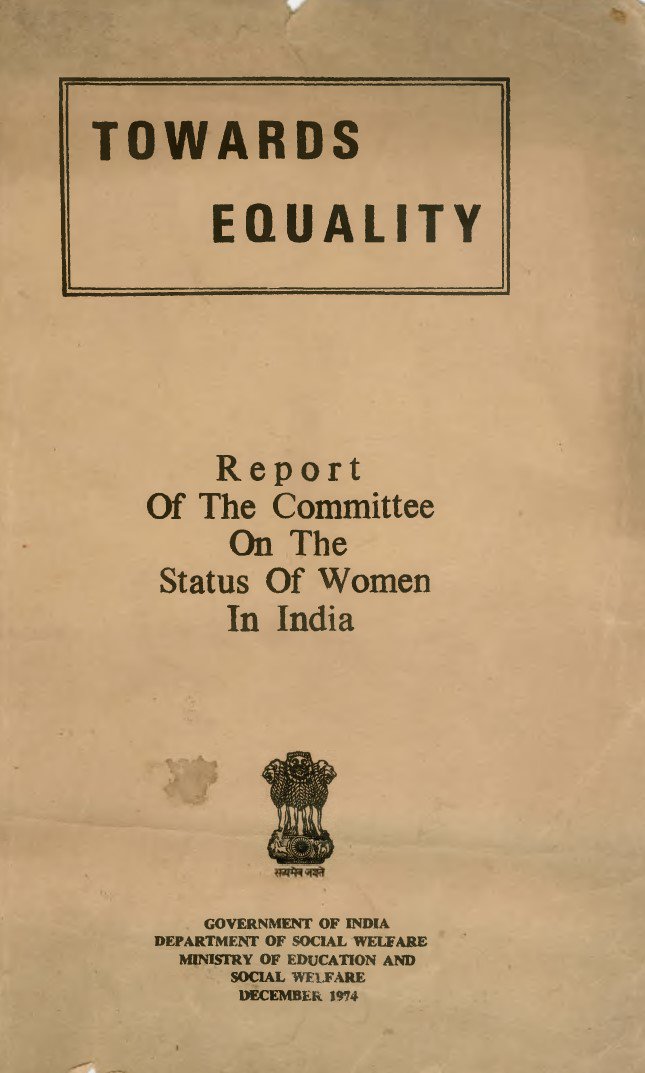
সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং আইনব্যবস্থায় মেয়েদের অবস্থান আলোচনা করে রিপোর্টটি দেখায় সংবিধানে নারী-পুরুষের যে সমানাধিকারের কথা বলা হয়েছে, বাস্তবে তা অধরাই রয়ে গিয়েছে দেশের মেয়েদের কাছে। তথ্যের বিস্তার এবং বিশ্লেষণের গভীরতার নিরিখে এই রিপোর্টটি নজিরবিহীন। স্বাধীনতার পরে উন্নয়নের যে ধারা বেছে নিয়েছিলেন দেশের নীতি-নির্ধারকেরা তা যে লিঙ্গসাম্যের বিষয়টিকে সম্পূর্ণ রূপে অবজ্ঞা করেছে, এই রিপোর্টটি সেকথা তুলে ধরেছিল। বিশ্বজুড়ে নারীবাদী আন্দোলনের দ্বিতীয় তরঙ্গ চলছে তখন। এ দেশে নারী-আন্দোলনের যাত্রাপথেও রিপোর্টটি একটি মাইলফলক। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নীতি প্রণয়ন এবং নারীবাদী তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রেই শুধু এর গুরুত্ব নয়। ‘টুওয়ার্ডস ইক্যুয়ালিটি রিপোর্ট’ ভারতীয় গণতন্ত্রে লিঙ্গসাম্যের আলোচনাকে প্রথম একটি প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা দেয়।
উত্তর-ঔপনিবেশিক আমলের প্রথম আড়াই দশকে যে মেয়েরা সংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করতেন, আমাদের এই গবেষণা তাঁদের নিয়ে। টুওয়ার্ডস ইক্যুয়ালিটি রিপোর্টে তাঁদের ‘সার্ভিসেস অ্যান্ড প্রফেশনস’-এর আওতাভুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, পরিষেবা ক্ষেত্রের কর্মী এবং পেশাদার। আরও ভেঙে বললে, এঁদের মধ্যে ছিলেন প্রযুক্তিক্ষেত্রের কর্মী, শিক্ষিকা, প্রশাসক এবং ম্যানেজার, কেরানি, সেলসগার্ল, পরিবহণ ক্ষেত্রের কর্মী, ক্রীড়াক্ষেত্রের কর্মী, আর অদক্ষ অফিস-কর্মী।
রিপোর্টে বলা হয়েছে, স্বাধীনতার আগে, সার্ভিসেস অ্যান্ড প্রফেশনসের আওতাভুক্ত বেশিরভাগ মেয়েই কাজ করতেন শিক্ষা বা স্বাস্থ্যক্ষেত্রে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে শিক্ষিত মেয়েদের একটা ছোট, কিন্তু লক্ষণীয় অংশ কাজ পান সওদাগরি অফিসের ক্লার্ক বা সেক্রেটারি হিসাবে। স্বাধীনতার পর শিক্ষিত মেয়েদের জন্য সংগঠিত ক্ষেত্রের অন্যান্য নানা কাজের সিংহদুয়ার আস্তে আস্তে খুলতে শুরু করে। এর কারণ হিসাবে রিপোর্টের লেখকেরা চিহ্নিত করেছেন সে সময়ের সমাজ, রাজনীতি এবং অর্থনীতির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনকে। প্রথম, দেশের সংবিধানে ভেদাভেদহীনতা এবং সুযোগের সাম্যের গ্যারান্টি বা নিশ্চয়তা। দ্বিতীয়, শিক্ষায় মেয়েদের অগ্রগতি। তৃতীয়, মূল্যবৃদ্ধির কারণে শহুরে মধ্যবিত্ত পরিবারে বাড়তি রোজগারের প্রয়োজন এবং মেয়েদের বাইরে কাজ করা সম্পর্কে মানসিকতায় বদল। চতুর্থ, নতুন দেশে উন্নয়নের নানা প্রকল্পের ফলে পরিষেবা ও পেশাদারি ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ তৈরি হওয়া।

কমিটির মতে, স্বাধীন দেশে গোড়া থেকেই সরকারি চাকরির পরীক্ষায় মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামেন। কয়েক জন মেয়ে যখন সেইসব পরীক্ষায় সফল হয়ে সেকালের নারীবর্জিত অফিসে প্রথম পা রাখলেন, আস্তে আস্তে অন্যরাও প্রেরণা পেলেন। একটু একটু করে ভাঙতে লাগল মেয়েদের কাজ আর ছেলেদের কাজের ধারণা। টুওয়ার্ডস ইক্যুয়ালিটি রিপোর্টের গবেষণা দেখিয়েছে, কীভাবে মেয়েদের কাজ সম্পর্কে পুরুষ সরকারী কর্মচারীদের মানসিকতা বদলাতে শুরু করে। মধ্যবিত্ত পরিবারে মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোয় আগ্রহও বাড়তে থাকে একই কারণে।
তবে প্রমীলা কাপুরের মতো তৎকালীন গবেষকদের মতে– সামাজিক কারণের চেয়ে ঢের বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে অর্থনৈতিক কারণগুলি। সে সময়ে বাজার ছিল আগুন। শিক্ষা এবং বাসস্থানের খরচ বাড়ছিল। বাড়ির ছেলেরাও চাকরি পাচ্ছিলেন না। এমতাবস্থায় মেয়েদের চাকরির প্রয়োজন অস্বীকার করার মতো অবস্থায় ছিল না শহরের বহু পরিবার। আরেকটু সচ্ছলভাবে জীবন কাটানোর বাসনাও ছিল অনেকের।
১৯৭২ সালে ‘শ্রীরাম সেন্টার অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস’-এর একটি গবেষণা দেখায় সে যুগের মেয়েরা কেন বাইরে কাজ করতে বেরিয়েছেন জানতে চাইলে চাকুরিরতারা প্রায় সকলেই সব চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন পরিবারের আর্থিক প্রয়োজনের উপরে। তাঁরা বলেছেন ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা আর পুষ্টির পিছনে খরচ হয় তাঁদের রোজগার। এছাড়া, ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করাও সম্ভব হচ্ছে তাঁদের চাকরির ফলে। চাকুরিরতারা সব চেয়ে কম গুরুত্ব দিয়েছেন নিজেদের শখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপরে। জানিয়েছেন, আসবাবপত্র বা গৃহকর্ম সহজ করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কিনেছেন তাঁরা নিজেদের রোজগারের টাকা জমিয়ে। আমরা যাঁদের সঙ্গে কথা বলেছি গবেষণার সূত্রে, তাঁরাও অনেকে বলেছেন রোজগারের টাকায় ফ্রিজ বা প্রেশার কুকার কিনেছেন, যাতে সংসারোর কাজ সারতে একটু সুবিধা হয়। সে কথা আমরা আলোচনা করেছি আগের এক কিস্তিতে।
/shethepeople/media/media_files/2025/08/14/1950s-post-independence-india-2025-08-14-13-25-40.png)
টুওয়ার্ডস ইক্যুয়ালিটির লেখকেরা জানিয়েছেন তাঁদের সমীক্ষায় অর্থনৈতিক প্রয়োজনের কথা উঠে এসেছে প্রবলভাবে। শহর ও গ্রামের মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরা বার বার বলেছেন উপযুক্ত কাজ পেলেই করবেন, না হলে পরিবারের সকলের দু’বেলার অন্নসংস্থান করাই দায় হয়ে উঠবে এর পর। লক্ষণীয়, রিপোর্টে পশ্চিমবঙ্গকে বলা হচ্ছে, মেয়েদের কাজ সম্পর্কে মনোভাবের ক্ষেত্রে সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা অঞ্চল। সেই পশ্চিমবঙ্গেও মধ্যবিত্ত পরিবারের বয়স্ক মহিলারা বলেছেন, বাড়ির মেয়ে-বউরা চাকরি না পেলে বয়স্ক ও শিশুদের অভাবে পড়তে হবে সব চেয়ে বেশি।
রিপোর্টের জন্য করা সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল, পুরুষ এবং মহিলাদের প্রায় অর্ধেক মনে করেন ছেলেরা যে, কাজ করতে পারে, মেয়েরাও তা পারে এবং ৮৭ শতাংশ বলেছেন, একই কাজের জন্য সমান পারিশ্রমিক পাওয়া উচিত ছেলে এবং মেয়েদের। উত্তরদাতাদের ৫০ শতাংশ অবশ্য মনে করতেন যে, মেয়েদের কাজের উপযুক্ত পরিবেশ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নেই। বাড়ির মেয়েদের পড়াচ্ছেন কেন জানতে চাইলে অনেকেই বলেছেন, ভবিষ্যতে স্বামী না দেখলে বা মারা গেলে হঠাৎ বিপদে পড়তে হবে চাকরি করার যোগ্যতা না থাকলে। যৌথ পরিবার ভেঙে যাওয়ার কারণে গ্রামের জমিজমা থেকে আসা আয় কমে যাওয়ার কথা জানিয়েছিল শহুরে অনেক পরিবার। অবিবাহিত, বিবাহবিচ্ছিন্ন বা বিধবা মেয়েদেরও নিজের অন্নসংস্থান নিজেকেই করতে হত।
আমরা আগের লেখাগুলিতে দেখিয়েছি, মেয়েদের চাকরি সম্পর্কে সে যুগে একটি অন্যতম আপত্তির কারণ ছিল, মেয়েরা চাকরি করলে ছেলেরা কাজ পাবে না। রিপোর্টের লেখকেরা বলছেন এই যুক্তি যাঁরা দিচ্ছেন, তাঁরা যেন ধরেই নিচ্ছেন মেয়েরা চাকরি করেন পরিবারের বাড়তি রোজগারের জন্য। অথচ কত মহিলার সঙ্গে তাঁরা কথা বলেছেন, যাঁদের রোজগারেই সংসার চলে। বয়স্ক মা-বাবা, ছোট ভাই-বোন বা সন্তানের গ্রাসাচ্ছদনের পুরো দায়িত্বই ছিল এই মেয়েদের কাঁধে। সমীক্ষায় দেখা মিলেছিল কয়েক জন বিবাহিত মহিলার, যাঁরা বিয়ের পরেও বাপের বাড়ির সংসারে বাবা-মা-ভাইবোনদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। রিপোর্টের লেখকেরা তাঁদের সাহসকে কুর্নিশ জানিয়েছেন, কারণ শ্বশুরবাড়ির আপত্তি এবং গভীর সামাজিক বাধার মোকাবিলা করে এই দায়িত্ব পালন করতেন তাঁরা। বিয়ের পরে মেয়ের রোজগারে অধিকার হারাতে হবে– এই ভয়ে সে সময়ে বহু শহুরে পরিবার মেয়েদের বিয়ে দিতে চাইত না। সেই সব নীতাদের গল্প আমরা সে যুগের সিনেমা-সাহিত্যে অনেক পেয়েছি। টুওয়ার্ডস ইক্যুয়ালিটি উল্লেখ করেছে, ১৯৭৩ সালের ১১ মে’র সানডে ওয়ার্ল্ডে শান্তি সীতারমণের একটি প্রবন্ধের কথা। শান্তি কথা বলেছিলেন এক মহিলা টেলিফোন অপারেটরের সঙ্গে। তিনি বলেছিলেন, ‘মা বাবা যখন এই কাজে আমাকে পাঠিয়েছিলেন, বলেছিলেন কয়েক মাস চাকরি করতে, তার পর আমার বিয়ে দেবেন। কিন্তু বহু মাস কেটে গিয়েছে। আমার বিয়ে হলে সংসার চালানোর টাকা কমে যাবে, তাই সানাই আর বাজল না।’
………………………
টুওয়ার্ডস ইক্যুয়ালিটি রিপোর্ট প্রকাশের পর কেটে গিয়েছে অর্ধশতক। দেশের শহরাঞ্চলে ২০০৪-০৫ থেকে ২০১৯-২০’র মধ্যে মহিলাদের শ্রমের বাজারে যোগদানের হার রয়ে গিয়েছে একই জায়গায়, ১৭ শতাংশের আশপাশে। উন্নত দেশগুলির তুলনায় তো বটেই, উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যেও এ দেশের মহিলাদের কর্মনিযুক্তির হার শোচনীয়। এর কারণ খুঁজতে অনেক গবেষণাই হয়েছে, তবে পরিবারের অন্দরে গৃহকাজে শ্রমের অসম বণ্টনের কথা বলেছেন বেশির ভাগ গবেষক। শুধু অসংগঠিত ক্ষেত্রে নয়, সংগঠিত ক্ষেত্রেও রয়ে গিয়েছে মজুরির অসাম্য। কাজের বাজারে লিঙ্গ সাম্যের কারণ বুঝতে, এবং তা কমানোর লক্ষ্যে ঠিকঠাক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে আজও বার বার ফিরে যাওয়া দরকার টুওয়ার্ডস ইক্যুয়ালিটি রিপোর্টে।
………………………
রিপোর্টে দেখানো হয়েছিল, গত শতাব্দীর ছয়ের দশকে সরকারি অফিসে এবং স্কুলে মেয়ে-কর্মীদের সংখ্যা বাড়লেও সমস্ত কর্মীর শতাংশ হিসাবে মেয়েদের যোগদানের হার মোটামুটিভাবে একই থেকে গিয়েছিল (তিন শতাংশের আশপাশে)। বেসরকারি ক্ষেত্রে কেরানিগিরি আর শিক্ষকতায় মেয়েদের যোগদান বেড়েছিল মোট সংখ্যা এবং শতাংশ, দুইয়ের নিরিখেই। ম্যানেজার বা প্রশাসক হিসাবে কাজ করতেন উচ্চবিত্ত সমাজের উচ্চশিক্ষিত মেয়েরা। টুওয়ার্ডস ইক্যুয়ালিটি রিপোর্ট উল্লেখ করেছে সে যুগে উচ্চপদে আসীন কয়েকটি মেয়ের কথা। যেমন ‘দ্য ইন্ডিয়া হোটেলস প্রাইভেট লিমিটেড’-এর এক জন সেলস ম্যানেজার ও মার্কেটিং ম্যানেজার, ‘হিন্দুস্থান মিল্ক ফুডস’-এর এক জন প্রোডাক্ট ম্যানেজার, ‘ইন্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানি লিমিটেড’-এর কর বিভাগের শীর্ষস্থানের এক জন অ্যাকাউন্টেন্ট এবং মানবসম্পদ বিভাগের গবেষণা শাখার প্রধান এক মহিলা। আমাদের গবেষণার সূত্রে জেনেছি– ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স অ্যাকাডেমির প্রধান সন্ধ্যা মিত্রের কথা, তাঁর ননদ স্মৃতি দাসের কাছে। কথা বলেছি, ব্যাঙ্ক অব বরোদার উচ্চপদস্থ কর্মী ছায়া সেনের সঙ্গে।
টুওয়ার্ডস ইক্যুয়ালিটি রিপোর্ট প্রকাশের পর কেটে গিয়েছে অর্ধশতক। দেশের শহরাঞ্চলে ২০০৪-’০৫ থেকে ২০১৯-’২০-র মধ্যে মহিলাদের শ্রমের বাজারে যোগদানের হার রয়ে গিয়েছে একই জায়গায়, ১৭ শতাংশের আশপাশে। উন্নত দেশগুলির তুলনায় তো বটেই, উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যেও এ দেশের মহিলাদের কর্মনিযুক্তির হার শোচনীয়। এর কারণ খুঁজতে অনেক গবেষণাই হয়েছে, তবে পরিবারের অন্দরে গৃহকাজে শ্রমের অসম বণ্টনের কথা বলেছেন বেশির ভাগ গবেষক। শুধু অসংগঠিত ক্ষেত্রে নয়, সংগঠিত ক্ষেত্রেও রয়ে গিয়েছে মজুরির অসাম্য। কাজের বাজারে লিঙ্গ সাম্যের কারণ বুঝতে, এবং তা কমানোর লক্ষ্যে ঠিকঠাক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে আজও বার বার ফিরে যাওয়া দরকার টুওয়ার্ডস ইক্যুয়ালিটি রিপোর্টে।
আমাদের এই সিরিজটি এখানেই শেষ হল। পূর্বমাতৃকাদের জীবন, ঘরে বাইরে তাঁদের লড়াই– সময়ের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে, পরিবারের সঙ্গে, তাঁদের চলার পথের চড়াই উতরাই খানিকটা অনুভব করার চেষ্টা করলাম। শুনলাম তাঁদের কাহিনি, কখনও তাঁদের নিজেদের মুখ থেকে, কখনও সে যুগের সিনেমা, সাহিত্য, খবরের কাগজ থেকে। ঘরে, যাত্রাপথে, কর্মক্ষেত্রে তাঁরা পাশে পেয়েছিলেন কাকে, কীসে আরও কঠিন হয়ে উঠেছিল লড়াই– দেখলাম তাঁদের দিনযাপনের চলচ্ছবি। নতুন যুগ, নতুন সময়, বদলে যাওয়া প্রযুক্তি আর ঘর-বাইরের সমীকরণ আজ ফিরে দেখে মনে হল পাথরে পাথরে রেখে যাওয়া তাঁদের চরণচিহ্ন ধরেই এগিয়ে চলেছি আমরা। মেয়েদের পথ আজও বন্ধুর। পৃথিবী জুড়ে দক্ষিণপন্থী রাজনীতির উত্থানের সঙ্গে লিঙ্গসাম্যের প্রশ্নে মনুষ্যজাতি এক পা এগোলে, দু’পা পিছোচ্ছে। পূর্বমাতৃকাদের প্রতি দায়বদ্ধ থেকেই আমাদের হেঁটে যেতে হবে পথের শেষ পর্যন্ত।
… পড়ুন চৌকাঠ পেরিয়ে কলামের অন্যান্য পর্ব …
পর্ব ২৭: রোজগারে কার অধিকার– প্রথম যুগের চাকুরিরতা মেয়েদের থেকে শুরু হয়ে আজও বহাল সেই বিতর্ক
পর্ব ২৬: বিজ্ঞাপনে উপার্জনক্ষম পাত্রীর খোঁজ পাওয়া যায় ১৯৫০ সাল থেকেই
পর্ব ২৫: রান্নাঘরে প্রযুক্তির দৌলতে চাকুরিরতা মেয়েরা সময়কে বাগে আনতে পেরেছিলেন
পর্ব ২৪: চাকরিরতা মায়েদের সুবিধার্থে তৈরি সন্তান পরিচর্যার ক্রেশ কলকাতায় বন্ধ হয়েছে বারবারই
পর্ব ২৩: ‘কে তুমি নন্দিনী’র মধ্যে কি লুকিয়েছিল চাকরিরতা মেয়েদের প্রতি সস্তা রসিকতা?
পর্ব ২২: প্রথম যুগের মেয়েরা কি আদৌ চাকরিতে স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছিলেন?
পর্ব ২১: উদ্বাস্তু, শিক্ষক বা খাদ্য আন্দোলনে চাকুরিরতা মেয়েদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো
পর্ব ২০: অদক্ষ হলেও চলবে, কিন্তু মেয়েলি বৈশিষ্ট্য না থাকলে চাকরি পাওয়া ছিল দুষ্কর!
পর্ব ১৯: শৌচাগার নেই, এই অজুহাতে মেয়েদের চাকরি দেয়নি বহু সংস্থা
পর্ব ১৮: অফিসে মেয়েদের সখ্যকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নিছক পরনিন্দা-পরচর্চার ক্ষেত্র মনে করেছিল
পর্ব ১৭: পুরুষ সহকর্মীদের ‘বন্ধু’ ভাবতে অস্বস্তি হত পাঁচ ও ছয়ের দশকের চাকুরিরতাদের
পর্ব ১৬: ট্রামের স্বস্তি না বাসের গতি, মেয়েদের কোন যান ছিল পছন্দসই?
পর্ব ১৫: অনাকাঙ্ক্ষিত স্পর্শই শুধু নয়, চৌকাঠ পেরনো মেয়েরা পেয়েছিল বন্ধুত্বের আশাতীত নৈকট্যও
পর্ব ১৪: লীলা মজুমদারও লেডিজ সিট তুলে দেওয়ার পক্ষে ছিলেন!
পর্ব ১৩: অল্পবয়সি উদ্বাস্তু মহিলারা দেহব্যবসায় নেমে কলোনির নাম ডোবাচ্ছে, বলতেন উদ্বাস্তু যুবকরা
পর্ব ১২: মৃণাল সেনের ‘ইন্টারভিউ’ ছবির মিঠুর মতো অনেকে উদ্বাস্তু মেয়েই চাকরি পেয়েছিল দুধের ডিপোতে
পর্ব ১১: প্রথম মহিলা ব্যাঙ্ককর্মীর চাকরির শতবর্ষে ব্যাঙ্কের শ্রমবিভাজন কি বদলে গিয়েছে?
পর্ব ১০: সেলসগার্লের চাকরিতে মেয়েরা কীভাবে সাজবে, কতটা সাজবে, তা বহু ক্ষেত্রেই ঠিক করত মালিকপক্ষ
পর্ব ৯: স্বল্পখ্যাত কিংবা পারিবারিক পত্রিকা ছাড়া মহিলা সাংবাদিকরা ব্রাত্য ছিলেন দীর্ঘকাল
পর্ব ৮: অভিভাবকহীন উদ্বাস্তু মেয়েদের ‘চিরকালীন বোঝা’র তকমা দিয়েছিল সরকার
পর্ব ৭: মেয়েদের স্কুলের চাকরি প্রতিযোগিতা বেড়েছিল উদ্বাস্তুরা এদেশে আসার পর
পর্ব ৬: স্বাধীনতার পর মহিলা পুলিশকে কেরানি হিসাবেই দেখা হত, সেই পরিস্থিতি কি আজ বদলেছে?
পর্ব ৫: প্রেম-বিবাহের গড়পড়তা কল্পকাহিনি নয়, বাস্তবের লেডি ডাক্তাররা স্বাধীনতার নিজস্ব ছন্দ পেয়েছিলেন
পর্ব ৪ : নার্সের ছদ্মবেশে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কেও যৌন হেনস্তার কবলে পড়তে হয়েছিল
পর্ব ৩ : উদ্বাস্তু মেয়েদের রোজগারের সুযোগ মিলেছিল টাইপ-শর্টহ্যান্ডের কাজে
পর্ব ২ : পিতৃতন্ত্রের কাঠামোয় কিছু ফাটল নিশ্চয়ই ধরিয়েছিলেন সে যুগের মহিলা টেলিফোন অপারেটররা
পর্ব ১ : দেশভাগের পর ‘চঞ্চল চক্ষুময়’ অফিসে চাকুরিরত মেয়েরা কীভাবে মানিয়ে নিলেন?
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
