
বাঙালদের ডাল বড় প্রিয়। মাছের চেয়েও ডালের খাতির বেশি ছিল। কারণ পূর্ববাংলায় মাছ খুব সহজলভ্য, বরং ডাল পাওয়া যেত না। কেবলমাত্র খেসারি ডালের ফলন ছিল কিছু। ডালের চাষ হত– বিহার, উত্তরপ্রদেশ আর পাঞ্জাবে। সেই ডাল পদ্মার ওপারে খুব কম পাওয়া যেত। এ কারণে ডালের সম্মানই ছিল আলাদা। কিছু বিশেষ ধরনের অতিথিকে দু’রকমের ডাল খাওয়ালে আপ্যায়নটা ভালো হয়েছে বলা যেত।
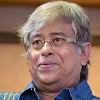
২৬.
আমিও বালক ছিলাম। অতিথি এলে সদ্যবিবাহিতার শুভদৃষ্টির মতো লজ্জা অথচ লোভদৃষ্টিতে অতিথির সামনে রাখা খাবার প্লেটের দিকে তাকাতাম, আর অপেক্ষা করতাম অতিথি কখন বলবে, ‘এসো বাছা, এই দানাদারটা ধরো।’ বড়দের বলা ছিল অতিথিকে খাবার দিলে সামনে যাবি না কিন্তু। কিন্তু ও যে মানে না মানা। এই আইন অমান্যর জন্য মা-জেঠিমারা যে খুব কঠিন সাজা দিতেন বা বকাবকি করতেন, তেমনও নয়। বোধ হয় ‘এরকম তো হয়েই থাকে’ তত্ত্বে আস্থা ছিল।
অতিথিদেরও শ্রেণিভেদ ছিল। রসগোল্লাদি মিষ্টি সমন্বিত প্লেট দেওয়া হত বেয়াই-জাতীয় আত্মীয়দের, আর টাকাপয়সা পাবেন, তাগাদা দিতে আসা এমন কিংবা বাবা-কাকাদের কর্মক্ষেত্রের উচ্চপদস্ত ব্যক্তিকে। বাড়ির বিবাহযোগ্যা মেয়েকে দেখতে আসা পাত্রপক্ষের লোকজন ছিল অতিথি নম্বর ওয়ান! প্লেট ভরা খাবার থাকত তাদের জন্য। প্লেট ভরানোর জন্য নানারকম ফিকির-ফন্দি ছিল। একটা জিবেগজা হলে অনেকটা ভরাট হয়ে যায়। মালপোয়াও এই কাজটা ভালোভাবে করতে পারে। রসগোল্লা বা সন্দেশ একটা করে দেওয়া ভালো দেখায় না, তাই দুটো দরকার। কিন্তু দানাদার একটাই দেওয়ার দস্তুর ছিল, কারণ ওটা খুব বেশি মিষ্টি, মুখ ফিরিয়ে দেয়। একটা তেকোনা নিমকিও বেশ কিছুটা জায়গা দখল করে এবং একমুঠো ডালমুট দিয়ে দিলেই কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেল।
তবে পাত্রপক্ষের বেলায় একটু অন্যরকম ভাবতে হত। ছানার মিষ্টির পরিমাণ একটু বাড়ত ওই ধরনের ভিআইপি অতিথি এলে, ওই ঘরে প্রবেশ ছোটদের পক্ষে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। আমরাও ‘হ্যাংলা’ অপবাদের ভয়ে ওদিকে যেতাম না, কানখাড়া থাকত অতিথি কখন বলে– ‘এত কেন, এত কী করে খাব!’ বাড়ির বড়রা কী নিষ্ঠুর, বলত– ‘খেয়ে নিন, খেয়ে নিন, বেশি কিছু তো নয়।’ কিছু ভালো অতিথি ছিল, বলত, ‘পারব না, একটা প্লেট আনুন, তুলে দিই।’ সেইসব ভালো অতিথির জন্যই আমরা মাঝেমধ্যে এটা-ওটা পেতাম। তবে অধিকাংশই নিমকিটা, গজাটা তুলে দিত। ছানার জিলিপি, সন্দেশ, পান্তুয়া-টান্তুয়া সাবাড় করে দিত। তখন ডায়াবেটিসটাও ছাই ছিল না বোধ হয় তেমন!

আমরা ছিলাম রিফিউজি পরিবার। আত্মীয়স্বজন তো রিফিউজিই হত। তাঁদের জন্য মিষ্টির দোকানে যাওয়ার দরকার হত না। মোয়া করা থাকত প্রায়শই– মুড়ির কিংবা চিড়ের। নারকোল নাড়ুও থাকত। পূর্ববঙ্গে প্রচুর নারকোল পাওয়া যেত। বাঙালরা খুব নারকোল-প্রেমী। মোয়ার সঙ্গে একটু নারকোল দিয়ে দিলেই হল। আবার ‘এইদিক দিয়া যাইতেছিলাম, ভাবলাম একটু খোঁজ কইর্যা যাই’– এই ধরনের অতিথিও কিছু আসত, তাঁদের জন্য গুড়-চিড়ে বা মুড়ি-বাতাসা। কিন্তু প্রায়শই এমন সময় আসতেন যে বলতেই হত, ‘দুফরে, ডাইল-ভাত খাইয়াই যান।’ উত্তর আসত– ‘আপনের কথা কি ফ্যালান যায় নিকি?’ এঁরা সত্যিই অভাবী অতিথি! এরকমভাবে বাঁচা ওঁরা ভাবতেও পারেননি উদ্বাস্তু হবার আগে।
একজন আসতেন, পুরো ভাতের সঙ্গে ডাল মেখে একটু নুন ছেটাতেন, তারপর বলতেন, ‘লবণ বেশি হইল, দুগা ভাত দেন।’ ভাত এল, ‘তখন বড় শুকনা হইয়া গেল, এক হাত ডাইল।’ সঙ্গে তরকারিও পাতে পড়ত, ঠাকুরমার হাতের আশ্চর্য কায়দায় সে কুমড়োর ঘ্যাট বা আলু চচ্চড়ি ‘যেতে পারি কিন্তু কেন যাব’ হয়ে হাতার গায়েই লেগে থাকত। বেলা ১১টার পর কেউ বাড়িতে এলেই দুপুরের ভাত খেয়ে যাওয়ার অনুরোধ আবশ্যিক ছিল। সে অনুরোধে সাড়া দেওয়া বা না-দেওয়া তাঁদের নিজস্ব ব্যাপার।
আত্মীয়দের বিস্তার ছিল ব্যাপক। ছোটমামার মেজো শ্যালকের ভায়রা ভাই, কিংবা ছোট কাকিমার মেজো পিসেমশাইও আত্মীয়স্বজনের মধ্যেই গণ্য হতেন। ওঁরা তখনও তাঁদের পরিচয়ে ছেড়ে আসা গ্রামের নাম ব্যবহার করতেন। বিয়ের চিঠিতে লেখা থাকত ‘দত্তপাড়ার অমুকের জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত মাইজদিয়ার তমুকের একমাত্র কন্যার বিবাহ…।’ আসলে ওঁরা হয়তো থাকছেন গাঙ্গুলিবাগান আর বাঘাযতীন কলোনিতে। কিংবা রাণাঘাট বা ধুবুলিয়া। শামুকের খোলার মতো নিজেদের ভার্চুয়াল গ্রাম বয়ে বেড়াতেন। আমার পিতামহ তখন প্রায় চোখে দেখেন না, একজন কেউ এসে তাঁকে প্রণাম করল। দাদু জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ক্যাডা?’ উত্তর এল– ‘আমি কানাই।’ দাদু তখন বললেন, ‘কোন কানাই? কতই তো কানাই আছে দুনিয়ায়।’ তখন উত্তর এল– ‘আমি চৌমুহনির কানাই।’ দাদু বললেন, “হ’, বুজছি। দুর্লভ চক্রবর্তীর জ্যেষ্ঠপুত্র।”
একজন আসতেন, উনি সম্পর্কে আমাদের কেমন যেন জামাই হতেন। ঠাকুরমার মাসতুতো বোনের জামাই– মানে আমাদের বাড়ির জামাই। ওঁর ধুতির কোঁচাটা পকেটে পোরা থাকত। ধুতির সঙ্গে ফুলশার্ট এবং তাঁর মনে সদা সর্বদা ঢুকে থাকত জামাইসত্তা, ফলে বিশেষ খাতির তাঁর প্রাপ্য। ঘরে একটি বা দু’টি চেয়ার থাকত। যদি কেউ ওখানে বসে থাকত, উনি তক্তপোশে বসতেন না। দাঁড়িয়ে থাকতেন। কেউ চেয়ার ছেড়ে দিলে তবে বসতেন। ডালটা বাটি করে আগে দিয়ে রাখতে হত। ওটা হল বিশেষ খাতির। বাঙালদের ডাল বড় প্রিয়। মাছের চেয়েও ডালের খাতির বেশি ছিল। কারণ পূর্ববাংলায় মাছ খুব সহজলভ্য, বরং ডাল পাওয়া যেত না। কেবলমাত্র খেসারি ডালের ফলন ছিল কিছু। ডালের চাষ হত– বিহার, উত্তরপ্রদেশ আর পাঞ্জাবে। সেই ডাল পদ্মার ওপারে খুব কম পাওয়া যেত। এ কারণে ডালের সম্মানই ছিল আলাদা। কিছু বিশেষ ধরনের অতিথিকে দু’রকমের ডাল খাওয়ালে আপ্যায়নটা ভালো হয়েছে বলা যেত।
এখনও লক্ষ করে দেখবেন, তিন প্রজন্ম পরেও বাঙালরা আগে মাছ, পরে ডাল খায়। আর ঘটিদের মৎস সম্ভার কম বলে মাছটাই প্রিয়তর। বাঙালরা কলকাতায় এসে এই উল্টো কারবার দেখে বেশ হকচকিয়ে ছিল। মাছের চেয়ে ডালের দাম কম বলে টানাটানির সংসারে ডালের ব্যবহার বেড়ে গেল বটে, কিন্তু ডালকে অসম্মান করল না। জলসায় আগে মানবেন্দ্র, ধনঞ্জয়, পিন্টু, কিন্তু শেষে হেমন্ত। তেমন শেষে ডাল।
আমার ঠাকুরমার কয়েকজন বান্ধবী কাম বোন আসতেন। ওঁরা বিধবা ছিলেন। ঠাকুরদার মৃত্যুর পর ঠাকুরমাও তাই। আমরা ছোটরা ঠাকুরমার ভইনডি (বোনটি) দের জন্য উন্মুখ থাকতাম। কারণ ওঁরা এলে আশ্চর্য সুন্দর সব লোভনীয় পদ বানাতেন। তরকারির খোসার চচ্চড়ি, তিল, কচুর লতি, করমচা, পাতুরি নানা রকমের পদ। ওরা পুজো, ব্রত– এসবও করতেন। তখন নাড়ু বানাতে বানাতে প্রায়শই ওদের হাত থেকে কিংবা সন্দেশের কাঠের ছাঁচ থেকে কিছুটা পড়ে যেত। ভুঁয়ে পড়া জিনিস তো আর পবিত্র থাকে না, তাই ওগুলো আমাদের দিকে ছুঁড়ে দিত, আর মিষ্টি করে হাসত। ঠাকুরমা নিজেও এটা করতেন আর ওঁর বিমলা, সুরবালা ভইনডিরা। ওঁরা চলে গেলে খুব দুঃখ হত। ওদের জপের মালার ব্যাগ লুকিয়ে রাখতাম যেন না যেতে পারে।
তখন জুতো লুকিয়ে রাখারও খুব চল ছিল। ঠাকুরমার বোনদের জুতো ছিল না। বিধবারা জুতো পরতেন না। কিন্তু আমি যখন মামার বাড়ি যেতাম মায়ের সঙ্গে, মামাতো ভাইবোনেরা আরও দু’দিন থেকে যাওয়ার ব্যাপারে চাপ সৃষ্টির জন্য আমাদের জুতো লুকিয়ে রাখত। তেমনি আমাদের বাড়িতে আমার সমবয়সি কেউ এলে আমিও জুতো লুকোতাম। এটা ‘যেতে নাহি দিব’ আন্দোলনের একটা পদ্ধতি ছিল। এখন সম্পূর্ণ লুপ্ত।

আমাদের পরিবারের কোনও গুরুদেব ছিল না। আমার ঠাকুরমার বাপের বাড়ি ছিল পূর্ববাংলার সম্বিতপুরে, দেশভাগের পর চিৎপুরের ঘিঞ্জি গলিতে। ওদের একজন গুরুদেব ছিল। ট্রামের সেকেন্ড ক্লাসের হলুদ টিকিটটা চেয়ে নিতাম জমাব বলে। শুনতাম ওঁর বাবা হাতির পিঠে চেপে শিষ্যবাড়ি যেতেন। গুরুদেবরা হলেন ভিভিআইপি অতিথি। তেনারা এলে বাড়িতে মালপোয়া হত, লুচি, সুজির পায়েস ইত্যাদি। জলখাবারের লুচির সঙ্গে আবার তরকারি চলত না। কারণ দিনে একবারের বেশি পক্বাহার, মানে পাকা আহার অশাস্ত্রীয়। লবণ প্রয়োগে আহার্য পক্ব হয়ে যায়, তাই জলখাবারে তরকারি নয়। মূল ভোজনেই তরকারি। মাছও চলত। তবে মাছে কাঁচাকলা প্রয়োগ করতে হত। সেই কাঁচাকলা প্রয়োগের উৎস সম্প্রতি আবিষ্কার করেছি একটি সংস্কৃত শ্লোকে– ‘আমরম্ভা সমাযুক্তে সর্ব মৎসা নিরামিষাঃ।’ আমরম্ভা মানে কাঁচাকলা।
…………………….
ফলো করুন আমাদের ওয়েবসাইট: রোববার.ইন
…………………….
একজন দাদুর কথা মনে পড়ল। আমার ঠাকুরদার পিসতুতো ভাই। সম্পর্কে ঠাকুরমার দেবর। বউদির প্রশ্রয়ে তিনি একটা অবৈধ কর্ম করতেন। ডিম খেতেন। বামুনদের ডিম্ব ভক্ষণ নিষেধ। এতে স্ত্রী হত্যার পাপ হতে পারে। কারণ ডিম দেখে তো বোঝার উপায় নেই এর থেকে পুংশাবক জন্মাবে নাকি স্ত্রী? তাই ‘কিং করোমি’ ভেবে ডিম্বই বামুনদের জন্য নিষিদ্ধ। বৃথা মাংসও নিষিদ্ধ। বলিপ্রদত্ত মাংস অবশ্য বৃথা মাংস নয়। বলির পশু সর্বদা পুরুষ হয়। সুতরাং, বলির মাংস ভক্ষণে স্ত্রী হত্যার পাপ নেই। ঠাকুরমা গোপনে তাঁর প্রিয় দেবরের বাঞ্ছা পূরণ করতেন। আমি একবার দাদুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম মৎস ভক্ষণে নিষেধ নেই কেন? মাছ খেলেও তো স্ত্রী হত্যার পাপ লেগে যেতে পারে। তাছাড়া ডিমভরা ট্যাংরা, পারশে এসব তো খুব আয়েশ করে খাও দাদু। পিতামহ একটা সংস্কৃত শ্লোক বলেছিলেন, তার একটা লাইন মনে আছে– ‘জলবাইঙ্গনং সর্বদা নিরামিষ্য ভবতি।’
এই প্রিয় দেবরটির হাসি আজও মনে পড়ে। ‘হেঁ হেঁ ঠারিন। আমনের তুলনা নাই।’ ইনি প্রতি মাসে একবার অন্তত আমাদের অতিথি হতেন।
…পড়ুন ব্লটিং পেপার-এর অন্যান্য পর্ব…
২৩. হীনম্মন্য বাঙালি সমাজে শব্দের প্রমোশন হয় মূলত ইংরেজি বা হিন্দিতে
২১. বাঙালির বাজার সফর মানেই ঘ্রাণেন অর্ধভোজনম
২০. জাত গেল জাত গেল বলে পোলিও খাব না!
১৯: ধোঁয়া আর শব্দেই বুঝে গেছি আট-তিন-পাঁচ-দেড়-দেড়!
১৮: নামের আগেপিছে ঘুরি মিছেমিছে
১৭: টরে টক্কার শূন্য এবং ড্যাশের সমাহারে ব্যাঙের ‘গ্যাগর গ্যাং’ও অনুবাদ করে নিতে পারতাম
১৬: ছদ্মবেশী পাগলের ভিড়ে আসল পাগলরা হারিয়ে গেল
১৫. ধূমপান নিষেধের নিয়ম বদলান, আকাশবাণীর স্টেশন ডিরেক্টরকে বলেছিলেন ঋত্বিক ঘটক
১৪. এমএলএ, এমপি-র টিকিট ফ্রি, আর কবির বেলা?
১২. ‘গাঁধী ভগোয়ান’ নাকি ‘বিরসা ভগোয়ানের পহেলা অবতার’
১১. কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্টের চক্করে বাঙালি আর ভোরবেলা হোটেল থেকে রওনা দেয় না
৫. তিনটে-ছ’টা-ন’টা মানেই সিঙ্গল স্ক্রিন, দশটা-পাঁচটা যেমন অফিসবাবু
৪. রাধার কাছে যেতে যে শরম লাগে কৃষ্ণের, তা তো রঙেরই জন্য
৩. ফেরিওয়ালা শব্দটা এসেছে ফার্সি শব্দ ‘ফির’ থেকে, কিন্তু কিছু ফেরিওয়ালা চিরতরে হারিয়ে গেল
২. নাইলন শাড়ি পাইলট পেন/ উত্তমের পকেটে সুচিত্রা সেন
১. যে গান ট্রেনের ভিখারি গায়কদের গলায় চলে আসে, বুঝতে হবে সেই গানই কালজয়ী
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
