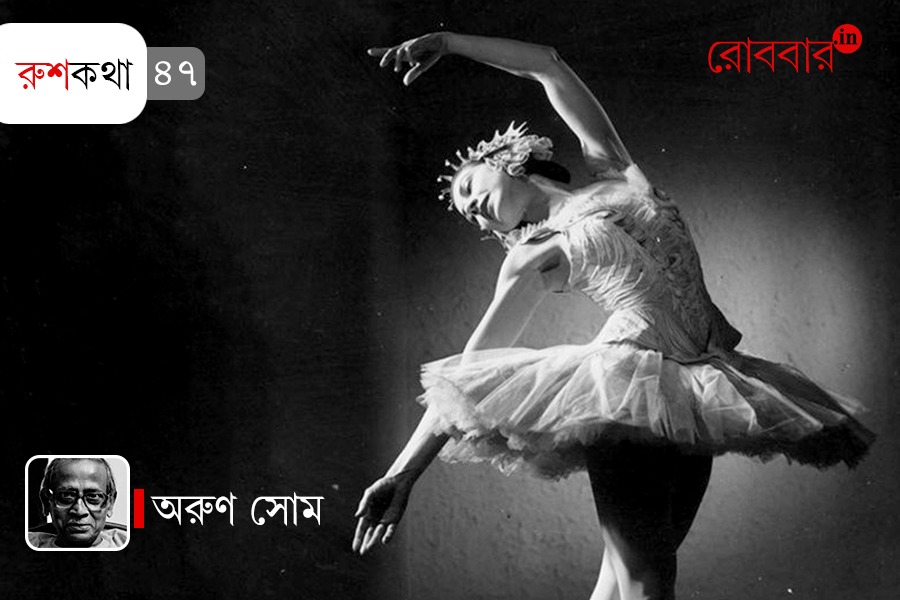
আজকাল দোকানে দামি জিনিস দেখে ক্রেতা অর্থাভাবের দোহাই পেড়ে মুখ ঘুরিয়ে নিলে মালিক মুচকি হেসে উপদেশ দেয় ‘রোজগার করতে জানতে হয়।’ সহজে রোজগারের একটি পন্থা– ভিক্ষাবৃত্তি। ইদানীং রাস্তাঘাটে সে-দৃশ্য বিরল নয়। পাতাল রেলের সাবওয়েগুলিতে ভিখারির সংখ্যা বেড়ে চলেছে। সকলে যে পেটের দায়ে ভিক্ষা করছে এমন মনে করার কোনও কারণ নেই। ত্ভের্স্কায়া স্ট্রিট (এককালের গোর্কি স্ট্রিট) দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম একজন দাঁড়িয়ে আছে সামনে একটা কাগজে-লেখা-আবেদন পেতে– ইংরেজিতে লেখা– সপরিবারে মার্কিন মুলুকে migrate করতে চাই– সাহায্যপ্রার্থী।

৪৭.
পেরেস্ত্রৈকার শেষ বছর: সোভিয়েতের শেষ নিশ্বাস
মস্কো, ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৯১
গত মাসে দূরদর্শনের এক সম্প্রচারে ধনীদের সম্পর্কে আপনার মনোভাব কী– এই প্রশ্নের ভিত্তিতে জনমতের পরিচয় দেওয়া হয়। প্রশ্ন যাদের করা হয়েছিল সবরকম বয়সের লোকজন ছিল তাদের মধ্যে। কিন্তু তাদের বেশির ভাগেরই বেশভুষা ও চেহারার চাকচিক্য চোখে পড়ার মতো। জানা যায়, শতকরা ৭৫ জনই ধনীদের প্রতি ভালো মনোভাব পোষণ করেন এবং যেনতেন প্রকারেণ বড়লোক হতে তাদের নিজেদেরও কোনও আপত্তি নেই। অথচ তার ঠিক কয়েক দিন আগেই শহরের কেন্দ্রস্থলে তথাকথিত কো-অপারেটিভ, জয়েন্ট স্টক কোম্পানি এবং ইয়ং মিলিয়নিয়রদের বিরুদ্ধে মহিলাদের একটি বিক্ষোভ প্রকাশ সমাবেশ ঘটেছিল তার কোনও উল্লেখ ছিল না। দূরদর্শনে সেদিন এক কোটিপতি মহিলাকেও দেখানো হয়। একনজরে দেখেই বুঝতে বাকি থাকে না যে, ব্যাপারটি সাজানো। পরে Radio Liberty ফাঁস করে দেয় সেই রহস্য। কো-অপারেটিভের মালিক বলে যে সুন্দরী মহিলাকে দেখানো হয়েছিল, তার আসল মালিক অন্য লোক– মহিলাকে রাখা হয়েছে তদন্তকারীদের মনোরঞ্জনের জন্য। এই ঝুঁকির জন্য তিনি বেতন পান।
কিন্তু তাতে স্থানীয় প্রচারমাধ্যমগুলির কিছু এসে যায় না। উঠতি বড়লোকেরা বিভিন্ন চ্যারিটি শো আর সুন্দরী প্রতিযোগিতার আয়োজন করে অর্থ তুলে যেভাবে জনসেবা করছেন, তার পরিচয় তুলে ধরাতে তাদের ভাবমূর্তি জনসমক্ষে অবশ্যই বৃদ্ধি পাচ্ছে।
ইয়ং মিলিয়নিয়রদের ক্লাব আজকাল বেশ জনপ্রিয়। কোনও কোনও প্রাচীন ব্যক্তি এই আশাও প্রকাশ করেছেন যে, বড়লোকদের জনকল্যাণমূলক কাজের দৌলতে তাঁদের দারিদ্র লাঘব হবে। রাজধানীতে পাইওনিয়ের ধরনের সংগঠনের জায়গায় উঠতি বয়সি ছেলেমেয়েরা গড়ে তুলেছে Teenage Republic নামে এক অ্যাসোসিয়েশন– নামটা অবশ্যই ইংরেজিতে। Management শেখার জায়গা। শুরু করছে খবরের কাগজে হকারি দিয়ে– পশ্চিমের অনেক বড় বড় লোকের জীবনও ওই দিয়েই শুরু। সুন্দরী মেয়েদের সুবর্ণ সুযোগ– বিদেশি বড়লোকদের বিয়ে করে বিদেশে Migrate করতে পারে– এই ধরনের বিয়ের ঘটকালির একটি এজেন্সি খোলা হয়েছে শহরে।
উলটপুরাণের কী মহিমা! প্রথমত, সোভিয়েত আমলে কোনও পত্র-পত্রিকায় ঘটকালির কোনও বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার সুযোগ ছিল না। দ্বিতীয়ত, এও কি সোভিয়েত আমলের এক চরমপন্থার এক ধরনের প্রতিক্রিয়া? সোভিয়েত আমলে এ ধরনের বিয়ে ছিল Cosmopolitanism-এর নামান্তর, এই Cosmopolitanism সোভিয়েতের দর্শনের সঙ্গে খাপ খায় না। মনে আছে, সোভিয়েত আমলে, সম্ভবত ১৯৭৮ সালেই হবে, সেই সময়কার জনপ্রিয় সাপ্তাহিক ‘লিতেরাতুনরনায়া গাজেতা’ (সাহিত্যপত্র)-তে ‘আমি তোমাদেরই’ এই শিরোনামে বেশ কয়েকটি সংখ্যা ধরে সেইসব সোভিয়েত নারীর দুঃখ-দুর্দশার করুণ কাহিনি তাদের নিজেদের বয়ানে প্রকাশিত হতে থাকে যারা বিদেশিদের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়ে শেষকালে তাদের ভুল বুঝতে পেরেছে। বিশেষ করে মনে পড়ে ১৯৮১ সালে ‘কম্সোমোল্স্কায়া প্রাভ্দা’ প্রত্রিকার কোনও এক সংখ্যায় প্রকাশিত দুটো চিঠির কথা। পত্রিকার কোনও এক পাঠিকা জনৈক বিদেশির প্রেমে পড়েছে, তাকে বিয়ে করা উচিত হবে কি না এই বিষয়ে পরামর্শ চেয়ে সে সম্পাদকের দপ্তরে একটি চিঠি লিখেছে। সম্পাদক মশাই এই সমস্যার সরাসরি কোনও সমাধান না দিয়ে এই চিঠিটার পাশাপাশি কাগজে ছাপিয়ে দিলেন আরেকজন মহিলার আরেকটি করুণ চিঠি, যেখানে সেই মহিলা এক বিদেশিকে বিয়ে করার পর নানা দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করে অবশেষে নিজের ভুল বুঝতে পেরে প্রেমের পাট চুকিয়ে স্বদেশে ফিরে আসে। দুটো চিঠির দুই কলমের মাঝের শিরোনামে লেখা হয়েছিল: ‘দুই পত্রের মুখোমুখি সাক্ষাৎ’। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। এই ব্যাপারে আমার নিজেরও তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে, আমিও ভুক্তভোগী তবে সোভিয়েত জনসমাজের কাছ থেকে ততটা নয়, যতটা সরকারি আমলাদের মহল থেকে।
প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৪৭ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর হুকুমনামা বলে সোভিয়েত ও বিদেশি নাগরিকদের মধ্যে বিবাহবন্ধন আইনত নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়।
স্তালিনের মৃত্যুর কয়েক মাস পরে, ১৯৫৩ সালের ২৪ অক্টোবর এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়। ১৯৫৪ সালের ২১ জানুয়ারি ঘোষিত রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর হুকুমনামাবলে বিদেশি ও সোভিয়েত নাগরিকদের মধ্যে যে সমস্ত বিবাহ আইনত অসিদ্ধ ছিল, সেগুলিকে রেজিস্ট্রি করার অনুমতি দেওয়া হয়।
সে যাই হোক, আগেকার মতো আজও পরামর্শ দেওয়ার লোকের কোনও অভাব নেই। অবশ্য সোভিয়েত আমলে তো এই নিয়ে একটা রসিকতাই প্রচলিত ছিল। রসিকতা এই যে, ‘হাজার হোক আমাদের দেশ সোভিয়েত (আক্ষরিক অর্থে পরামর্শ, পরিসর ইত্যাদি) দেশ!’– পরামর্শের দেশ। আজকাল দোকানে দামি জিনিস দেখে ক্রেতা অর্থাভাবের দোহাই পেড়ে মুখ ঘুরিয়ে নিলে মালিক মুচকি হেসে উপদেশ দেয় ‘রোজগার করতে জানতে হয়।’
সহজে রোজগারের একটি পন্থা– ভিক্ষাবৃত্তি। ইদানীং রাস্তাঘাটে সে-দৃশ্য বিরল নয়। পাতাল রেলের সাবওয়েগুলিতে ভিখারির সংখ্যা বেড়ে চলেছে। সকলে যে পেটের দায়ে ভিক্ষা করছে এমন মনে করার কোনও কারণ নেই। ত্ভের্স্কায়া স্ট্রিট (এককালের গোর্কি স্ট্রিট) দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম একজন দাঁড়িয়ে আছে সামনে একটা কাগজে-লেখা-আবেদন পেতে– ইংরেজিতে লেখা– সপরিবারে মার্কিন মুলুকে migrate করতে চাই– সাহায্যপ্রার্থী। অদ্ভুত আবদার!
এরই মধ্যে এক জায়গায় এক মহিলাকে খঞ্জনি বাজিয়ে গান গাইতে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। সুন্দর গলাটা। সাধে কি আর একশ্রেণির লোক এমন কথাও বলছে যে, মেট্রোর সাবওয়েগুলিতে নাচ-গান-বাজনার কল্যাণে আজকাল মেট্রো যাতায়াত করাটা বড় আনন্দের আর বৈচিত্রময় হয়ে উঠেছে।
মনে পড়ে গেল বছর দেড়েক আগে কোনও এক উৎসব উপলক্ষে আমারই পরিচিত এক ভদ্রলোকের বাড়িতে একটি পরিবারের সঙ্গে আলাপ হয়। স্বামী-স্ত্রী বয়স ৩০-৩৫-এর মধ্যে। এক ছেলে বয়স পাঁচ, আর এক মেয়ে বছর সাতেক বয়স। গান-বাজনায় ওরা সকলেই বেশ ওস্তাদ। সেদিন আসর মাতিয়ে তুলেছিল। স্বামী সরকারি আইনজীবী, স্ত্রীও সরকারি কর্মচারী। বেশ ভালো লেগেছিল। সেদিন শুনলাম স্বামী ভদ্রলোকটি নাকি ‘ধুত্তোর’ বলে চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন– বড় অল্প মাইনে। এখন সপরিবারে সপ্তাহে দিন চারেক সন্ধ্যাবেলায় শহরে চলে যান– রাস্তার ধারে ভালো একটা জায়গা বেছে নিয়ে গানের আসর বসিয়ে দেন। সপ্তাহে রোজগার ৫০০ রুবল। কেমন সহজে ভালো রোজগার! অনেক সময় বাবা-মা সন্ধ্যায় না বের হলে মেয়েই মনে করিয়ে দেয়। টাকা রোজগারে তারও উৎসাহ কম নয়। VCR কেনার যে স্বপ্ন তাদের ছিল, এইভাবে আর কিছুদিন চললে তা সফল হবে। মহিলার প্রথম প্রথম লজ্জা হত। এখন আর কোনও সংকোচ বোধ করেন না। কিন্তু এভাবে অর্থ উপার্জন? কৈফিয়ত– কেন? শ্রমের বিনিময়েই তো অর্থ উপার্জন করছি। আর সবচেয়ে বড় কথা– টাকা টাকাই, টাকায় কোনও গন্ধ লেগে থাকে না।

মস্কো, ২৯.০৯.১৯৯২
আজকের রাশিয়া– মুক্ত রাশিয়া। পথে যেতে যেতে চমকে উঠলাম। মস্কোর পাতাল রেলের সাবওয়েতে আধা অন্ধকারাচ্ছন্ন দেওয়ালের গায়ে মাথা ঠুকে আছড়ে পড়ছে লেনিনগ্রাদ সিম্ফনির সেই সুরমূর্ছনা। বড় করুণ শোনাচ্ছে।
Violincello, Flute, Saxophone, বেহালা– যাবতীয় বাদ্যযন্ত্রের পুরো একটা অর্কেস্ট্রা। সংগীত বিদ্যালয় থেকে সদ্য ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত বেকার সংগীতশিল্পীদের একটি দল। সামনে উল্টো করে পাতা টুপি।
এ কোনও আবিষ্কার নয়। আজকাল পেরেস্ত্রৈকার কল্যাণে রাস্তায় ঘাটে যেখানে-সেখানে শ্রবণেন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির অবকাশ পাবেন। একশ্রেণির মানুষের সংগতি নেই টিকিট কেটে হলঘরে গিয়ে গান-বাজনা শোনার, বেশ কিছু শিল্পীর সুযোগ নেই অন্য কোনওভাবে রুজি-রোজগারের। ফুটপাত আর সাবওয়েগুলি এখন এই দুই পক্ষের আদান-প্রদানের জায়গা। পথে এসে দাঁড়িয়েছে সোভিয়েত ধ্রুপদী সংগীত, যার স্থায়ী আসন ছিল বিশ্বের দরবারে।
ব্যালের দেশ বলে আমরা যাকে জানতাম সেই রাশিয়ায় আধুনিক ব্যালে শেখাতে এসেছে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে এক ব্যালে ট্রুপ।
গত ২৩ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় মস্কোর Young Spectators Theatre-এর নাট্যমঞ্চে ফিলাডেলফিয়ার এক নৃত্য ও নাট্যগোষ্ঠী পরিবেশন করল এইড্স সমস্যা নিয়ে এক নৃত্যনাট্য। উদ্দেশ্য– এইড্স সমস্যার ওপর রুশিদের আলোকপাত করা।
কিন্তু ফুটপাতে বা খোলা মাঠে বিনামূল্যে জ্ঞান বিতরণের জন্য এই অনুষ্ঠানের আয়োজন নয়। সৌভাগ্যবান দর্শকদের কথা মনে রেখে দর্শনী ধার্য হয় ২৫ রুবল। অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য সংস্কৃতি মন্ত্রালয় এবং ‘অগনিয়োক’ নামে পত্রিকার তহবিল থেকে যথাক্রমে দশ লক্ষ ও এক লক্ষ রুবল পাওয়া যায়।
গণমৈত্রীর ধ্বজা এখনও আছে। তবে জনগণ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ধ্যানধারণা ধীরে ধীরে পাল্টে যাচ্ছে এই যা।
এখানে ১৯৯৪ সালের ১৬ জানুয়ারির ‘কম্সোমোল প্রাভ্দা’ পত্রিকায় ‘একান্তই ব্যক্তিগত’ কলামে কোনও এক ভদ্রমহিলার একটি ক্ষুদ্র প্রতিবেদনের অংশ বিশেষ উদ্ধার করার লোভ সংবরণ করতে পারছি না।
‘‘১৯৪২ সাল দোন্-এর রস্তোভ্ বাজার চত্বরে ধরপাকড় শুরু হয়ে গেল। অল্পবয়সি মেয়ে ও বর্ষীয়সী মহিলাদের নিয়ে সংখ্যায় কয়েকশো হবে। জার্মানরা এবং তাদের পুলিশবাহিনী আমাদের সকলকে ধরে মালগাড়ির ওয়াগনে গাদাগাদি করে তুলে দিয়ে ঘটাং করে দরজা বন্ধ করে দিল। গাড়ি চলতে শুরু করে দিল। গাড়ি করে আমাদের চালান করে দেওয়া হবে, কোথায়? আমরা নিজেদের মধ্যে ফিসফিসিয়ে বলাবলি করতে লাগলাম: জার্মানিতে।
দু’দিন পরে খালাস করা হল। ভিনদেশি লাল আকাশ, খেলনার মতো ছোট্ট শহর, লাল টালি ছাওয়া ছোট বাড়িঘর। আমাদের ক্যাম্পে ঢুকিয়ে দেওয়া হল।…
১৯৪৪ সালের হেমন্তকাল। বিমানহানা শুরু হয়ে গেছে। তারই মধ্যে আমাদের মাঠে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হল, মনিবদের খেতের শালগম তুলতে হবে।… একদিন কাজের পর বুড়ো মনিব আমাদের তিন জনকে একটা কাজে তার বাড়িতে ডেকে পাঠাল। বসার ঘরে একটা গ্র্যান্ড পিয়ানো। আমি এগিয়ে গিয়ে ডালা তুললাম… মুহূর্তের মধ্যে কী হল… আমি সামনের চেয়ারে বসে পড়ে চড়া পর্দার একটা বাজনা ধরলাম। কাশফুলের মতো মাথায় একরাশ সাদা চুল এই বুড়ো মানুষটা কী করে জানবে এই ‘রুশি শুয়োরটা’ সংগীত বিদ্যালয় শেষ করেছে এবং তার স্বামী রাশিয়ায় একজন সুরকার।
‘বেঠোফেন মোৎসার্ট, রাখ্মানিনভ্ এবং বলাই বাহুল্য চাইকোভ্স্কি… রাশিয়া …রুশ গীতি..বুড়ো কোনো কথা না বলে ধপাস করে সোফায় গা এলিয়ে দিল, চোখের চশমা কোথাও খসে পড়ে ঝনঝন করে ভেঙে গেল। মাত্র গতকালই সে খবর পেয়েছে রাশিয়ার কোনো এক শহরে… মিনস্কে না কোথায় যেন তার ছেলে ওয়াল্টার যুদ্ধে মারা গেছে। এই পিয়ানো সে বাজাত।
আমি আমার জীবন পার করে এসেছি।… আমার বয়স চুরাশি। নিঃশব্দে হেঁটে চলেছি পাতাল রেলের সাবওয়ে দিয়ে। জীবনটা কেমন যেন দুর্বোধ্য, ভয়ংকর হয়ে উঠেছে, কেমন যেন অর্থহীন মনে হয় এখন।
…কিন্তু কী আশ্চর্য। পাভেলেৎস্কির কাছাকাছি আসতে দেখি একটা জায়গায় একটা বাচ্চা ছেলে বাঁশিতে মোৎসার্ত বাজাচ্ছে। আমি নিজেকে সামলাতে পারলাম না, আমার চোখে জল এসে গেল। পেনশনের টাকা থেকে পাঁচ রুবলের একটা নোট বার করে তার সামনে পেতে রাখা টুপিতে ফেলে দিলাম। সে মাথা নুইয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা জানাল, তারপর বাজাতে শুরু করল শুবের্তের ‘Ave Maria’। না। সংগীতের মৃত্যু নেই, যতক্ষণ সংগীত আছে ততক্ষণ জীবন আছে, জগৎও আছে। আমার থাকার মধ্যে আছে এই সংগীত, আমার হৃদয়ের স্মৃতিসুধা।… জীবনের কয়েকটা তাল আর লয়।’’
…পড়ুন রুশকথা-র অন্যান্য পর্ব…
পর্ব ৪৬। অক্টোবর বিপ্লবের উচ্ছ্বাস কোনও দেশে কমলে, অন্য দেশে বাড়তে থাকে
পর্ব ৪৫। ‘অক্টোবর বিপ্লব দিবস’ আর পালিত হবে না, পালিত হবে বড়দিন– চোখের সামনে বদলে যাচ্ছিল সোভিয়েত
পর্ব ৪৪। রাজনীতিতে অদূরদর্শিতার ফল যে কত সুদূরপ্রসারী, তার প্রমাণ আফগানিস্তান
পর্ব ৪৩। জানলা দিয়ে পূর্ব জার্মানি দেখতে দেখতে গর্বাচ্যোভ বলেছিলেন, তাহলে এখানেই শেষ!
পর্ব ৪২। পেরেস্ত্রৈকা শুরু হলে বুঝেছিলাম ‘প্রগতি’ ‘রাদুগা’– এসব কিছুই থাকবে না
পর্ব ৪১। কল্পনা যোশীর তুলনায় ইলা মিত্রকে অনেক বেশি মাটির কাছাকাছি বলে মনে হয়েছে
পর্ব ৪০। বেসরকারিকরণের শুরু দিকে রাস্তাঘাটে ছিনতাই বেড়ে গেছিল, কারণ সব লেনদেন নগদে হত
পর্ব ৩৯। হাওয়া বদলের আঁচ অনেকেই আগে টের পেয়েছিল, বদলে ফেলেছিল জীবনযাত্রা
পর্ব ৩৮। শুধু বিদেশে থাকার জন্য উচ্চশিক্ষা লাভ করেও ছোটখাটো কাজ করে কাটিয়ে দিয়েছেন বহু ভারতীয়
পর্ব ৩৭। একটা বিদেশি সাবানের বিনিময়েও নাকি মস্কোয় নারীসঙ্গ উপভোগ করা যায়– এমনটা প্রচার করেছে ভারতীয়রা
পর্ব ৩৬। মস্কোর ঠান্ডায় লঙ্কা গাছ দেখে পি.সি. সরকার বলেছিলেন, ‘এর চেয়ে বড় ম্যাজিক হয় নাকি?’
পর্ব ৩৫। রুশদের কাছে ভারত ছিল রবীন্দ্রনাথের দেশ, হিমালয়ের দেশ
পর্ব ৩৪। সোভিয়েত শিক্ষায় নতুন মানুষ গড়ে তোলার ব্যাপারে একটা খামতি থেকে গিয়েছিল
পর্ব ৩৩। দিব্যি ছিলাম হাসপাতালে
পর্ব ৩২। মস্কোর স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে সাধারণ ডাক্তাররা অধিকাংশই মহিলা ছিলেন
পর্ব ৩১। আমার স্ত্রী ও দুই কন্যা নিজভূমে পরবাসী হয়ে গিয়েছিল শুধু আমার জন্য
পর্ব ৩০। শান্তিদা কান্ত রায়ের প্রিয় কাজ ছিল মস্কোয় ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের কমিউনিজম পড়ানো
পর্ব ২৯। পেরেস্ত্রৈকার শুরু থেকেই নিরাপত্তার অভাব বোধ করছিলেন গোপেনদা
পর্ব ২৮। দেশে ফেরার সময় সুরার ছবি সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি পাননি গোপেনদা
পর্ব ২৭। বিপ্লবের ভাঙা হাট ও একজন ভগ্নহৃদয় বিপ্লবী
পর্ব ২৬। ননী ভৌমিকের মস্কোর জীবনযাত্রা যেন দস্তইয়েভস্কির কোনও উপন্যাস
পর্ব ২৫। ননীদা বলেছিলেন, ডাল চচ্চড়ি না খেলে ‘ধুলোমাটি’র মতো উপন্যাস লেখা যায় না
পর্ব ২৪। মস্কোয় শেষের বছর দশেক ননীদা ছিলেন একেবারে নিঃসঙ্গ
পর্ব ২৩। শেষমেশ মস্কো রওনা দিলাম একটি মাত্র সুটকেস সম্বল করে
পর্ব ২২। ‘প্রগতি’-তে বইপুথি নির্বাচনের ব্যাপারে আমার সঙ্গে প্রায়ই খিটিমিটি বেধে যেত
পর্ব ২১। সোভিয়েতে অনুবাদকরা যে পরিমাণ অর্থ উপার্জন করত, সে দেশের কম মানুষই তা পারত
পর্ব ২০। প্রগতি-র বাংলা বিভাগে নিয়োগের ক্ষেত্রে ননীদাই শেষ কথা ছিলেন
পর্ব ১৯। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নাকি খুব ভালো রুশভাষা জানতেন, প্রমথনাথ বিশী সাক্ষী
পর্ব ১৮। লেডি রাণু মুখার্জিকে বাড়ি গিয়ে রুশ ভাষা শেখানোর দায়িত্ব পড়েছিল আমার ওপর
পর্ব ১৭। একদিন হঠাৎ সুভাষদা আমাদের বাড়ি এসে উপস্থিত ফয়েজ আহমেদ ফয়েজকে নিয়ে
পর্ব ১৬। মুখের সেই পরিচিত হাসিটা না থাকলে কীসের সুভাষ মুখোপাধ্যায়!
পর্ব ১৫। রুশ ভাষা থেকেই সকলে অনুবাদ করতেন, এটা মিথ
পর্ব ১৪। মস্কোয় ননীদাকে দেখে মনে হয়েছিল কোনও বিদেশি, ভারতীয় নয়
পর্ব ১৩। যিনি কিংবদন্তি লেখক হতে পারতেন, তিনি হয়ে গেলেন কিংবদন্তি অনুবাদক
পর্ব ১২। ‘প্রগতি’ ও ‘রাদুগা’র অধঃপতনের বীজ কি গঠনপ্রকৃতির মধ্যেই নিহিত ছিল?
পর্ব ১১। সমর সেনকে দিয়ে কি রুশ কাব্যসংকলন অনুবাদ করানো যেত না?
পর্ব ১০। সমর সেনের মহুয়ার দেশ থেকে সোভিয়েত দেশে যাত্রা
পর্ব ৯। মস্কোয় অনুবাদচর্চার যখন রমরমা, ঠিক তখনই ঘটে গেল আকস্মিক অঘটন
পর্ব ৮: একজন কথা রেখেছিলেন, কিন্তু অনেকেই রাখেননি
পর্ব ৭: লেনিনকে তাঁর নিজের দেশের অনেকে ‘জার্মান চর’ বলেও অভিহিত করত
পর্ব ৬: যে-পতাকা বিজয়গর্বে রাইখস্টাগের মাথায় উড়েছিল, তা আজ ক্রেমলিনের মাথা থেকে নামানো হবে
পর্ব ৫: কোনটা বিপ্লব, কোনটা অভ্যুত্থান– দেশের মানুষ আজও তা স্থির করতে পারছে না
পর্ব ৪: আমার সাদা-কালোর স্বপ্নের মধ্যে ছিল সোভিয়েত দেশ
পর্ব ৩: ক্রেমলিনে যে বছর লেনিনের মূর্তি স্থাপিত হয়, সে বছরই ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙার সূচনাকাল
পর্ব ২: যে দেশে সূর্য অস্ত যায় না– আজও যায় না
পর্ব ১: এক প্রত্যক্ষদর্শীর চোখে রাশিয়ার খণ্ডচিত্র ও অতীতে উঁকিঝুঁকি
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
