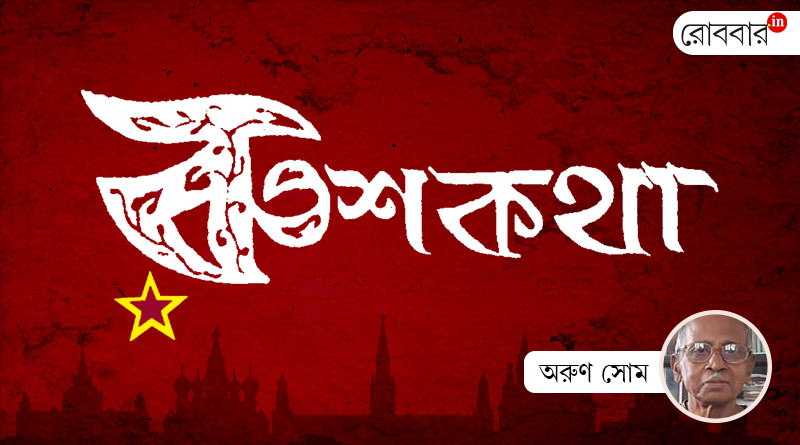
যখন বন্ধুবান্ধব, চেনা পরিচিত অনেকেরই ধীরে ধীরে চৈতন্যোদয় হল যে উনি আত্মহননের পথে চলে যাচ্ছেন। তখন তাঁরা তাঁকে সযত্নে পরিহার করে চলতে লাগলেন। আমরা ছিলাম নীরব দর্শক। হয়তো করারও কিছু ছিল না। তাঁর বাড়িতে নিত্য পানাহার করে গভীর রাতে চ্যাপলিনের ছবির নায়কের মতো এলোমেলো পা ফেলে যাঁরা নিজ নিজ আবাসের দিকে যাত্রা করতেন, একসময় তাঁদের অনেকে অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। কেউ কেউ বিরক্তিও প্রকাশ করতেন। মরশুমি পাখিরা মস্কোয় যাতায়াত করলেও ননীদার বাড়িমুখো হতেন না, যেহেতু তাঁদের কাছে তাঁর আকর্ষণ কমে গিয়েছিল।

২৪.
মস্কোয় পথহারা ননী ভৌমিক
মস্কোতে গিয়ে অনুবাদক হিসাবে কাজ করার সময়ও ননীদার বাড়িতে ঘনঘন যাওয়া হত– ননীদা বা সভেত্লানা নেমন্তন্ন করুন বা না করুন। ননীদাই রান্না করতেন– বাঙালি রান্না। ওঁর সবচেয়ে প্রিয় খাবার ছিল খিচুড়ি। মাঝে মাঝে ছাত্রছাত্রীরা যাঁরা যেতেন, তাঁরাও রান্না করতেন। আমাদের পুরনো বন্ধু, মস্কো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতক, পরে সেই বিষয়ে পিএইচডি-ও করেছিল, মস্কোর পুরনো বাসিন্দাদের একজন– বিশু দাশগুপ্ত। সে থাকলে তো কথাই ছিল না– রান্না সে-ই করত। মস্কোয় রন্ধনপটু হিসেবে বাঙালিমহলে তার নাম হয়ে গিয়েছিল। পরে ওর সঙ্গে মিলে রান্না করতে আমিও রন্ধনপটু হয়ে গিয়েছিলাম। মস্কোর বাঙালিদের বড় বড় ভোজের আসরে রান্নার জন্য আমাদের দু’জনের ডাক পড়ত।
পরের দিকে ননীদার বাড়িতে রান্নাটা আমিই করতাম। সে কাজও ছিল অনেক সময় ভারি ঝামেলার। গরমের দিনে ওদেশে বাজারে নানারকম শাকসবজি মিলত। সেগুলির একটার সঙ্গে আরেকটার আদায় কাঁচকলায় সম্পর্ক হলেও সভেত্লানার আবদার মতো সেসব একসঙ্গে মিশিয়ে ঘন্টজাতীয় তরকারি রান্না করতে হত। একদিন তো গিয়ে দেখি ঘরে সবজি বলতে লাউ আর বেগুন পড়ে আছে। দুটো মিশিয়ে যে জুতসই কোনও তরকারি রান্না করা যায় না, সভেত্লানা সেটা মানতে নারাজ। অগত্যা তাই রান্না করতে হল, কিন্তু রান্না কেমন হয়েছিল চেখে দেখার সুযোগ আমার হয়নি। তার আগেই কথা কাটাকাটি হতে সভেত্লানা ননীদাকে লক্ষ করে একটা প্লেট ছুড়ে মারলেন, আমি ননীদাকে সরিয়ে দিলাম। সভেত্লানা কেন জানি, আমার ওপর বেজায় খাপ্পা হয়ে দরজা খুলে দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিলেন। দু’দিন বাদে সভেত্লানার সঙ্গে দেখা হতে আবারও আগের মতোই এমন অন্তরঙ্গ সুরে কথা বললেন যেন সেদিন কিছুই হয়নি। এমনকী, মুখে হাসি। নির্লিপ্ত হাসি বলে কি কিছু হতে পারে? নাকি ইনি দস্তয়েভস্কির ব্যক্তিজীবনের বা তাঁর উপন্যাস থেকে উঠে আসা কোনও কুহকিনী?
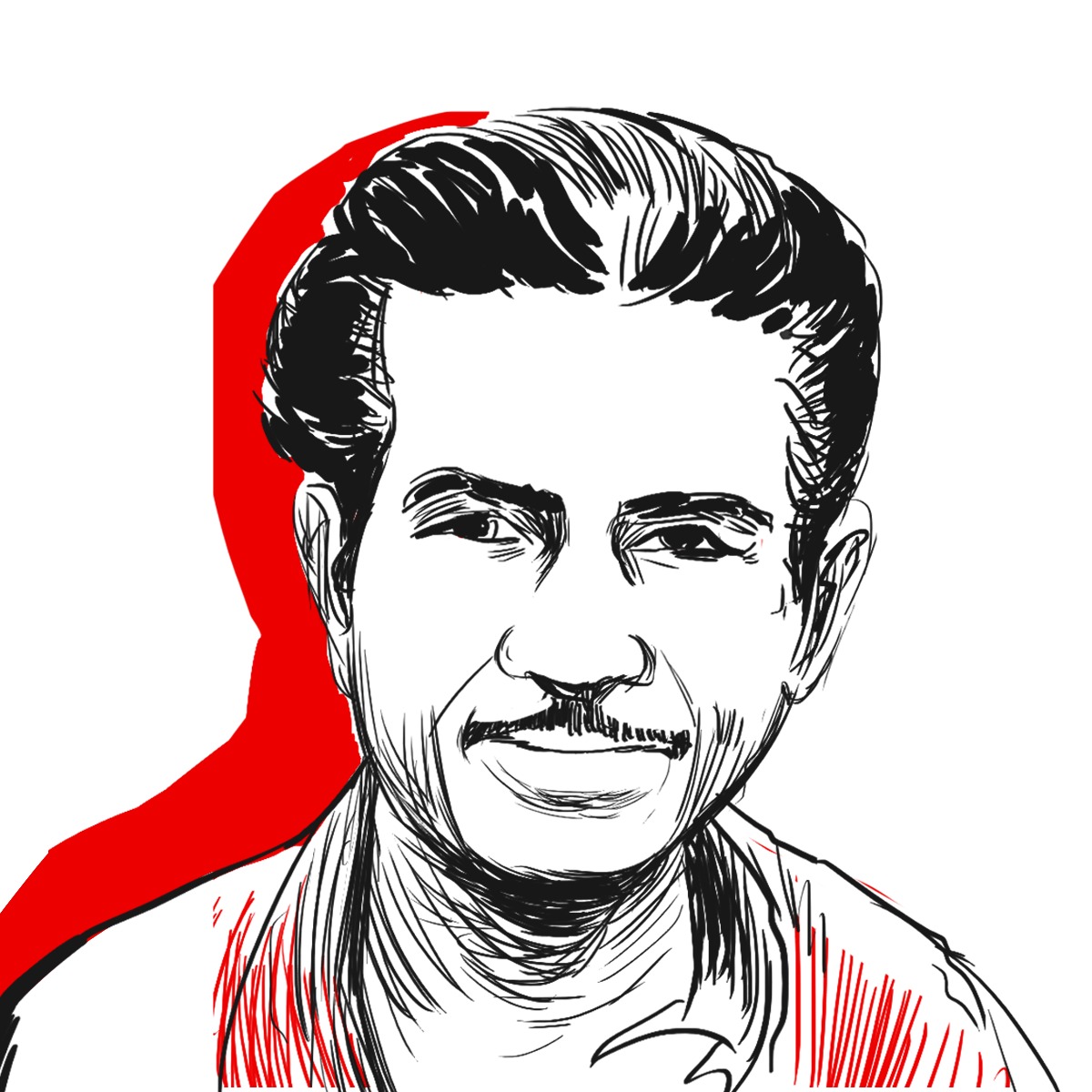
তাছাড়া ওঁদের বাড়িতে গেলে সময় সময় আরও একটা বিড়ম্বনা হত। ভোদকার স্টক ননীদার কাছে ভালোই থাকত। এছাড়া অতিথি অভ্যাগতরা অনেকেই দু’-একটা বোতল নিয়ে আসতেন। কিন্তু প্রায়ই বেশি রাতে দেখা যেত স্টক শেষ হয়ে গেছে। দোকান তো সেই কখন বন্ধ হয়ে গেছে, ফলে ছোট রেস্তোরাঁয়, ওঁদের বাড়ির কাছেই ছিল একটা রেস্তোরাঁ, আমাকে বা হায়াৎকে সেখানে পাঠানো হত। রেস্তোরাঁর একটা চোরা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে বেশি দাম দিয়ে বোতল কিনে নিয়ে আসতে হত। আরও পরে অবশ্য অভিজ্ঞতায় জেনেছি বেশি রাতে ট্যাক্সিওয়ালাদের কাছ থেকেও চড়া দামে পাওয়া যেত।
প্রথম প্রথম ভাবতাম, ননীদা এত বছর ধরে এখানে কাজ করছেন, আর এইভাবে আসর চলছে দিনের পর দিন রাতের পর রাত, তাহলে উনি কাজটা করে যাচ্ছেন কী করে! আমি তো কিছুতেই করতে পারছি না। আর এইভাবে যদি ভোদকা খেতে থাকি, তাহলে তো আমি মারা যাব। বেশিদিন টিকব না। আমার অবাক লাগত কী করে উনি এত বছর ধরে এরকমভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন। আমার তো মাথা ঝিমঝিম করছে। কাজকর্ম করতে পারছি না। খুব খারাপ লাগত। কলকাতায় থাকতে আমি যথেষ্টই আয় করতাম। একমাত্র অনুবাদক হওয়ার জন্যই কাজকর্ম ঘরবাড়ি সবকিছু ছেড়ে মস্কোতে এসেছি। একটু খারাপ লাগলেও ননীদার বাড়িতে যাওয়াটা আস্তে আস্তে কমিয়ে দিলাম– সভেত্লানার শত ডাকাডাকি সত্ত্বেও নানা অজুহাতে এড়িয়ে যেতে লাগলাম।

…………………………………………………………………………………………
কথা কাটাকাটি হতে সভেত্লানা ননীদাকে লক্ষ করে একটা প্লেট ছুড়ে মারলেন, আমি ননীদাকে সরিয়ে দিলাম। সভেত্লানা কেন জানি, আমার ওপর বেজায় খাপ্পা হয়ে দরজা খুলে দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিলেন। দু’দিন বাদে সভেত্লানার সঙ্গে দেখা হতে আবারও আগের মতোই এমন অন্তরঙ্গ সুরে কথা বললেন যেন সেদিন কিছুই হয়নি। এমনকী, মুখে হাসি। নির্লিপ্ত হাসি বলে কি কিছু হতে পারে? নাকি ইনি দস্তয়েভস্কির ব্যক্তিজীবনের বা তাঁর উপন্যাস থেকে উঠে আসা কোনও কুহকিনী?
…………………………………………………………………………………………
কিন্তু সে যাই হোক, ননীদাকে মস্কোয় পেয়ে সেই সময় নিজেদের ভারি ভাগ্যবান বলে মনে হত। আলাপের প্রথম দিন থেকেই তিনি ‘ননীদা’। মস্কোয় কোনও বাঙালি কিছুদিনের জন্য এলে ননীদার বাড়িতে অন্তত একবার আসবেন না এমন হত না– অন্তত সাতের দশকের শেষ পর্যন্ত তাই দেখেছি।

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় একবার তাঁর বন্ধু ননী ভৌমিকের বাড়িতে বসেই এক টুকরো কাগজের ওপর একটা ছড়া লিখেছিলেন–
‘ননী–
ভালোবাসার খনি,
ভালোবাসার আস্তানা–
সভেত্লানা,
ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী–
দমিত্রি।’
এখন পিছু ফিরে তাকালে ভাবতেই কষ্ট হয়, ননীদাকে ঘিরে আমরা তখন কী একটা ঘোরের মধ্যে, একটা মায়ার জগতে ছিলাম। সভেত্লানার আর্তি ছিল ‘তিনশো বছর, তিনশো বছর আমরা বাঁচব!’ তাঁর এই আর্তিটা আমাদের মুগ্ধ করত।
পরের ইতিহাস তো একেবারে অন্য। যখন বন্ধুবান্ধব, চেনা পরিচিত অনেকেরই ধীরে ধীরে চৈতন্যোদয় হল যে উনি আত্মহননের পথে চলে যাচ্ছেন। তখন তাঁরা তাঁকে সযত্নে পরিহার করে চলতে লাগলেন। আমরা ছিলাম নীরব দর্শক। হয়তো করারও কিছু ছিল না। তাঁর বাড়িতে নিত্য পানাহার করে গভীর রাতে চ্যাপলিনের ছবির নায়কের মতো এলোমেলো পা ফেলে যাঁরা নিজ নিজ আবাসের দিকে যাত্রা করতেন, একসময় তাঁদের অনেকে অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। কেউ কেউ বিরক্তিও প্রকাশ করতেন। মরশুমি পাখিরা মস্কোয় যাতায়াত করলেও ননীদার বাড়িমুখো হতেন না, যেহেতু তাঁদের কাছে তাঁর আকর্ষণ কমে গিয়েছিল। ধীরে ধীরে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেন তিনি– শেষের বছর দশেক ছিলেন একেবারে নিঃসঙ্গ।

সোভিয়েত ইউনিয়নে পেরেস্ত্রৈকার সঙ্গে সঙ্গে যেন ভোল পাল্টে গেল সকলের। কিন্তু ননীদা রয়ে গেলেন সেই পুরনো জগতে– পেরেস্ত্রৈকার আগের জগতে। দেশে যখন রাজনৈতিক ডামাডোল চলছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল তাঁর বাস্তবতাবোধ। ঘটনাটা কাকতালীয়, কিন্তু প্রতীকধর্মীও। ইতিহাসের সেই টালমাটাল মুহূর্তে পায়ের তলার মাটি সরে যেতে আমাদের স্বপ্নভঙ্গ হল, কিন্তু ননীদা সেই ঘোরের মধ্যেই রয়ে গেলেন।
সভেত্লানার সঙ্গে ননীদার মনের মিল কোথায় হতে পারে– এই নিয়ে জল্পনাকল্পনার শেষ ছিল না আমাদের মধ্যে। অনেক সময় ওঁর সঙ্গে তাল দিয়ে ননীদা নিজেও কেন জানি চটুল হয়ে পড়তেন। সেটা তাঁর শিশুসুলভ সারল্যের জন্য, নাকি স্রেফ নিজেকে ভুলে থাকার প্রয়াস? সেসব আড্ডায় আবৃত্তি গান ইত্যাদি অবশ্যই হত, কিন্তু সাহিত্য সংক্রান্ত আলোচনা বিশেষ একটা হত না– অন্তত আমার তো মনে পড়ে না। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত নামার সঙ্গে সঙ্গে আসরের চেহারা পাল্টে যেত। আসর ছেড়ে উঠে যাওয়াই দায় হত। সভেত্লানা ততক্ষণে রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ড ছেড়ে দিয়ে ‘ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে…’-র সঙ্গে তাল মিলিয়ে নাচের আসর নামিয়ে দিয়েছেন ফ্লোরে। সে আসর তখন অল্পবয়সিদের দখলে, ননীদা সেখানে নীরব দর্শক। আপনমনে গুনগুন করে গেয়ে চলেছেন, ‘আমার বেলা যে যায়…।’ দু’জনের সুরে মিলছে কোথায়? একজনের মুখে যেখানে তিনশো বছর এমনি করে কাটিয়ে দেওয়ার সুর, অন্যজন সেখানে বেলাশেষের গান ধরেছেন। এই বেদনা কিন্তু অস্পষ্টভাবে মাঝে মাঝে প্রকাশ করে ফেলতেন চাপা মানুষটি। কিন্তু সেটা উড়িয়ে দেওয়ার জন্য আবার কোনও কোনও সময় ‘দে গরুর গা ধুইয়ে…’ ধরনের হুল্লোড়ধ্বনিতেও গলা মেলাতেন। বুঝতে কষ্ট হত না, ওটা কৃত্রিম।
তাঁর নিজের সাহিত্যকৃতির প্রসঙ্গ তিনি আড্ডায় উঠতেই দিতেন না, সযত্নে পরিহার করে যেতেন। আমরা যখন কথায় কথায় ননীদার অতীতকে খুঁচিয়ে তুলে আবার তাঁকে সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করতে বলতাম, তখন তিনি একটা চোখ পিটপিট করে মুচকি হাসতেন, মুঠো পাকিয়ে সিগারেট ধরে হুস হুস করে টানতেন– মনে হত বড় মজা পাচ্ছেন। কোনও মন্তব্য করতেন না। কখনও কখনও বড়জোর বলতেন, ‘ওসব কথা বাদ দাও। বরং ঢালো আরও এক পেগ।’
…………………………………………………………..
ফলো করুন আমাদের ফেসবুক পেজ: রোববার ডিজিটাল
…………………………………………………………..
মস্কোতে আসার পর ননীদা মধ্য এশিয়া ভ্রমণ করে বাংলায় ‘মরু ও মঞ্জরী’ নমে সত্তর-আশি পৃষ্ঠার একটা ভ্রমণকথা লিখেছিলেন। মস্কোর প্রগতি প্রকাশন থেকে ১৯৬৯ সালে বইটি প্রকাশিত হয়। কর্মসূত্রে নতুন দেশে এসে সেখানে বসবাস করার সুবাদে নতুন সমাজ সম্পর্কে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন এই ভ্রমণকথায়, আবার এই বই প্রকাশিতও হয়েছে সেই বিদেশের প্রকাশন সংস্থা থেকেই বাংলা ভাষায়, যা এর আগে অন্তত সোভিয়েত ইউনিয়নে কখনও হয়নি, পরে তো নয়ই। এছাড়া ১৯৬৭-’৬৮ সালে সাপ্তাহিক ‘দেশ’ পত্রিকায় ‘মস্কোর চিঠি’ নামে গোটা বারো কিস্তির যে কলাম লিখেছিলেন, সেগুলি বাদ দিলে ‘মরু ও মঞ্জরী’ই তাঁর শেষ মৌলিক লেখা। ‘মরু ও মঞ্জরী’র প্রশংসাসূচক একটি সমালোচনাও ওই সাপ্তাহিকেই বের হলে আমরা সেদিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি ওই একই ভঙ্গিতে সিগারেট টানতে টানতে চোখ টিপে শুধু হেসে বললেন, ‘তা এখন তো ওরা এসব কথা লিখবেই, লিখতে বাধাটা কোথায় যখন আমি কলম ছেড়ে দিয়েছি? আমি যদি নিয়মিত লিখতাম, তাহলে ওরাই উল্টো কথা বলত।’ ‘মস্কোর চিঠি’ লেখার সুযোগও কিন্তু তিনি বেশিদিন পেলেন না। কেন?
…পড়ুন রুশকথা-র অন্যান্য পর্ব…
পর্ব ২৩। শেষমেশ মস্কো রওনা দিলাম একটি মাত্র সুটকেস সম্বল করে
পর্ব ২২। ‘প্রগতি’-তে বইপুথি নির্বাচনের ব্যাপারে আমার সঙ্গে প্রায়ই খিটিমিটি বেধে যেত
পর্ব ২১। সোভিয়েতে অনুবাদকরা যে পরিমাণ অর্থ উপার্জন করত, সে দেশের কম মানুষই তা পারত
পর্ব ২০। প্রগতি-র বাংলা বিভাগে নিয়োগের ক্ষেত্রে ননীদাই শেষ কথা ছিলেন
পর্ব ১৯। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নাকি খুব ভালো রুশভাষা জানতেন, প্রমথনাথ বিশী সাক্ষী
পর্ব ১৮। লেডি রাণু মুখার্জিকে বাড়ি গিয়ে রুশ ভাষা শেখানোর দায়িত্ব পড়েছিল আমার ওপর
পর্ব ১৭। একদিন হঠাৎ সুভাষদা আমাদের বাড়ি এসে উপস্থিত ফয়েজ আহমেদ ফয়েজকে নিয়ে
পর্ব ১৬। মুখের সেই পরিচিত হাসিটা না থাকলে কীসের সুভাষ মুখোপাধ্যায়!
পর্ব ১৫। রুশ ভাষা থেকেই সকলে অনুবাদ করতেন, এটা মিথ
পর্ব ১৪। মস্কোয় ননীদাকে দেখে মনে হয়েছিল কোনও বিদেশি, ভারতীয় নয়
পর্ব ১৩। যিনি কিংবদন্তি লেখক হতে পারতেন, তিনি হয়ে গেলেন কিংবদন্তি অনুবাদক
পর্ব ১২। ‘প্রগতি’ ও ‘রাদুগা’র অধঃপতনের বীজ কি গঠনপ্রকৃতির মধ্যেই নিহিত ছিল?
পর্ব ১১। সমর সেনকে দিয়ে কি রুশ কাব্যসংকলন অনুবাদ করানো যেত না?
পর্ব ১০। সমর সেনের মহুয়ার দেশ থেকে সোভিয়েত দেশে যাত্রা
পর্ব ৯। মস্কোয় অনুবাদচর্চার যখন রমরমা, ঠিক তখনই ঘটে গেল আকস্মিক অঘটন
পর্ব ৮: একজন কথা রেখেছিলেন, কিন্তু অনেকেই রাখেননি
পর্ব ৭: লেনিনকে তাঁর নিজের দেশের অনেকে ‘জার্মান চর’ বলেও অভিহিত করত
পর্ব ৬: যে-পতাকা বিজয়গর্বে রাইখস্টাগের মাথায় উড়েছিল, তা আজ ক্রেমলিনের মাথা থেকে নামানো হবে
পর্ব ৫: কোনটা বিপ্লব, কোনটা অভ্যুত্থান– দেশের মানুষ আজও তা স্থির করতে পারছে না
পর্ব ৪: আমার সাদা-কালোর স্বপ্নের মধ্যে ছিল সোভিয়েত দেশ
পর্ব ৩: ক্রেমলিনে যে বছর লেনিনের মূর্তি স্থাপিত হয়, সে বছরই ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙার সূচনাকাল
পর্ব ২: যে দেশে সূর্য অস্ত যায় না– আজও যায় না
পর্ব ১: এক প্রত্যক্ষদর্শীর চোখে রাশিয়ার খণ্ডচিত্র ও অতীতে উঁকিঝুঁকি
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
