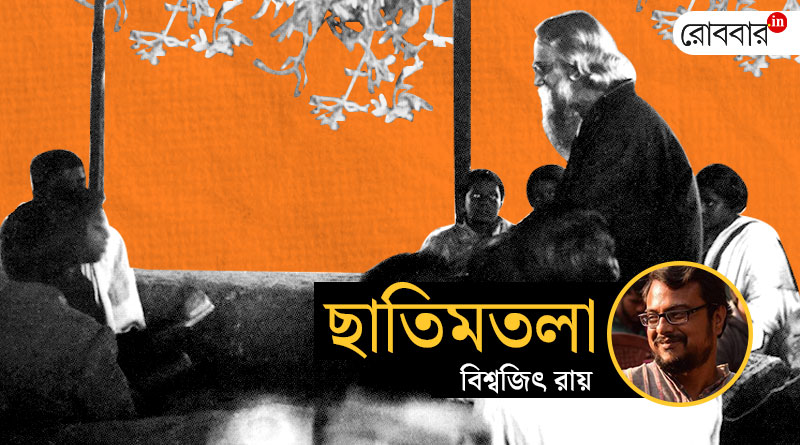
রবীন্দ্রনাথ দেবেন্দ্রনাথের জমিদারিতে ‘চাকরি’ করতেন। নিজের মেয়েদের কম বয়সে বিবাহ দেওয়ার কারণ দেবেন্দ্রনাথের আদেশ ও নির্দেশ, তা পালন করেছিলেন। লেখক রবীন্দ্রনাথ যা ভাবেন পিতা রবীন্দ্রনাথ তা করতে পারেননি। হয়তো রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথের মতো স্বাধীনজীবী ছিলেন না বলেই তাঁকে পিতৃ আদেশ মেনে চলতে হত।

৪০.
পিতৃদেবের সঙ্গে কিশোর রবির সম্পর্ক কেমন ছিল?
‘জীবনস্মৃতি’র সাক্ষ্য বলছে সে-সম্পর্ক ভয়ের নয়, স্নেহময় সাহচর্যের। তবে সেই স্নেহময় সাহচর্য সবসময় পাওয়া যেত না। ‘বাল্যকালে তিনি আমার কাছে অপরিচিত ছিলেন বলিলেই হয়। মাঝে মাঝে তিনি কখনো হঠাৎ বাড়ি আসিতেন; …।’ পরে এই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছিল।
দেবেন্দ্রনাথ কি তাঁর পিতা দ্বারকানাথের সাহচর্য পেয়েছিলেন? রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ দ্বারকানাথের স্নেহময় সাহচর্য তেমন না পেলেও দ্বারকানাথের বন্ধু রামমোহন রায়ের আদর পেয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের আত্মচরিতে সে-কথা আছে। কিশোর দেবেন্দ্র স্কুলের পর রামমোহনের মানিকতলার বাগানে যেতেন। বাগানের গাছের লিচু ছিঁড়ে, কড়াইশুঁটি ভেঙে খেতেন। এই উপদ্রবে রামমোহন বিরক্ত হতেন না। বলতেন, ‘বেরাদর! রৌদ্রে হুটা-পাটি করিয়া কেন বেড়াও, এইখানে বোসো। যত নিচু [লিচু] খেতে পার এখানে বসিয়া খাও।’

দৃশ্যটি মনোরম। রামমোহন দেবেন্দ্রকে আদর করে ‘বেরাদর’ বলে ডাকছেন, লিচু খাওয়াচ্ছেন। মাঝে মাঝে দেবেন্দ্রকে বাগানের দোলনায় বসিয়ে রামমোহন দোলাও দিতেন – খানিক পরে নিজে বসতেন, তখন দেবেন্দ্রকে দোলনা ঠেলতে হত। এই স্নেহসম্পর্ক গড়ে উঠেছিল বলেই হয়তো দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের একেশ্বরবাদী ধর্মের উত্তরাধিকারকে নিজের পরিকল্পিত ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে গ্রহণ ও সম্প্রসারণ করেছিলেন। পিতা দ্বারকানাথ দেবেন্দ্রকে এরকম সাহচর্য প্রদানের সময় পেতেন না, তিনি উদ্যোগপতি ব্যবসায়ী। দেবেন্দ্রর ব্রাহ্মধর্ম নিয়ে মাতামাতিকে বড়ো সুনজরে দেখতেন না। এই ভেবে শঙ্কিত হতেন তাঁর ব্যবসা-উদ্যোগ দেবেন্দ্র রক্ষা করতে পারবেন না। সে শঙ্কা অমূলক ছিল, একথা বলার উপায় নেই। দ্বারকানাথের প্রয়াণের পর দেবেন্দ্র পূর্ব বৈভব হারিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ কিশোরবেলায় যে ব্যবহার করতেন, তা দ্বারকানাথ সুলভ নয়, রামমোহন সুলভ। প্রথম প্রথম পিতা সম্বন্ধে কিশোর রবির যে দূরত্বময় দ্বিধা ছিল, তা উপনয়নের পর পিতৃ-সাহচর্যে কেটে গিয়েছিল। মাঝে মধ্যেই পিতাকে কিশোর রবি নিজের বিচিত্র সাধের কথা বলতেন। যৌবনের গোড়াতেও সেইসব কথা প্রকাশে খামতি ছিল না। দেবেন্দ্র কিশোরবেলাতে এবং যৌবনে কখনও রবিকে নিরাশ করেননি। উপনয়নের পর কিশোর রবি বোলপুরে দেবেন্দ্রনাথের সাহচর্যে কিছুদিন ছিলেন। প্রায় প্রতিদিন খোয়াই থেকে ‘জামার আঁচলে নানা প্রকারের পাথর সংগ্রহ করিয়া পিতার কাছে উপস্থিত’ হতেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, “তিনি আমার এই অধ্যবসায়কে তুচ্ছ বলিয়া একদিনও উপেক্ষা করেন নাই। তিনি উৎসাহ প্রকাশ করিয়া বলিতেন, ‘কী চমৎকার! সমস্ত তুমি কোথায় পাইলে!’ আমি বলিতাম, ‘এমন আরো কত আছে! কত হাজার হাজার! আমি রোজ আনিয়া দিতে পারি।’ তিনি বলিতেন, ‘সে হইলে তো বেশ হয়। ঐ পাথর দিয়া আমার এই পাহাড়টা তুমি সাজাইয়া দাও।’ ” এই অংশটুকু পড়তে পড়তে রবীন্দ্রনাথের ‘ডাকঘর’ নাটকের কথা মনে পড়তে পারে– সেখানে অমল ফকিরের কাছে তার মনের নানা সাধ প্রকাশ করত। ফকির বেশধারী ঠাকুরদা অমলকে নিরুৎসাহ না করে নানা ভাবে তার কল্পনা উসকে দিতেন। অমলকে তিনি বিচিত্র দেশে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখাতেন। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এমন কাজ করতেন দেবেন্দ্রনাথ।

পুনশ্চ জীবনস্মৃতির সাক্ষ্য উদ্ধার করা যাক। “আমার যৌবনারম্ভে এক সময়ে আমার খেয়াল গিয়াছিল, আমি গোরুর গাড়িতে করিয়া গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া পেশোয়ার পর্যন্ত যাইব। আমার এ প্রস্তাব কেহ অনুমোদন করেন নাই এবং ইহাতে আপত্তির বিষয় অনেক ছিল। কিন্তু আমার পিতাকে যখনই বলিলাম, তিনি বলিলেন, ‘এ তো খুব ভালো কথা; রেলগাড়িতে ভ্রমণকে কি ভ্রমণ বলে।’ এই বলিয়া তিনি কিরূপে পদব্রজে এবং ঘোড়ার গাড়ি প্রভৃতি বাহনে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাহার গল্প করিলেন।”
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
পুত্র পরবর্তী প্রজন্ম দেবেন্দ্রনাথকে নিয়ে কৌতুক করছিল– রথীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণায় মহর্ষি সম্বন্ধে তির্যক মন্তব্য আছে। মহর্ষি যে টাকা-পয়সার বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথ তা লিখেছেন। আর রবীন্দ্রনাথ? পিতৃদেবের কাছে তাঁর ঋণ যথেষ্ট, তবু পিতৃদেবের প্রয়াণের পর রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বও যেন স্বাধীন ভাবে বিকশিত হতে পারছে। পুত্র রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রতিমার বিবাহ দিলেন তিনি – সে তো বিধবা বিবাহ।
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ডাকঘরের অমলের তো বয়স হয় না। সুধা তাকে ভোলে না, মনে রেখে দেয়। রবীন্দ্রনাথের ‘ডাকঘর’ নাটকের অমল-ঠাকুরদা সংবাদের মধ্যে রবীন্দ্র-দেবেন্দ্র সংবাদ মিশে থাকা অসম্ভব নয়, তবে রবীন্দ্র-দেবেন্দ্র সম্বন্ধ তো ওই কৈশোর বা যৌবনের প্রারম্ভেই আটকে রইল না। রবীন্দ্রনাথের পিতৃদেব তাঁর আত্মজীবনকথা প্রকাশ করেছিলেন ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে। সেই জীবনকথাটির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশের দায়িত্ব দিয়েছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথকে। সত্যেন্দ্রনাথ দেবেন্দ্রনাথের বিশেষ অনুগত পুত্র ছিলেন না। বিশেষত স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনীকে কর্মক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়ার সূত্রে পিতা-পুত্রে বিরোধ হয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথ না চাইলেও স্বাধীন চাকরিজীবী সত্যেন্দ্রনাথ পিতার আদেশ অমান্য করার সাহস দেখিয়েছিলেন।
রবীন্দ্রনাথ দেবেন্দ্রনাথের জমিদারিতে ‘চাকরি’ করতেন। নিজের মেয়েদের কম বয়সে বিবাহ দেওয়ার কারণ দেবেন্দ্রনাথের আদেশ ও নির্দেশ, তা পালন করেছিলেন। লেখক রবীন্দ্রনাথ যা ভাবেন, পিতা রবীন্দ্রনাথ তা করতে পারেননি। হয়তো রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথের মতো স্বাধীনজীবী ছিলেন না বলেই তাঁকে পিতৃ আদেশ মেনে চলতে হত। বলেন্দ্রনাথের প্রয়াণের পর তাঁর বিধবা স্ত্রী পুনরায় বিবাহ করুন দেবেন্দ্রনাথ তা চাননি। দেবেন্দ্রনাথের সেই বার্তা বলেন্দ্রনাথের বিধবা স্ত্রীর কাছে রবীন্দ্রনাথকেই বহন করতে হয়েছিল।
১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে যে আত্মজীবনকথা দেবেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন তা ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দেই সমাপ্ত, পরবর্তী জীবনকথা সেখানে নেই। সেই পরবর্তী জীবন যত অগ্রসর হচ্ছিল ততই কি গুরুত্ব হারাচ্ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ! পুত্র পরবর্তী প্রজন্ম তাঁকে নিয়ে কৌতুক করছিল– রথীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণায় মহর্ষি সম্বন্ধে তির্যক মন্তব্য আছে। মহর্ষি যে টাকা-পয়সার বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথ তা লিখেছেন। আর রবীন্দ্রনাথ? পিতৃদেবের কাছে তাঁর ঋণ যথেষ্ট, তবু পিতৃদেবের প্রয়াণের পর রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বও যেন স্বাধীন ভাবে বিকশিত হতে পারছে। পুত্র রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রতিমার বিবাহ দিলেন তিনি– সে তো বিধবা বিবাহ। মহর্ষি তখন প্রয়াত। একদা ব্রাহ্মসমাজের সেক্রেটারি রবীন্দ্রনাথ ক্রমশই মহর্ষির প্রয়াণের পর ব্রাহ্মধর্মের সীমা অতিক্রম করলেন। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম যে তাঁর আত্মধর্ম নয় সে-কথা পরবর্তীকালে স্পষ্ট করেই তাঁর বিদেশে প্রদত্ত ‘রিলিজিয়ান অফ ম্যান’ বক্তৃতায় জানিয়েছিলেন।
পিতা-পুত্রের এই সম্পর্ক একটা পর্ব পর্যন্ত স্নেহ-সাহচর্যের। একটা পর্বের পর তা দ্বন্দ্বের। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পিতা-পুত্রের সম্পর্ক বঙ্গসংস্কৃতিতে নতুন রূপ লাভ করছে। তা সাহচর্যের, আবার দ্বন্দ্বের। অনেকের ক্ষেত্রেই দ্বন্দ্বই মুখ্য– মধুসূদনের সঙ্গে তাঁর পিতার সম্পর্ক দ্বন্দ্বেরই। বাংলা সিনেমায় কমল মিত্র বা ছবি বিশ্বাস যে দোর্দণ্ড প্রতাপ পিতার ভূমিকায় অভিনয় করতেন সেই ভূমিকা যুবাপুত্রের সঙ্গে পিতার ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্বকে তুলে ধরেছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় বিশ-শতকে এই দ্বন্দ্বের আদিকল্প দেখা যায়। রবীন্দ্র-দেবেন্দ্র সম্পর্ক বাংলা ছবির কমল মিত্র-উত্তমকুমার (দেয়া নেয়া), ছবি বিশ্বাস-উত্তমকুমার (সপ্তপদী) সম্পর্ক নয়। তার মধ্যে কত কী যে আছে– স্নেহে-শ্রদ্ধায়, বেহাগে-ললিতে, বলায় আর না-বলায়।
…ছাতিমতলা-র অন্যান্য পর্ব…
ছাতিমতলা পর্ব ৩৯: তেমন মাতৃসাহচর্য পাননি বলেই নৈর্ব্যক্তিকভাবে মা-সন্তানের সম্পর্ককে দেখতে পেরেছিলেন
ছাতিমতলা পর্ব ৩৮: রবি ঠাকুরের জন্মদিনের সাংস্কৃতিক ‘ফ্যাশন’ নিয়ে ফুট কাটা যাবে না কেন!
ছাতিমতলা পর্ব ৩৭: রবীন্দ্রনাথের মতে, ভোট সামাজিক মঙ্গলের নিঃশর্ত উপায় নয়
ছাতিমতলা পর্ব ৩৬: টক্সিক রিলেশনশিপ কি রবীন্দ্রনাথের লেখায় আসেনি?
ছাতিমতলা পর্ব ৩৫: রবীন্দ্রনাথ কি আড্ডা মারতেন?
ছাতিমতলা পর্ব ৩৪: চিনের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের সভ্যতা-ভাবনা ছিল কল্পনা বিলাস
ছাতিমতলা পর্ব ৩৩: পুরস্কার মূল্যকে হেলায় ফেরাতে জানে কবিই, জানতেন রবীন্দ্রনাথ
ছাতিমতলা পর্ব ৩২: তরুণ রবির তীক্ষ্ণ সমালোচক পরিণত রবীন্দ্রনাথ
ছাতিমতলা পর্ব ৩১: ভোটের মঞ্চে উড়ছে টাকা, এসব দেখে কী বলতে পারতেন রবীন্দ্রনাথ?
ছাতিমতলা পর্ব ৩০: শিক্ষিত ভদ্রলোকের ‘নাগরিকত্ব’ বিষয়ক ভাবনার সঙ্গে দেশের সাধারণ মানুষের যোগ তৈরি হচ্ছে না, বুঝেছিলেন রবীন্দ্রনাথ
ছাতিমতলা পর্ব ২৯: কলকাতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অপ্রেম রয়েছে যেমন, তেমনই রয়েছে আবছায়া ভালোবাসা
ছাতিমতলা পর্ব ২৮: মনের ভাঙাগড়া আর ফিরে-চাওয়া নিয়েই মধুসূদনের ভাষা-জগৎ– রবীন্দ্রনাথেরও
ছাতিমতলা পর্ব ২৭: বাংলা ভাষা কীভাবে শেখাতে চাইতেন রবীন্দ্রনাথ?
ছাতিমতলা পর্ব ২৬: ‘খানিক-রবীন্দ্রনাথ-পড়া’ প্রৌঢ়ের কথায় রবীন্দ্রনাথের প্রেম চেনা যাবে না
ছাতিমতলা পর্ব ২৫: সুকুমার রায় যে অর্থে শিশু-কিশোরদের মনোরঞ্জন করতে পারতেন, রবীন্দ্রনাথ তা পারেননি
ছাতিমতলা পর্ব ২৪: বিশ্বভারতীর ছাপাখানাকে বই প্রকাশের কারখানা শুধু নয়, রবীন্দ্রনাথ দেশগঠনের ক্ষেত্রেও কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন
ছাতিমতলা পর্ব ২৩: ধর্মবোধের স্বাধিকার অর্জনের কথা মনে করিয়ে দিয়েও রবীন্দ্রনাথ দেশের মানুষের সাম্প্রদায়িক মনকে মুক্ত করতে পারেননি
ছাতিমতলা পর্ব ২২: রামায়ণে রাম-রাবণের যুদ্ধ রবীন্দ্রনাথের কাছে ছিল গৌণ বিষয়
ছাতিমতলা পর্ব ২১: রবীন্দ্রনাথ পড়ুয়াদের সঙ্গে বৃষ্টিতে ভিজতেন, চাঁদের আলোয় গান গাইতেন
ছাতিমতলা পর্ব ২০: সুভাষচন্দ্র বসুকে তীব্র তিরস্কার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ!
ছাতিমতলা পর্ব ১৯: আবেগসর্বস্ব ধর্ম ও রাজনীতির বিরোধিতা করে অপ্রিয় হয়েছিলেন
ছাতিমতলা পর্ব ১৮: রবীন্দ্রনাথ কখনও গীতাকে যুদ্ধের প্রচারগ্রন্থ হিসেবে বিচার করেননি
ছাতিমতলা পর্ব ১৭: ক্রিকেটের রাজনীতি ও সমাজনীতি, দু’টি বিষয়েই তৎপর ছিলেন রবীন্দ্রনাথ
ছাতিমতলা পর্ব ১৬: রবীন্দ্রনাথ কি ক্রিয়েটিভ রাইটিং শেখানোর কিংবা কপি এডিটিং করার চাকরি পেতেন?
ছাতিমতলা পর্ব ১৫: কবি রবীন্দ্রনাথের ছেলে হয়ে কবিতা লেখা যায় না, বুঝেছিলেন রথীন্দ্রনাথ
ছাতিমতলা পর্ব ১৪: ছোট-বড় দুঃখ ও অপমান কীভাবে সামলাতেন রবীন্দ্রনাথ?
ছাতিমতলা পর্ব ১৩: পিতা রবীন্দ্রনাথ তাঁর কন্যা রেণুকার স্বাধীন মনের দাম দেননি
ছাতিমতলা পর্ব ১২: এদেশে ধর্ম যে চমৎকার অস্ত্রাগার, রবীন্দ্রনাথ তা অস্বীকার করেননি
ছাতিমতলা পর্ব ১১: কাদম্বরীকে বঙ্গজ লেখকরা মুখরোচক করে তুলেছেন বলেই মৃণালিনীকে বাঙালি জানতে চায়নি
ছাতিমতলা পর্ব ১০: পাশ্চাত্যের ‘ফ্যাসিবাদ’ এদেশেরই সমাজপ্রচলিত নিষেধনীতির প্রতিরূপ, বুঝেছিলেন রবীন্দ্রনাথ
ছাতিমতলা পর্ব ৯: দেশপ্রেম শেখানোর ভয়ংকর স্কুলের কথা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, এমন স্কুল এখনও কেউ কেউ গড়তে চান
ছাতিমতলা পর্ব ৮: অসমিয়া আর ওড়িয়া ভাষা বাংলা ভাষার আধিপত্য স্বীকার করে নিক, এই অনুচিত দাবি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথও
ছাতিমতলা পর্ব ৭: বাঙালি লেখকের পাল্লায় পড়ে রবীন্দ্রনাথ ভগবান কিংবা ভূত হচ্ছেন, রক্তমাংসের হয়ে উঠছেন না
ছাতিমতলা পর্ব ৬: যে ভূমিকায় দেখা পাওয়া যায় কঠোর রবীন্দ্রনাথের
ছাতিমতলা পর্ব ৫: চানঘরে রবীন্দ্রসংগীত গাইলেও আপত্তি ছিল না রবীন্দ্রনাথের
ছাতিমতলা পর্ব ৪: যে রবীন্দ্র-উপন্যাস ম্যারিটাল রেপের ইঙ্গিতবাহী
ছাতিমতলা পর্ব ৩: ‘রক্তকরবী’র চশমার দূরদৃষ্টি কিংবা সিসিটিভি
ছাতিমতলা পর্ব ২: ‘পলিটিকাল কারেক্টনেস’ বনাম ‘রবীন্দ্র-কৌতুক’
ছাতিমতলা পর্ব ১: ‘ডাকঘর’-এর অমলের মতো শেষশয্যা রবীন্দ্রনাথের কাঙ্ক্ষিত, কিন্তু পাননি
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
