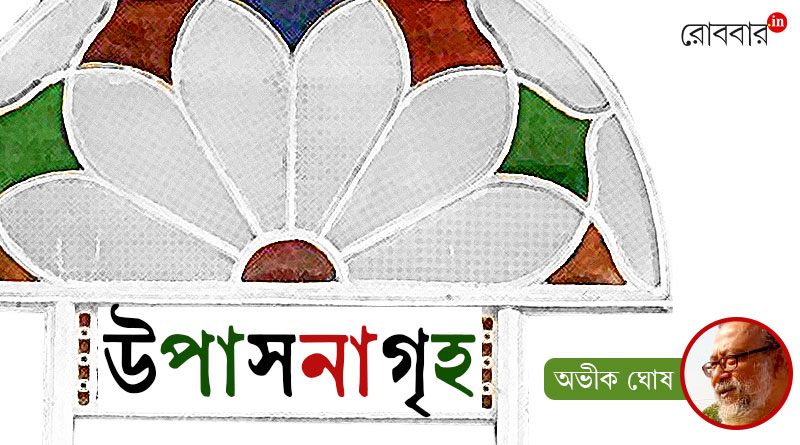
রবীন্দ্রনাথ বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, প্রকৃতি আমাদের কাউকেই বিশেষ ব্যক্তি বলে মানে না, তার কাছে আমরা সকলেই সমান, মানুষের সেজন্য দুঃখ আছে। কিন্তু মানুষের বিশেষত্ব তার সত্তার একটি প্রান্তমাত্র। একপ্রান্তে তার বিশ্ব, অন্যপ্রান্তে তার বিশেষত্ব, দুইয়ে মিলে মানুষের সম্পূর্ণতা, তার আনন্দ। মানুষের নিজত্বের মধ্যে যদি মানুষের যথার্থ আনন্দ থাকত, তাহলে নিজের একটা স্বতন্ত্র জগতের মধ্যে সে বাস করতে পারত।

১৬.
ঝড়বৃষ্টিতে মাঠে বেড়ানোর সময় এক ছাত্রের মনে হয়েছিল, প্রকৃতির এই বিরাট আন্দোলনের মধ্যে তার ব্যক্তিসত্তার যেন কোনও গুরুত্বই নেই! রবীন্দ্রনাথ সেকথা শুনে কী বলছেন, সেটাই আলোচনা করেছেন ‘বিশেষত্ব ও বিশ্ব’ শীর্ষক অভিভাষণে। বলছেন–
‘আমি তাকে বললুম: সেইজন্যেই তো বিশ্বপ্রকৃতির উপরে পৃথিবীসুদ্ধ লোক এমন দৃঢ় করে নির্ভর করতে পারে। যে বিচারক কোনো বিশেষ লোকের উপর বিশেষ করে তাকায় না, তারই বিচারের উপর সর্বসাধারণে আস্থা রাখে।
এ উত্তরে আমার ছাত্রটি সন্তুষ্ট হলেন না। তাঁর মনের ভাব এই যে, বিচারকের সঙ্গে তো আমাদের প্রেমের সম্বন্ধ নয়, কাজের সম্বন্ধ। আমার মধ্যে যখন একটি বিশেষত্ব আছে, আমি যখন ব্যক্তিবিশেষ, তখন স্বভাবতই সেই বিশেষত্ব একটি বিশেষ সম্বন্ধকে প্রার্থনা করে।’

রবীন্দ্রনাথ বোঝার চেষ্টা করেছেন, প্রকৃতি আমাদের কাউকেই বিশেষ ব্যক্তি বলে মানে না, তার কাছে আমরা প্রত্যেকেই সমান, মানুষের সেজন্য দুঃখ আছে। কিন্তু মানুষের বিশেষত্ব তার সত্তার একটি প্রান্তমাত্র। একপ্রান্তে তার বিশ্ব, অন্যপ্রান্তে তার বিশেষত্ব– দুইয়ে মিলে মানুষের সম্পূর্ণতা, তার আনন্দ। মানুষের নিজত্বের মধ্যে যদি মানুষের যথার্থ আনন্দ থাকত, তাহলে নিজের একটা স্বতন্ত্র জগতের মধ্যে সে বাস করতে পারত। তার সেই নিজস্ব জগতে, তার নিজের ইচ্ছামতো সবকিছু ঘটত, সূর্য উঠত অথবা উঠত না, কাউকে তার জানারও দরকার হত না, সুতরাং তার কোনও দুঃখ থাকত না। কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতির অটল নিয়মের সামান্যতম নড়চড় হওয়া যে অসম্ভব। নিজের অভিজ্ঞতার কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করছেন রবীন্দ্রনাথ। “একদিন বর্ষার সময় আমার মাস্তুল তোলা বোট নিয়ে গোরাই সেতুর নীচে দিয়ে যাচ্ছিলুম, মাস্তুল সেতুর গায়ে ঠেকে গেল। এ দিকে বর্ষা নদীর প্রবল স্রোতে নৌকাকে বেগে ঠেলছে, মাস্তুল মড়মড় করে ভাঙবার উপক্রম করছে। লোহার সেতু যদি সেই সময় লোহার অটল ধর্ম ত্যাগ করে, যদি এক ফুট মাত্র উপরে ওঠে, কিংবা মাস্তুল যদি এক সেকেন্ড মাত্র তার কাঠের ধর্মের ব্যত্যয় করে একটুমাত্র মাথা নিচু করে, কিংবা নদী যদি বলে ‘ক্ষণকালের জন্য আমার নদীত্বকে একটু খাটো করে দিই– এই বেচারার নৌকোখানা নিরাপদে বেরিয়ে চলে যাক’, তা হলেই আমার অনেক দুঃখ নিবারণ হয়। কিন্তু, তা হবার জো নেই– লোহা সে লোহাই, কাঠ সে কাঠই, জলও সে জল।”
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
আমাদের বিশেষত্বের বা ব্যক্তিত্বের প্রধান সম্বল হল ইচ্ছা। সেই ইচ্ছা নিজেকে নিয়ে তৃপ্ত নয়। সে চায় আপনার বাইরের সবকিছুকে। তাই যে বিশ্বকে নিয়ে আমার বিশেষত্ব আনন্দিত, সেই বিশ্বের কাছে বাধা তাকে পেতেই হয়। বিশ্ব নিজের নিয়মে সত্য না হলে এই আনন্দ দিতে পারত না। আমার ইচ্ছা যদি আপনার নিয়মেই আপনি বাঁচত, তাহলে ইচ্ছাই থাকত না। সত্যের সঙ্গে যোগ ঘটাতে হয় বলেই ইচ্ছা সার্থক।
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
লোহা-কাঠ-জলের ধর্মকে আমাদের জানতেই হয়, এবং তারা কোনও ব্যক্তিবিশেষের প্রয়োজন অনুসারে আপন ধর্মের কোনও ব্যতিক্রম করে না বলেই প্রত্যেক ব্যক্তি তাকে জানতে পারে। বিশ্ব আমার ইচ্ছার অধীন নয় বলেই তার সমস্ত বাধা অতিক্রমের চেষ্টায় বিজ্ঞান-দর্শন-শিল্পকলা-সাহিত্য-ধর্মকর্ম– যা কিছু মানুষের সাধনার ধন, তা সম্ভবপর হয়েছে।
আমাদের বিশেষত্বের বা ব্যক্তিত্বের প্রধান সম্বল হল ইচ্ছা। সেই ইচ্ছা নিজেকে নিয়ে তৃপ্ত নয়। সে চায় আপনার বাইরের সবকিছুকে। তাই যে বিশ্বকে নিয়ে আমার বিশেষত্ব আনন্দিত, সেই বিশ্বের কাছে বাধা তাকে পেতেই হয়। বিশ্ব নিজের নিয়মে সত্য না হলে এই আনন্দ দিতে পারত না। আমার ইচ্ছা যদি আপনার নিয়মেই আপনি বাঁচত, তাহলে ইচ্ছাই থাকত না। সত্যের সঙ্গে যোগ ঘটাতে হয় বলেই ইচ্ছা সার্থক।
কবি যখন নিজের ভাবের আনন্দকে বিশ্বের আনন্দ করতে চান, তখন তাঁকে এমন ভাষা আশ্রয় করতে হয়, যা সকলের ভাষা। নিজের খেয়ালমতো কবি সে ভাষাকে অস্বীকার করতে পারেন না। আবার সকলের ভাষা আছে বলেই কবির বিশেষ আনন্দ আপনাকে বিশ্বের আনন্দ করে তুলতে পারে। এই বিশ্বের ভাষা-নিয়মকে মানার মধ্যে এই দুঃখ আছে যে, সে আমাকে খাতির করে না, কিন্তু এই দুঃখকে কবি আনন্দে স্বীকার করেন। ভাষার সৌন্দর্যের যে বিশ্বনিয়ম তাকে সে নিজের রচনার মধ্যে ক্ষুণ্ণ করে অসম্মান করতে চায় না। কবির বিশেষত্ব যত মহৎ হয়, ততই বিশ্বনিয়মের সমস্ত শাসন সে স্বীকার করে। এই বিশ্বকে স্বীকার করার দ্বারাই তার বিশেষত্ব সার্থক হয়ে ওঠে।
পশু বিশ্বের কাছ থেকে কেবলই নেয়। মানুষ যেমন বিশ্বের কাছ থেকে নানারকম করে নেয়, তেমনই নানারকম করে দিতেও চায়। তার সৌন্দর্যবোধ, তার কল্যাণচেষ্টা কেবলই সৃষ্টি করতে চায়, না করতে পারলে পঙ্গু হয়ে খর্ব হয়ে যায়। নিতে গেলেও তার নেওয়ার ক্ষেত্র বিশ্ব, দিতে গেলেও তার দেওয়ার ক্ষেত্র বিশ্ব। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, “তুমি যদি বল ‘বিশ্বপ্রকৃতি আমার ব্যক্তিগত বিশেষত্বকে মেনে চলে না বলে আমার দুঃখবোধ হচ্ছে’ তখন তোমাকে বুঝে দেখতে হবে– মেনে চলে না বলেই তোমার আনন্দ। বিশেষকে মানে না বলেই সে বিশ্ব এবং সে বিশ্ব বলেই বিশেষের তাতে প্রতিষ্ঠা। দুঃখের একান্ত অভাব যদি ঘটত, অর্থাৎ যদি কোথাও কোনো নিয়ম না থাকত, কেবল আমার ইচ্ছাই থাকত, তা হলে আমার ইচ্ছাও থাকত না; সে অবস্থায় কিছু থাকা না– থাকা একেবারে সমান।”
(চলবে)
…পড়ুন উপাসনাগৃহ-র অন্যান্য পর্ব…
পর্ব ১৫। যিনি অসীম তিনি সীমার আকর হয়ে উঠেছেন ইচ্ছার দ্বারা, আনন্দের দ্বারা
পর্ব ১৪। সংসার যেন স্যাকরা গাড়ির গাড়োয়ান আর আমরা ঘোড়া
পর্ব ১৩। জন্মোৎসবের ভিতরকার সার্থকতা খুঁজেছিলেন রবীন্দ্রনাথ
পর্ব ১২। বিশ্বপ্রকৃতির কাছে সামঞ্জস্যের সৌন্দর্য শিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ
পর্ব ১১। মানুষের নববর্ষ আত্মসংবরণের, দুঃখস্বীকারের নববর্ষ
পর্ব ১০। যে পাওয়ার স্বাদ পেলে মৃত্যুভয় চলে যায়
পর্ব ৯। আমাদের অবস্থা অনেকটা পৃথিবীর গোড়াকার অবস্থার মতো
পর্ব ৮। রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি, মানুষকে ত্যাগ করা মানুষের ধর্ম নয়
পর্ব ৭। সমগ্র অখণ্ড সৃষ্টির সৌন্দর্য একটি গানের মতো পূর্ণ
পর্ব ৬। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন উপনিষদ ভারতবর্ষের ব্রহ্মজ্ঞানের বনস্পতি
পর্ব ৫। ‘ঈশ্বর সর্বত্র আছেন’ কথাটা অভ্যাসের মতো হয়ে গেলে তার মধ্যে আর প্রাণ থাকে না
পর্ব ৪। আনন্দের ভাষা শেখাকেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন মুক্তির পথ
পর্ব ৩। সমগ্রের সঙ্গে যোগসাধনে আমাদের মঙ্গল
পর্ব ২। আমাদের চাওয়ার শেষ নেই, কারণ আমরা অনন্তকে চাই
পর্ব ১। ‘অসতো মা সদ্গময়’ মন্ত্রের অর্থ কৈশোরে বুঝিনি, শব্দগুলো ভালো লেগেছিল খুব
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
